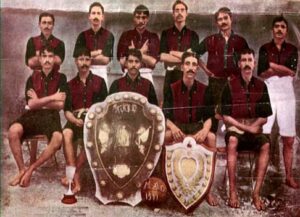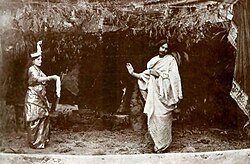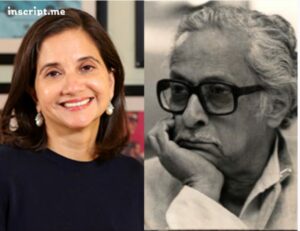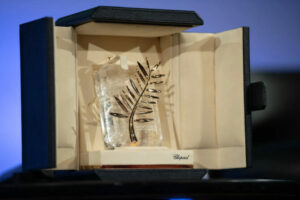শতবর্ষে গুরু দত্ত! যিনি মেলোড্রামাকে নিয়ে যেতেন মহাকাব্যে
Guru Dutt Centenary Year: আমার বিনীত ধারণা হিন্দি চলচ্চিত্রে তিনি, গুরু দত্ত-ই শীর্ষবিন্দু। ওই ‘তিনি’ই অদৃষ্ট ও অশ্রুতকে স্পর্শ করতে পারলেন প্রথম আরব সাগরের উপকূলে।
যেমন ‘গগ্যাঁর চেয়ার’, তেমনই গুরু দত্তের কোনও বারান্দার টুকরো— আসলে তারা ভগ্নস্তুপ ও আত্মবিলাপ। ভারতীয় চলচ্চিত্রে গুরু দত্ত (১৯২৫-’৬৪) এমনই এক স্রষ্টা, যাঁর চিত্রমালার স্তর থেকে স্তরান্তরে ভ্রমণকালে আমাদের নজর এড়ায় না তাঁর ক্রমউন্মোচনশীল আত্মপ্রতিকৃতিসমূহ। কী অলৌকিক সমাপতন যে ঋত্বিক ঘটক ও তাঁর জন্ম একই বছরে! দু-জনেরই পানপাত্র থেকে উপচে পড়ল দৃশ্য ও ছবি। কী বিধুর দু-জনের প্রস্থান! ঋত্বিক ভারতীয় চলচ্চিত্রের সেই অসমসাহসী অভিযাত্রী যিনি মেলোড্রামাকে উন্নিত করেন মহাকাব্যের স্তরে; গুরু দত্তের যাত্রা অত সুদূরে নয়, কিন্তু যখনই ‘পিয়াসা’ (১৯৫৭) ‘কাগজ কে ফুল’ (১৯৫৯), ‘সাহেব বিবি অউর গুলাম’ (১৯৬২) আমাদের মনোযোগ দাবি করে, দেখতে পাই অশ্রুনদীর পরপারে এক নির্জন ও রিক্ত কবিকে। আজ যখন বিপুল গৌরবে ভারতীয় চলচ্চিত্রে ঋত্বিক ঘটক ও গুরু দত্তের শতবর্ষ উদযাপিত হচ্ছে তখন আমার বিনীত ধারণা হিন্দি চলচ্চিত্রে তিনি, গুরু দত্ত-ই শীর্ষবিন্দু। ওই ‘তিনি’ই অদৃষ্ট ও অশ্রুতকে স্পর্শ করতে পারলেন প্রথম আরব সাগরের উপকূলে। আজ আর অস্বীকারের উপায় নেই যে গুরু দত্তের গীতিকবিতা আসলে ইতিহাসের তরঙ্গভঙ্গ।
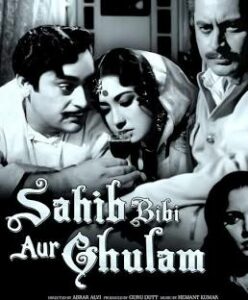
'সাহেব বিবি অউর গুলাম'-এর পোস্টার
আমাদের দেবতারা যে সবাই স্বর্গের উদ্যানবাসী তা তো নয়। অনেকে মর্তের গলিতে-উপগলিতে জনপ্রিয়তায় লুকিয়ে থাকেন ছদ্মবেশে। যেমন, গুরু দত্ত পাড়ুকোন। সারা দেশ তাঁকে গুরু দত্ত নামেই জানে আর তিনিও জানতেন যে, অন্য-অন্য শিল্পমাধ্যমে অন্তত আপেক্ষিক স্বাধীনতা আছে সমাজবিরহিত বোধ করার; কবিতা বা চিত্রকলা অন্তত কলাকৈবল্যবাদের ছলনায় মুখ লুকোতে পারে, কিন্তু সিনেমার তেমন আড়াল নেই। সিনেমা জন্মসূত্রেই জনপদবধূ। কবি শার্ল বোদলেয়ার যে মর্তে লিখেছিলেন ‘পাপের ফুল’, গুরু দত্তের সৌজন্যে ‘পিয়াসা’-সূত্রে এতদিনে সেই কুসুমে লেগে থাকা শিশিরবিন্দু ঝরে পড়ল স্বর্গের বাগানে, ‘প্যারিস স্প্লিন’-এর সেই বিখ্যাত গদ্যকবিতা মনে পড়ে— কবি যেখানে নিজের মহিমা হারিয়ে অসনাক্ত রাজকুমার, গুরু দত্তের কবিও তেমনই শিরোভূষণহীন। ‘পিয়াসা’ কখনওই কাব্যের শিখরপ্রদেশ ছুঁতে পারেনি কিন্তু শিল্পের সম্ভ্রম যে কবিকে ক্লান্ত করে তা বুঝিয়ে দিয়েছে সভ্যতার রুগ্ন বিকেলে। আমাদের জনপ্রিয় ছবির জগতের ‘পিয়াসা’-র মতো কনে-দেখা-আলো আর নেই।
আরও পড়ুন-
‘ভাবা প্র্যাকটিস’ নয়, আজ ঋত্বিককে ভুলতে পারলেই কেন সুবিধা বাঙালির?
এক-একটি নারী যেন ঈশ্বরীর মতো। সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে থাকেন ওয়াহিদা রহমান: নরকের সুরবিস্তার! গুরু দত্ত চলকে-ওঠা আলোর টুকরোয় তাঁর গুলাবকে দেখলেন জীবনের পানপাত্রে। বাসনার বহ্নিশিখা কিন্তু এক অলৌকিক দৃষ্টিপাত যা সহসা অন্তর্হিত হয়; আবার অমরতা পরমুহূর্তেই যাকে ফিরিয়ে দেয় সময়ের বেলাভূমিতে। ‘আজ সাজন মোহে অঙ্গ লাগা লো’— গানটিতে গুলাব তার মৃত্যুকে, জীবন অধিক জীবনকে লুকিয়ে রাখে চোখের পল্লবে, মুখের রেখায় জমে থাকে শ্রাবস্তীর কারুকার্য। অথবা ক্রেন শট-এ অন্তিম দৃশ্যের ঠিক আগের দৃশ্য, কামনার দগ্ধাবশেষ এই নারী দয়িতকে স্পর্শ করতে চায়, তবু বোঝে কবিতার নৈকট্যে তিনি কত সুদূর। দেহের উৎসব শেষে ইতিহাস গুলাব-কে পুনর্নির্মাণ করে ভোরের কল্লোলে। এই নারী, যুগপৎ পতিতা ও উত্থিতা। আমাদের পাপ ও পুণ্যের মোহনা হয়ে যায় এক ধরনের স্বস্তিবাচন ও স্থিরতার পটভূমি। ‘shall I not see you till eternity!’ ‘দেবদাস’ উপন্যাসটি অবশ্য শান্তভাবে আমাদের জানায় ‘পিয়াসা’র গুলাব চন্দ্রমুখীর সহোদরা, তাঁর ছায়াসঙ্গিনী। সেই যে কবে আমরা ওয়াহিদাকে প্রণয়পিপাসা পাঠাই ‘শ্রাবণ ঘন গহন মোহে’ আজও তা নিরসন হল না, আজ মনে হয় এই যুবতী স্থির বিজুরী, আত্মার পানীয়।
ভাগ্যিস কবি বিজয় ভূমিকায় নির্বাচিত অভিনেতা দিলীপকুমার প্রথম দিনের শুটিং-এ আসতেই ব্যর্থ হলেন, আর ঠিক দু-বছর আগে বিমল রায়ের ‘দেবদাস’ চরিত্রের দায় নিতে হওয়ায় দিলীপকুমারের আশঙ্কা হয়েছিল যে তাঁকে পুনরাবৃত্তি করতে হবে। অগত্যা গুরু দত্ত স্বয়ং অভিনয়ের দায়িত্ব নেওয়ায় চলচ্চিত্রের আখ্যান জীবনের তটরেখা পার হয়ে গেল। যা হতে পারত কোনও কবির নির্বিকল্প জীবনী, তা হয়ে দাঁড়াল স্রষ্টার আত্মাবিবরণী; পূর্বনির্ধারিত আত্মহননের আখ্যান। গুরু দত্ত, গীতা দত্ত, ওয়াহিদা রহমান এমন এক স্তব্ধ ত্রিকোণ, যা চিত্রনাট্যের অপর পারে।

'কাগজ কে ফুল' ছবির দৃশ্য
গুরু দত্তকে হয়তো রোম্যান্টিক গোত্রের ভাবাই সঠিক। এক প্রান্তিকতা থেকেই গুরু দত্ত জীবনবিষয়ে তাঁর মন্তব্য শুরু ও শিল্পকর্মের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁর আত্মজৈবনিকতা রূপায়ণের দিক থেকে মেলোড্রামাকেই বেছে নেয়। অথচ ওই মেলোড্রামায় ইতিহাসের সমর্থন আছে। শিল্পায়ন ও শহরায়নের চাপ গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই গান্ধী-নেহেরুর স্বপ্নকে ফিকে করে দেয়। তাতে যেমন দেশে আধুনিকতার পরিসর উন্মোচিত হয়, তেমনই সামাজিক স্থানচ্যুতি মর্মান্তিক হয়ে ওঠে। গুরু দত্তের প্রধান কৃতিত্ব, রাষ্ট্র ও সংস্থা বনাম ব্যক্তির সংঘাতকে প্রধানত নারী চরিত্রের বিভঙ্গে তিনি নথিভুক্ত করেন। ‘পিয়াসা’-র গুলাব বা ‘সাহেব বিবি অউর গুলাম’-এর ছোটি বহু দৃষ্টান্ত মাত্র। অর্থাৎ গুরু দত্তের সামাজিক ছায়াছবি রূপান্তরের নৈতিক উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তাকে ব্যক্তির, বিশেষত নারীর চরিত্রায়নে দেখতে চায়। যা ঐতিহাসিক, তা যখন পারিবারিক সমস্যায় পর্যবসিত হয় তখন মেলোড্রামার স্বর্ণসম্ভাবনা। আর এই মুহূর্তটি পপুলার হিন্দি ছবিতে গুরু দত্তের প্রতি চিরনিবেদিত।
আরও পড়ুন-
সত্যজিতের থেকে ক্যামেরার স্বাধীনতা পাননি সৌমেন্দু রায়
কিংবদন্তি থেকে মহাকাব্যের উত্তরণের পথে গুরু দত্তের নিজস্ব ত্রুটিসমূহ তিনি গোপন করেননি। বরং দেশভাগকে নিয়ে ঋত্বিক ঘটক যেভাবে সমকেন্দ্রিক বৃত্তগুলি রচনা করেন, যা ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক দরজাগুলি পার হয়ে স্বর্গারোহণপর্ব সমাপ্ত করে, তার অভাবে গুরু দত্ত কীভাবে আত্মধ্বংসের অভিজ্ঞতাগুলিকে সম্মুখবর্তী করতে থাকেন, সেই আলোচনায় আমরা সংস্কারহীনভাবেই প্রবেশ করতে পারি। অতিরিক্ততার কথা বলার সময় কিছুতেই সংশ্লিষ্ট শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবন সংকটের বিষয়ে আমরা আলোচনা করব না, যা গুরু দত্তের ছবি সম্পর্কে মন্তব্য করার সময় একটি জাতীয় সংকট তৈরি করে। বাস্তববাদ ও মেলোড্রামার সংঘাত-বর্ণনায় গুরু দত্ত চলচ্চিত্র বাস্তবের নকলনবিশি থেকে উদ্ধার পেয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। গুরু দত্ত এমন এক পরিসর যেখানে আধুনিক চলচ্চিত্রের আরোহণ ও অবরোহণ, দুই অনুভূত হয়। ‘পিয়াসা’-র বিজয় যে একা ও দণ্ডিত, তা কবিদের নিয়তি। কিন্তু খেয়াল করার যে, এই আউটসাইডার জীবনেও বেছে নিচ্ছেন এমন একজনকে যিনি বেশ্যা, রূপোপজীবিনী, ফলে আউটসাইডার। এক প্রান্তিকতা থেকে গুরু দত্ত তাঁর জীবনবিষয়ে মন্তব্যসমূহ শিল্পকর্মে অন্তর্ভুক্ত করেন।

'পিয়াসা'-র পোস্টার
আত্মজৈবনিকতা ও মেলোড্রামার অনন্যতার দিকে তাকালে গুরু দত্তকে প্রায় ঋত্বিকের সহযোদ্ধা মনে হয়। প্রতিভার বিস্তর ফারাক থাকলেও, কী আশ্চর্য দু-জনেই অশ্রুরেখাকে ছুঁতে পেরেছেন। ‘পিয়াসা’ যখনই দেখি তখনই ভাবি স্বভাবের নৈরাজ্য পার হয়ে থরে-থরে উপহারের সম্ভার রয়ে গেছে আমাদের জন্য। এ-কথা ‘কাগজ কে ফুল’ সম্পর্কেও সত্যি। ছোটি বহু মিনাকুমারী যে-মাংসের কবিতা রচনা করেছেন তা ভারতীয় উপমহাদেশে বিরল। আলোর এমন প্রত্যক্ষ অবদান সে-যুগের ক-টা ভারতীয় ছবিতে ছিল? যে-আলো গুলাব-কে লক্ষ করে তা অরসন ওয়েলস-এর ‘সিটিজেন কেন্’-কে প্রণতি জানিয়ে, যে-আলোয় উন্মুক্ত জানালা দিয়ে জীবনের পাণ্ডুলিপি উড়ে যেতে থাকে, যেভাবে স্থির শূন্যতায় চাহনি মেলে দেন মালা সিনহা ও গুলাব ভিন্ন দুটি মুহূর্তে, তা চিরদিনের জন্য গুরু দত্তকে স্বাক্ষরিত করে রাখে। তখন পশ্চিমভারতে মূলত মিড শট ও লং শট-এ কাজ চালানো হত, গুরু দত্ত এস্টাবলিশমেন্ট শট-এর পরে-পরে ক্লোজআপ শট-এর সূচনা করেন। অর্থাৎ ৭৫ মিমি, ১০০ মিমি লেন্স মুম্বাই ছবিতে ক্লোজআপ নেওয়ার জন্য তিনিই ব্যবহার করেন প্রথম, আর ওয়াহিদা রহমানকে দেখে আসমুদ্র হিমাচল ভাবে ‘ওরে চিত্ররেখাডোরে বাঁধিল কে’।
হয়তো গানের কথা বলা যেতে পারত। কী গান, এ শুধু গানের দিন। শচীন দেববর্মণ-সাহির লুধিয়ানভির যুগলবন্দি, যে না বুঝতে পারে সে-পাপিষ্ঠ নিপাত যাক। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুররচনা যে ‘সাহেব বিবি অউর গুলাম’-এ না বুঝতে পারে, তার কোনও পরিত্রাণ নেই। হিন্দি সিনেমায় বৈধ-সংগীতের অনুপ্রবেশ ঘটল, এই যে অতিশয়োক্তি, এই অতিশয়োক্তিই মাত্রাবৃত্তের অধীন। গুরু দত্ত এমন একজন মানুষ যিনি আর কোনও ছবি রচনা না করে যদি শুধু ‘পিয়াসা’-ই রচনা করতেন, ভারতীয় চলচ্চিত্রে তিনি স্মরণীয় শুধু নন অবিস্মরণীয় হয়ে থাকতেন। গুরু দত্ত এমন এক চলচ্চিত্র সমাবেশ যা আসলে পরিত্যক্তদের জলসাঘর। শতবর্ষের প্রণাম!



 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp