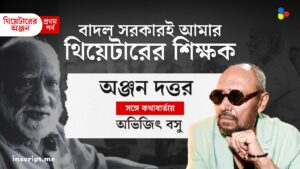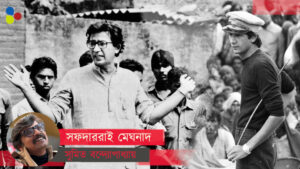নসফেরাতু ২০২৪: যৌন-অবদমন, নৈতিকতা আর ভ্যাম্পায়ারের নয়া নির্মাণ
Robert Eggers' Nosferatu: মোরগের ডাকে শহরবাসী উঠে দেখে— একটি মেয়ে যে যৌন-তৃপ্তির প্রশ্নে ঈশ্বরের অথরিটিকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল, তার প্রায়শ্চিত্ত কীভাবে লেখা হচ্ছে।
মাটি এবং বীজ— বাইবেল-রূপকে মনুষ্যজাতি এবং ঈশ্বরবাক্য। ঈশ্বরের রাজ্যে এই দুইয়ের মাঝে ঐশী চুক্তি। সার্থক সিঞ্চনে তা হতে পারে ফলদায়ী বৃক্ষ। কিন্তু যদি এ চুক্তি লঙ্ঘন করে কেউ? বীজ যদি হয় শয়তানের? তাহলে আটকানো যাবে না বিষবৃক্ষের আবাদ। ফলবে মহামারী। আর সেই শয়তানের সন্তান, যার ছায়ায় নেমে আসবে এ গজব— নসফেরাতু, ওরফে ‘দ্য ভ্যাম্পায়ার’। ঊনিশ শতকের চৌকাঠ সদ্য টপকানো ইওরোপের গাঁ-মফসসল— যেখানের মধ্যযুগীয় জ্ঞানকাণ্ডে যুক্তিবাদের কুঠার চালাননি কোনও পরশুরাম, সরলবর্গীয় আঁধারের পাহাড়ি বাঁকে দীপায়নের চিলতে আলো তাই পথ খুঁজে পায়নি তখনও— সেখানেই ঘনিয়ে ওঠে এমন একটি কাহিনি।
১
স্থান ১৮৩৮-এর জার্মানির শহরতলি উইসবর্গ। সেখানের এক রিয়েল-এস্টেট ফার্মের কর্মচারী থমাস। কোন এক পাহাড়পুরের কাউন্ট সমতলে বাসা কিনবেন, আর দলিলপত্র নিয়ে আইনি হস্তান্তর করতে যেতে হবে বেচারা থমাসকে, তাও কিনা সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীকে বন্ধু আর বন্ধুপত্নীর ভরসায় ছেড়ে। বিরহকাতর স্ত্রীকে দ্রুত ফিরবার আশ্বাস দিয়ে ওপরওয়ালার নির্দেশে থমাস ঘোড়া ছোটায় দুর্গের উদ্দেশ্যে। মাঝে একরাত তার কাটে জিপসি বস্তিতে। জিপসিরা সাবধান করে— দুর্গটা বেয়াড়া আর অশুভ, আর কাউন্ট তো বিলকুল মনিষ্যি নয়, নসফেরাতু! কিন্তু থমাসের মতো আলোকপ্রাপ্ত শহুরে যুবকেরা কবেই বা কেয়ার করেছে এসব কুসংস্কারের! যদিও ওরলকের প্রাসাদদুর্গে এসে থমাসকে অচিরেই বুঝতে হয় নিজের ভুল। দলিলের কাজের ফাঁকে থমাসের কাছে তাঁর স্ত্রীর ছবিওয়ালা এক লকেট দেখে নিঃসঙ্গ কাউন্ট কামনামদির হন। জাহাজপথে নিজের উইসবর্গ যাত্রার ব্যবস্থা করেন। জাহাজ শহরে এসে পড়তেই কফিনবোঝাই অপবিত্র মাটি থেকে ইঁদুরের পাল বেরিয়ে শহরে ছড়ায় মহামারী— ব্ল্যাক ডেথ। এসবের মধ্যেই কোনওক্রমে নিজেকে মুক্ত করে বাড়ি ফিরে আসে দুর্বল রক্তশূন্য থমাস।
হামেশাই দেখা যায়, এসময় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ ততটা কাজে আসে না যতটা আসে গুপ্তজ্ঞান। অমনই এক পুঁথি থেকে জানা যায়, শহরের ওপর নেমে আসা অভিশাপ-মোচনে চাই অপাপবিদ্ধা নারীর রক্তের বিনিময়— স্বেচ্ছাসমর্পণ ও আত্মত্যাগ। যদি নিশাচর নসফেরাতুকে মাটির আড়ালে লুকিয়ে পড়া থেকে বিরত রাখা যায় পাখিডাকা ভোর অবধি, হাজির করা যায় প্রকাশ্য সূর্যের আলোয়— তাহলেই তার চিরতরে ধ্বংস সম্ভব। ছল করে থমাসকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে এলেন তাই নিজেকে সঁপে দেয় কাউন্ট ওরলকের কাছে। ওরলক আসে। রক্তপান করে। ভোরের মোরগ ডাকে, তবু রক্তের নেশায় বুঁদ ওরলককে মাথা তুলতে দেয় না এলেন। ক্রমশ সূর্য উঁকি মারে জানালায়। ওরলক যখন পুড়ে ধোঁয়া হচ্ছে, এলেন তখন আর বেঁচে নেই।
আরও পড়ুন- রক্ত নয়, শসা-গাজর খেতেন বাস্তবের ‘ড্রাকুলা’?

১৯২২-এর 'নসফেরাতু'-তে কাউন্ট ওরলক
‘নসফেরাতু : দ্য সিম্ফনি অফ হরর’, এমনই কাহিনিসূত্রের, জার্মান পরিচালক এফ মুরনাও পরিচালিত ১৯২২ সালের একটি নির্বাক ছায়াছবি। ভ্যাম্পায়ার কাহিনির দুনিয়ায় সবচেয়ে চর্চিত নাম যে ‘ড্রাকুলা’, এই সিনেমাটি আন-অফিসিয়ালি তারই প্রথম চলচ্চিত্রায়ন হিসেবে পরিকল্পিত হয়েছিল। ব্রাম স্টোকারের স্ত্রীর অনুমোদন না পাওয়ায় ‘ড্রাকুলা’-র মূল কাহিনিকাঠামোয় চরিত্রদের নাম ও ঘটনার কিছু অদল-বদল ঘটিয়ে ছবিটি করেছিলেন মুরনাও, যথা— ‘ড্রাকুলা’-র জোনাথন হারকার, মিনা হারকার ও কাউন্ট ড্রাকুলা ‘নসফেরাতু’ (১৯২২)-তে যথাক্রমে থমাস হাটার, এলেন হাটার ও কাউন্ট ওরলক। স্থান হিসেবে ইংল্যান্ড নয়, ১৮৩৮ এর জার্মানির উইসবর্গ নামের এক শহরে এই কাহিনির শুরু। যদিও নাম-ধাম বদলে শেষরক্ষা হয়নি, স্টোকারের স্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে আইনি মারপ্যাঁচে সিনেমাটির বিপণনে বসে নিষেধাজ্ঞা। ইওরোপে সিনেমার কপিগুলি নষ্ট করা হয় কিন্তু জাহাজে আমেরিকা পাড়ি দিয়ে বেঁচে যাওয়া কিছু কপির দৌলতে পরবর্তীতে ‘কাল্ট হরর’ হিসেবে অমর হয়ে যায় মুরনাওয়ের এই এক্সপ্রেশনিস্ট ঘরানার ছবি। ড্রাকুলার হুবহু অনুসরণ নয় বলেই ১৯২২ সালের এই ছবির কাহিনি ড্রাকুলার থেকে আস্বাদে অনেকটাই আলাদা। ১৯২২-এর 'নসফেরাতু'-র ভ্যাম্পায়ার চেহারাতেও 'ড্রাকুলা' (১৯৩১) ছবির ভ্যাম্পায়ারের মতো ব্যাকব্রাশড রোম্যান্টিক হিরো-মার্কা নয়, বরং ঢের বেশি অমানুষিক ও উদ্ভট। বাদুড় নয়, ইঁদুরের পাল তার হার্মাদ-পল্টন এবং অ্যানিমিয়া নয়, প্লেগ তার অভিশাপের সংক্রমণ।
‘ড্রাকুলা’-র কপিরাইট উঠে যাওয়ার পর ‘নসফেরাতু : আ সিম্ফনি অফ হরর’ (১৯২২) এর ‘নসফেরাতু দ্য ভ্যামপায়ার’ (১৯৭৯) নামেও একটি সবাক পুনর্নির্মাণ হয়। মুরনাওয়ের আইনি হারের বদলা নিতেই হয়তো ‘ড্রাকুলা’-র চরিত্রসমূহের নাম এবার দাপটের সঙ্গে নিজের ছবিতে ব্যবহার করেছিলেন পরিচালক ভার্নার হেরৎসগ। এই ছবির কাহিনিতে বিশিষ্টতা এই যে— শেষ দৃশ্যে ভ্যাম্পায়ার মরে না, কাউন্টের জীর্ণ লেবাসটি পরিত্যাগ করে গ্রহণ করে জোনাথনের সোমত্থ শরীরখানা।


'নসফেরাতু'-র ১৯২২ ও ১৯৭৯ সিনেমা দু'টির পোস্টার
আবার একই কাহিনি যখন ফেরে ২০২৪ সালে রবার্ট এগার্সের নবনির্মাণে— তাতে মিলেমিশে যায় নতুন ব্যাখ্যার সম্ভাবনা। রবার্ট এগার্স, একচল্লিশ বছরের এই তরুণ পরিচালক গথিক ও ফোক হররের উপস্থাপনায় ইতিপূর্বে যে মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন তা থেকে স্পষ্ট— যৌনতা, মিথ এবং মনস্তত্ত্ব, এই তিনটি উপাদানের ব্যবহার তাঁর হররকে শিল্পরূপ দেয়। দ্য উইচ (২০১৫), দ্য লাইটহাউস (২০১৯) দ্য নর্থম্যান (২০২২) পর গতবারের শীতে এগার্স রোমানিয়ার কার্পেথিয়ান পাহাড়ের ওপার থেকে যে বিস্মৃত নসফেরাতু-কাহিনিকে ফিরিয়ে আনলেন এবার নজর ফেরানো যাক তাতে।
২
১৯২২-এর মূল কাহিনিতে— বন্দি থমাসের কাছে এলেনের ছবি দেখার আগে অবধি নসফেরাতু থুড়ি ওরলকের সঙ্গে এলেনের কোনও পূর্বযোগ ছিল না। ছিল না বলেই, স্বামীর ভুলের দায়ে এলেনের নির্দোষ আত্মত্যাগটি যেন তাঁর প্রতি কাব্যিক অবিচার। শতবর্ষ আগের এই অবিচার শুধরে ওঠা, একই সঙ্গে শিল্পের নীতিতেও নিরপেক্ষ থাকার দায়ে এগার্স যে পন্থা নিলেন তা হলো— কাহিনিতে ওরলকের সঙ্গে এলেনের একটি পূর্বসূত্র যোগ করা, এলেনকে যথোচিত ট্রাজিক নায়ক হিসেবে গল্পে নিয়ে আসা— যেখানে এলেনের একটি ‘হ্যামারশিয়া’ বা 'গলতি' প্রতিষ্ঠা করে তার উপরেই পল্লবিত করা সম্ভব হবে এলেনের ভাবী-পতনের বা আত্মত্যাগের কেয়ামতটি। এগার্স-আখ্যানে তাই এলেনকে কাহিনির কেন্দ্রে এনে ফেলা হয়। এলেনের শৈশব ও কুমারী বয়সের এক স্খলনেই সেই সমস্যার বীজটি রেখে দেওয়া হয়, ভাবীকালে যেখান থেকে উঠে আসবে নসফেরাতুর মতো আদিম শ্বাপদ। মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের পবিত্র নির্দেশ, বিবাহ-পূর্বের যৌন-বিচ্যুতি থেকে নিজের দেহ ও আত্মাকে রক্ষাই কর্তব্য। ‘নসফেরাতু’ (২০২৪)-তে কুমারী বয়সের এলেনের ‘পাপ’— সে অবদমিত কামনা আর একাকীত্বে এই ঐশী চুক্তি লঙ্ঘন করে বসে, এক অজানা দুষ্টসত্তাকে দেহে আবাহন করে ফেলে, অজ্ঞাতসারেই, কিন্তু তাই-ই কি পতনের জন্য যথেষ্ট নয়? কারণ এই সত্তাই গল্পে বাইবেল-কথিত ‘Son of Belial’, (হিব্রু বাইবেলে শয়তানের নামান্তর)। প্রাথমিকভাবে তৃপ্ত এলেন এই 'গলতি' থেকে পরে সরে আসতে চায়— কিন্তু শাইলক আর শয়তানের সুদ আদৌ এত সস্তায় চোকানো যায়? এরপরই এগার্স-কাহিনিতে এলেনের রোগলক্ষণ, দুর্বলতা, মৃগীর উপসর্গ দেখা দেয়। চিরস্থায়ী হয় মেলাঙ্কলিয়া (ডিপ্রেশন)।
এর অনেককাল পরে ফ্রয়েড নামে এক মনোচিকিৎসক বলবেন, এ ব্যাধি আদতে মানসিক। কুমারী বয়সের অনৈতিক স্খলনের স্মৃতি ও তজ্জনিত অপরাধবোধই বিবাহ-পরবর্তী সময়ে অচেতনের আগল ভেঙে নিজেকে জাহির করছে ‘হিস্টিরিয়াক ফিট’ হিসেবে। কিন্তু বাইবেল বলবে, ‘বিবাহবন্ধন’ ঐশী চুক্তির একটি, স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র লক্ষণরেখা টপকাতে পারে না শয়তানও। তাই বিয়ের পরই ব্যামো কমে আসে এলেনের— যতদিন না স্বামীর সঙ্গে দূরদেশে মোলাকাত হয় দুষ্টসত্তা নসফেরাতুর, লকেটে এলেনকে চিনতে পেরে নিজের ‘অধিকার’ ফেরত নিতে উদ্যোগী হয় সে। এখানে এগার্স দেখান, রিয়েল-এস্টেট চুক্তির আড়ালে ‘স্বামী’-কে ঠকিয়ে তার স্ত্রীর স্বত্বটাই হাতবদল করে নেন ধূর্ত ওরলক। কিছু 'গলতি' থাকে থমাসেরও, না-পড়ে তড়িঘড়ি সই করে ফেলে থমাস, খুলে যায় বিবাহবন্ধনের গেরো (পরে এই চুক্তির জোরেই নসফেরাতু হানা দেবে এলেনের শয্যায়, তাঁর সমর্পণ চাইবে, অন্যথায় একে একে মারবে তাঁর প্রিয়জনদের)। দু’টি নরনারীর জীবনে এভাবেই সংকট ঘনিয়ে ওঠে। ১৯২২ থেকে চলে আসা নসফেরাতু-আখ্যানের সামান্য সংকটটি এভাবে গ্রিক ট্র্যাজেডির মহৎ মাত্রা পায়। কাহিনি এগোয়। মিথ আর মনস্তত্ত্ব, কাহিনির দু’টি সমান্তরাল ভাষ্য রচনা করতে থাকে।
আরও পড়ুন- সত্যিই রয়েছে রক্তচোষারা! গলায় কাস্তে বাঁধা মহিলা ‘ভ্যাম্পায়ারের’ কঙ্কাল ঘিরে ঘনাচ্ছে রহস্য

নসফেরাতু ২০২৪
৩
ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের চুক্তি— ঈশ্বরের রাজ্যে মানুষকে রক্ষা করতে হয় কিছু দৈবনির্দেশ, যৌন নৈতিকতা তার মধ্যে একটি। ভ্যাম্পায়ার নামের মৃত্যুহীন পিশাচ রাতের আঁধারে কবরের অন্ধকার থেকে উঠে আসে। ঘুমন্ত মানুষের (বা মানুষীর) কনসেন্টের বিশেষ তোয়াক্কা না-করেই ঘাড়ে গলায় দাঁত বসিয়ে রক্ত চুষে নেয়, নিজের জীবনীশক্তি হিসেবে নিদ্রিতের দেহ থেকে শোষণ করে প্রাণকণা। ভ্যাম্পায়ারিজম— তাই ঈশ্বরের বাস্তুতন্ত্রে নিছক পরজীবি সম্পর্ক নয়, গথিক রোম্যান্স ও ফ্যান্টাসির আড়ালে বিষয়টিতে আদতে প্রচ্ছন্ন আছে যৌন-রূপক। শিকার ও শিকারী এখানে যেন-বা গথিক রোমান্স-কাব্যের নায়ক-নায়িকা। শায়িত শিকারের গ্রীবায় ধমনীতে শ্বদন্ত গেঁথে দেওয়া এখানে সেক্সুয়াল পেনিট্রেশনের সমতুল; রক্তশোষণ: দেহতরলের লেনদেন। গথিক হররের মিস্টিক আবরণে ঢাকা ‘ভ্যাম্পায়ারিজম’ ব্যাপারটির আড়ালে ‘নিষিদ্ধ’ বা ‘অনৈতিক’ যৌন-মিলনেরই ব্যঞ্জনা। কেবল ইওরোপ নয়, খোদ প্রাচ্যদেশেও ভ্যাম্পায়ার বা তুলনীয় সত্তাদের কাহিনিতে এই যৌন-ব্যঞ্জনাটি অমিল নয়। চিনের মিথে হুলি জিং (hulijing) এমনই এক ভোলবদলকারী শৃগালসত্তা, যে সুন্দরী নারীর রূপ ধরে পুরুষের দেহতরল (jing) শোষণ করে যায়। এই শিকার-নির্বাচন তথা পরদেহগমনে ভ্যাম্পায়ার পক্ষপাতহীন, বহুগামী, নীতিহীন। ঈশ্বরের চুক্তি বা যৌন-নৈতিকতার ধার সে ধারে না।
ব্যতিক্রম কি নেই তা বলে? ১৯৩৬ নাগাদ প্রকাশিত থিওফিল গতিয়ের-এর ‘La Morte Amoureuse’ নামের ফরাসি গল্পটি (ইংরাজি অনুবাদে ‘দ্য ড্রিমল্যান্ড ব্রাইড’) মানুষ ও ভ্যাম্পায়ারের প্রেমকাহিনি। তরুণ ধর্মযাজক রোম্যুয়ালের প্রণয়পিয়াসী সুন্দরী ভ্যাম্পায়ার ক্ল্যারিমোঁদ প্রাণমন সঁপে এক পুরুষেই। পুষ্টির উপাদান সে শুষে নেয় কেবল রোম্যুয়েলের দেহ থেকে— তাও শ্বদন্তে নয়, ঘুমন্ত প্রেমিকের দেহ সূঁচে বিদ্ধ করে। ‘পিশাচের রাত’-এ ভ্যাম্পায়ার না-হলেও সঙ্গীর দেহতরলে পোষিত ওয়্যার-উলফ যুগলের কাহিনি লেখেন অনীশ দেবও ১৪০৮ সালের শারদীয়া ‘শুকতারা’-তে। তবে এরা প্রতিক্ষেত্রেই ‘যুগল’, দাম্পত্য বা প্রেমসম্পর্ক আছে তাদের মধ্যে, কামবাসনা তাদের ‘এরস’-চালিত, ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তির তাড়না এখানে নেই। এদের উল্টোদিকে দেখা চলতে পারে ড্রাকুলা এবং তার বেলাগাম তিন সঙ্গিনীকে। সুতরাং, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গথিক লিটারেচারের পপুলারতম অতিপ্রাকৃত অস্তিত্ব ভ্যাম্পায়ারের বহুগামী চরিত্রটি স্পষ্ট হয়।

হরর-আখ্যানে প্রচ্ছন্ন সমাজভাষ্য গেঁথে রাখাটা ইদানীং লিবারাল ট্রেন্ড— এতে হররকে ছাপিয়ে তার একটা বিস্তৃত সামাজিক পাঠ ও আবেদন তৈরির সুযোগ থাকে। ‘স্মাইল’ (২০২২) যেমন হররের আবডালে এমন ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশনের কথা বলে যেখানে ‘ভয়’ নিজের অন্ধকারে প্রতিপালিত ট্রমা, মুক্তি আত্মহনন নামের অনিবার্য খাদ। বলিউডেও হালফিলের ‘স্ত্রী’ (২০১৮), ‘বুলবুল’ (২০২০) এরকম আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যায়, যেখানে অতিপ্রাকৃতকে অতিক্রম করে যায় সমাজ-সমালোচনার নারীবাদী বয়ান। কিন্তু এগার্সের ফুটনোটে এক্সক্লুসিভ সমাজভাষ্য থাকে তার অলৌকিকতার বয়ানটিকে খাটো না করেই— দু’য়ে মিলে একটা দ্বন্দ্ব তৈরি করতে চায়। যুক্তি আর যুক্তিহীনতা, বিশ্বাস আর অবিশ্বাস, রটনা আর ঘটনা, মিথ আর মনস্তত্ত্ব— দুইয়ের একটা অদ্ভুত দোটানায় পড়ে যান দর্শক। মনে করা যাক, ফোক-হরর ‘দ্য উইচ’-এর কাহিনি। যুক্তিবাদ-আলোকিত দর্শক বোঝেন নিষ্পাপ কিশোরীটির শিরে ঘনিয়ে উঠছে ক্রূর ইওরোপিয় মধ্যযুগ, পরিস্থিতির কী আশ্চর্য সমাপতনে পরিবারের সকলের কাছে সে প্রতিপন্ন হচ্ছে ডাইনি। ফের দর্শককে বোঝানো হয় পরিবারের সবাই কি নেহাতই ভুল? সরল যুক্তিবুদ্ধির অতীত অব্যাখ্যাত কিছু ঘটনায় বিস্মিত দর্শকের হাঁ-চোখের সামনে ধীরে ধীরে প্রতিপাদিত হয় সেই কিশোরীর ডাইনিত্ব।
এগার্সের নসফেরাতু একইভাবে অতিপ্রাকৃত হয়েও শেষাবধি প্রচণ্ডরকম প্রাকৃত অস্তিত্ব, দূর কার্পেথিয়ান পাহাড়বাসী হলেও মনেরই দুর্গম প্রদেশে তার দুর্গখানি। ১৯২২-এর কাহিনিসূত্রের উত্তরাধিকারে সে খোদ, আঁধারের আদিম পিশাচ; পাশাপাশি এগার্সের নবনির্মাণে সে ভিক্টোরিয়ান নারীর যৌন-অবদমন, স্খলন, অতৃপ্তির মিলমিশে সৃষ্ট অপরাধবোধ ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার আদলও বটে। বেচারা থমাস! নিঃসঙ্গ স্ত্রীর মনের গোলকধাঁধায় নয়, সে যখন মূল সমস্যাটিকে খ্যাপার মতো খুঁজে ফেরে বাইরের জগতে— তখনই একাকী এলেনের দখল নিতে তারই ভেতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়ে নসফেরাতু। অচেতন থেকে বেরিয়ে আসা এই আঁধারের মোকাবিলা এলেনকেই করতে হয়, সূর্যের আলো ফেলতে হয় সেই অন্ধকারে। মোরগের ডাকে শহরবাসী উঠে দেখে— একটি মেয়ে যে যৌন-তৃপ্তির প্রশ্নে ঈশ্বরের অথরিটিকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল, তার প্রায়শ্চিত্ত কীভাবে লেখা হচ্ছে। মেলাঙ্কলিয়া বা অবসাদে ভোগা স্বামীসঙ্গহীন একাকিনীর মৃত্যুকামনা— প্রাণকণা শুষে নেওয়া এই মৃত্যুদূতই এগার্সের ছবির ভ্যাম্পায়ার। এগার্সের নায়িকা নিজেও সেটা জানে, তাই তার প্রশ্ন থাকে— ‘Does evil come from within us, or beyond?’ আদিতে মনের গহনে যে মৃত্যুর বাস, অন্ত্যে সেই মৃত্যুর সঙ্গেই রচিত তার ফুলশয্যা। এলেনের লীলাময় লিবিডোর গতি সিনেমার শেষতক এই ‘থ্যানাটোস’-সর্বস্ব মরণের দিকে ক্রমশ ধাবমান। সত্যিই রমণ আর মরণ একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ কি নয় তাঁর কাছে?

এলেনের অবদমিত কামনা, যা 'অসামাজিক', বাইবেল অসমর্থিত— সেটাই নসফেরাতুকে তার বিভীষণ চেহারা দেয়। মনের প্রতিরক্ষা দফতর তা ঢেকে-চেপে রাখতে পারে না। ফ্রয়েডভাষ্যে ‘আত্ম’-এর (ego) দু’টি ডিফেন্স মেকানিজম— ‘প্রজেকশন’ এবং ‘রিয়্যাকশন ফর্মেশন’। নিজের যে অস্বীকৃত কামনা আমরা চেতন স্তরে উঠে আসতে দিই না— তা আরোপ করে ফেলি অপর-সত্তায়। আবার, অপর-সত্তায় আরোপিত মানতে-না-পারা সেই বিষয় তার চরিত্র বদলে হয়ে যায় বিপরীতধর্মী। অর্থাৎ, অবদমিত অনুভূতির আশ্রয় আলম্বন ও চরিত্রের বদল। আমার, অপরের প্রতি চাপা কামনা, আমার কাছে মূর্ত হতে পারে ‘তার আমার প্রতি কামনা’-র (এমনকী জিঘাংসারও) রূপ নিয়ে। নসফেরাতু আদতে যে এলেনেরই গূঢ়ৈষা, ভিক্টোরিয় ডিফেন্স মেকানিজমের গরাদ গলে বেরনো মনোবিকার— তার একটি যথার্থ প্রমাণ ধরা থাকে ছবির শেষভাগে হিস্টিরিয়াক ফিটের মুহূর্তে স্বামী থমাসের পৌরুষকে টিটকিরি দেওয়া এবং কাঙ্খিত পুরুষ হিসেবে নসফেরাতুর সঙ্গে তুলনা টানার দৃশ্যে। সমস্তটাই— যখন ওরলকের প্রকৃত সত্তা আর গোপন নেই, মড়কে শহর উজাড়, প্রিয় আত্মীয়-বন্ধুদের ওপর মৃত্যু নেমে আসছে। এরপরেই সিনেমার সেই অভাবিতপূর্ব দৃশ্য। উত্তেজিত থমাসের বলপূর্বক এলেনকে পীড়ন ও গ্রাস, ডমিন্যান্ট পুরুষ ও সাবমিসিভ নারীর যৌনমিলন। আর তা ছাপিয়ে এলেনের আনন্দশীৎকার, সর্বোপরি নসফেরাতুকে সেই মিলনদৃশ্য দেখানোর পুলক— যৌনতৃপ্তি আর ভয়্যারিজমের কী অদ্ভুত মিশেল। গথিক ফ্যান্টাসিতে প্রচ্ছন্ন সাইকোসেক্সুয়াল টেনশানের বয়ানটি মুহূর্তে স্পষ্ট করে দেন এগার্স। তাই অতিপ্রাকৃত অস্তিত্বের নসফেরাতু যখন বলে ওঠে: ‘I am appetite’: ‘আমিই খিদে’— অতিপ্রাকৃতের খোলস ছেড়ে এলেনের বাস্তব যৌন-অবদমনের স্পষ্ট অবয়ব হয়ে ওঠে ভ্যাম্পায়ার। এই ভাষ্যে নসফেরাতু এলেনের নির্মাণ। এলেনেরই অতৃপ্ত-বাসনা, যা নৈতিকতা আর অপরাধবোধের চাপে মনের রহস্যময় দুর্গে নির্বাসিত, কিন্তু নির্বাপিত নয়; সমাজে সংসারে ব্যক্তিগত পরিসরে স্বামীসঙ্গে—এলেনের সঙ্গে বারবার তার মুখোমুখি বোঝাপড়া।
খেয়াল পড়ে সেই আইকনিক দৃশ্য, খোলা ব্যালকনির দিকে মুখ করে স্বপনচারিণী এলেন দাঁড়িয়ে আছে ‘সাদা’ (মৃত্যুর মতো বিধুর, আবার বিবাহসভায় কনের পোষাকের সফেনও কি নয়?) নাইটগাউনে— পর্দায় পিশাচের প্রলম্বিত ছায়া উড়ে যেন ধরতে চাইছে এলেনকে। পর্দার ওপারে কে আর এলেন ছাড়া? সব স্বপ্নদৃশ্যের যবনিকা তুললে তো আসলে নিজেরই মুখোমুখি হওয়া।




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp