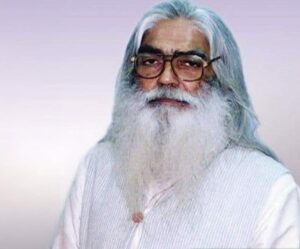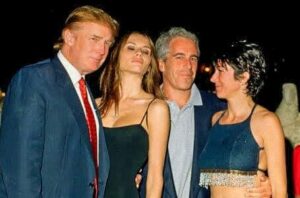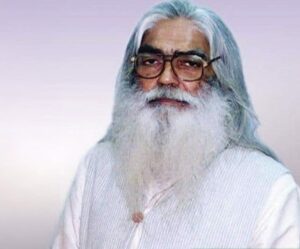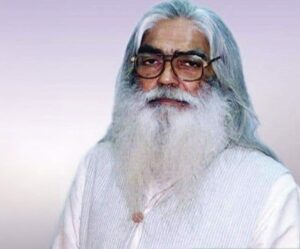কেন্দ্রের শিক্ষানীতি রাজ্যে চালু না হতে দিলেই সমস্যা মিটে যাবে?
National Education Policy 2020: এই শিক্ষানীতি সেই পরিবেশকে নিশ্চিত করতে চায় যেখানে শাসক, এলিট সম্প্রদায় দেশের বৌদ্ধিক ক্ষেত্রগুলোতে রাজত্ব করবে এবং অন্ত্যজ তথা প্রান্তিক পরিবারের ছেলে মেয়ের সস্তা শ্রমের জোগানে পরিণত হওয়া...
সম্প্রতি নয়া শিক্ষানীতি রাজ্যে প্রয়োগের বাধ্য-বাধ্যকতা শীর্ষক একটি মামলায় দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় নতুন করে সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ও ভাষাগত বিতর্ককে সামনে এনেছে। এই জনস্বার্থ মামলার বিষয় ছিল তামিলনাড়ু, কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে ত্রিভাষা সূত্র সহ নয়া শিক্ষানীতি-২০০০-কে লাগু করার জন্য সর্বোচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপ। মামলাকারীদের বক্তব্য ছিল, সংবিধানে উল্লিখিত আর্টিকেল-৩২ অনুসারে নাগরিকের যে মৌলিক অধিকার আছে, শিক্ষানীতি না প্রয়োগের কারণে এই তিনটি অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যে তা লঙ্ঘিত হচ্ছে। সর্বোচ্চ আদালত তার রায়ে এই মামলাটিকে খারিজ করে জানিয়েছে, শিক্ষা যেহেতু যুগ্ম তালিকায় রয়েছে তাই রাজ্য সরকারকে কোনওভাবেই কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি মানতে বাধ্য করা যায় না। একইসঙ্গে সর্বোচ্চ আদালত এও জানিয়েছে যে, কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির প্রশ্নে রাজ্য সরকারের কোনও কাজ যদি মৌলিক অধিকারের বিরোধী হয় তবে সেখানে আদালত হস্তক্ষেপ করবে। এই রায়কে স্বাগত জানিয়েই বলা যেতে পারে, এই রায় এক সম্ভাবনার রাস্তা খুলে দিয়েছে মাত্র কিন্তু নয়া শিক্ষানীতির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই আরও বৃহত্তর হওয়া উচিত।
একথা প্রথমেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা উচিত যে, এই মামলার কেন্দ্রে রয়েছে কেন্দ্রীয়ভাবে দেশজুড়ে হিন্দি ভাষার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে স্টালিনের নেতৃত্বাধীন তামিলনাড়ু ডিএমকে সরকারের ধারাবাহিক লড়াই। তামিলনাড়ু সরকার পরিষ্কার জানিয়েছে, সে রাজ্যের শ্রেণিকক্ষে তারা তামিল ও ইংরেজি ভাষাকেই পড়াবে, হিন্দির কোনও প্রবেশাধিকার থাকবে না। কেন্দ্রীয় সরকার তামিলনাড়ু সরকারের এই সিদ্ধান্তকে ঔদ্ধত্য হিসাবে দেখছে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান রাজ্য সরকারকে 'অসভ্য'-দের সরকার আখ্যা দিয়েছে। গোদি মিডিয়া যথারীতি বিষয়টিকে উত্তর-দক্ষিণ ভারতের মধ্যেকার 'সাংস্কৃতিক যুদ্ধ' হিসাবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছে এবং ডিএমকে সরকারকে বিভেদকামী শক্তি হিসাবে দেগে দিয়েছে। যদিও হিন্দি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তামিলনাড়ুর মানুষের লড়াইয়ের এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে এবং আজও এই সময়ে তামিলনাড়ুকে তার মাশুল দিতে হচ্ছে। ত্রিভাষা সূত্র না মানার কারণে কেন্দ্রীয় সরকার সে রাজ্যের জন্য ২,১৫২ কোটি টাকার শিক্ষাখাতে কেন্দ্রীয় সাহায্য স্থগিত করে দিয়েছে। সংবিধানকে পাশ কাটিয়ে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা বানানোর চক্রান্ত পুরনো, পার্থক্য হলো মোদি সরকারের আমলে বিষয়টি নতুন মাত্রা পেয়েছে। স্টালিন খুব যুক্তিপূর্ণ ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, ২০১৭-২০২০ সময়পর্বে বর্তমানে প্রায় অব্যবহৃত সংস্কৃত ভাষার প্রচার ও প্রসারে কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে ৬৪৩ কোটি টাকা খরচ করেছে, সেখানে পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ভাষা হিসাবে নথিভুক্ত তামিলের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার খরচ করেছে মাত্র ২৩ কোটি টাকা। স্টালিনের মতে এই খরচ প্রমাণ করছে অ-হিন্দি ভাষাগুলির প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণ। অ-হিন্দিভাষী রাজ্যগুলোকে হিন্দির উপনিবেশ বানানোর সরকারি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ শুধু আজ দক্ষিণ ভারতে সীমাবদ্ধ নেই। অতি সম্প্রতি মহারাষ্ট্রে হিন্দিকে বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত সেখানকার বিজেপি সরকার যেভাবে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে তা নিশ্চিত করছে আগামীদিনে ভাষা বিতর্ক আরও জটিল আকার ধারণ করবে।
আরও পড়ুন- শিক্ষার মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া আঘাত! বিচারক থেকে মন্ত্রী— দায় কার?
এই শিক্ষানীতির সবচেয়ে বড় বিপদ হলো, শিক্ষার কেন্দ্রীকরণ যা এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বর্তমান সময়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছতে পেরেছে। দল নির্বিশেষে উপুর্যুপরি সরকার কীভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ভেঙে শিক্ষার কেন্দ্রীকরণ ঘটিয়েছে সেই ইতিহাস আলোচনায় আসা জরুরি। সংবিধান যখন চালু হয়, তখন সপ্তম তফশিলে 'সাধারণ শিক্ষা' শিরোনামে তাকে রাজ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর অর্থ, শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় নীতি প্রণয়ণের অধিকার রাজ্য সরকারের উপর ন্যাস্ত থাকবে। এই সপ্তম তফশিলে রাজ্য তালিকা, কেন্দ্রীয় তালিকা এবং যুগ্ম তালিকা (কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের দায়িত্ব) — তিনটি তালিকার মাধ্যমে ক্ষমতার বিন্যাস করা হয়। এই তালিকা মোতাবেক কারিগরি শিক্ষা, গবেষণা ও উচ্চশিক্ষা ছিল কেন্দ্রীয় তালিকায়। প্রথম থেকেই শিক্ষা নিয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে বিরোধ ছিল যেহেতু কারিগরি ও চিকিৎসা শিক্ষা ছিল কেন্দ্রীয় তালিকায়। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজনের রূপরেখা ঠিক করার জন্য যে সারকারিয়া কমিশন গঠিত হয় তারাও এই বিরোধের উল্লেখ করেছে, বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডাক্তারিতে ভর্তির সময় ডোমিসাইলকে মানদণ্ড স্থির করার প্রশ্নে। এই অবস্থার পরিবর্তন হয় জরুরি অবস্থার সময়। ভারতীয় গণতন্ত্রের সেই অন্ধকার পর্বে সংবিধান সংশোধন করে শিক্ষাকে যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই প্রশ্নে আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য শিক্ষাবিদ শ্যাম মেনন মন্তব্য করেছিলেন:
"Emergency was used for bringing about greater centralisation of control in education. Indira Gandhi had wanted higher education to come increasingly under the Union government's control"
আজ যখন ভারতের মতো আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের দেশে বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যের সন্ধান ও বিকেন্দ্রীকরণকে শাসনের সেরা পদ্ধতি বলে মনে করা উচিত তখন আদতে কেন্দ্রীকরণ রাষ্ট্রের প্রধান প্রশাসনিক নীতি হয়ে উঠেছে। উপুর্যুপরি শিক্ষা কমিশন জাতীয় সংহতির নামে রাজ্যের শিক্ষা সংক্রান্ত অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করেছে। কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৬), নয়া শিক্ষানীতি (১৯৮৬) জাতীয় মূল্যবোধ ও স্লোগানের আড়ালে কেন্দ্রীকরণের পক্ষে সওয়াল করেছে। এর ফল হয়েছে মারাত্মক। এক্ষেত্রে আমরা বহু বিতর্কিত 'নিট' পরীক্ষার কথা বলতে পারি। এই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার সিলেবাস এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে কেন্দ্রীয় বোর্ডের শিক্ষার্থীরা সুবিধা পায়। রাজ্যস্তরের বোর্ডের শিক্ষার্থীদের কাছে এই সিলেবাস এতটাই আলাদা যে তারা প্রথম থেকেই পিছিয়ে পড়ে। তামিলনাড়ুতে রাজ্যবোর্ডের একাধিক শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা সারা দেশে বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। এই কেন্দ্রীকরণ কিন্তু শুধু রাজ্যের ক্ষমতা হ্রাস করছে না, তা একইসঙ্গে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসনের অধিকারকেও হ্রাস করছে।
কেন্দ্রীয় সরকার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ৪৫টি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য কমন এনট্রান্স টেস্ট (CUET) চালু করেছে। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিশ্ববিদ্যালয় এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম, অ্যাডমিশন টেস্টের মানকে এক করে দেওয়া আসলে কেন্দ্রীকরণের চক্রান্ত। এই প্রসঙ্গে দেশের অগ্রগণ্য শিক্ষাবিদ হরগোপালের পর্যবেক্ষণ উল্লেখযোগ্য:
"In education development, you can't have one single system operating for an educationally developed state like Tamilnadu and relatively backward states like Bihar. Decision- making must be completely left to the federating states"
সুপ্রিম কোর্টের রায়ে কাগজে কলমে শিক্ষার প্রশ্নে যুগ্ম তালিকার অধিকার স্বীকৃত হলেও আদতে যেভাবে নয়া শিক্ষানীতি-২০২০-র মাধ্যমে দেশ জুড়ে একই সিলেবাস, প্রশ্নপত্র ও মূল্যায়ন পদ্ধতির জন্য চাপ বৃদ্ধি করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন রাজ্য তাদের রাজনৈতিক আনুগত্যের কারণে নয়া শিক্ষানীতিকে মেনে নিয়েছে তাতে বলা যায় শিক্ষাকে কেন্দ্রীয় তালিকায় আনার চক্রান্ত সফল হওয়া সময়ের অপেক্ষা মাত্র।
আরও পড়ুন- শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গই ছিলেন শিক্ষাচিন্তক রবীন্দ্রনাথ
আমাদের সবাইকে একথা উপলব্ধি করতে হবে যে, নয়া শিক্ষানীতি শুধু হিন্দি চাপানোর এক যন্ত্র নয়, এ এক ট্রোজান হর্স যার মধ্যে লুকিয়ে আছে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থাকে নয়া উদারবাদী ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধীনে করার নীল নকশা। এই শিক্ষানীতি বেসরকারিকরণ, কর্পোরেটকরণের পক্ষে সওয়াল করে। শিক্ষার ভারতীয়করণের নামে উচ্চবর্ণের আধিপত্য ও গেরুয়াকরণকে নিশ্চিত করতে চায়। এটা যতটা না এক শিক্ষানীতি, তার চেয়ে বেশি জনশিক্ষাকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা। এটা নিশ্চিত করতে চায় যে সুলভ উচ্চশিক্ষা এক প্রাগৈতিহাসিক মিথ মাত্র। এই শিক্ষানীতিতে বহুবার উল্লিখিত ‘light but tight' নীতি কার্যক্ষেত্রে হলো এক আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ যেখানে সরকারি ব্যয়বরাদ্দ ক্রমহ্রাসমান কিন্তু নিয়ন্ত্রণ— কে শেখাবে, কী শেখাবে, কে শিখবে ইত্যাদি মূলগত প্রশ্নে ভীষণ কঠোর। এখানে 'ভোকেশনাল ট্রেনিং'-কে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো প্রান্তিক মানুষদের উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে তাদের প্রাথমিক মানের কারিগরি দক্ষতা নির্ভর শ্রমশক্তিতে রূপান্তরিত করা যাতে তারা কর্পোরেট দুনিয়ার কম মাইনের মজুরের চাহিদা পূরণ করতে পারে। এই শিক্ষানীতি সেই পরিবেশকে নিশ্চিত করতে চায় যেখানে শাসক, এলিট সম্প্রদায় দেশের বৌদ্ধিক ক্ষেত্রগুলোতে রাজত্ব করবে এবং অন্ত্যজ তথা প্রান্তিক পরিবারের ছেলে মেয়ের সস্তা শ্রমের জোগানে পরিণত হওয়াকে তাদের ভবিতব্য বলে মেনে নেবে। এই শিক্ষানীতি প্রায় স্লোগানের মতো ডিজিটাল শিক্ষার কথা বলে। একে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ বলা হচ্ছে অথচ চূড়ান্ত অসাম্যের এই দেশে ডিজিটাল বৈষম্য এত তীব্র যে শুধুমাত্র পয়সার অভাবে হাজার হাজার শিক্ষার্থী অতিমারীর সময় অনলাইন ক্লাসে অংশ নিতে পারেনি। এই শিক্ষানীতি ভারতকে বিদেশি ও দেশি বেসরকারি শিক্ষায়তনগুলির চারণক্ষেত্রে রূপান্তরিত করবে। এই শিক্ষানীতি শুধু সিলেবাস ঠিক করছে না, কারা উন্নত মানের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে তাও নির্দিষ্ট করছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সেল্ফ-ফিনান্সিং কোর্সের রমরমা, বেসরকারি পুঁজিকে আহ্বান ইতিমধ্যেই চালু থাকা শিক্ষাকে পণ্য বানানোর নয়া উদারবাদী অর্থনীতির পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।
নয়া শিক্ষানীতি শিক্ষার্থীকে নাগরিক, চিন্তক, বিজ্ঞানী, কবি বা স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে সতত বিদ্রোহী হিসাবে না দেখে 'সম্পদ' (resource) হিসাবে দেখতে চায়। তাই তো নয়া শিক্ষানীতি ড্রাফট কমিটির চেয়ারম্যান কে কস্তুরিরঙ্গন সগর্বে ঘোষণা করেন, তাদের শিক্ষানীতি তৈরি করবে "workforce aligned to the needs of the market"। এই শিক্ষানীতি বিশ্ববিদ্যালয়কে চিন্তা ও মননের অনুশীলন কেন্দ্র হিসাবে না দেখে ইনকিউবেটর হিসাবে দেখতে চায় যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের ছদ্ম জাতীয়তাবাদ ও উগ্র বিদ্বেষের নিয়ন্ত্রিত আবহাওয়ায় তৈরি হবে শাসক অনুগত, প্রশ্নহীন মানবযন্ত্র। আশার কথা হললো, সর্বোচ্চ আদালতের রায় অন্তত মনে করিয়ে দিয়েছে যে শিক্ষা যুগ্ম তালিকার অন্তর্গত। এটা কোনও পদ্ধতিগত বিষয় নয়, এ রায় সাংবিধানিক। এই রায় এক সম্ভাবনা তৈরি করেছে। শুধু মাত্র নয়া শিক্ষানীতিকে প্রত্যাখান নয়, শুধু ত্রিভাষা সংক্রান্ত বিতর্কে সীমাবদ্ধ থাকা নয়, আজ প্রয়োজন শিক্ষা কেমন হতে পারে, কেমন হওয়া দরকার সেই আলোচনাকে গণতান্ত্রিক সংলাপের অন্তর্ভুক্ত করা।




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp