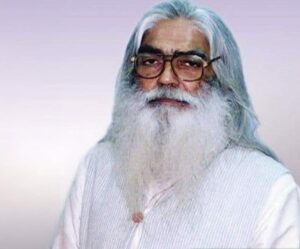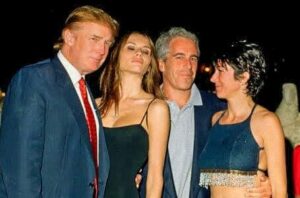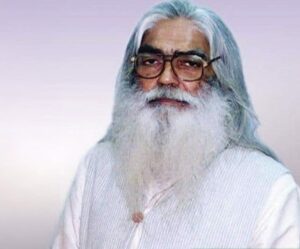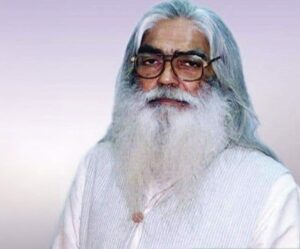সতর্ক করেই হয় মৃত নয় একঘরে: বিশ্বজুড়ে হুইসেলব্লোয়ারদের পরিণতি
Whistleblower's Protection: চিকিৎসা ব্যবস্থাপক ববিতা ডেওকরণ গৌতেং প্রদেশের স্বাস্থ্যখাতে বড় দুর্নীতি ফাঁস করেছিলেন, তাঁকে ২০২১ সালে গাড়ির ভেতর ১২বার গুলি করে হত্যা করা হয়। তাঁর মৃত্যু বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড় তোলে।
আহমেদাবাদে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় যখন ২৭৪ জন যাত্রী ও সাধারণ মানুষ প্রাণ হারান এবং ভারতজুড়ে শোক ও ক্ষোভের আবহ তৈরি হয়, তখন বোয়িংয়ের নির্মাণ প্রক্রিয়া ও কর্পোরেট সংস্কৃতির দিকে চোখ ফেরানো ছাড়া উপায় থাকে না। এয়ার ইন্ডিয়ার এই ড্রিমলাইনারটি একটি ২০১৪ সালে তৈরি হওয়া বোয়িং ৭৮৭– যা ওই সময়েই বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক তদন্তে বারবার প্রশ্নের মুখে পড়েছিল। আর এ দুর্ঘটনার পরপরই ফের সামনে এসেছে বোয়িংয়ের সেই একই পুরনো দোষ– মান নিয়ন্ত্রণে অবহেলা, উৎপাদনে তাড়াহুড়ো, কর্পোরেট লোভ ও হুইসেলব্লোয়ারদের প্রতি শত্রুতামূলক আচরণ।
'দ্য আমেরিকান প্রসপেক্ট' একটি দৈনিক অনলাইন এবং দ্বিমাসিক আমেরিকান রাজনৈতিক ও জননীতি বিষয়ক পত্রিকা, যা আমেরিকার আধুনিক উদারনীতি ও প্রগতিবাদের কথা বলে। ওয়াশিংটন ডিসি-তে অবস্থিত এই প্রকাশনা সংস্থাটি জানায় যে, তারা "প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জননীতি নিয়ে তথ্যাভিজ্ঞ আলোচনা প্রচারে নিবেদিত।" সেই ‘দ্য আমেরিকান প্রসপেক্ট’-এর অনুসন্ধানী প্রতিবেদনগুলোতে উঠে এসেছে বোয়িংয়ের চার্লসটন প্ল্যান্টে কাজ করা প্রাক্তন মান নিয়ন্ত্রক সিনথিয়া কিচেন্সের উদ্বেগের কথা। কিচেন্স যে ১১টি বিমান নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন, তার মধ্যে ছয়টিই ছিল এয়ার ইন্ডিয়ার জন্য নির্মিত। তিনি অভিযোগ করেছিলেন, এই বিমানগুলোর অভ্যন্তরে গুরুতর কাঠামোগত ত্রুটি ছিল, এমনকী এগুলোর ভেতরে 'ফরেন অবজেক্ট ডেব্রি' বা অবাঞ্ছিত বস্তু রয়ে গিয়েছিল, যা বিপজ্জনক যান্ত্রিক ত্রুটির জন্ম দিতে পারে। অথচ বোয়িংয়ের উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষ তাঁকে জানিয়েছিল, চিন্তার কিছু নেই, এই বিমানগুলো মার্কিন মাটিতে কখনই নামবে না– এগুলো কেবল ‘বিদেশি গ্রাহকদের’ জন্য। মানে স্পষ্টতই বোয়িং নিজেদের নিরাপত্তার মানদণ্ডকে মার্কিন ও বিদেশি বাজারের মধ্যে ভাগ করে দেখেছে।
এই কথিত বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি বোয়িংয়ের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ রয়েছে। প্রাক্তন কর্মী এবং হুইসেলব্লোয়ার জন বার্নেট, যিনি ২০২৩ সালে রহস্যজনকভাবে মারা যান, বারবার সতর্ক করেছিলেন যে বোয়িং ড্রিমলাইনারের উৎপাদনে খরচ কমাতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে মৌলিক নিরাপত্তা পদ্ধতি উপেক্ষা করছে। তাঁর কথামতো, নির্মাণ শেষ হওয়ার পর বিমানের ভেতরে ছোট ধাতব স্ক্রু, সরঞ্জামের টুকরো কিংবা প্লাস্টিকের আবর্জনা পড়ে থাকত, যা উচ্চগতির উড়ানের সময় প্রাণঘাতী যান্ত্রিক বিপর্যয় ঘটাতে পারে। এটা কেবল এক বা দুইটি বিমানের ঘটনা নয়। ২০২০ সালে নরওয়েজিয়ান এয়ার শাটল এবং আর্কটিক এভিয়েশন অ্যাসেটস কর্তৃপক্ষ সরাসরি বোয়িংয়ের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনে, দাবি করে যে তাদের সরবরাহ করা ৭৮৭ ড্রিমলাইনার বিমানে "অসাধারণ ত্রুটি" ছিল, যা উৎপাদন পর্যায়ের গাফিলতির ফল।

জন বার্নেট
আরও পড়ুন- এয়ার ইন্ডিয়া বিমান দুর্ঘটনা! এ যাবৎ কালের সবচেয়ে বড় বিমা নিষ্পত্তির সম্ভাবনা?
বোয়িংয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে জোরালো সংকেত এসেছে অবশ্য ২০১৮ ও ২০১৯ সালের দু'টি ভয়াবহ দুর্ঘটনায়। ইন্দোনেশিয়ার লায়ন এয়ার এবং ইথিওপিয়ার ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্সের দু'টি বোয়িং ৭৩৭ ম্যাক্স বিমান, যেগুলো উড়ানের কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিধ্বস্ত হয়, ৩৪৬ জন মানুষ মারা যান। বোয়িং সেই সময় দোষ চাপায় পাইলটের ঘাড়ে কিন্তু তদন্তে বেরিয়ে আসে অন্য সত্য— এমসিএএস নামে এক নতুন অটো-কন্ট্রোল সফটওয়্যার পাইলটদের না জানিয়েই যুক্ত করা হয়েছিল বিমানে। এর ফলে অ্যাঙ্গেল অফ অ্যাটাক সেন্সর সামান্য ত্রুটি দিলেও বিমান স্বয়ংক্রিয়ভাবে নীচের দিকে নেমে যেত এবং পাইলটদের হাতে মাত্র ১০ সেকেন্ড থাকত প্রতিক্রিয়ার জন্য। এই ভয়াবহ বাস্তবতা বোঝা গিয়েছিল দু’টি দুর্ঘটনার পর। অথচ তখনও বোয়িং গোপনেই রেখেছিল সফটওয়্যারের অস্তিত্ব ও এর ঝুঁকি। ২০২১ সালে এই ঘটনার সম্পূর্ণ দায় স্বীকার করে নেয় বোয়িং। কিন্তু ততক্ষণে কোম্পানির বিশ্বাসযোগ্যতা এবং হাজারও পরিবারের জীবনের ভিত্তি — দুই-ই ক্ষতির মুখে পড়ে গেছে। ২০১৯ সালে সম্পূর্ণ ৭৩৭ ম্যাক্স বহরকে ১৮ মাসের জন্য গ্রাউন্ড করা হয়। অভ্যন্তরীণ নথি থেকে জানা যায়, বোয়িং ইচ্ছাকৃতভাবেই এমসিএএস সিস্টেম সম্পর্কে গোপনীয়তা বজায় রেখেছিল যেন অতিরিক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন না হয় এবং ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এফএএ) কাছ থেকে দ্রুত ছাড়পত্র পাওয়া যায়।ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ভূমিকাও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। সংস্থাটি স্বীকার করেছে যে তাদের পর্যাপ্ত পরিদর্শক না থাকায়, তারা বোয়িং কর্মীদের উপর নির্ভর করেছে নিজেদেরই উৎপাদন ব্যবস্থা পরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য। অর্থাৎ, বোয়িং নিজের তৈরি বিমান নিজেরাই পরীক্ষা করে নিজেদের ‘পাস’ সার্টিফিকেট দিয়েছে। এ যেন বিচারকের আসনে অভিযুক্তের অবস্থান! এমন অবস্থায় বোঝা যায়, কীভাবে ফেডারেল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং বড় কর্পোরেশনের মধ্যে এক গভীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, যা শিল্পের মৌলিক নিরাপত্তা কাঠামোকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।
ড্রিমলাইনার প্রকল্পের সময়ে, প্রধান ফিউজলাজ তৈরি হয় ইতালি ও জাপানে, ব্যাটারি সিস্টেম তৈরি হয় ফ্রান্সে, অবজেক্টিভ ইন্টিগ্রেশন দুর্বল হয়ে পড়ে, একাধিকবার ব্যাটারির বিস্ফোরণ ঘটে এবং বহুবার গ্রাউন্ডিং করতে হয়। একীভূতকরণের সংস্কৃতির দীর্ঘমেয়াদি ফল আসে ২০১০-এর দশকে ৭৩৭ ম্যাক্স নির্মাণের সময়। এয়ারবাস A320neo এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে বোয়িং নেতৃত্ব সময় বাঁচাতে এবং এফএএ -এর অনুমোদন প্রক্রিয়া এড়িয়ে যেতে মরিয়া হয়ে পড়ে। ফলে, নতুন ডিজাইনের বদলে পুরনো ৭৩৭ মডেলে নতুন ইঞ্জিন বসিয়ে বিক্রি শুরু হয়, এই ইঞ্জিনের জন্য MCAS নামে একটি নতুন সফটওয়্যার যোগ করা হয়, যা বিমানের নাক নীচের দিকে ঠেলে দেয়, পাইলটদের এই সফটওয়্যার সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ বা তথ্য দেওয়া হয়নি, এফএএ-এর সঙ্গে বোয়িংয়ের একপ্রকার 'শেয়ারড অথরিটি' ছিল বলে তারা নিজেরাই সেফটি সার্টিফিকেট ইস্যু করতে পারত। এর পরিণতিতে ইথিওপিয়ান এয়ারলাইনস এবং লায়ন এয়ারের দু'টি মারাত্মক দুর্ঘটনায় শত শত মানুষ নিহত হন।
একীভূত হওয়ার পর বোয়িং ২০০৯ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ৪৩ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত শেয়ার বাইব্যাক করে— অর্থাৎ মুনাফার বড় অংশ নতুন প্রযুক্তিতে না খরচ করে ব্যবস্থাপকদের বোনাস বাড়াতে এবং শেয়ারমূল্য কৃত্রিমভাবে বাড়াতে ব্যয় করা হয়। এই প্রবণতা ম্যাকডনেল ডগলাস থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে আসে, যারা শেয়ারহোল্ডার মানসিকতায় অভ্যস্ত ছিল।নতুন সিইও কেলি অর্টবার্গ দায়িত্ব নেওয়ার পর বোয়িং একটি নতুন প্রতিশ্রুতি দিয়েছে— সংস্কার, স্বচ্ছতা এবং নিরাপত্তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। কিন্তু আহমেদাবাদের দুর্ঘটনা সেই প্রতিশ্রুতির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘাতে দাঁড় করিয়েছে বোয়িংকে। অর্টবার্গ ও কমার্শিয়াল এয়ারপ্লেনস প্রধান স্টেফানি পোপ প্যারিস এয়ার শো বাতিল করে তদন্তে সহযোগিতার কথা বললেও, প্রশ্ন থেকেই যায়— এই কর্পোরেট সংস্কৃতি কি বদলানো সম্ভব? দীর্ঘদিন ধরে বোয়িং একটি ব্র্যান্ড হিসেবে বিশ্বের আকাশপথে আধিপত্য করে এসেছে। কিন্তু আজ, যখন আকাশ থেকে ধসে পড়া ধ্বংসাবশেষ মানুষের জীবনের মূল্য দাবি করছে, তখন বোয়িংকে নতুন করে জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হচ্ছে। শুধু প্রযুক্তি নয়, নীতির স্তরে, সিদ্ধান্তগ্রহণের স্তরে এবং সবার ওপরে— মানবিকতার স্তরে। নিরাপত্তা আর বিশ্বাস যদি কর্পোরেট মুনাফার কাছে বারবার হার মানে, তাহলে শুধু বোয়িং নয়, গোটা বিমান শিল্পই এক গভীর বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বোয়িং কি আদৌ এই বিপর্যয়ের দায় স্বীকার করে নতুন পথে হাঁটবে? এখন সেটাই দেখার।
একাধিক বোয়িং প্রকৌশলী, যাঁদের কেউ কেউ প্রাক্তন ম্যাকডনেল ডগলাস কর্মী ছিলেন না, অভ্যন্তরীণ মেমোতে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে কোম্পানির সংস্কৃতি সরে যাচ্ছে 'সেফটি-ফার্স্ট' নীতির থেকে। কিন্তু তাঁদের কথা উপেক্ষা করা হয়। ডকুমেন্টারি এবং মার্কিন কংগ্রেসের শুনানির মাধ্যমে আজ এসব বেরিয়ে এসেছে। দুর্নীতি বা বেআইনি কার্যকলাপের ক্ষেত্রে তথ্য বা ডকুমেন্টারি প্রমাণ প্রকাশ করাও আজ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। বিকৃত পুঁজির ঔরসে জন্ম নেওয়া আজকের কর্পোরেট মুনাফায় কোনও বাধা মানতে রাজি নয়। আর কর্পোরেটের এই মুনাফাকেন্দ্রিক মানসিকতা লালিত-পালিত হচ্ছে শাসকের স্নেহচ্ছায়ায়। বোয়িং-এর মুনাফায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন জন বার্নেট এবং জো লার্ডনার, যাঁরা বোয়িংয়ের কোয়ালিটি কন্ট্রোল টিমে কাজ করতেন, ৭৩৭ ম্যাক্স বিমানের নিরাপত্তা সংকট নিয়ে তাঁরা বারবার অভিযোগ করেন। কিন্তু তাঁদের অভিযোগ গুরুত্ব পায়নি। পরে জো লার্ডনারকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। পুলিশ এটিকে আত্মহত্যা বললেও অনেক বিশেষজ্ঞ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তা নিয়ে। ২০২৪ সালে আরেক বোয়িং হুইসেলব্লোয়ার জো ডি ফ্রাঙ্কো সরাসরি গণমাধ্যমে বলেন, “আমরা প্রতি ঘণ্টায় ৩-৪টি জটিল বিমানের অংশ তৈরি করছি, অথচ প্রশিক্ষণ, সময় বা নিরাপত্তা কোনও কিছুই ঠিকঠাক নেই। আমি যদি চুপ থাকি, মৃত্যুর দায় আমার হবে। আমি যদি বলি, তাহলেও মরতে পারি।” এঁদের মৃত্যু বা সামাজিক নিঃশেষিত হওয়া মূলত একধরনের ‘ন্যায়বিচারহীন শাস্তি’— যা কর্পোরেট ক্ষমতাচক্রের বাস্তব রূপ।
বোয়িং ড্রিমলাইনারের দুর্ঘটনা ও তার প্রেক্ষিতে হুইসেলব্লোয়ারদের হুঁশিয়ারি এবং তাঁদের করুণ পরিণতি আমাদের ভাবতে বাধ্য করে রাষ্ট্র ও কর্পোরেটের যৌথ দ্বিচারিতার অন্ধকার দিক নিয়ে। বিশেষ করে পশ্চিমা দুনিয়া প্রায়শই নিজেকে গণতন্ত্র, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচারের এক প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, আইনি রক্ষাকবচ এবং তথাকথিত ‘ওপেন সোসাইটি’-র গর্বগাথা পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো বহু বছর ধরেই প্রচার করে চলেছে। কিন্তু এই প্রচারের নীচে চাপা পড়ে থাকে এক অন্ধকার, এক নিষ্ঠুর বাস্তবতা— বিশেষ করে তাঁদের জন্য, যাঁরা ক্ষমতার ভিত কাঁপিয়ে দেওয়া সত্যকে প্রকাশ্যে আনতে চান। এঁদেরই বলা হয় হুইসেলব্লোয়ার— কর্মক্ষেত্রে, প্রশাসনে কিংবা সেনাবাহিনীতে, কর্পোরেট ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া দুর্নীতি, অন্যায় বা জনবিরোধী সিদ্ধান্তের কথা ফাঁস করা যাঁদের নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৮৯ সালের Whistleblower Protection Act এবং ইওরোপিয় ইউনিয়নের ২০১৯ সালের Whistleblower Protection Directive —দুইটিই এই হুইসেলব্লোয়ারদের আইনি সুরক্ষা দেওয়ার জন্য তৈরি। কিন্তু বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা ও গবেষণা রিপোর্টে দেখা গেছে, এই সুরক্ষা হামেশাই কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে।
আরও পড়ুন- আইএমএফ ঋণের অপব্যবহার: ঋণ নয়, রাষ্ট্রের ছদ্মবেশী যুদ্ধ তহবিল
ন্যাশনাল হুইসেলব্লোয়ার সেন্টারের (NWC) ২০২২ সালের এক সমীক্ষায় বলা হয়, হুইসেলব্লোয়ারদের ৬৮% তাঁদের নিয়োগকর্তার প্রতিশোধ স্পৃহার মুখে পড়েন, যার মধ্যে রয়েছে চাকরিচ্যুতি, বদলি, পেশাগত অপবাদ এবং মানসিক হয়রানি। একইভাবে ইওরোপিয় কমিশনের অভ্যন্তরীণ তথ্য বলছে— বেশিরভাগ সদস্য রাষ্ট্রই ২০১৯ সালের আইনটি কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছে। জার্মানি ও ফ্রান্স সহ বহু দেশ হুইসেলব্লোয়ারদের নিরাপত্তা বিষয়ে বাস্তব কোনও নীতিমালা তৈরি করেনি। এডওয়ার্ড স্নোডেন যখন ২০১৩ সালে NSA-র নজরদারি প্রোগ্রামের গোপন তথ্য ফাঁস করেন, তখন যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' ঘোষণা করে। অথচ স্নোডেনের ফাঁস করা তথ্যে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্র সরকার নিজের নাগরিকদের ই-মেইল, ফোন, এমনকী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমও নজরদারির আওতায় রাখছিল—বিনা পরোয়ানায়। আজ তিনি রাজনৈতিক আশ্রয়ে রাশিয়ায় বাস করছেন, যুক্তরাষ্ট্রে ফিরলে আজীবন কারাবাসের মুখে পড়বেন। চেলসি ম্যানিং, যিনি ইরাক ও আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাবাহিনীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের তথ্য উইকিলিকসে দেন, তাঁকে ৩৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়— যদিও পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট ওবামা সাজা হ্রাস করেন। ম্যানিং কারাগারে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন এবং মুক্তির পরও সামাজিকভাবে একঘরে হয়ে যান। ফ্রান্সেস হাউগেন, যিনি ফেসবুকের অভ্যন্তরীণ গবেষণা ফাঁস করে জানান যে, কোম্পানিটি ইচ্ছাকৃতভাবে হিংসা, ঘৃণা ও মানসিক অবসাদ ছড়ায় এমন কনটেন্টকে অ্যালগরিদমে গুরুত্ব দেয়, তাঁকেও কংগ্রেসে সাক্ষ্য দেওয়ার পর ফেসবুক তথা মেটা কর্পোরেশনের ভয়াবহ অপবাদ ও আইনি চাপের মুখে পড়তে হয়েছে।
যুক্তরাজ্যে হুইসেলব্লোয়ারদের ওপরও রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা আইন Official Secrets Act (1989) এক ভয়ংকর তলোয়ার হয়ে ঝুলে থাকে। এই আইনের আওতায় যারা “আস্থার লঙ্ঘন” করে সিক্রেট ফাঁস করে, তারা যেকোনও সময়ে ফৌজদারি মামলার মুখে পড়তে পারে। ক্যাথরিন গান-এর উদাহরণ এখানে প্রাসঙ্গিক। ২০০৩ সালে তিনি প্রকাশ করেন যে, ইরাক যুদ্ধের আগে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য কূটনীতিকদের ওপর নজরদারি চালাচ্ছিল যুদ্ধ অনুমোদনের জন্য। সরকারের গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁস করলেও তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। যদিও মামলা পরে তুলে নেওয়া হয় কিন্তু তাঁর পেশাগত জীবন ধ্বংস হয়ে যায়।
ফ্রান্সের হুইসেলব্লোয়ারদের সুরক্ষা এখনও বেশ দুর্বল। Anticorruption law Spain II (2016) কিছু আইনি সুরক্ষা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু এর বাস্তব প্রয়োগ এখনও প্রশ্নসাপেক্ষ। আন্তোনিও দেলতোরে, যিনি ফরাসি পারমাণবিক সংস্থা Areva-র দুর্নীতির কথা ফাঁস করেন, তাঁকে চাকরিচ্যুত করা হয় ও মানসিক হয়রানির শিকার হতে হয়। ফ্রান্সের জুলিয়েন আসাঞ্জের প্রতি সরকারি আচরণও দেখায় যে তথাকথিত মানবাধিকারপন্থী রাষ্ট্রগুলো যখন নিজেরাই তথ্য প্রকাশের হুমকির মুখে পড়ে, তখন তারা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধে যৌথভাবে উঠে পড়ে লাগে। জুলিয়েন অ্যাসাঞ্জ Wikileaks-এর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বহু যুদ্ধাপরাধের দলিল প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁকে সন্ত্রাসবাদী ও হ্যাকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ তিনি কখনই কোনও তথ্য নিজে চুরি করেননি— তিনি শুধু সত্যের বাহক ছিলেন। ২০১৮ সালে ফ্রান্সে করা একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, ৭৫% হুইসেলব্লোয়ার মানসিক স্বাস্থ্যের সংকটে পড়েন এবং ৪৫% আর্থিকভাবে ধ্বংস হয়ে যান।

জুলিয়েন অ্যাসাঞ্জ
জার্মানি বহুদিন হুইসেলব্লোয়ারদের সুরক্ষায় পিছিয়ে ছিল। ২০২৩ সালে ইওরোপিয় ইউনিয়নের নির্দেশ অনুযায়ী অবশেষে জার্মান পার্লামেন্ট একটি আইন পাস করে। এই আইনের মাধ্যমে এখন সরকারি-বেসরকারি দুই কর্মক্ষেত্রে দুর্নীতি বা অনিয়মের বিরুদ্ধে কথা বলা কর্মীদের কিছুটা আইনি সুরক্ষা প্রদান করা হয়। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। মার্টিন পোরসেন, একজন সিভিল সার্ভেন্ট, যিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের আর্থিক অপচয় ফাঁস করেন, তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানিকভাবে দমন-পীড়ন চালানো হয়। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পরও তিনি তাঁর চাকরি ফিরে পাননি। জার্মান সমাজে হুইসেলব্লোয়ারদের অনেক সময় 'বিশ্বাসভঙ্গকারী' হিসেবে দেখা হয়, ফলে তারা একাকীত্ব, পেশা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মুখোমুখি হন। ইওরোপিয় ইউনিয়ন ২০১৯ সালে EU Whistleblower Protection Directive পাস করলেও, বেশিরভাগ দেশ তা কার্যকর করেনি বা অসম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করেছে। ফলে, ফ্রান্স, জার্মানি ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যে বিশাল পার্থক্য থেকে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই স্থানীয় প্রশাসন বা কর্পোরেট ব্যবস্থাপনা আইনের অপব্যবহার করে অভিযোগকারীকে কর্মচ্যুত করে, বা তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা ঠুকে দেয়। এমনকী আইন কার্যকর হলেও “ভালো আইনজীবী” না থাকার অনিশ্চয়তায় সুরক্ষা পাওয়ার আশায় চড়া পড়ে যায়।
কানাডায় পাবলিক সার্ভেন্টস ডিসক্লোজার অ্যাক্ট (পিএসডিপিএ) ২০০৭ সাল থেকে কার্যকর, যা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের জন্য হুইসেলব্লোয়ার সুরক্ষা প্রদান করে কিন্তু এই আইনের প্রয়োগ নিয়ে তীব্র সমালোচনা রয়েছে। ডেভিড হটসন, কানাডিয়ান ফুড ইনস্পেকশন এজেন্সির প্রাক্তন কর্মকর্তা, মাংস শিল্পে অনিয়ম ও জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি তুলে ধরেছিলেন। তাঁর তথ্য সত্য হলেও, তিনি বারবার হুমকি, শাস্তিমূলক বদলি ও মানসিক হয়রানির শিকার হন। শেষমেশ তিনি চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ২০২১ সালে এক পার্লামেন্টারি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, পিএসডিপিএ আইনের আওতায় শতাধিক অভিযোগ জমা পড়লেও, মাত্র ২% মামলায় তদন্তে সত্যতা মিলেছে—এটি ব্যবস্থার ব্যর্থতাকেই তুলে ধরে।
অস্ট্রেলিয়ায় রয়েছে Public Interest Disclosure Act (2013)। তবে এই আইন এমনভাবে প্রণীত যে, অভিযোগকারী ব্যক্তিকেই পরে বিচারের মুখে পড়তে হয়। প্রাক্তন সামরিক আইনজীবী ডেভিড ম্যাকব্রাইড, আফগানিস্তানে অস্ট্রেলিয়ান সেনাবাহিনীর যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কিত নথি ফাঁস করেন, তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা চলছে। এমনকী বিচারাধীন অবস্থায় সরকারের কাছে কোনও “জনস্বার্থ” যুক্তি দেওয়া থেকেও তাঁকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। বার্নার্ড কোলারি এবং তাঁর ক্লায়েন্ট, ASIS-এর প্রাক্তন কর্মকর্তা, যাঁরা পূর্ব তিমোরে অস্ট্রেলিয়ার গুপ্তচরবৃত্তি ফাঁস করেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও দীর্ঘদিন ধরে বিচার চলেছে। এই ঘটনাগুলো অস্ট্রেলিয়ার তথাকথিত “উন্মুক্ত সরকার” সংস্কৃতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক।
দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৯৯৪ সালে গণতন্ত্রে উত্তরণের পর যে “স্বচ্ছ রাষ্ট্রব্যবস্থার” স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল, তা দুর্নীতিতে ক্রমেই জর্জরিত হয়। হুইসেলব্লোয়ারদের জন্য রয়েছে Protected Disclosures Act (2000), যা বেসরকারি ও সরকারি কর্মচারীদের নির্দিষ্ট সুরক্ষা দেয়। কিন্তু এই আইনের বাস্তব প্রয়োগ প্রায় অনুপস্থিত। চিকিৎসা ব্যবস্থাপক ববিতা ডেওকরণ গৌতেং প্রদেশের স্বাস্থ্যখাতে বড় দুর্নীতি ফাঁস করেছিলেন, তাঁকে ২০২১ সালে গাড়ির ভেতর ১২বার গুলি করে হত্যা করা হয়। তাঁর মৃত্যু বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড় তোলে কিন্তু আজও তাঁর হত্যাকারীদের রাজনৈতিকভাবে আড়াল করা হচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় তথ্য ফাঁসকারীদের অনেকেই শেষমেশ চাকরি হারান, হুমকি পান, অথবা হত্যার আশঙ্কায় আত্মগোপন করেন। সত্যের পক্ষ নেওয়ার মূল্য হামেশাই প্রাণ দিয়ে চোকাতে হয়।

ববিতা ডেওকরণ
ব্রাজিলে দুর্নীতি এক গভীর প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা, আর হুইসেলব্লোয়াররা প্রায়শই রাজনৈতিক রোষানলে পড়েন। ২০১১ সালে Federal Whistleblower Protection Law প্রণয়ন করা হলেও, তা দুর্বল ও অপর্যাপ্ত বলে গণ্য হয়। বাস্তবে সুরক্ষা না পাওয়ায় অনেকেই চুপ থাকাই শ্রেয় মনে করেন। জোসে অগাস্তো রদ্রিগেজ, যিনি তেল-গ্যাস সংস্থা Petrobras-র দুর্নীতি ফাঁস করেন, তাঁর বিরুদ্ধে ভুয়ো মামলার বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়। তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত হয়, পরিবারকে হুমকি দেওয়া হয়, অবশেষে তিনি বিদেশে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। অপারেশন কার ওয়াশ, পর্তুগিজ ভাষায় 'Lava Jato' নামে পরিচিত, ব্রাজিলের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় দুর্নীতিবিরোধী তদন্তগুলোর মধ্যে একটি। ২০১৪ সালের মার্চ মাসে শুরু হওয়া এই অভিযানটি প্রাথমিকভাবে ব্রাজিলের রাজধানী ব্রাসিলিয়ার একটি গ্যাস স্টেশনে ছোট আকারের অর্থ পাচারের তদন্ত হিসাবে শুরু হয়েছিল। কিন্তু দ্রুতই তা ব্রাজিলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গভীরে প্রোথিত দুর্নীতির বিশাল জাল উন্মোচন করে, যা বিশ্বজুড়ে আলোচনার ঝড় তোলে। তদন্তে উঠে আসে যে, রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি পেত্রোব্রাসের (Petrobras) সঙ্গে জড়িত ঠিকাদারি কোম্পানিগুলো অতিরিক্ত মূল্য দেখিয়ে চুক্তি করত এবং সেই অতিরিক্ত অর্থ রাজনীতিবিদ ও কর্মকর্তাদের ঘুষ হিসেবে দিত। শুধু নগদ অর্থই নয়, দামি গাড়ি, রোলেক্স ঘড়ি, মূল্যবান ওয়াইন, হেলিকপ্টার, বিলাসবহুল জাহাজ— বিভিন্ন উপঢৌকনের মাধ্যমে ঘুষ লেনদেন হতো। বিপুল অঙ্কের অর্থ সুইস ব্যাংকে জমা রাখা হতো এবং বাকি টাকা ছোট ছোট গ্যাস স্টেশনের মাধ্যমে নয়ছয় করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠানো হতো। দুর্নীতির মাত্রা এতটাই ছিল যে, একটি প্রকল্পের জন্য ৬ বিলিয়ন ডলার বাজেট ধরা হলেও, কাজ শুরুর দুই বছরের মধ্যে ব্রাজিল সরকার ১৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে ফেলে। অপারেশন কার ওয়াশ কেলেঙ্কারিতে বেশ কিছু ব্যক্তি তদন্তে সহযোগিতা করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেছেন, যাদের কারণে এই বিশাল দুর্নীতির জাল উন্মোচিত হয়েছে। বিচারপতি ট্রেভর জাভাস্কি সরাসরি হুইসেলব্লোয়ার ছিলেন না, তিনি এই মামলার একজন গুরুত্বপূর্ণ বিচারক ছিলেন এবং তাঁর রহস্যজনক মৃত্যু অনেকের মনে প্রশ্ন তুলেছিল।
আরও পড়ুন-বিশ্বের বিপদ বাড়বে নিমেষেই! কেন এত গুরুত্বপূর্ণ ইরানের হরমুজ প্রণালী?
জাপান এমন এক সমাজ যেখানে প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য এবং ‘মুখ বাঁচানো’— এই দু'টি মূলনীতি প্রায় ধর্মীয় গুরুত্ব পায়। ফলে হুইসেলব্লোয়িংকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ হিসেবে দেখা হয়। যদিও ২০০৬ সালে Whistleblower Protection Act চালু হয়, তবে তা কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ অভিযোগের ক্ষেত্রেই কার্যকর। প্রকৌশলী হিরোশি কুরাতা ফুকুশিমা পরমাণু দুর্যোগের আগে TEPCO-এর নিরাপত্তা ত্রুটি সম্পর্কে রিপোর্ট করেছিলেন, তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। পরে তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন: “জাপানে হুইসেলব্লোয়ারদের জন্য সবচেয়ে ভয়াবহ শাস্তি হচ্ছে— তাঁদের যেন সমাজে আর কোনও অস্তিত্ব থাকে না।” আত্মহত্যা প্রবণতা, মানসিক বিপর্যয়, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা— এই তিনটি ছায়া জাপানে হুইসেলব্লোয়ারদের নিত্যসঙ্গী।
দক্ষিণ কোরিয়ায় Anti-Corruption and Civil Rights Commission হুইসেলব্লোয়ারদের অভিযোগ গ্রহণ করে। ২০০১ সালে গৃহীত Act on the Protection of Public Interest Whistleblowers কিছুটা এগিয়ে দিয়েছিল কিন্তু কর্পোরেট ও আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার দাপটে আইনি কাঠামো বারবার ব্যর্থ হয়েছে। চোই জুন-ওং একটি বড় নির্মাণ সংস্থার দুর্নীতির কথা ফাঁস করেন, তাঁকে কোর্ট-অফ-ল অর্ডারে মানসিক রোগী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তাঁর চিকিৎসা নথি ফাঁস করে সামাজিকভাবে অপদস্থ করা হয়। তিনি পরে কোরিয়ান প্রেস ক্লাবে দাঁড়িয়ে বলেন: “যদি সত্য বলা মানেই পাগল হয়ে যাওয়া হয়, তাহলে কোরিয়ায় আমরা সবাই অসুস্থ।” দক্ষিণ কোরিয়ার গণমাধ্যম উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর হলেও কর্পোরেট শক্তির বিরুদ্ধে কেউ গেলে সেই ব্যক্তিকে সমাজের বাইরে ঠেলে দেওয়ার একটি সুগঠিত যন্ত্র হিসেবে সক্রিয় হয়ে ওঠে।
উন্নত পশ্চিম যেমন হুইসেলব্লোয়ারদের হয়রানির এক ‘ভদ্রসজ্জিত সংস্কৃতি’ চালায়, তেমনি দক্ষিণে (গ্লোবাল সাউথে) একই কাজ হয় নির্মম, খোলামেলা দমন-পীড়নের মাধ্যমে। তবে উদ্দেশ্য একই— রাষ্ট্র ও কর্পোরেট কাঠামোর অপরাধ ঢেকে রাখা, সত্যভাষীকে নিঃশেষ করা। একজন হুইসেলব্লোয়ার গোটা সমাজের জন্য লড়েন, একা লড়েন, আমাদের জন্য। কিন্তু আমরা কি তাঁদের সঙ্গী হচ্ছি? না কি রাষ্ট্রের সুবিধাজনক নীরবতাই মেনে নিচ্ছি? উত্তর আমাদের জানাই।




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp