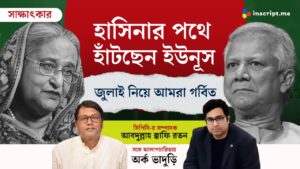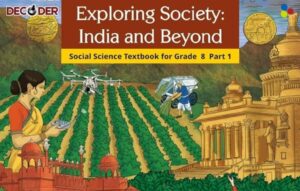পশ্চিমবঙ্গে জাতপাত নেই! দাবির আড়ালে লুকিয়ে যে আসল সত্য
West Bengal Casteism: রাজ্য যে জাতপাত মুক্ত এই বিশ্বাস কি একদিনে জন্মেছে? নাকি গঠনতান্ত্রিক উপায়ে বাংলা যে জাত প্রশ্নে ব্যতিক্রম সেটা নির্মাণ করা হয়েছে? খুঁজে দেখা জরুরি।
কাটোয়ার গিধগ্রামের শিবমন্দিরে ‘দাস’ সম্প্রদায়ের মানুষজন স্বাধীনতার ৭৮ বছর পর নিজেদের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা পেলেন। পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে গ্রামের ‘অস্পৃশ্য’ চামাররা মন্দিরে ঢুকলেন, সংবিধানের আর্টিকেল ২৫-এ ন্যাস্ত ধর্মাচরণের অধিকার প্রয়োগ হলো, পাশাপাশি ৩৫০ বছরের প্রথা ভাঙা গেল। তালিকা এইখানেই শেষ নয়। রবিদাসীয় মহাসঙ্ঘ তরফ থেকে সম্প্রতি একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়, সেখানে বলা হয় কেতুগ্রামের গঙ্গাটিকুরি শিবমন্দির, বিল্লেশ্বর শিবমন্দির, নদীয়ার কালিগঞ্জে একই পরিস্থিতি। প্রাথমিকভাবে নিজেদের প্রগতিশীল দাবি করা বাঙালি নিজেদের ইমেজ বাঁচাতে গিধগ্রামের মতো ‘এক অজ পাড়াগাঁয়ের’ নিছকই বিছিন্ন বলে উড়িয়ে দিতে শুরু করে। কিন্তু তালিকা লম্বা হতে শুরু করতেই কপালের ভাঁজ বাড়বে নিশ্চিত; প্রশ্ন উঠবে,"জাতপাত এসব তো বিহার উত্তরপ্রদেশের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গে এসব এল কবে!" কলকাতা হাইকোর্টের এক বিচারপতি নদিয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে সম্প্রতি বলেন, "বাংলায় তো এসব ছিল না। এখনও এই ধরনের সমস্যা বাংলায় নেই বলেই বিশ্বাস করি।" এ যেন অতীতেরই অনুরণন। ১৯৮০ সালে মণ্ডল কমিশনের প্রতিক্রিয়ায় তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছিলেন, "পশ্চিমবঙ্গে শুধুমাত্র দু'টি জাত, ধনী এবং দরিদ্র"। রাজ্য যে জাতপাত মুক্ত এই বিশ্বাস কি একদিনে জন্মেছে? নাকি গঠনতান্ত্রিক উপায়ে বাংলা জাত প্রশ্নে ব্যতিক্রম এমন ধারণা নির্মাণ করা হয়েছে? খুঁজে দেখা জরুরি।
বাংলার এই ব্যতিক্রমী চরিত্র নির্মাণের একটা রাজনৈতিক ইতিহাস আছে। স্বাধীনতার পূর্বে জাতি নমঃশূদ্র, রাজবংশী ইত্যাদি জাতি আন্দোলন হলেও স্বাধীনতার এবং দেশভাগের উদ্বাস্তু প্রশ্নে তা ঢাকা পড়ে যায়। পরবর্তীতে বাম রাজনীতিতে ‘শ্রেণি’ মূলত প্রধান পরিচয়ের জায়গা দখল করে। পশ্চিমবঙ্গে দলিত জনগোষ্ঠী মোট জনসংখ্যার ২৩.৫১% এটি ভারতীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে তৃতীয় সর্বোচ্চ দলিত জনসংখ্যার। ভারতজুড়ে মোট দলিত জনগোষ্ঠীর ১০.৬৬% পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করে,যা সর্বভারতীয় স্তরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। ঔপনিবেশিক বাংলায় শক্তিশালী দলিত সংগঠনের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও জাতি কখনও নির্বাচনী রাজনীতির প্রধান নিয়ামক হয়ে ওঠেনি। কোনও বড় রাজনৈতিক দল জাতিভিত্তিক দাবিকে তাদের মূল ইস্যু হিসেবে গ্রহণ করেনি। কারণ এই জাত প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গ যে ভারতের বাকি রাজ্য থেকে সম্পূর্ণই আলাদা এই জনবিশ্বাসের একটি দৈনন্দিন এবং একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ আছে।

আরও পড়ুন- ‘অপর’-কে বুঝে ফেলার বিভ্রান্তিকর মহত্বের অহংকে প্রশ্ন করে যান গায়ত্রী
জুরগেন হ্যাবারমাস বলেছেন, একটি সমাজে দৈনন্দিন জনপরিসর নির্মিত হয় তার সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও, বিদ্যাজীবী পরিসরের আলোচনার মধ্যে দিয়ে। আমাদের রাজ্যে এই জনপরিসর পুরোপুরি কলকাতা-কেন্দ্রিক। সেখানে জনপরিসর নির্মাণের ক্ষেত্রগুলিতে বামুন, বদ্যি আর কায়েত ছাড়া বাকি নিচু জাতের প্রতিনিধিত্ব নেই বললেই চলে। বাংলার বহুল প্রচলিত সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে লেখকগণের বিগত ৭৫ বছরের পদবির তালিকা করলেই বোঝা যাবে। রেডিও, টিভি সঞ্চালক জনগোষ্ঠীর মধ্যেও ‘জলঅচল’ জাতের জনসংখ্যার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নেই বললেই চলে। একই অবস্থা ছিল বিদ্যাজীবিতার অঙ্গনেও। এই প্রসঙ্গে একটা ছোট উদাহরণ দিলে হয়তো বিষয়টা আরও একটু পরিস্কার হবে। অর্থনীতিতে নোবেল পাওয়ার পর ইন্ডিয়া টুডে-র রাহুল কমল অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। অভিজিৎবাবু সেখানে বলেন, তিনি জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে না এলে জাতব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি অজ্ঞ থেকে যেতেন কারণ তাঁর আগের বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসিডেন্সিতে তাঁদের ক্লাসে তথাকথিত ছোট জাতের কেউ পড়তই না। ফলে তাঁর মনে হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে বুঝি জাত ব্যবস্থা নেই। এইভাবে দৈনন্দিন ধারণা আস্তে আস্তে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে শুরু করে। এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে কি সত্যি পশ্চিমবঙ্গে জাতকেন্দ্রিক বৈষম্য নেই? পরিসংখ্যানের দিকে তাকানো যাক।
সন্দীপ মণ্ডল ভারতীয় মানব উন্নয়ন সমীক্ষার (India Human Development Survey ২০১২) পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন। পশ্চিমবঙ্গে একদিকে ভদ্রলোক শ্রেণি জাতিভিত্তিক পদ্ধতিকে অবজ্ঞা করে, অন্যদিকে বিয়ের মতো সামাজিক প্রতিষ্ঠানে জাতি প্রভাবশালী থেকে যায়। আমাদের রাজ্যে ৯০.৬% বিবাহই সবর্ণ বিবাহ, অর্থাৎ একই জাতের মধ্যে বিয়ে,যা জাতীয় গড়ের চেয়ে সামান্য বেশি। খবরের কাগজে বিয়ের বিজ্ঞাপন দেখলেও বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। আবার শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতিগত বৈষম্য বিশেষভাবে স্পষ্ট। উচ্চবর্ণের ৭৮.৭৪% মানুষ বিদ্যালয়ে গিয়েছে, যেখানে দলিতদের ক্ষেত্রে এই হার ৬৭.৭৯%। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে যথাক্রমে ২৬.৯৫% ও ৩০.৬১% দলিত শিক্ষিত হলেও উচ্চশিক্ষার স্তরে এসে এই হার মারাত্মকভাবে কমে যায়। উচ্চবর্ণের মধ্যে ১০.৩৭% মানুষ স্নাতক স্তরে পৌঁছতে পারলেও, দলিতদের মধ্যে এই হার মাত্র ২.৯৭%। অন্যদিকে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও এই বৈষম্য প্রকট। সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে উচ্চবর্ণের প্রতিনিধিত্ব ৭২.৯%, যেখানে দলিতরা মাত্র ১৩%। বিশেষত গ্রুপ-এ ক্যাডারের উচ্চ বেতনের চাকরিতে উচ্চবর্ণের উপস্থিতি ৮১.৩৯%, যা প্রমাণ করে সংরক্ষণ নীতি কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। স্থানীয় প্রশাসনের ক্ষেত্রেও এই চিত্র একই রকম। পঞ্চায়েত সচিব, গ্রাম সেবক ও লেখপাল পদগুলোতে কোনও সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় উচ্চবর্ণের আধিপত্য রয়েছে। দলিত, তফসিলি জাতি (ST) ও অনগ্রসর শ্রেণির (OBC) প্রতিনিধিত্ব শুধুমাত্র সংরক্ষিত পদেই সীমাবদ্ধ।
এই তথ্যে স্পষ্ট হয় যে, জাতি পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। জাতি বিয়ের মতো ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সরকারি চাকরি, সামাজিক নেটওয়ার্ক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে। তবুও, জাতি কখনও রাজ্যের নির্বাচনী রাজনীতির প্রকাশ্য ইস্যু হয়ে ওঠেনি। আসলে,পশ্চিমবঙ্গের ভদ্রলোক শ্রেণি জাতিভিত্তিক বিভাজনকে সচেতনভাবে অস্বীকার করেছে এবং জাতির অস্তিত্বকে আড়াল করে রেখেছে। জাতি কখনই পশ্চিমবঙ্গের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী এজেন্ডার অংশ হয়নি। বামফ্রন্টের শ্রেণিকেন্দ্রিক রাজনীতি জাতির প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে গেছে। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস ও ভদ্রলোক শ্রেণির আধিপত্যে, যা জাতিগত বাস্তবতাকে অস্বীকার করে এক ‘ব্যতিক্রমী’ ও ‘জাতিহীন’ পরিচয়ের ধারণা তৈরি করেছে।
আরও পড়ুন- জাতপাত ব্যবস্থা থেকে মুক্তির বড় উপায় গাজনের সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া

এ তো গেল রাষ্ট্রকেন্দ্রিক জাতের বিন্যাস কিন্তু জাতের সামাজিক উলম্ব বিভাজন এবং তার বৈষম্যের চিত্র নিয়েও কথা বলা জরুরি। পোস্টবক্স কলকাতার বাইরে, গ্রামে এবং মফসসলে জাতি প্রশ্নের দৈনন্দিন চিত্র আরও জটিল। রাষ্ট্রের হিসাবে যারা সবাই তফশিলি জাতির মধ্যে পড়ে, সেই সাব-কাস্টের মধ্যেও বিভেদ-বৈষম্যে অনেক। যে বাগদি মেয়ে শুঁড়ির বাড়িতে বাসন মাজার কাজ করে তাঁকে কাজ শেষে খাবার দেবার সময় শুঁড়িবাড়ির বউ দূর থেকে খাবার পরিবেশন করে, পাছে বাগদি মেয়ের ছোঁয়া তার কাপড়ে লেগে যায়। তাঁর চা খাবার কাপ আলাদা, সে দুয়ারে বসে চা খাবে, ঘরের ভিতরে তার প্রবেশ নেই। পুণ্ড্রদের দুর্গা মন্দিরে বায়েন ঢাক বাজাবে কিন্তু নৈবেদ্য দেবার সময় তাঁকে উপর থেকে ঢেলে দেওয়া হবে। রাষ্ট্রের চোখে শুঁড়ি, বায়েন, বাগদি সবাই তফশিলি জাতি কিন্তু সামাজিক ভাবে বায়েন বাগদি ‘ছোটলোক’।
যদিও বেশ কিছু বছর ধরে ‘মতুয়া’ শব্দের সঙ্গে বাঙালি কিছুটা হলেও অবগত, এর জন্য ঋণ স্বীকার করতে হয় দু'টি ঘটনার, এক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণা যা বাঙালি বিদ্যাজীবীদের ‘দলিত’ শব্দের সঙ্গে পরিচয় ঘটালেন। দুই, পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতে ‘ঠাকুরবাড়ির’ প্রবেশ এবং ‘মতুয়া’ ভোটব্যাংক যা মাঠে ময়দানে ‘দলিত’ শব্দের রাজনীতিকরণ ঘটিয়েছে ইতিমধ্যে। কিন্তু শহুরে ভদ্রসমাজে জাতি নিয়ে আলোচনা করা শিষ্টাচারবহির্ভূত ও অস্বস্তিকর বলে গণ্য হয়, কারণ এটি জাতিহীন, মার্জিত সমাজের স্বাভাবিকতার পরিপন্থী বলে মনে করা হয়। কাঞ্চা ইলাইয়া তাই সত্যই বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে জাতের প্রশ্নটি উপসর্গহীন ক্যানসার; মাঝে মাঝে গিধগ্রামের মতো ঘটনা একটু ব্যথার মতো মাঝে মাঝে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp