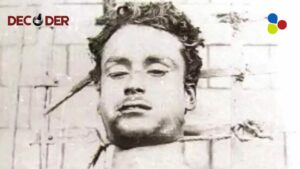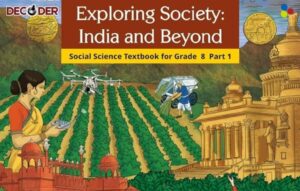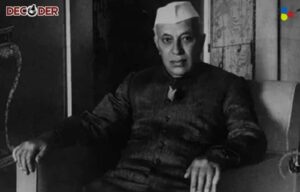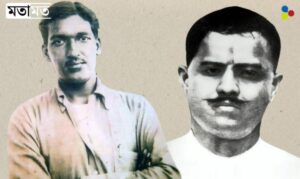প্লাস্টিক, ডিজে, গাছ কাটা — সোনাঝুরি হাটের যে কুৎসিত দশা চোখে দেখা যায় না
Shonajhuri Haat: সোনাঝুরির হাটে স্থানীয়দের উৎপন্ন তো কোন ছাড়। লুধিয়ানা, জলন্ধর, হরিয়ানা আর কলকাতার বড়বাজারের মালের ছয়লাপ। তাকেই শান্তিনিকেতনের হস্তশিল্প বলে চালানোর চেষ্টা চলছে।
কুমোরপাড়ার গরুর গাড়ি কি প্রতি শুক্রবার বক্সীগঞ্জের হাটে যেত? ভাগ্নে মদন কি বংশীবদনের সঙ্গে নিয়মিত থাকত? এইসব মামুলি প্রশ্নে খানিকটা হলেও আমাদের অনেকেরই শিশুকাল কেটেছে। ইংরেজি মাধ্যমের দাপটের সঙ্গে সঙ্গে তা উধাও হয়েছে। হাট ক্রমে একটা পোশাকি শব্দেই বেঁচে আছে। বড়বেলায় এসে জেনেছি, শুধু হাট কবিতাটিই নয়, বৌঠাকুরাণীর উপন্যাস বৃত্তান্ত থেকে পল্লীসমাজের বিস্তৃতি থেকে নানা চিঠিপত্রে হাটের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছিল এক নিগূঢ় সম্পৃক্ততা। সে সমস্ত উদাহরণ মায় দৃষ্টান্ত লিখে বর্তমান প্রতিবেদনটি ভারাক্রান্ত করতে চাই না। তারচেয়ে বরং হাট নিয়ে দু-চার বাক্য লিখে মূল বিষয়মুখে ঢুকব। তা হলো, হাট বসে উদয় অস্ত। সপ্তাহের নির্দিষ্ট একদিন। কোথাও কোথাও দু'দিনও বসে। কিন্তু সারা সপ্তাহ কোনওমতেই নয়। তবে বাজার চলে সন্ধ্যার পরও, সপ্তাহভর। এই হলো হাট ও বাজারের প্রাথমিক পার্থক্য। শহর থেকে শুধু নয় বৃহত্তর পশ্চিমবঙ্গে হাট নিপাতনে গেলেও এখনও গ্রাম-মফসসলে তার এক-আধটার খোঁজ মেলে কিন্তু তার চরিত্র যাচ্ছে বদলে।
এখন হাট বসে পাঁচতারার উঠোনে, বহুতল কমপ্লেক্সের কোলে, পুজোর অঙ্গসজ্জায় আর পর্যটকদের খাতিরে কনজিউমার প্রোডাক্ট বিপণনের মঞ্চ হিসেবে। হাটের শুদ্ধসত্ত্ব চরিত্র নেই এখানে। ভোক্তার বাবুগিরি আছে। বেনামের এই হাটই আজ সমাদরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কোণঠাসা হতে হতে আদতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে পণ্য সমাজের দায় ভার বইতে গিয়ে। এর কারণ কি শুধুই নগরায়ন? না, শহুরে মানুষের মনন ও চাহিদার সমীকরণেই তা জব্দ হয়ে গেছে। সে গেছে খোলা বাজারের জয়গানে, ঐতিহ্যলালিত মেধা ও মননের উল্টো বাঁকে। অর্থনীতির অঙ্কে এই হাট শব্দটিকে যেভাবে দোহন করা হয়েছে বা হচ্ছে তা বাঙালি সমাজের ধারাবাহিক সেই অনপনেয় স্মৃতিকে চিরতরে মুছে দেবে কিনা জানা নেই। তবে প্রকৃত 'হাট' যে বর্তমান সমাজসংস্থায় প্রত্যাখ্যাত ও উপেক্ষণীয় তা হলফ করে বলা যায়।

নিউটাউনের সোনাঝুরি হাট
আরও পড়ুন- মদ, মাংস এবং … হোটেল-রিসর্টময় শান্তিনিকেতন এখন যেখানে দাঁড়িয়ে
তবে যে কথা জানাতে এত শব্দের আয়োজন সেটা হলো শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরির হাটের চরম এক বিধিনিষেধ ভাঙা, ঐতিহ্য বা নিয়মকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো অব্যবস্থা। এখানে হাট প্রতিদিনই বসে। এখানে হাট সন্ধ্যার পর মোফোনের আলো কিংবা ব্যাটারি লাইটে চলে। এ হলো শান্তিনিকেতন পর্যটন কেন্দ্রের শ্রীক্ষেত্র।
রবীন্দ্রনাথ নয়, শান্তিনিকেতন নয়, চিত্রকলা-ভাস্কর্য নয়, নদী জঙ্গল নয়, আদিবাসীদের গ্রামও সেই অর্থে নয়। এখন এখানে পর্যটনের মূল আকর্ষণ সোনাঝুরির হাট। যার এককালীন ডাকনাম ছিল শনিবারের হাট। যার উৎপত্তি দু-দশক পিছিয়ে ২০০৪ বা ২০০৫-এ। কিছু শিল্পপ্রেমী উদ্যোগী (মূলত চিত্রকলা) মানুষ এই হাটের আয়োজন করেছিলেন এক সাঁওতাল কৃষকের ছোট একখণ্ড জমির ওপর। তিনি এমনিতেই জমিটি হাটের ব্যবহারের জন্য দেন। এইভাবে শুরু হয় শনিবারের হাট।
কেমন ছিল সেই হাট? নিজের চোখে সেই হাট দেখেছি এবং তারিফ করেছি। সেই হাটের শুরুয়াত নিয়ে শান্তিনিকেতন নিবাসী আশ্রমিক ও লেখিকা অহনা বিশ্বাসের লেখা থেকে এখানে খানিকটা উদ্ধৃত করি।
১ . প্রাকৃতিক উপাদান ছাড়া কোনও কৃত্রিম বস্তু সেখানে ব্যবহার করা যেত না। প্লাস্টিকের প্যাকেটের তো কথাই নেই।
২.মাথায় কোনও ছাউনি ব্যবহার হতো না।
৩. আগুন জ্বালানো যেত না। যেসব খাবার ও চা-কফি বিক্রি করা হতো, তা সবই বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে হতো। এখানে বানানো হতো না। বিক্রির পর আবর্জনা পরিষ্কারের দায় তাদেরই ছিল।
৪. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এই হাটে শুধু কারিগর বা শিল্পীরাই বসতে পারতেন। কোনও মিডলম্যান বা ফড়ে বসতে পারত না। ফলে বিক্রেতা প্রচুর বিক্রয়দ্রব্য জড়ো করতে পারত না। এই কারিগরদের অবশ্যই স্থানীয় বাসিন্দা হতে হতো।
৫. ডিজাইনের বিভিন্নতা ও নতুনত্বের দিকে নজর দেওয়া হতো। এ বিষয়ে স্বাভাবিক তর্কবিতর্ক থাকলেও এর প্রয়োজনীয়তা সবাই মেনে নিত।
৬. প্রতি শনিবার মধ্যাহ্ন পার হলে এই হাট বসত। শেষ হতো অন্ধকার নামলে। কোনও আলো জ্বালানো হতো না। কোনওভাবেই মাইকের ব্যবহার হতো না।
৭. হাট বসত সোনাঝুরিতে ব্রিজ পার হয়েই, যাকে আমরা ভাঙা খাল বলি, তার পাশে।
৮. প্রথম প্রথম নিয়ম ছিল, যার বিক্রি হবে, সে মেলা কমিটিকে একটাকা করে দেবে, যার বিক্রি হবে না, সে কিছু দেবে না। পরে সবাইকেই একটাকা করে দিতে হতো।
৯. হ্যাঁ এটাও বলা দরকার, চর্মজাত দ্রব্যও নিষিদ্ধ ছিল।
এবার প্রশ্ন হলো, আজ কেন এই প্রতিটি বিষয় আমূল পাল্টে গেল? মানে, তার বিপরীত কাজকারবারই কেন জোরদার ভাবে চালু হলো?
দিনে দিনে সেই সংক্ষিপ্ত পরিসরের হাট ক্রমশ বাড়তে থাকল। ভেস্টেড জমি থেকে ফরেস্টের জমি সবই অধিকৃত হলো হাটের নামে ও তা ঘটল রাজনৈতিক সহায়তায়। দুর্মূল্য সব গাছ রাতের অন্ধকারে সাবাড় করে দেওয়া হলো। জঙ্গল চুলোয় গেল। এক নতুন বিস্থাপন জায়গা পেল প্রকৃতি ধ্বংস করে। সোনাঝুরির হাট এভাবেই দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বেড়ে চলল। আজ তা বাড়তে বাড়তে গোটা ক্যানাল পাড়ের অনেকটাই গিলে বসেছে। প্লাস্টিক আর কাগজের ঠোঙায় সমস্ত এলাকা আবর্জনার লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে। কারও কোনও তাপ উত্তাপ নেই। লক্ষ্য শুধু, টাকার বিনিময়ে ব্যবসাকে জায়গা করে দেওয়া। এ এক মারাত্মক ব্যবসায়িক চক্র। যেখানে সরকার স্বয়ং পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ মদদদাতা (হাটের লেজে কর্মতীর্থ বসেছে) সেখানে পরিবেশের দায় কে নেবে? একাধিক বেআইনি হোটেল ও রিসর্ট তৈরি হয়েছে এই বন দপ্তরের জায়গাতেই। সন্ধের পরে হাট সংলগ্ন এই হোটেলগুলিতে কুৎসিত এলইডি আলোর ঝকমকানির সঙ্গে শুরু হয় পিলে চমকানো ডিজে। বেশিরভাগ হিন্দি ও ভোজপুরি 'বিড়ি জ্বলাইলে' টাইপ গান। কর্ণপটাহের দফারফা। কিছুদিন আগে ধরা পড়েছে যে, সেখানে নিয়মিত ব্লু ফিল্মের শুটিং চলছে। তা নিয়ে খানিকটা হইচই হতে বন্ধ করা হলো রিসর্ট। আবার কিছুদিন পর খুলে গেল অদৃশ্য হাতের ইশারায়। যেই কে সেই!

ওই যে লিখেছি, এই হাট ছিল গ্রামীণ পরিসরে একটি শিল্পবান্ধব আয়োজন। আশেপাশের গ্রামের চাষিদের ক্ষেতের উৎপন্ন ফসল, ঘরে তৈরি আচার থেকে কাঁথাফোঁড়ের সামগ্রী, নানা হস্তনির্মিত শিল্পনিদর্শন, লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে পসরা সাজিয়ে বসতেন স্থানীয় মানুষরা। ঠিক সেভাবে ব্যবসা কেন্দ্র ছিল না এই হাট। কেনাবেচা ছিল কিন্তু মুনাফার এই প্রমত্ত বহদ্দারহাট বেশরম চেহারাটা ছিল না। গাছের ছায়া ছিল, মাইক ছিল না। ক্রেতা ছিল, ভিড় ছিল না।
আরও পড়ুন- পলাশের ডাল ভাঙা, মদের মোচ্ছব | শান্তিনিকেতনে দোলখেলার শ্মশানযাত্রা
এখন আছে মাঝারি ও ছোট পুঁজির উচ্চকিত বোলবোলাও। স্থানীয়দের উৎপন্ন তো কোন ছাড়। লুধিয়ানা, জলন্ধর, হরিয়ানা আর কলকাতার বড়বাজারের মালের ছয়লাপ। তাকেই শান্তিনিকেতনের হস্তশিল্প বলে চালানোর চেষ্টা চলছে। বাইরের লোকের অর্থে চলছে দোকান। স্থানীয়রা আজ এখানে সংখ্যালঘু। সিংহভাগ ক্রেতা ও বিক্রেতা শহরের ব্যবসায়ী ও বোলপুরের দোকানদার, যাদের দু-চারটে দোকান ছিল এবং এখনও আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।
কলকাতায় ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বুটিকের মালিকরা এখান থেকে পোশাক ও অন্যান্য দ্রব্য কম দামে কিনে শহরে চড়া দামে বেচতে নিয়ে যাচ্ছে। ফি-সপ্তাহে গাড়ি বোঝাই করে মাল আসছে। সেই মাল কিনছে আশেপাশের শহর ও কলকাতার লোকজন। আর আছে অঢেল পর্যটকদের যাওয়া আসা। শান্তিনিকেতন নয়, বর্তমানে বোলপুর শান্তিনিকেতন পর্যটন কেন্দ্রের উন্মত্ততা, যাকে আজকাল 'ক্রেজ' বলে ডাকে লোকে, তুঙ্গে তুলেছে সোনাঝুরির হাট। এখানে গেলেই সুরে-বেসুরে তথাকথিত বাউল গান শোনা যায়, তাঁদের সঙ্গে ছবি তোলা যায়। কিছু না হোক, ওঁদের থেকে একটা তালবাদ্যযন্ত্র নিয়ে বেতালা পেটানো যায়। আর নতুন সংযোজন হচ্ছে সাঁওতালরা। তারাও সোনাঝুরির হাটে নাচতে আসে। মেলায় আসা মহিলারা তাদের সঙ্গে নাচার চেষ্টা করে। তথাকথিত বাউল আর সাঁওতালদের কিছুটা রোজগার হয়। এখন তো এই অঞ্চলে নিজের মতো ছবি তুলতে গেলেও টাকা চায়।
শেষ করব এই সোনাঝুরি হাট সংলগ্ন রাস্তার অবস্থা জানিয়ে। প্রতিদিনই, বিশেষ করে শনি-রবিবার ও রাস্তায় যায় কার সাধ্য। গাড়ি, টোটো আর বাইকে ছয়লাপ। 'কার পার্কিং' গোছের কিছুটা জায়গা আছে। কিন্তু দু-চাকা, তিনচাকা, চারচাকা সব ওই একফালি সরু ক্যানাল রোডের ওপর। বল্লভপুর থেকে প্রান্তিক স্টেশন যাওয়ার এটাই মূলত রাস্তা। যাতায়াতের উপায় নেই। যেতে হলে তিন কিলোমিটার রাস্তা চোদ্দ কিলোমিটার ঘুরে যেতে হবে। টাকা লাগবে চারগুণ। দরিদ্র, সাধারণ মানুষের কোনও উপায় নেই। তাতে কার কী! বিনোদনের সঙ্গে মুনাফার এ তো শক্ত গাঁটছড়া বাঁধা!
প্রশাসন ঝোল খাচ্ছে শুধু।




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp