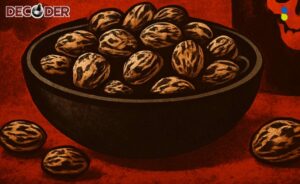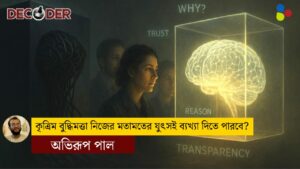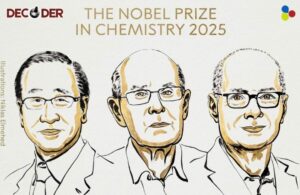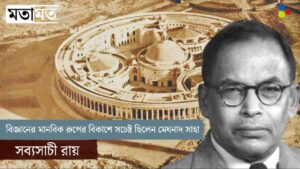মাল্টিভার্স সত্যিই আছে? ২২৫ বছরের প্রাচীন পরীক্ষার আধুনিক ব্যাখ্যা যা বলছে
Double Slit Experiment: মাল্টিভার্স তত্ত্ব বলে যে আমাদের মহাবিশ্বই একা নয়, এর অনেকগুলো দোসর রয়েছে, যারা একে অপরের সঙ্গে সমান্তরালভাবে থাকতে পারে
সনাতনী পদার্থবিদ্যার ধারণায়, একটি কণা কখনও দুটো আলাদা আলাদা জায়গায় একই সময়ে থাকতে পারে না, কিন্তু কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় সেটি হতে কোনও বাধা নেই। অন্যভাবে বললে বলা যায়, সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানের জগৎ যেখানে নির্ধারণবাদী, সেখানে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার জগত সম্ভাবনাময়। সম্প্রতি, পদার্থবিদ্যার ইতিহাসে বহুল আলোচিত, ডাবল-স্লিট বা দ্বি-ছিদ্র পরীক্ষায় বিজ্ঞানীরা এমন কিছুর সন্ধান পেয়েছেন, যা দেখে মনে হচ্ছে, বাস্তবেই একটি ফোটন (আলোর কণা) একই সময়ে দুই জায়গায় থাকতে পারে। এই ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠিত হলে, অনেকগুলি বিশ্ব, অর্থাৎ মাল্টিভার্স তত্ত্বের যে ধারণা বিজ্ঞানী মহলে প্রচলিত আছে, তা মুখ থুবড়ে পড়বে।
মাল্টিভার্স তত্ত্ব কী?
এই তত্ত্ব বলে যে আমাদের মহাবিশ্বই একা নয়, এর অনেকগুলো দোসর রয়েছে, যারা একে অপরের সঙ্গে সমান্তরালভাবে থাকতে পারে; এমনকী তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল সূত্রগুলি স্বতন্ত্র হলেও।
আজ থেকে দুই শতাব্দীরও বেশি আগে, ব্রিটিশ পদার্থবিদ টমাস ইয়ং সর্বপ্রথম এই পরীক্ষাটি করেছিলেন। তিনি একটি আলোক উৎসের সামনে দুটো সরু রেখা ছিদ্র (double-slit) রেখে দেখেন পর্দায় তার কী পটি পাওয়া যায়। তিনি দেখেন, এক্ষেত্রে আলো তরঙ্গের মতো আচরণ করে দ্বি-ছিদ্রের পেছনে থাকা পর্দায় ঢেউয়ের মতো একধরনের পটি বা রেখাচিত্র তৈরি হয়। উৎস থেকে নির্গত আলো অর্থাৎ ফোটন কণার স্রোত দ্বি-ছিদ্র অতিক্রম করে পর্দায় উজ্জ্বল বা অন্ধকার পটি তৈরি করে। ফোটন কণার স্রোত বাদ দিলেও, যদি হাতে গোনা কয়েকটি ফোটনও দ্বি-ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে, পর্দায় তার তরঙ্গ ধর্ম প্রতিফলিত হয়। এর থেকে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন, আলো একইসঙ্গে কণা ও তরঙ্গ — দুই ধর্মই মেনে চলে। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা বলে, আলো অর্থাৎ ফোটন কণা দু'টি ছিদ্রের মধ্য দিয়েই একসঙ্গে যেতে পারে! সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা ভাবতে পারি, কয়েকটি ফোটন বাঁ পাশের ছিদ্র দিয়ে, কয়েকটি ডান পাশের ছিদ্র দিয়ে যেতে পারে। কিন্তু না, কোয়ান্টাম তত্ত্ব আপনাকে ভাবতে বাধ্য করে যে আপনি যদি উৎস থেকে একটি ফোটনও পাঠান, সেটি দু'টি ছিদ্র দিয়েই যাবে।
আরও পড়ুন- চাঁদে বা মহাকাশে কীভাবে অন্তর্বাস কাচেন মহাকাশচারীরা? অবাক করবে যে তথ্য

মাল্টিভার্সের কাল্পনিক চিত্র
ফোটন ঠিক কোন ছিদ্রটা দিয়ে গেল, সেটা জানার চেষ্টা করলেই গণ্ডগোল বাঁধে। কাজের সুবিধার্থে আমরা যদি দুটো ছিদ্রের মুখেই একটা করে ডিটেক্টর লাগিয়ে দেখার চেষ্টা করি, ঠিক কোন ছিদ্র দিয়ে ফোটনটি অতিক্রম করেছে, তখন পর্দায় তরঙ্গের সেই সুন্দর প্যাটার্ন হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। এই ব্যাপারটাকে বোঝাতে পদার্থবিজ্ঞানীরা ‘ওয়েভ ফাংশন’ বা ‘তরঙ্গ আপেক্ষক’ নামক একধরনের গাণিতিক ধারণা ব্যবহার করেন, যেটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাব অ্যাটমিক কণাগুলোর বিভিন্ন তথ্য জমা করে রাখে; এর সাহায্যে বোঝা যায়, ফোটনের সম্ভাব্য অবস্থান কোথায়। কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের এইসব তাত্ত্বিক কচকচানি না হয় মানা গেল, কিন্তু বাস্তবে এর কি কোনও অস্তিত্ব আছে? শুরু হলো এক মহা জল্পনা।
তখনই আসরে নামে মাল্টিভার্স তত্ত্ব। এই তত্ত্ব বলে, বিজ্ঞানীরা যখন ফোটনের গতিপথ মাপার চেষ্টা করছেন, তখন আসলে বিশ্ব দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়— এক বিশ্বে ফোটন ডান দিকের ছিদ্র দিয়ে যায়, অন্য বিশ্বে বাঁ দিকে। অন্যভাবে বললে, প্রতিটি সম্ভাবনার জন্য তৈরি হয় এক একটি নতুন বিশ্ব!
কিন্তু একদল জাপানি গবেষক দাবি করেছেন যে, তাঁরা পরীক্ষায় দেখেছেন একটি ফোটন একইসঙ্গে দু'টি ছিদ্র দিয়েই গেছে — অর্থাৎ মাল্টিভার্স তত্ত্বের সমান্তরাল মহাবিশ্বের অবতারণা আর না করলেও চলে! গবেষক দলের প্রধান হফম্যানের মতে, ওয়েভ ফাংশন শুধুমাত্র একটি তাত্ত্বিক ধারণা নয়,তার বাস্তবিক প্রয়োগ রয়েছে।

ডবল-স্লিট পরীক্ষা
হফম্যানের নেতৃত্বাধীন গবেষক দলটি এই কাজে ইন্টারফেরোমিটার ব্যবহার করেছেন। এতে L আকৃতির বিশেষ একধরনের আয়না লাগানো থাকে, যার দ্বারা ফোটনের ওয়েভ ফাংশনকে দু'টি ভিন্ন দিকে বিভক্ত করে। পরে আবার তারা মিলিত হয় । সেসময় দ্বি-ছিদ্রের সামনে রাখা ডিটেক্টরের দু'টির সাহায্যে ফোটনের গতিপ্রকৃতি পরিমাপ করা হয়।
কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানে পরিমাপ খুব সূক্ষ বিষয়। সাব অ্যাটমিক জগতে কণাদের গতিবিধি মাপতে গেলেই তার পরিস্থিতি বা স্টেট পাল্টে যায়। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতির কথা তো আমরা সকলেই জানি — কোনও সিস্টেমের অবস্থান নিখুঁতভাবে মাপতে গেলে তার ভরবেগের পরিমাপ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এই সব সমস্যা মাথায় রেখে হফম্যানরা ‘উইক মেজারমেন্ট’ নামক এক বিশেষ ধরনের কৌশল অবলম্বন করেন। এই পদ্ধতিতে কণাকে বিরক্ত না করে খুব ম্রিয়মান তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তারপর বারবার এই পরিমাপ করে একটা তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়। তারপর সেই তথ্য থেকে কণাটির গতিপথের একটি পরিসংখ্যানগত চিত্র তুলে ধরা হয়। এক্ষেত্রে ডিটেক্টর ও নির্দিষ্ট কোয়ান্টাম সিস্টেমের মধ্যে একটা ক্ষীণ মিথস্ক্রিয়া ঘটে। ফলে সিস্টেমের কোয়ান্টাম অবস্থার কোনও পরিবর্তন হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। এক কথায়, এই পদ্ধতিতে ফোটনের গতিপথের কোনও পরিবর্তন ছাড়াই এর গতিপ্রকৃতির হদিশ মেলে। সে না হয় মিলল, কিন্তু দুটি রেখা ছিদ্রের ভেতর দিয়েই যে ফোটনটি গেছে, কীভাবে নিশ্চিত হলেন তাঁরা?
আরও পড়ুন- নেহাত সাধনা নাকি ঈশ্বরত্বের হাতছানি, কেন সর্বঘাতী পরমাণু বোমা বানিয়েছিলেন ওপেনহাইমার?
সেজন্য বিজ্ঞানীরা সম্ভাব্য দু'টি পথেই এক বিশেষ ধরনের কাঁচের পাত ফিট করে রেখেছিলেন, যা ফোটনের ঘূর্ণনের দিক সামান্য বদলে দেয়। পদার্থবিদ্যার ভাষায়, পাত দু'টি ফোটনের পোলারাইজেশনের সামান্য পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম। ফলে একটি ঘূর্ণনের দিক হয় দক্ষিণমুখী, অন্যটি উত্তরমুখী। ফোটন যদি দ্বি-ছিদ্রের দু'টি পথেই যায়, তাহলে দুই বিপরীত ঘূর্ণন, একে অপরকে প্রশমিত করে দেবে। বারংবার পরীক্ষায় তাঁরা দেখেন, সত্যিই দুই বিপরীত মুখি ঘূর্ণন একে অপরকে প্রশমিত করে দিচ্ছে। ফলে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উৎস থেকে নির্গত ফোটন একই সঙ্গে দু'টি রেখা ছিদ্র দিয়ে গেছে।

এই পরীক্ষার ফলে, এখনই মাল্টিভার্স বা বহুবিশ্বের তত্ত্ব বাতিল হয়ে যাবে, এমনটা মনে করছেন না অনেক বিজ্ঞানীই। ক্যালিফোর্নিয়ার চ্যাপম্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অ্যান্ড্রু জর্ডান বলছেন, "এই ধরনের দুর্বল পরিমাপ থেকে একক ফোটনের গতিবিধি সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায় না।" আসলে বারংবার উইক মেজারমেন্ট থেকে পাওয়া তথ্যের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ অনেক তাত্ত্বিক পদার্থবিদ মানতে চান না। অপরদিকে, ইজরায়েলের তেল আভিভ বিশ্ববিদ্যালয়ের লেভ ভেইডম্যান বলেন, "এই ফলাফল মাল্টিভার্স তত্ত্বের বিরোধিতা করে, একথা পুরোপুরি সঠিক না। কারণ, আমরা একটি বাস্তবতার শাখা দেখছি, অন্য শাখায় ফোটন আরেকটি পথ বেছে নিতে পারে।" নতুন তত্ত্ব নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হবে না, বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে। যদিও হফম্যান আশাবাদী, তিনি বলছেন, "আগে সবার ধারণা ছিল যে এসব ব্যাখ্যার পরিমাপ সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা বলছি, এসব ব্যাখ্যাও পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা সম্ভব।" এই সব তর্ক বিতর্ক পেরিয়ে পাল্লা কোনদিকে ঝুঁকবে, তা সময় বলবে। তবে তাঁদের ব্যখ্যা বিজ্ঞানীমহলে পুরোপুরি গৃহীত হলে বহুবিশ্বের পাশাপাশি অনেক ধারণাই বদলে যেতে পারে বলে পদার্থবিজ্ঞানীরা মনে করছেন।




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp