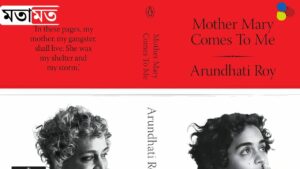বাংলা গানের ধারণক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছেন প্রতুল মুখোপাধ্যায়
Pratul Mukhopadhyay: প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের প্রধান বিশ্বাস ছিল বামপন্থায়। সেই রক্তিম বিশ্বাসেই তিনি দেশদুনিয়ার মুক্তির সন্ধান করতেন।
১
আমাদের চোখের সামনে, গত শতকের নয়ের দশক নাগাদ, বাংলা গানে একটা নবতরঙ্গ দেখা দিয়েছিল। নিঃসন্দেহে তার প্রধান কারিগর হিসেবে দেখা দেবেন কবীর সুমন। বিদেশ থেকে ফিরে কলকাতার গানের মঞ্চে তিনি রীতিমতো সাড়া জাগিয়েছেন তখন। তারপর আরও বেশ কিছু গায়ক, গীতিকার, সুরকার এই আন্দোলনের শরিক হিসেবে জনমানসে সাদরে গৃহীত হয়েছেন। সলতে পাকানো শুরু হয়েছিল আগেই। এবার এল জোয়ার। ফেলে আসা সেই বিচিত্র সুরসাধনার দশকগুলির কথা ভাবি। শ্রোতা হিসেবে আমাদের উন্মাদনাও কিছু কম ছিল না। কত রকমের গান, কত ধরনের কথা-সুর বা অ্যারেঞ্জমেন্টের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কত নতুন মুখ, কত নতুন প্রয়াস। তাদের গান শোনা, সে নিয়ে তর্ক-বিতর্ক, সংশয়, সমর্থন। তাদের কেউ কেউ টিঁকে গেলেন, জনতার দরবারে থেকে গেলেন, কেউ টুপ করে ঝরে গেলেন, কখন যেন, কোন অবেলায়। ‘আসমানদারি’-র এই কিস্তি সেই সূত্রে মন ভার করে তাকাবে সদ্যপ্রয়াত গায়ক/গীতিকার/ সুরকার প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের দিকে। দীর্ঘদিন তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। প্রথম যুগে দূর থেকে তাঁকে কুর্নিশ জানিয়েছি। ২০০৬-২০১১ – এই সময়কালে, বিশেষত সিঙ্গুর কৃষক আন্দোলনের অগ্নিভ পরিস্থিতিতে নানা মিটিং, মিছিল, জমায়েত এবং আলোচনায় নিজস্ব ধারার গান সহ হাজির থাকতেন প্রতুল দা। সদাহাস্যময়। প্রফুল্ল এবং নির্মল।
নিজস্ব ধারার গান। এটাই হলো প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের প্রকৃত পরিচয় এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী টিপছাপ। প্রতুলদা জন্মেছিলেন ২৫ জুন ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে আর প্রয়াত হলেন ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫। দীর্ঘ ৮২ বছরের জীবন। তাঁর সংগীত তথা সুরসাধনার অনবদ্য বহিঃপ্রকাশ তাঁর গানে। বাংলা এবং ভারতবর্ষে তো বটেই, বেবাক বিশ্বজুড়ে, তাঁর মতো এমন বহু দক্ষ উপস্থাপনার শিল্পী বিরলতম। গান পরিবেশন তো করেন অনেক ক্ষণজন্মা উঁচুদরের শিল্পী। যন্ত্রসংগীতে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গত করেন অনেক মানীগুণী উদযাপিত যন্ত্রশিল্পী কিন্তু প্রতুলদা ছিলেন নিজের একটি স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। এও এক আশ্চর্যের সমাহার। তিনি একইসঙ্গে ছিলেন গীতিকার, সুরকার, গায়ক এবং সর্বোপরি সহশিল্পী। যন্ত্রীদের অনুপস্থিতি টের পাওয়াই যেত না। প্রথম যুগে দু-একবার গিটার বা অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রীকে তাঁর সঙ্গে মঞ্চে দেখা গিয়েছিল কিন্তু অচিরেই বোঝা যায়, ওই ধরনের প্রচলিত গৎ-এ তিনি গান পরিবেশন করে না। ফলে, ভেস্তে যায় সেই পরিকল্পনা।
আরও পড়ুন- মফস্সলের রান্নাঘরের খুনসুটির দুলুনি ছিল প্রতুলদার উচ্চারণে
২
প্রতুল মুখোপাধ্যায় ছিলেন আধুনিক এক শিল্পী, যিনি বারংবার নিজেকে নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতেন। তাঁর গায়কির মধ্যে তিনি প্রকৃতপক্ষে পুরো গানটিকেই ধরতে চাইতেন। কথা এবং সুরে তিনি উপস্থাপন করতেন মূল গান, অন্যদিকে এক কলি থেকে অন্য কলি যাওয়ার পথ তাঁর কণ্ঠে নানা ভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠত। হামিং, তান এবং বোল, উঁচু-নিচু নানা পর্দায় বিস্ময়কর দক্ষতায় অনুপ্রবেশ করতেন তিনি। কখনও কখনও মনে হতো অর্কেস্ট্রেশনের মতো, স্থাপত্যের মতো, তিনি যেন ধাপে-ধাপে আকাশের দিকে ক্রমোচ্চ সোপানে গানকে নিয়ে চলেছেন। এই কণ্ঠকে যন্ত্রশিল্পীদের সুর হিসেবে ব্যবহার করার অভিনবত্ব পূর্ণত প্রতুলদার কৃতিত্ব। কখনও কখনও আমার মনে হয়েছে, সারা উপমহাদেশ তো বটেই, সারা বিশ্বে তাঁর এই অভিনব উপস্থাপন রীতির জুড়ি মেলা ভার। তাঁর কণ্ঠ ছিল মিহি, তাঁর কণ্ঠ ছিল পেলব আর সুরেলা। ফলে নানা খাঁজখোঁজ এবং সুরতন্ত্রীর উচ্চাবচতায় অনায়াসে পাড়ি জমাতে পারত। ধরা যাক, তাঁর ‘চ্যাপলিন’ গানটি। কী আশ্চর্য নৈপুণ্যে তিনি ‘লাইমলাইট’ সিনেমার ‘লাভ লাভ লাভ লাভ’ গানটির বাংলা তর্জমা করলেন ‘প্রেম প্রেম প্রেম প্রেম প্রেম’ আর তাকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে প্রচণ্ড অভিঘাতে আশা-স্বপ্ন-অঙ্গীকার এবং প্রতিরোধ হিসেবে ছুঁড়ে দিলেন আকাশের দিকে। ভালোবাসাকে এত তীব্রভাবে চ্যাপলিনের অনুষঙ্গে, হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে অন্য কোনও সমকালীন বাংলা গানকে দেখিনি। ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি এবং বাস্তবতায় মনে হয় এই গান অত্যন্ত ‘রাজনৈতিক’! চতুর্দিকে ধর্মীয় মৌলবাদ, দমচাপা শাসানি, রক্তচক্ষু, মাতব্বরি, কণ্ঠরোধ আর ঘৃণার দাপট! এই সময় তো প্রেম আর ভালোবাসার নিরবিচ্ছিন্ন অনুশীলনই প্রতিরোধ। হাসি, উল্লাস, দয়া, প্রেম, মানবিকতা যেন অস্ত্র, দৃপ্ত কদমে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে কামান অথবা ট্যাঙ্কের সামনে।
‘রাজনৈতিক’ শব্দটিকে ইদানীং আমরা খুবই সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করি। পার্টি তথা দলীয়তার কলুষতা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে লেগে আছে। এখানেই কিন্তু প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের মতো মানুষের মুক্তচিন্তা আমাদের পাথেয় হয়ে ওঠে। কোনও সন্দেহ নেই প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের একটা রাজনীতি-বিশ্বাস ছিল। বরিশালে জন্ম। ফলে দাঙ্গা, দেশভাগ, পঞ্চাশ-ষাটের অগ্নিগর্ভ কলকাতা, স্বদেশ-স্বজনের আর্তরূপ, দরিদ্র মানুষের হাহাকার, শরণার্থী শিবিরে অসীম দুর্দশাগ্রস্ত হাজার মানুষ তাঁর অভিজ্ঞতার অংশ ছিল। হয়তো সেই সূত্রেই প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের প্রধান বিশ্বাস ছিল বামপন্থায়। সেই রক্তিম বিশ্বাসেই তিনি দেশদুনিয়ার মুক্তির সন্ধান করতেন। তাঁর গানে এই বিশ্বাসের স্পষ্ট প্রত্যয় ছিল কিন্তু যান্ত্রিকতা ছিল না। ‘স্লোগান দিতে গিয়েই আমি চিনতে শিখি নতুন মানুষজন’— এই সূত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ গান। উন্মত্ত মোষকে রক্তনিশানে খেপিয়ে তুলে তাকে চ্যালেঞ্জ ছোঁড়ার চিত্রকল্পটি ইশারায় বামপন্থার দিকে নিয়ে যায়। বহুমাত্রিক, বিমূর্ত এই বক্তব্যই প্রকৃতপক্ষে প্রতুলদার স্বাক্ষর। বামপন্থা, দলীয়তা, ভোট সর্বস্বতা, এবং অনুশাসনমূলক বিবৃতির যে রমরমা আমরা বারংবার দরবারি মার্ক্সবাদীদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি, প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গান তার সঙ্গে আড়াআড়ি দূরত্বে ‘শিল্প’, ‘সংকেত’ প্রভৃতিকে আলিঙ্গন করে। চেনাশোনা একবগ্গা ঘোষণায় তার তৃপ্তি নেই। ফলে, বাংলা গানে তাঁর উচ্চারণ প্রথম থেকেই নব এবং অভিনব। ‘আলু বেচো, ছোলা বেচো’ দিয়ে যে-গান শুরু তার অকস্মাৎ মোচড় লক্ষ্য করা যায় শেষাংশে ‘হাতের কলম জনমুখী, তাকে বেচো না’। এখানেই স্মরণীয় হয়ে যান প্রতুল। তিনি এক গভীর ‘দায়বদ্ধতা’ বিষয়ে আমাদের অর্থাৎ শ্রোতাকে সচেতন করেন।
প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের জন্য সবথেকে উপযুক্ত শব্দ হলো গানের মাধ্যমে এক ধরনের দায়বদ্ধতার প্রচার। কোনও সন্দেহ নেই, নকশালবাড়ি আন্দোলন, সেই তরুণ-যুবকদের দুর্মর স্বপ্ন, পাল্টে দেওয়ার প্রত্যয় – তাঁকে স্পর্শ এবং আবিষ্ট করেছিল। ফলে, কখনও দলিতের আর্তনাদে, কখনও ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, কখনও কানোরিয়া জুট মিলে শ্রমিক আন্দোলনে, কখনও সিঙ্গুরের কৃষক আন্দোলনে, কখনও ধর্মীয় সংখ্যালঘুর নিপীড়নের বিরুদ্ধে – ঝলসে উঠেছে তাঁর কণ্ঠ, তাঁর গান। নানা মিছিল শেষের জমায়েতে, ছোটছোট আলোচনা সভায়, প্রতিবাদ কনভেনশনে তাঁকে নিয়মিত দেখা গেছে। উজ্জ্বল চোখ, মুখে মৃদু হাসি, গান গাইতে গাইতে উদ্যত উদ্ধত হাতের নানা মুদ্রা, একমাথা চুলের দোলা আর ছোটখাটো শরীরের দীপ্ত ভঙ্গিমা – মাইক বা মাইক ছাড়া, মঞ্চ বা মাটিতে তিনি অপ্রতিরোধ্য। ‘তোমাকে চাই’ ক্যাসেট, কবীর সুমন, পূর্ববর্তী মহীনের ঘোড়াগুলি প্রভৃতি মিলিয়ে বাংলা গানের যে নবতরঙ্গ শুরু হয়েছিল নয়ের দশকে, প্রতুলদা তাঁর সমান্তরাল সঙ্গী।
আরও পড়ুন- ভাষাবিভ্রাট দেখেও চোখ বুজে থাকে বাঙালিরাই
৩
মনে পড়ে, বইমেলায়, সম্ভবত '৯৮ বা ২০০০ সালে তিনি খোলা মাঠে গাইছিলেন, ‘হেই ছোকরা চাঁদ/ ও জোয়ান চাঁদ’ গানটি। আফ্রিকার লোকসংগীত থেকে বঙ্গীকরণ। তাঁর মাথার ওপর জ্বলছিল অতিকায় এক চাঁদ। বোধহয় পূর্ণিমা ছিল সেদিন। তাঁকে ঘিরে অল্পবয়সিদের ভিড়। সাদামাটা, সরল-অনাড়ম্বর জীবনযাপন ছিল তাঁর পরিচয়। সারা জীবন ব্যাঙ্কে কাজ করেছেন। আন্তর্জাতিক সংগীতের নানা সম্পদ সযত্নে লগ্নি করেছেন বাংলা গানে। নিজে গান লিখেছেন কিন্তু সবথেকে বড় কথা বাংলা গানের ধারণক্ষমতা বাড়িয়ে চলার চেষ্টা সর্বদা করে গেছেন। সেই পদ্ধতির কথা একটু বলি। বাংলার মহান কবিদের কবিতায় তিনি সুর দিয়েছেন, বহু অনূদিত কবিতায় সুর দিয়েছেন, কখনও অন্যান্য দেশের কবিতায় সুর বসিয়ে তর্জমা করে পরিবেশন করেছেন। আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে, কবি অরুণ মিত্রের বিখ্যাত কবিতা – ‘আমি এত বয়সে গাছকে বলছি’। সেই অসামান্য কবিতা থেকে আশ্চর্য গান তৈরি করেছিলেন প্রতুল। শেষে ‘এক মাঠ ধান’ উচ্চারণে একটা হীরকদ্যুতি টান দিতেন, ফলে দিগন্তবিস্তারী মাঠ, রক্তমাখা পা আর বিকশিত বীজের ছবিটা স্পষ্ট দেখা যেত। মনে পড়ে, লং মার্চ নিয়ে প্রতুলদার গান। মনে পড়ে বিপ্লবী কবি চেরাবান্দারাজুর কবিতা থেকে শঙ্খ ঘোষের অনুবাদে গান – ‘কী আমাদের জাত আর ধর্মই বা কী’। জাতপাত আর ধর্মকারায় বদ্ধ ভারতবর্ষে এমন একটি গান, আমার তো মনে হয় বিদ্যালয়ে পাঠ্য হওয়ার দাবি রাখে। প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের সম্ভবত সবথেকে উদযাপিত গান ‘আমি বাংলায় গান গাই’। শাশ্বত বাংলা, শাশ্বত বাংলাভাষীর আবেগ এবং মমতা যেন এই গানে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ‘বাংলা আমার তৃষ্ণার জল/ তৃপ্ত শেষ চুমুক’ এবং ‘আমি যা কিছু মহান গ্রহণ করেছি বিনম্র শ্রদ্ধায়/ মেশে তেরো নদী সাত সাগরের জল গঙ্গায় পদ্মায়’ গানটিকে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে যায়। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ থেকে মুক্ত বহুস্বরে তার উড়ান। এবারের একুশে ফেব্রুয়ারিতে কত কণ্ঠে কতবার এই গান পরিবেশিত হবে। প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে তখন তীব্রভাবে অনুভূত হবে। তবে শিল্পীর তথা স্রষ্টার অস্তিত্ব চিরায়ত সৃষ্টিতে, দেহে নয়, শিল্পরূপে।
সাতের দশকের গোড়ায় জার্মান অর্থনীতিবিদ ই. এফ. শুমাখার একটি জগৎ বিখ্যাত বই লিখেছিলেন যার নাম ‘স্মল ইজ বিউটিফুল’। বিপুল উৎপাদন তথা বপুর মহাকায় শিল্পায়ন এবং দানবিক শিল্পস্থাপনের বিরোধিতা করেছিল এই বই। সেটি ভিন্ন আলোচনার বিষয়। নামটি থেকে, প্রতুল মুখোপাধ্যায় যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠেন। কোনওদিন তাঁর অনুষ্ঠান বড় প্রেক্ষাগৃহে টিকিট বিক্রি করে হয়েছে বলে জানা নেই। খুবই অনাড়ম্বরে কয়েকটি ক্যাসেট এবং সিডি বাজারে এসেছিল, ছোট কোম্পানি বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে। তিনি প্রবল প্রতিপত্তি, সমর্থন, উজ্জ্বল আলো, যশখ্যাতি থেকে দূরে, সাধারণ মানুষের জোট-জটলার কাছাকাছি থাকতে চেয়েছেন। তাঁর জীবনযাপন, সুর সাধনা, রাজনৈতিক অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি সবই মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। আজীবন। স্বতন্ত্র এক সাধারণ জীবন তিনি সর্বদা বাঁচতে চাইতেন। খ্যাতির বিড়ম্বনা, ক্ষমতার আস্ফালন এবং বিজ্ঞাপনের জৌলুশ থেকে খানিকটা দূরত্বে থাকতে চেয়েছিলেন। সামান্য কয়েকজন অনুরাগী, কিছু আড্ডা, কিছু চেতনা, কিছু প্রতীক, কিছু উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন! বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনবদ্য কবিতা থেকে তাঁর গান – ‘ন্যাংটো ছেলে আকাশে হাত বাড়ায়,/ কেননা তার খিদেয় পুড়ছে গা/ ফুটপাতে আজ নেমেছে জ্যোছোনা’ – আজ খুব মনে পড়ছে। ছোটতেই তিনি সুন্দরকে খুঁজেছেন, ছোটতেই তৃপ্তি এবং ঠিকানা। স্ফীত পেশীর অর্থ-যশ-সফলতাকে প্রত্যাখ্যান করার সাহস দেখিয়েছিলেন তিনি।
সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় দেখেছি তিনি কী নিরন্তর ছুটেছেন অন্যায়ের মোকাবিলায়। দেখেছি, কত বাধাবিঘ্নে অটল প্রত্যয়ে গান জুড়তে। ‘এই তো যুক্তি জনগণের/ এ পথে মুক্তি জনগণের/ অমিত শক্তি জনগণের/ তুমি তো তাদেরই একজন/ তুমি একাকী কখনও নও।’ তাঁর গানকে আমার মনে হয়, বলা চলে, মিশ্রমাধ্যমের গান। চিত্রকলার ব্যাকরণ থেকে শব্দটি আমি ধার নিলাম। নানা সুরের চলনে, কথায়, তানে সংগীতে মিশে তাঁর গানের অবয়ব। উপরন্তু, প্রতুলদার গান সবসময় এমন এক আধুনিকতার সঙ্গে সংলাপ জুড়েছে যার পা স্বদেশ-স্বভূমি আর স্বভাষায় প্রোথিত, যার সুরের চলন প্রধানত পশ্চিমি, যদিও মাঝেমধ্যেই পূর্বী কিছু আবেশ সেখানে খেলা করে, যে গান সংলাপ চালায় দুনিয়ার সংবেদনশীল সচেতন সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে, কোনও মতাদর্শের অন্ধতা নয়, যার কেন্দ্রে আছে নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের দীর্ঘশ্বাস আর পাল্টা আক্রমণের খোয়াব। ব্যবস্থা এবং কাঠামো দুমড়ে ভেঙে নতুন পৃথিবী গড়ার আহ্বান। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের বাংলার জনপদ মাটি জল বিষয়ক কবিতা থেকে প্রতুলদার গানের একটি পঙ্ক্তি – ‘তুই কি ভাবিস তার ঘুমে সেই স্বপ্ন নেই?/ আছে, সাপের মাথায় পা দিয়ে সে নাচে’। প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের কোনও পূর্বসূরি বা উত্তরসূরি নেই। তিনি একক অনন্য এবং চিরন্তন। প্রণাম প্রতুলদা। অভিবাদন!



 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp