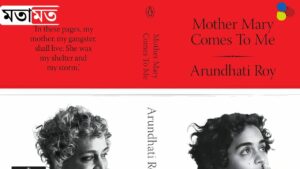গানে হেমন্ত ঋতুকে এড়িয়ে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ?
Rabindranath Tagore: শীত এলে যে বসন্ত দূরে থাকতে পারে না, এটা লিখেছিলেন এক বিদেশি কবি। তবে কি হেমন্ত মানে প্রৌঢ়ত্বের সুনির্দিষ্ট বার্তা? যে প্রৌঢ়ত্বের অপেক্ষা শুধু আসন্ন বার্ধক্যের স্রোতে মিশে গিয়ে পরিণতির মোহনায় পৌঁছনো?
গীতবিতানের গানগুলিকে কবি স্বয়ং বিভাজিত করেছিলেন কয়েকটি উপপর্বে, তার অন্যতম হলো প্রকৃতি। মূলত ‘প্রকৃতি’ পর্যায়ের গানে তিনি ধরতে চেয়েছেন আমাদের প্রচলিত ছ'টা ঋতুকে। এটা করতে গিয়ে একেকটা ঋতুর জন্য এক বা একাধিক রূপক। গ্রীষ্ম যদি তাঁর চোখে ধরা দেয় মৌনী তাপস হিসেবে তবে বর্ষা তাঁর কাছে পাগলা হাওয়ায় মুক্তির ডাক পাঠানো এক বাউল। আবার কখনও সে মেঘের ঘোমটা পরা অবগুণ্ঠিতা এক রহস্যময়ী, শ্রাবণ গগনের অন্ধকারে গোপন চরণে যে এসে দাঁড়ায় আমাদের দুয়ারে। শরতের অমল আকাশ-বাতাস একদিকে অরুণ আলোর অঞ্জলি দিয়ে কমল মুকুল দলকে উন্মোচিত করে মোহনরূপে, অন্যদিকে যে ছায়াকে ধরবেন বলে কবির প্রতিজ্ঞা, শরতের সুর সেই বাঁধনকে মেনে নেওয়ায় তাঁর অনাবিল স্ফূর্তি। বসন্তের প্রতি তাঁর প্রবল পক্ষপাতের পাশে পাশে আমাদের মনে পড়ে শীতের হাওয়ায় আমলকী বনের নাচনে ‘ঝরিয়ে দেওয়ার মাতন’ তাঁকে সরিয়ে আনে একরকম বেদনার কিনারে। কিন্তু ব্যপ্ত আর বিচিত্র এই গানের ভুবনে সব থেকে অবজ্ঞাত হিসেবে পাই হেমন্তকে — কবির নিজের নির্বাচনেই মাত্র চারটে গান সংকলিত হয়েছে গীতবিতানে।
ভেবে অবাক লাগে, এই চারটের মধ্যে দুটো গানে (‘হিমের রাতে এই গগনের দীপগুলিরে’ আর ‘হেমন্তে কোন বসন্তের বাণী’) একটায় ‘আপন আলোয়’ তামসীকে জয় করার সংকল্প আর অন্যটায় হেমন্তের ধরায় বসন্তকে খুঁজে ফেরা। অর্থাৎ হেমন্ত এখানে শুধু উপলক্ষ্য মাত্র। হেমন্তকে কি তবে এড়িয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ?
এই প্রশ্নে যাওয়ার আগে আরেকটা কথা সেরে নেওয়া যাক। ঋতুচক্রের সঙ্গে আমাদের জীবনধারার নানা পর্যায়ের সামঞ্জস্য তৈরির চেষ্টা খুব নতুন নয়। রবীন্দ্রনাথের গানেও তার প্রচুর ইশারা ইঙ্গিত রয়েছে। বর্ষার সঙ্গে নতুন জীবনের অঙ্কুরোদ্গমের বার্তাকে যেমন মিলিয়ে নেওয়া যায়, ঠিক তেমনই বসন্ত মানে তো সাধারণভাবে নব যৌবনের জয়গান। বর্ষা আর বসন্তের এমন এক যৌথ উচ্চারণ পেয়ে যাই একটা গানে, 'আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ/ খেলে যায় রৌদ্রছায়া/ বর্ষা আসে বসন্ত'— যিনি পথ চেয়ে আছেন আসলে তার উদ্দিষ্ট নতুন জীবন আর তার বিকশিত যৌবন, এটা তো ভাবাই যায়। অন্যদিকে শীত, সে তো স্পষ্টত জরার সূচক, যার অবসানে আবার ফিরে আসবে বসন্তের স্পন্দন।
আরও পড়ুন- শান্তিনিকেতনের বর্ষা: বিপর্যয়কে পূর্ণতায় শমিত করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ
শীত এলে যে বসন্ত দূরে থাকতে পারে না, এটা লিখেছিলেন এক বিদেশি কবি। তবে কি হেমন্ত মানে প্রৌঢ়ত্বের সুনির্দিষ্ট বার্তা? যে প্রৌঢ়ত্বের অপেক্ষা শুধু আসন্ন বার্ধক্যের স্রোতে মিশে গিয়ে পরিণতির মোহনায় পৌঁছনো? মাঝে মাঝে মনে হয়, আমাদের জীবনের সবথেকে ধূসর দুটো সময়কাল বোধহয় কৈশোর আর প্রৌঢ়ত্ব, যাদের সীমানাগুলো খুব অমীমাংসিত। বিশেষত, প্রৌঢ়ত্বের যেন রয়েছে এক অনন্য চরিত্র। হেমন্ত-বিষয়ক চারটে গানের মধ্যে ‘হায় হেমন্তলক্ষ্মী’-তে তার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সন্ধ্যাপ্রদীপ তোমার হাতে মলিন হেরি কুয়াশাতে/ কণ্ঠে তোমার বাণী যেন করুণ বাষ্পে মাখা'। তবে এই বিষয়ে আরও প্রত্যক্ষ ছবি খুঁজে পাব হেমন্তপর্বের অন্য গান ‘সেদিন আমায় বলেছিলে’-র সঞ্চারী ও আভোগে:
আজি এল হেমন্তের
দিনকুহেলীবিলীন,
ভূষণবিহীনবেলা আর নাই বাকি সময় হয়েছে নাকি
দিনশেষের দ্বারে বসে পথপানে চাই।
আমাদের চারপাশের গড়পরতা প্রৌঢ় জীবনের ছবিটাও যেন এমন আভরণহীন — বেলাশেষের পথের দিকে তাকিয়ে থাকায় ক্লিষ্ট। কিন্তু ঋতুগত বর্ণনা বিন্যাসকে চেনা জীবনের ছবিতে বিম্বিত করে দেখবার একেবারে বিপরীতে রয়েছে আরেকটা তুলনায় কম চেনা গান, যেখানে জীবনের ছবিকেই মিলিয়ে ধরা হয়েছে হেমন্তের সঙ্গে। পূজা পর্যায়ের এ-গানে রয়েছে সেই বহুমাত্রিক প্রতিসরণ।
জীবন যখন ছিল
ফুলের মতোপাপড়ি তাহার
ছিল শত শত ।।বসন্তে সে হত যখন দাতা
ঝরিয়ে দিত দু-চারটি তার পাতা
তবুও যে তার বাকি রইত কত ।।
আজ বুঝি তার
ফল ধরেছে তাইহাতে তাহার
অধিক কিছু নাইহেমন্তে তার সময় হল এবে
পূর্ণ করে আপনাকে সে দেবে
রসের ভারে তাই সে অবনত।।
চেহারায় গান হলেও আমরা একেবারে কবিতার আদলেও পড়ে নিতে পারি এ-গানের টেক্সটকে। আর তেমন করতে গেলে গোড়াতেই যা মনে হয় তা হলো, এই গান যেন প্রৌঢ়ত্বে উপনীত কোনও ব্যক্তিমানুষের দিনানুদিনের লিপি যার মধ্যে ছড়িয়ে আছে তার এযাবৎ জীবনেরই কথা। কেমন সেই কথা?
গানের প্রথম দু'লাইনে (স্থায়ী) বলা হচ্ছে এক অতীতের কথা: জীবন যখন ছিল ফুলের মতো — তার মানে এটা এখনকার জীবন নয়। সেই জীবনের কথা বলা হবে আরেকটু পরে। তার আগে স্থায়ী ও অন্তরা জুড়ে অতীত জীবনের কথাই উঠে এল নানাভাবে। ফুল শব্দে আমরা সাধারণত একটা সৌন্দর্যের ধারণাই পাই, আর যে ফুলের বর্ণনায় ‘শত শত’ পাপড়ির উল্লেখ সে নিশ্চয়ই রূপে আর আভিজাত্যে সম্পন্ন হতে বাধ্য। সেইরকম ফুলের মতো যে জীবন সেই জীবনও বেশ সম্পন্ন রঙিন ও সামর্থ্যবান— যার সামনে দীর্ঘ পথচলার রসদ। এমন একটা জীবন তো তার বসন্ত সমাগমে নিজেকে বিস্তৃতভাবে মেলে ধরতেই পারে। পুষ্পে পর্ণে যে জীবনের এমন অফুরন্ত ভাঁড়ার, সে তো অনায়াসেই তার দু'একটা পাতা ঝরিয়ে দাতা হওয়ার যোগ্যতায় উত্তীর্ণ হতে পারে। এই পাতা ঝরিয়ে দেওয়ার ব্যঞ্জনা যদি ধরা যায় একটু ব্যক্তিগত জীবনের বৃত্ত থেকে কিছুটা বৃহত্তর জীবন ও সমাজের দিকে নিজেকে ছড়িয়ে ধরার চেষ্টা, তাহলে মনে হতে থাকে, এই কথাগুলোর মধ্যে আমাদের খুব চেনা জীবনেরই এক ছবি ভেসে আছে। ধরা যাক, কোনও যুবক-যুবতীর কথা। সেই বয়সটা তো সুন্দর বটেই যা ক্রমশ ভরে উঠবে যৌবনের লাবণ্যে, ছড়িয়ে যেতে থাকবে অস্তিত্বের ডালপালায়। আর ওই ‘দাতা’ শব্দটাকেও যদি একটু বিছিয়ে ভাবি, তবে তারও মধ্যে ইশারা দেয় ভিন্ন অর্থ।
তরুণ উত্তীয় যখন সুন্দরী শ্যামার প্রেমে নিজেকে আহুতি দেয় সে যেমন এক দান, আবার নন্দিনীর ডাকে বিশু যখন কেবলই চেনার কূল থেকে অচেনার ধারে ভেসে পড়তে চায়, তাকেও কি দান ভাবা ভুল হবে? অথবা, পূর্ণ প্রাণের একদল দীপ্ত যুবা যখন দিন বদলের স্বপ্নে মশগুল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক কঠিন অনিশ্চয়তার স্রোতে — সেও কি একরকম দান নয় ? কিংবা আরও আটপৌরে জীবনে কোনও বড় আদর্শের অনুবর্তী না হয়েও কেউ কেউ হয়তো পথশিশুদের নিয়ে একটা স্কুল চালান, কেউ বা শারীরিকভাবে আর্ত ও অক্ষম প্রান্তীয় মানুষকে বল-ভরসা জোগান, কেউ মনোরোগীদের এক পুনর্বাসন কেন্দ্রে গিয়ে সপ্তাহে একদিন তাঁদের গান শুনিয়ে আসেন, কিংবা আরও আরও কত কাজ — এগুলো সবটাই, সবটুকুই হয়ে উঠতে পারে এক একটি দান, কিছু দেওয়া। নিজের বেঁচে থাকা থেকে দু-একটি মুহূর্ত ঝরিয়ে কারও আশ্রয় হয়ে ওঠা। ‘বসন্তে সে হত যখন দাতা’ লাইনে জীবনের এইসব অভিজ্ঞতাগুলোই যেন পুরে দেওয়া হলো গানে।
কিন্তু অন্তরার তিনটে লাইনের শেষেরটা আবার অন্যরকম: তবুও যে তার বাকি রইত কত। অর্থাৎ বসন্তের অফুরান বিস্তার থেকে সামান্য কিছু দিয়েও আরও অনেকটা থেকে গেল জীবনে! কী থেকে গেল? নিশ্চয়ই জীবনের উদ্যম, শক্তি, সামর্থ্য, ভালোবাসা আর শ্রম। ফুলের মতো জীবন, ডালপালা মেলা তার বিস্তার — তার থেকে সে কিছু দান করেছে, তবু তার অনেকটাই কি অবশিষ্ট থেকে গেল? এই থেকে যাওয়ার (ভিন্ন অর্থে নিঃশেষ করে না-দেওয়া) অন্য একটা মানে কি ভেবে নেওয়া যায় ? আমরা যাকে দান বলে ভেবে নিচ্ছিলাম এতদিন, তাহলে কি সেটা সম্পূর্ণ নয় কোথাও? তাহলে যে প্রেমিক সবটুকু উজাড় করে দিতে চাইল তার ভালোবাসার জনকে সেটাই তার সব নয়? খণ্ডাংশ? যে যুবক দিনবদলের ঘূর্ণিপাকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তারও কি ছিল কোনও অবশিষ্ট সংশয়ের পিছুটান? সামাজিক সেবাব্রতে যাদের মনে হয়েছিল আপাত নিবেদিত, তারাও কি তাদের সবটুকু দিতে পারলেন না সেই কাজে? ‘তবুও যে তার বাকি রইত কত’ এই প্রশ্নের কিনারে আছড়ে ফেলে আমাদের। কিন্তু এই থেকে-যাওয়াটা নিয়ে শেষ অবধি কী করবে একজন? এই জিজ্ঞাসার নিরসন আছে গানের সঞ্চারী আর আভোগে। আর, এই সঞ্চারীতেই গানের সময় ফিরে আসে অতীত থেকে বর্তমানে।
এখানে গানের সুরের চলাচল নিয়েও দু-একটা কথা বলা দরকার। বসন্তের অতীতচারিতা দিয়ে এই গান আরম্ভ হয়েছিল একেবারে চড়ায় নিখাদের সুর বুকে ধরে, স্থায়ী পেরিয়ে অন্তরায় এসে সেই সুর থেমে গেল মধ্যমে। সঞ্চারীতে এসে গান আরম্ভই হচ্ছে নীচের দিকে পঞ্চমে, গাইতে গেলে যেখানে গলা নিয়ে আসা খুব কঠিন আর এইভাবেই যেন বোঝা যাচ্ছে গান এবার মোড় ঘুরছে ভিন্ন কোনও মাত্রায়। সুরের দিক দিয়ে তা এক রকম শমিত বিষাদেরই ইঙ্গিতবহ। সঞ্চারীর প্রথম লাইনে ‘আজ বুঝি তার’ পর্যন্ত সুরের গড়ন বেশিটাই খাদের দিকে, পরে তা আবার উঠে যাবে গান্ধারে আর আভোগের ‘পূর্ণ করে আপনাকে সে দেবে’ অংশে ‘আপনাকে’ পঞ্চম ছুঁয়ে নেমে আসবে কোমল মধ্যমের সুর, যে সুর আসলে বিনতির। রবীন্দ্রনাথের গানে কথার সঙ্গে সুরের যে অপার্থিব সামঞ্জস্যের কথা যে আমরা শুনে এসেছি বারেবারে সেটা ধরতে গেলে গানের টেক্সটের পাশেপাশে সুরের এই উপকরণগুলোও খেয়াল করা দরকার। এবার আমরা ফিরে যাই সঞ্চারী আর আভোগের কথায়। এতক্ষণ যা বলা হচ্ছিল তার সবটাই অতীতের কথা — ছিল, দিত, রইত; আর এবার বলা হলো ‘আজ বুঝি তার ফল ধরেছে তাই/ হাতে তাহার অধিক কিছু নাই’। এখানে দুটো আশ্চর্য নিরীক্ষণ রয়েছে। এর আগে ফুলের মতো জীবনটাকে আমরা দেখতে চেয়েছি রূপের দিক থেকে — ফুলের মতো শিশু বা ফুলের মতো কিশোরী বললে আমরা ইঙ্গিত করি তার সৌন্দর্যের দিকে। কিন্তু ফুল মানে তো আরেকদিক দিয়ে ফল হয়ে ওঠার সম্ভাব্যতা! সেই ফুলের মতো জীবনে এবার ফল ধরেছে। এইখানে এসে ফুল আর ফলের জৈব প্রবাহের মধ্যে গানকে যে ঢুকে পড়তে দেখা গেল তাই নয়, খেয়াল করতে হবে পরের লাইনটাও: হাতে তাহার অধিক কিছু নাই। এই ‘না-থাকার’ সঙ্গত কারণও বুঝিয়ে দেওয়া হলো ‘তাই’ শব্দে — ফুল থেকে ফলে পৌঁছতে পারার জন্যই এই না-থাকার শূন্যতা। অথচ ফুলের মতো জীবন যখন বসন্তে দু-চারটি পাতা ঝরিয়ে দিত তার পরেও ‘বাকি রইত কত…’। কিন্তু ফল ধরার পর শুধুই শূন্যতা। শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ, পথে পথে।
আরও পড়ুন- শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গই ছিলেন শিক্ষাচিন্তক রবীন্দ্রনাথ
গোড়ায় যে কথা বলার চেষ্টা হয়েছিল, অর্থাৎ প্রৌঢ়ত্বের কথা, সঞ্চারীর এই উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এ গান ছুঁয়ে ফেলে সেই প্রৌঢ় জীবনের আদল। যৌবনের অফুরান জীবন প্রৌঢ়ত্বের উপকূলে যেন নিজেকে ফুরিয়ে ফেলেছে প্রায় — হাতে তাহার অধিক কিছু নাই। একজন প্রৌঢ়ের জীবনে কি ঠিক এইটাই বিম্বিত হতে দেখি না আমরা? যৌবন বিগত, পরিবার পরিজনের দায়বদ্ধতা মেনে তাঁর তখন মেপে চলা জীবনযাপন। হয়তো সন্ততিরা ততদিনে বেড়ে উঠেছে অনেকটাই, তাদের জীবনের সামনে অথৈ দিগন্তের হাতছানি কিন্তু সেই মানুষটির জীবন এক ক্রমসংকুচিত প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ। হয়তো পুত্র কন্যার কেরিয়ার নিয়ে তাঁর উদ্বেগ, নিজের রোগবালাই নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তা, হয়তো নিজের মাথা গোঁজার একটা আস্তানা করেছিলেন, তার দেনা মিটিয়ে নিজেকে মুক্ত করার বাসনা। ফুলের মতো জীবনের বসন্তে ঝরিয়ে দেওয়া পাতা থেকে এখন হাতে কিছু অধিক না থাকার সঞ্চারপথ তিনি পেরিয়ে এসেছেন আর ওই স্বল্প অবশেষ নিয়েই তাঁকে পেরোতে হবে জীবনের বাকি পথ। এর পরের জীবন চলে যাবে জরা আর বার্ধক্যের শীতার্ত মোহানায়। তাহলে কি এখন হেমন্ত নয়?
হ্যাঁ তাই। আভোগের প্রথম লাইনেই তার সুতীব্র আভাস। ‘হেমন্তে তার সময় হল এবে/ আপনাকে সে পূর্ণ করে দেবে’। তার মানে আজকের যে সময়ের কথা বলা হলো তা আসলে হেমন্তের কাল — ‘আজি এল হেমন্তের দিন/ কুহেলীবিহীন, ভূষণবিহীন’। আর এখনই তার পূর্ণ করে নিজেকে দেওয়ার সময়। পূর্ণ করে মানে? একেবারে উজাড় করা নিঃস্বতায়। হাতে থাকা ‘অধিক’-টুকুও এবার তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে দায়মুক্তির পথে-প্রান্তরে। বসন্তের দাতা থেকে হেমন্তে এসে উজাড় করে দেওয়ার ভিতর দিয়ে শেষ হলো এক বৃত্ত। এই বিশেষ মুহূর্তে এসে কি আমাদের মনে পড়ে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘যাও পাখি’ উপন্যাসের প্রৌঢ় ব্রজগোপাল চরিত্রের কথা? শহরের স্ত্রী-পুত্র পরিবার ছেড়ে তিনি থাকতেন এক দূর গ্রামে, আপাতভাবে তাঁকে দায়িত্বজ্ঞানহীন বলেই মনে করা হতো। তাঁর ছোট ছেলে সোমেন একদিন গিয়ে পড়ল সেই খামারবাড়িতে, ব্রজগোপাল তখন তাঁর ঘরে অনুপস্থিত। সন্ধে হয়ে আসছে, ঘরে জ্বলছে একটা মৃদু হ্যারিকেন। অস্থির সোমেন টেবিলে খুঁজে পেল একটা ডায়েরি, তারই একটা পাতায় সেই প্রৌঢ় লিখে রেখেছেন, "ভগবান, উহারা যেন সুখে থাকে।" সোমেন চমকে ওঠে। সংসারছুট এক প্রৌঢ়ের এও তো একরকম পূর্ণ করে দেওয়ারই আর্তি! এই বিশেষ আখ্যানের প্রসঙ্গ এসে গেল এই কারণে যে, গানের শেষ লাইনে বলা হয়: রসের ভারে তাই সে অবনত। এই অবনমনের মধ্যে কোথাও ক্লান্তি বা আগতপ্রায় শীতের প্রতীক্ষার ছবি থাকলেও এই নুয়ে পড়া আসলে ‘রসের ভারে’ নুয়ে পড়া — রসের ভার বলতে ফলে ফলে ভরে ওঠা এক গাছের পরিণতি ভারেরই ছবি যেন মনে আসে আমাদের। একদিক দিয়ে সেটাও তো এক পূর্ণতারই পটচিত্র — ফলে ভরন্ত বৃক্ষের দিকে তাকিয়ে এরকমই এক প্রশান্তির বোধ জেগে ওঠে না আমাদের ভিতর? তাই সংসারছুট ব্রজগোপাল যখন একান্তে লিখে রাখেন উত্তরপুরুষের শুভাকাঙ্খা তখন এই মানুষটিকে মনে হয় বৃক্ষপ্রতিম, ফলবান।
প্রকৃতির নিরিখে যখন হেমন্তকে দেখতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ সেখানেও অবশ্য এই নিঃস্বতা ও পূর্ণতার এক পারস্পরিক সাম্যের কথা পেয়ে যাই তাঁর ‘হায় হেমন্তলক্ষ্মী’ গানে, যেখানে বলা হয়, ধরার আঁচল ভরে দিলে প্রচুর সোনার ধানে/ দিগঙ্গনার অঙ্গন আজ পূর্ণ তোমার দানে। এইভাবে মিলিয়ে দেখলে আরও মনে হতে থাকে তিনি প্রৌঢ়ত্বের জীবনের সঙ্গে একাকার করে নিতে চাইছেন হেমন্তকে। যে প্রৌঢ়ত্ব আসলে সব দিয়ে নিঃস্ব হতে চায় আর সেই উজাড় করে দেওয়ায় সে পূর্ণতার অবনতিতে স্তব্ধ হয়ে থাকে — একটু আড়ালে, একটু স্মৃতিময়তায়,একটু বা গোপন বেদনায় আর অন্তঃশীল জরার প্রতীক্ষায়। এই কথাটাও রবীন্দ্রনাথ জানান অন্য একটি গানে — "আপন দানের আড়ালেতে রইলে কেন আসন পেতে/ আপনাকে এই কেমন তোমার গোপন রাখা।" নিজের দানের আড়ালে নিজেকে গোপন রাখা কি প্রৌঢ়ত্বের অনিবার্য পরিণতি নয় ?
তবে সব থেকে আশ্চর্য হলো, পূজা পর্যায়ে সংকলিত এই গান রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ডে বসে লিখেছিলেন তাঁর বাহান্ন বছর বয়সে (অগাস্ট ১৯১৩)। সে তো তাঁর প্রৌঢ়ত্বেরই ঋতু। আসলে তখন তাঁর হেমন্তদিন।




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp