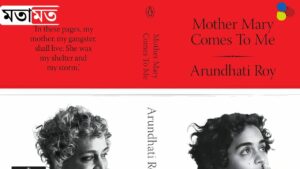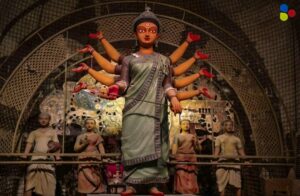সমাজের চোখে 'অস্বাভাবিক', যে অভিমান আজীবন বয়ে বেড়ালেন ঋতুপর্ণ
ঋতুপর্ণ ঘোষের নির্মিত চলচ্চিত্র, তাঁর লেখা এবং সাক্ষাৎকার- একমাত্র এর মধ্যেই ধরা আছে তাঁর জীবন ও জীবনের সঙ্গে শিল্পের সংমিশ্রণ-মুহূর্ত।
মৃত্যুর কয়েক বছর আগে, নিজের জন্মদিনে ‘উদ্বোধন’ নামের একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন:
বহু জনতার মাঝে অপূর্ব একা
১৯৩৮ সালে যখন এই কথা লিখছেন রবীন্দ্রনাথ, ততদিনে সারা পৃথিবীতে তিনি বিপুল শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত। প্রায় পঁচিশ বছর আগে পেয়ে গেছেন নোবেল সম্মান। গোটা দেশ যাঁর অনুরাগী, যাঁর চারপাশে সারাক্ষণ রয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, অমিয় চক্রবর্তী, শৈলজারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, মৈত্রেয়ী দেবী-র মতো মানুষরা, সেই রবীন্দ্রনাথ নিজেকে একা বলছেন কেন?
আসলে যে-কোনও মানুষকে আমরা কেবল তাঁর বহিরঙ্গ-জীবন দিয়েই বিচার করে থাকি। অথচ সেই ব্যক্তির অন্তর্জীবনের মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রবেশ করতে পারি না। কিন্তু যিনি প্রকৃত শিল্পী, তিনি নিজের জীবনের একান্ত-অভিজ্ঞতাকেও করে তোলেন শিল্পের অভিজ্ঞতা।
‘বহু জনতার’- এই শব্দবন্ধটির মধ্যে যে বিপুল কোলাহল রয়েছে, তার উল্টোদিকে কেবল ‘একা’ শব্দটিকে রাখলে কি সেই একাধিক মানুষের উপস্থিতির পাশে, কিংবা বিপরীতে, সেই উপস্থিতির সমপরিমাণ একাকিত্ব-ভার, লাইনটি বহন করতে পারত? দাঁড়িপাল্লায় কিছু কম পড়ত না?
আরও পড়ুন: আরও কত ছবি করতে পারতাম একসঙ্গে, ঋতুদার মতো গাইডের, বন্ধুর অভাববোধ করি
মনে হয়, ‘অপূর্ব’ শব্দটিকে সামনে রেখে রবীন্দ্রনাথ ‘একা’ শব্দটিকে তাই যেন এক দিগন্ত দিলেন। এবং ‘অপূর্ব’ শব্দটি তখন কেবলমাত্র সুন্দরের প্রতিরূপ হয়ে আর থাকল না। তার মধ্যে এসে যোগ দিল আড়াল, নির্জনতাও।
আজীবন, এভাবেই, নিজের অভিজ্ঞতার পাশে ‘অপূর্ব’ শব্দটির মতোই শিল্পের-অভিজ্ঞতাকে যোগ করতে চেয়েছিলেন ঋতুপর্ণ ঘোষ। তাঁর তৈরি ছবি বারংবার অর্জন করেছে একাধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার। দর্শক নিরন্তর উৎসাহে দেখতে গিয়েছেন তাঁর ছবি। দেশের প্রথম শ্রেণির অভিনেতারা সব সময়ে উন্মুখ থেকেছেন তাঁর চলচ্চিত্রে কাজ করার জন্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এসবের ঊর্ধ্বে উঠে, আমাদের সমাজের এক বিরাট অংশের মানুষের আগ্রহ ও আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল কেবল তাঁর নারীসুলভ আচরণ, ভিন্ন যৌন অভিমুখ ও সাজপোশাক। ২০০৭ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ‘রোববার’ পত্রিকার ‘একা’ নামক একটি বিশেষ সংখ্যায় ঋতুপর্ণ ঘোষ লিখেছিলেন:
যে-জীবন হয়তো-বা আমাকে একাকিত্বের এই বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিতে পারত, আমাদের সমাজে তার কোনও স্থান নেই। আমার স্বভাবপ্রণোদিত ‘অস্বাভাবিকতা’ নিয়ে আমি বাস করেছি আমার একাকিত্বের বন্দিজীবনে- আর আমার সামনে ছিল সমাজের এক বিরাট কারাগার। যেখানে ঐতিহাসিকভাবে যে কোনও নতুন প্রথাকেই প্রবেশ করতে হয়েছে দণ্ডিত বিদ্রোহীর মতো, অনেক হিংসা এবং রক্তপাতের মূল্যে।
এই অপ্রতিরোধ্য অপমানের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি কী করেছিলেন? না, কিছুই করেননি। কেবল তাঁর ছবির চরিত্রদের নানাবিধ আচরণের মধ্য দিয়ে তিনি খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন জীবনে সম্মানের সঙ্গে বাঁচার স্বাধীনতাটুকু! যেমন, ‘দহন’-এর রোমিতা। ‘দোসর’-এর কাবেরী। ‘দ্য লাস্ট লিয়র’-এর বন্দনা। অথবা ‘চোখের বালি’-র বিনোদিনী। যদিও মূল-উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্রে ‘চোখের বালি’-র বিনোদিনীকে বেশ কিছু ক্ষেত্রে ভিন্নরূপে দেখা যায়। এই যে বিনোদিনীকে নিজের মতো করে সাজিয়ে তুলেছিলেন ঋতুপর্ণ, তার কারণ কী? ঋতুপর্ণ ঘোষ লিখছেন:
বিধবাবিবাহ যেখানে কেবলমাত্র একটা আইন, একটা প্রথা নয়- আইনগতভাবে সম্পূর্ণ জীবনযোগ্য হয়েও যে জীবননির্বাসিতা, কোথায় যেন মনে-মনে, হয়তো আবেগবশতই তার সঙ্গে নির্মাণ করে নিয়েছিলাম, কোনও এক আত্মজৈবনিক সমান্তরলতা।
এখানে ‘আত্মজৈবনিক সমান্তরলতা’ কথাটিকে খেয়াল করতে অনুরোধ করব। নিজের জীবনের প্রান্তিক-অবস্থানকে নিজের তৈরি ছবির একটি চরিত্রের সমাজরুদ্ধ অবস্থানের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চেয়েছিলেন ঋতুপর্ণ। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতায় রয়েছে এরকম লাইন: ‘নিজেকে চার টুকরো করে একটাকে যাই রেখে’- এও যেন ঠিক তাই!

'চোখের বালি'-র বিনোদিনীর চরিত্রে ঐশ্বর্য রাই
আব্বাস কিয়ারোস্তামি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন:
My highest aim presently is to give new information about myself.
কিন্তু আমাদের ‘সেলফ’ তো একইরকম থাকে না। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে ‘সেলফ’ পালটাতে থাকে। সেইজন্যই কিয়ারোস্তামি বলছেন ‘new information’ কথাটি। নিজের সম্পর্কে নিজেরই অজানা কোনও দিক, যা এই মুহূর্তে প্রকাশিত হলো আমার সামনে, তা আমার শিল্প-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমি বলে দেব। ঋতুপর্ণ ঘোষের লেখা ও তাঁর তৈরি ছবিগুলি পাশাপাশি রাখলে মনে হয়, তাঁর মন ছিল এই চিন্তারই সমর্থক। হয়তো এ-কারণেই, ঋতুপর্ণ ঘোষ তাঁর ছবির চরিত্রদের বারবার ছুড়ে দিয়েছেন নিয়তির পরিহাসের সামনে। এবং সম্পর্কের বিচিত্র সব টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে সেইসব চরিত্রদের ভেতর থেকে বের করে আনতে চেয়েছেন মনের সেই ‘new information’-কেই।
শুধু তাই নয়, সমকাম ও তার বহুমুখী গতিপথকেও তিনি একইভাবে খুঁজতে চেয়েছিলেন। ২০০৯ সালের ১৯ জুলাই, ঋতুপর্ণ ঘোষ লিখছেন:
‘পুরুষ’ এবং ‘নারী’ এই দুটি বিপরীত শব্দের মাঝখানে এক অসীম প্রান্তর, যেখানে বসবাস করেন অর্ধনারীশ্বতার নানা প্রতিভূ।
‘আরেকটি প্রেমের গল্প’, ‘মেমোরিজ ইন মার্চ’ এবং ‘চিত্রাঙ্গদা’- এই তিনটি ছবির মধ্যে অর্ধনারীশ্বরতার সেই নানান প্রতিভূকেই দেখতে পাই আমরা।

'আরেকটি প্রেমের গল্প'-র একটি দৃশ্যে ঋতুপর্ণ ঘোষ ও ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত
সকলেই জানেন, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত ‘আরেকটি প্রেমের গল্প’ দিয়ে ঋতুপর্ণ ঘোষের অভিনয়-জীবন শুরু হয়। ছবিতে একইসঙ্গে চপল ভাদুড়ী এবং পরিচালক অভিরূপের চরিত্রে দেখা যায় ঋতুপর্ণ-কে। দু'টি চরিত্র-ই বিকল্প-স্রোতের মানুষ। কিন্তু চপল যেখানে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে মেয়ে ভাবতে চায়, সেখানে অভিরূপ তা চায় না। সে নারী-পুরুষের মধ্যবর্তী সেই অসীম প্রান্তরের কোনও এক স্থানে নিজেকে দেখতে পায়।
‘মেমোরিজ ইন মার্চ’-এর চিত্রনাট্য লিখেছিলেন ঋতুপর্ণ ঘোষ। পরিচালনা সঞ্জয় নাগের। ছবিতে অর্ণব একজন সমকামী মানুষ। চরিত্রটিতে অভিনয় করেছিলেন ঋতুপর্ণ ঘোষ। অফিস-কলিগ সিদ্ধার্থ ও অর্ণবের মধ্যে জন্ম নেয় প্রেমসম্পর্ক। পথ-দুর্ঘটনায় মারা যায় সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থ-র মা দিল্লি থেকে এসে জানতে পারে সন্তানের বিকল্প যৌন-পরিচয়ের কথা। ঠিক এখান থেকেই শুরু হয় ছবি। প্রথমে মেনে না-নিলেও, ধীরে-ধীরে সিদ্ধার্থ-র চলে যাওয়াকে ঘিরে সিদ্ধার্থ-র মা আরতি ও অর্ণবের মধ্যে তৈরি হয় বন্ধুত্ব। যে-বন্ধুত্বে, কথোপকথনে, দু'-জনেই কিন্তু খুঁজে চলে সিদ্ধার্থকেই। একজন সমকামী মানুষের জীবন-প্রেম-আকাঙ্ক্ষা-যন্ত্রণা যে অন্য একজন মূল-স্রোতের মানুষের মতোই, এই সহজ সত্যটুকু সঞ্চয় করে শিল্পের দরজায় পৌঁছে যায় ‘মেমোরিজ ইন মার্চ’।

'মেমোরিজ ইন মার্চ'-এ ঋতুপর্ণ ঘোষ ও দীপ্তি নাভাল
তবে, ঋতুপর্ণ ঘোষের আত্মখননের সর্বাত্মক স্ফুরণকে বোধহয় ধারণ করে আছে ‘চিত্রাঙ্গদা’। ছবিটির প্রথম দিকেই আমরা শুনতে পাই এই সংলাপ: ‘চিত্রাঙ্গদা একটা ইচ্ছের গল্প, that you can choose your gender.' অর্থাৎ আমি দেহগতভাবে পুরুষ না নারী, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমার মনের পরিচয় কী? মনোগতভাবে আমি কি ‘পুরুষ’? না ‘নারী’? না এ-দুয়ের বাইরে অচেনা-অজানা অন্য কিছু? বহু-বিচিত্র হতে পারে তার রূপ! কিন্তু শরীরী-পরিচয়ের বাইরে, মনের সেই ইচ্ছেটাই আমার প্রকৃত যৌন-পরিচয়! এমনই আশ্চর্য চিন্তাভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে সম্পূর্ণ ছবিটি।

'চিত্রাঙ্গদা'-র একটি দৃশ্যে ঋতুপর্ণ ঘোষ ও যীশু সেনগুপ্ত
এখানে মনে পড়ে যায়, ‘মনোলগ: দুই বাংলার লেসবিয়ান কথন’ নামক একটি বইয়ের কথা। পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের কুড়ি জন লেসবিয়ান-এর সাক্ষাৎকার একত্র করে মীনাক্ষী সান্যাল মালবিকা ও সুমিতা বীথি-র সম্পাদনায় বইটি কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে। বইটিতে চব্বিশ বছর বয়সি একজন লেসবিয়ান মহিলা নিজের যৌন-অভিমুখ সম্পর্কে জানাচ্ছেন:
…আগে আমি শুধু মেয়েই ভাবতাম নিজেকে, এখন মনে হয়, রোজ আমি মেয়ে হতে চাই না, এক-একদিন আমার অন্য কিছু হতে ইচ্ছে করে। …সাজগোজ তো মেয়েদের মতোই করি, রোজই, কারণ ওরকম সাজতে আমার ভাল লাগে, কিন্তু ভেতরের ফিলিং-টা এক-একদিন এক-একরকম হয়।
খেয়াল করুন, এখানেও দেখা দিল সেই একই শব্দ: ইচ্ছে। যে-ইচ্ছে এক-একদিন এক-একরকম রূপ নেয়। যে-ইচ্ছে সব সময় পরিবর্তনশীল। এখানে আবারও ফিরিয়ে আনতে চাইব ‘চিত্রাঙ্গদা’-র সেই সংলাপ: ‘চিত্রাঙ্গদা একটা ইচ্ছের গল্প, that you can choose your gender’। যৌনতাকে এমনই সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছিলেন ঋতুপর্ণ ঘোষ। জীবনকেও তাই।
সদ্য পেরিয়ে গেল ৩১ অগাস্ট, তাঁর জন্মদিন। ষাট বছরে পা দিলেন তিনি। অথচ এখনও এক অর্থে প্রান্তিক হিসেবেই যেন থেকে গেছেন ঋতুপর্ণ ঘোষ।
হ্যাঁ, ঋতুপর্ণ ঘোষের ফোটোগ্রাফ বা ছবির বিভিন্ন দৃশ্য তাঁর জন্ম ও মৃত্যুতারিখে সোশ্যাল মিডিয়া-য় দাপটের সঙ্গে তাঁর উপস্থিতি জানায়। কিন্তু সত্যি বলতে, সেই উপস্থিতি কি তাঁর চিন্তার যথার্থতা আমাদের কাছে পৌঁছে দেয়? দেয় না।
ঋতুপর্ণ ঘোষের নির্মিত চলচ্চিত্র, তাঁর লেখা এবং সাক্ষাৎকার- একমাত্র এর মধ্যেই ধরা আছে তাঁর জীবন ও জীবনের সঙ্গে শিল্পের সংমিশ্রণ-মুহূর্ত।
সেই প্রান্তরে তিনি আজীবন যতখানি একা। ততখানিই অপূর্ব!




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp