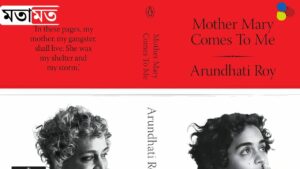উৎসব : একটি শব্দে যেভাবে সম্পর্কের জাগরণ এঁকেছিলেন ঋতুপর্ণ
Rituparno Ghosh Utsab: পূরবী’ কথাটিকে যেভাবে সংলাপের প্রথমের ব্যবহার করলেন ঋতুপর্ণ, তখন তা নিছকই একটি রাগ-শব্দ মাত্র। কথোপকথন যত এগোল, সেই পূরবীকেই তিনি যুক্ত করে দিলেন কেয়া ও অরুণের বিবাহ-সম্পর্কের সঙ্গে।
ঋতুপর্ণ ঘোষ নিজের সিনেমায় কীভাবে একটি দৃশ্যকে ভাবতেন? সেই দৃশ্যকে সাজাতেন কীভাবে? দৃশ্যটির প্রথম মুহূর্ত ও তার সমাপ্তি-মুহূর্তের মধ্যে কীভাবে এঁকে দিতেন এক নিবিড় সংযোগরেখা?
এই প্রশ্নগুলির সামনে আজ দাঁড় করাতে চাইব ‘উৎসব’-এর একটি ছোট্ট সংলাপকে। দৃশ্যটি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় অভিনীত। ছবিতে চরিত্র দু'টির নাম ছিল, কেয়া ও অরুণ। যাঁরা ছবিটি দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই মনে করতে পারবেন, ‘উৎসব’-এ কেয়া ও অরুণের বিবাহজীবন অশান্তিপূর্ণ। আর্ট কলেজে পড়ত দু-জনেই। সেখানেই প্রেম। তারপর বিয়ে। নিজের জীবনে তেমন কিছু করে উঠতে পারেনি অরুণ। পলিটিক্স করত। সেটাও ছেড়ে দিয়েছে। মদ খায়। মাতাল অবস্থায় থাকে। একটা ফাস্ট্রেশন কাজ করে অরুণের মধ্যে। কেয়া চায়, তাঁদের দাম্পত্যে সব কিছু ঠিক হয়ে যাক। কিন্তু অরুণের ফাস্ট্রেশন তা হতে দেয় না। বারংবার কেয়াকে সে অসম্মানের মুখে ফেলে দেয়। কেয়ার নিজের বাড়ির লোকের সামনেও তাদের দাম্পত্য-কলহ অরুণ লুকিয়ে রাখে না। গ্রামে, কেয়ার বাপের বাড়ির পুজোয় ক'টা দিন নিজেদের সম্পর্ককে আরেকটা ‘চান্স’ দেওয়ার জন্য এসে থাকবার সিদ্ধান্ত নিলেও, ঝগড়া করে আত্মীয়ভর্তি বাড়ির সামনেই বেরিয়ে যায় অরুণ। ফিরে আসে অষ্টমীর দিন। গায়ে জ্বর নিয়ে। এরপর তাদের একাকী কথোপকথন এমন:
অরুণ। পূরবী বাজছে না?
কেয়া। হ্যাঁ, বিসমিল্লাহ। রেকর্ডটা ছিল আমাদের বাড়িতে।
অরুণ। হুম। আমাদের বিয়ের দিন বাজছিল। তোমাদের নীচের ঘরটা দেখাবে বলেছিলে, বিয়ের দিন যেখানে বসেছিলাম।
কেয়া। তুমি একবার সকলকে গিয়ে প্রণাম করে এসো। ছোড়দা'রা বোধহয় চলে যাচ্ছে।
অরুণ। কতটা বলেছ বললে আমার একটু সুবিধে হতো।
কেয়া। ধরো, কিছু বলিনি।
অরুণ। সেটা আমায় বিশ্বাস করতে হবে?
কেয়া। তাহলে ধরো সবটাই বলেছি।
অরুণ। তাহলে আর বাচ্চাদের জামাকাপড় দেওয়া নিয়ে নাটক করার দরকারটা কী?
কেয়া। তোমার যা ইচ্ছে তুমি তাই বলো।
অরুণ। ওহ। এই ব্যাপারে তোমার কোনও রিকোয়েস্ট নেই?
কেয়া। (জানলার কাছে উঠে গিয়ে) পূরবী না, মারোয়া!
অরুণ। তাহলে এটা বাজছিল না বিয়ের দিন।
কেয়া। বাইরে বাজছিল, তুমি হয়তো বুঝতে পারোনি।

ঋতুপর্ণ কী দিয়ে শুরু করলেন সংলাপটি? অরুণ জিজ্ঞেস করল, ‘পুরবী বাজছে না?’ কেয়ার উত্তর, ‘হ্যাঁ বিসমিল্লাহ। রেকর্ডটা ছিল আমাদের বাড়িতে।’ সঙ্গে সঙ্গে অরুণের স্মৃতিতথ্য জানায়, এই পূরবীর রেকর্ডটাই ওদের বিয়ের দিন বাজছিল। কত সাধারণ-স্বাভাবিক এই জিজ্ঞাসা-উত্তর। এবার যদি দৃশ্যটির সংলাপের দিকে আমরা তাকাই, দেখতে পাব দু'জনের ধ্বংসোন্মুখ সম্পর্কের অগ্নিছাই সেখানে ক্রমাগত উড়ছে। দু'জনের কথাতেই এক ধরনের রাগ, অপ্রাপ্তি এবং দু'জনের অন্তরই যেন কুঁকড়ে আছে অব্যক্ত অপমান ও প্রেমের যন্ত্রণায়। এই সংলাপের এক জায়গায় দেখা যায়, কেয়া উঠে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়ায়। বাইরে তখন সানাইয়ের আওয়াজ ভেসে আসছে। যে-সানাইয়ের সুর ওদের বিয়ের দিন বেজে চলেছিল। কেয়া সেই সানাইয়ের সুরের ভেতর, জানলার বাইরে তাকিয়ে স্থিরভাবে বলে, ‘পূরবী না, মারোয়া।’
আরও পড়ুন- স্বীকৃতিহীন অপূর্ণ প্রেমের প্রদীপখানি — ঋতুপর্ণ ঘোষের উৎসব
এইখানে এসে ‘পূরবী’ শব্দটির গুরুত্ব কী এবং ‘পূরবী বাজছে না?’ কেন এই কথাটি দিয়ে শুরু হয়েছিল দৃশ্যটি, তা সামান্য যেন ধরিয়ে দিলেন ঋতুপর্ণ। সকলেই জানেন মারোয়া, সূর্যাস্তের রাগ। বিচ্ছেদ সেখানে সম্পূর্ণ। সম্পর্কের ভেতর ক্রমশ ফুরিয়ে আসা আলো। মারোয়ায় সর্বক্ষণ বিষাদ, বিষাদ। আত্মার ওপর ভারী পাথরের মতো আটকে থাকা বিষাদ। কেয়া, অরুণের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে এক সময় বুঝতে পারে, তাদের সম্পর্কের আর কোনও ভবিষ্যৎ নেই। বিয়েটা আর থাকবে না। তখন জানলায় কাছে গিয়ে বিয়ের দিনের সানাইয়ের সুরকে ওর মনে হয়, ‘পূরবী না, মারোয়া’। অর্থাৎ, ওদের সম্পর্কের আকাশে এখন শুধুই সমাপ্তির সুর।
দৃশ্যটির পরবর্তী সংলাপ এমন:
অরুণ। প্রণাম করতে আমি একা যাব? না তুমি সঙ্গে যাবে?
কেয়া। তুমিই তো বললে নাটক করার কোনও দরকার নেই।
অরুণ। একা গেলে আরও বেশি নাটক হবে।
কেয়া। দ্যাখো, সবে পুজো কেটেছে। ছোড়দা'রা বোধহয় আজই চলে যাবে। আমি এর মধ্যে কোনও অ্যাডেড টেনশন দিতে চাই না।
অরুণ। অ্যাডেড টেনশন কেন?
কেয়া। বাড়ি বিক্রি নিয়ে এমনিতেই যথেষ্ট টেনশন...
অরুণ। বাড়ি বিক্রি হচ্ছে শেষ পর্যন্ত?
কেয়া। কুড়ি লাখ টাকার অফার এসেছে। ভাগ করলে চার ভাইবোন আর মায়ের ভাগে চার করে হচ্ছে। চার-এ কোনও ফ্ল্যাটও হয় না, বাড়িও হয় না। মাকে কারও না কারও সঙ্গে থাকতে হবে।
অরুণ। আমাদের শেয়ারটা ছেড়ে দাও। আট-এ ঠিক হয়ে যাবে।
কেয়া। আমাদের মানে?
অরুণ। মানে, তোমার।
কেয়া। তারপর, আমি কোথায় থাকব?
অরুণ। যেখানে আছো এখন।
(কেয়া জানলার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। অরুণ উঠে গিয়ে পাশে দাঁড়ায়)
অরুণ। কেঁদো না। কাঁদছ কেন? বিয়ের আগে তো কতবার কত চিঠিতে লিখেছ, আমার সঙ্গে দেখা করবে না, আমার মুখ দেখবে না। মেনটেন করতে পেরেছ?
কেয়া। সেটাই তো আমার কাল হয়েছে। তুমি ধরেই নিয়েছ, তুমি যেটা করবে আমি সেটা মেনে নেব।
অরুণ। ডিভোর্সের কথাটা তুমি বলেছ, আমি বলিনি।
কেয়া। বলোনি, কাজে করে দেখিয়েছ। একটা মাতালকে দিয়ে চিঠি ড্রাফট করে পাঠিয়ে দিয়েছ।
অরুণ। কোনটায় আপত্তি তোমার? হুম? মেক আপ ইওর মাইন্ড। চিঠিটায়? না মাতালকে দিয়ে চিঠিটা ড্রাফট করিয়েছি বলে?
(অসম্ভব কাঁদতে-কাঁদতে কেয়া জড়িয়ে ধরে অরুণকে। দু'জনে আলিঙ্গনরত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে)
অরুণ। ধ্যাত, এটা পূরবী বাজচ্ছে।
দেখুন, সংলাপটি কীভাবে বাঁক নিল অরুণের একটি কথায়। ‘আমাদের শেয়ারটা ছেড়ে দাও, আট-এ ঠিক হয়ে যাবে’— এইখান থেকে সম্পূর্ণ কথোপকথন নরম ও নিবিড় হতে শুরু করল এবং দৃশ্যটিকে ঋতুপর্ণ শেষ করলেন কীভাবে? শুরু হয়েছিল যেখান থেকে, সেই সূচনাশব্দ ‘পূরবী’-তে ফিরে এসেই। কেয়া অরুণকে ভালবাসে। অরুণও তাই-ই। দু'জনের মান-অভিমান, অপমান-যন্ত্রণাকে সরিয়ে কেয়া যখন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে, তখন, আলিঙ্গনরত অবস্থায় অরুণ বলে, ‘ধ্যাত, এটা পূরবী বাজছে’।
পূরবী, সন্ধ্যার রাগ। মারোয়া-র ঠিক পরপরই। কিন্তু মারোয়ার মতো তীব্র যন্ত্রণা সেখানে নেই। বরং যন্ত্রণাকে সঙ্গী করে এক ধরনের উত্তরণ রয়েছে। জেগে ওঠা আছে। ‘দিনশেষের রাঙা মুকুল জাগল চিতে/সঙ্গোপনে ফুটবে প্রেমের মঞ্জরীতে’, ১৯২৪ সালে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই গানের মূল-সুর, পূরবী। কী বলছেন রবীন্দ্রনাথ? বলছেন দিন শেষের যে রাঙা মুকুল সে আমার মনে জেগে উঠছে। ফলে, ফুটে উঠছে প্রেমমঞ্জরী। এখানে খেয়াল করতে অনুরোধ করব, এ কিন্তু শুধুমাত্র প্রেমের উদ্ভাসন নয়। এখানে ‘রাঙা’ কথাটি যেমন জরুরি, তেমনই ‘দিনশেষে’-ও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একটি দিন মানে, একটি জীবনও তো। সারাটা জীবন পার করে, সূর্যাস্তে এসে একটি রাঙা মুকুল আমার প্রাণে জেগে উঠছে। তাই, এ জেগে-ওঠার মধ্যে ‘রাঙা’ কথাটির আনন্দ যেমন আছে, তেমনই তা ‘দিনশেষে’-র বিষাদক্লান্তিকে অস্বীকার করছে না।

এটাই তো কেয়া ও অরুণের সম্পর্কের প্রকৃত অবস্থান। তাঁদের কথোপকথনটি যে সম্মীলন-মুহূর্তে পৌঁছল সেখানে তাঁদের সম্পর্কের পূর্বতন বিষাদ-অভিজ্ঞতা ‘দিনশেষে’-র মতন বিদ্যমান। কিন্তু তার মধ্যে থেকেই ওঁরা দু'জনে, সম্পর্কের গভীরে নেমে ‘রাঙা’ কথাটিকে তুলে আনতে চায়। এখানেই পূরবী। এবং এখানেই, ঋতুপর্ণের একটি দৃশ্যভাবনার সংকেত সূত্রগুলিও হয়তো ফুটে ওঠে।
আসলে, অভিনবত্ব এখানে নয় যে একটি কথা দিয়ে শুরু করে, সেই কথাতেই ফিরে এল সংলাপ। এমন তো হয়-ই। কিন্তু যেভাবে, যে-শব্দ উপকরণ নিয়ে দৃশ্যভাবনা শুরু করলাম, সেইসব শব্দ কি কোনও উত্তরণ পেল? না কি ছড়িয়ে থাকল যে যার মতো? ‘পূরবী’ কথাটিকে যেভাবে সংলাপের প্রথমের ব্যবহার করলেন ঋতুপর্ণ, তখন তা নিছকই একটি রাগ-শব্দ মাত্র। কিন্তু কথোপকথন যত এগোল, সেই পূরবীকেই তিনি যুক্ত করে দিলেন কেয়া ও অরুণের বিবাহ-সম্পর্কের সঙ্গে। শেষে পৌঁছে, ‘পূরবী’ আর ওঁদের জীবন কোথায় যেন একাকার হয়ে গেল!
আরও পড়ুন- বাঙালি দর্শকের অস্পৃশ্য উদাসীনতা ছিল ঋতুপর্ণর চিত্রঙ্গদার প্রতি
আমার মনে পড়ছে জয় গোস্বামীর সঙ্গে ঋতুপর্ণ ঘোষের একটি কথোপকথনের কথা। এখানে উদ্ধৃত করছি:
‘অপুর সংসার’-এ অপু এসে অপর্ণাকে বলে, মানে ও চুল বাঁধছিল আর অপু এসে বলে, ‘আচ্ছা তোমার অনুশোচনা হয় না?’ শর্মিলা ঠাকুর কীরম একটা অদ্ভুত আধো-আধো করে বলেন, ‘অত শক্ত কথা বুঝি না। তখন সৌমিত্রদা (অপু) বলেন, ‘আপসোস হয় না?’— ‘কেন আপসোস হবে কেন?’— ‘তোমার বড় লোকের বাড়ির গিন্নি হওয়াটা ফসকে গেল বলে!’ — কীরকম হঠাৎ করে অপর্ণাকে মনে হয় সে ভীষণ অভিজ্ঞ একটা মেয়ে। গালে টোল ফেলে হাসতে-হাসতে বলে, ‘হ্যাঁ, কেমন পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকতে পারতুম। ঘরের কাজ করতে হত না।’ অপু বিছানার ওপর বাঁশিটা রাখে, বেরিয়ে চলে যায়। অপর্ণা উঠে গিয়ে বলে, ‘কোথায় যাচ্ছ?’ — অপু বলে, ‘এক্ষুনি একটা কাজের মেয়ে খুঁজে আনছি।‘ অপর্ণা বলে, ‘ভেতরে এসো, কী ছেলেমানুষি করছ!’ অপু এসে বসে। তারপর সেই বিখ্যাত ফ্রেমটা। অপুর কাঁধে অপর্ণার মুখ, অপু বসে আছে। অপর্ণা এসে বসে, মানে, তখন শর্মিলা ঠাকুরের এতখানি পানের মতো মুখ, অত বড়-বড় চোখ, ঠিক মুখটা এসে কাঁধে রেখে বলে যে, ‘আমি একটা কথা বলব?’ অপু বলে, ‘বলো।’ — ‘তাহলে আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও।’ তখন বলে, ‘কেন?’ বলে, ‘একেই তো রাত করে ছেলে পড়িয়ে বাড়ি ফেরো। অপু বলে, ‘তাহলে চলবে কী করে বলো?’ অপর্ণা তখন বলবে, ‘আমি বলব?, যে-টিউশনটা আছে ওটাও ছেড়ে দাও। তারপর আমার গরিব বর সন্ধের আগে বাড়ি ফিরে আসবে আর আমার অনুশোচনা থাকবে না।’ অনুশোচনা দিয়ে শুরু হল তারপরে তোমার মনে হবে প্রায় এই ‘অনুশোচনা’ শব্দটা যেন মুক্তি পাবার কোথায় ছটফট করছিল সিনটার মাঝখানে।… ‘অনুশোচনা’ শব্দটা যখন অপর্ণার মুখে ফিরে এল তখন মনে হলো মোক্ষম। এই শব্দটাই ফেরার কথা এবং ‘অনুশোচনা’ শব্দটা একটা বন্ধন তৈরি করে দিল ওদের মধ্যে। একটা অভিজ্ঞতায় আটকে দিল। অপুর অভিজ্ঞতাটা অপর্ণা নিয়ে নিল পুরো।
এখানে ঠিক যেভাবে ‘অনুশোচনা’ শব্দটি অপর্ণা ও অপুর কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে এক নতুন অভিজ্ঞতায় মুক্তি পেল। ‘উৎসব’-এও ‘পূরবী’ কথাটি কেয়া ও অরুণের কথোপকথনে ওদের জীবনটাকেই বর্ণনা করছিল যেন। মাঝখানে মারোয়ার বিষাদ এসে দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষণ। কিন্তু তারপরই পূরবীর রাঙা মুকুল নতুন জাগরণের দিকে নিয়ে যায় কেয়া ও অরুণকে।

এখানে আরেকটা মিল লক্ষ্য করি। অপর্ণা যখন বলে, যে ক'টা টিউশন আছে সেগুলোও ছেড়ে দাও, তখনই সংলাপটি ঘুরে যায়। ঋতুপর্ণ বলছেন, সেই মুহূর্তে অপুর অভিজ্ঞতাটা অপর্ণা নিয়ে নেয়। ঠিক তেমনই, ‘আমাদের শেয়ারটা ছেড়ে দাও, আট-এ ঠিক হয়ে যাবে।’ অরুণের বলা এই কথাটি ঘুরিয়ে দেয় ওদের সংলাপের গতি। এবং আস্তে-আস্তে এখানেও, কেয়ার অভিজ্ঞতাটা অরুণ নিজের করে নেয়। এবং অরুণই প্রেম-আলিঙ্গনে শেষে বলে, এই সানাইয়ের সুর মারোয়ার নয়, পূরবীর। অর্থাৎ, একটা উত্তরণ হয়তো আছে। সেই উত্তরণ, আমরা ঠিক খুঁজে পাব।
এই হলো ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। অভিনব, আশ্চর্য এবং সংকেতে পূর্ণ। জীবনের তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে থেকে সোনারুপো খুঁজে আনার আনন্দরস সেখানে বহমান!
বিশেষ কৃতজ্ঞতা: অনিন্দ্য সরকার, দীপাঞ্জন পাল




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp