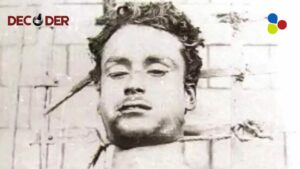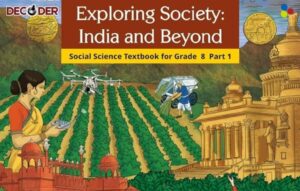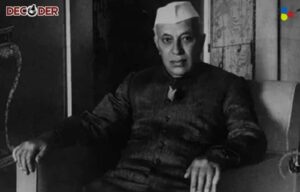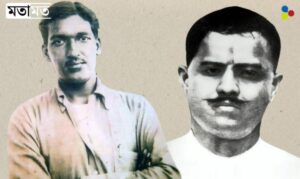কেন বিশ্বের অধিকাংশ মুখোশই ভয়ের? অবাক করবে মুখোশের এই ইতিহাস
History of Mask: শ্রীলঙ্কায় মুখোশধারী পুরোহিতকে পাওয়া যাবে চিকিৎসকের ভূমিকায়। লৌকিক বিশ্বাসে আঠারোটি কুঠুরি নিয়ে তৈরি একটি কুঁড়েঘরের সামনে রাখা হয় অসুস্থ মানুষকে। প্রতিটি কুঠুরিতে বাস এক একটি ভূত বা রাক্ষসের।
মুখ আর মুখোশ – এই দুইয়ের দ্বান্দ্বিক প্রকাশ সাহিত্যের এক গভীর চিত্রকল্প। যে মুখ কথা বলে, মুখোশের আড়ালে ঢাকা পড়লে সে কি অন্যরকম? এ ব্যাপারে অস্কার ওয়াইল্ডের মত নেহাতই সোজাসাপ্টা, “man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask and he will tell you the truth!” মঞ্চের অভিনেতা যেমনভাবে প্রবিষ্ট হন তার অভিনীত চরিত্রে - আপন কুশলতায় ফুটিয়ে তোলেন সেই চরিত্রের অবয়ব তার শরীরী ভাষায় - ঠিক সেভাবেই মুখোশের ঘেরাটোপে আমরা দেখি অন্য কোনওজনকে, যার পরিচয় মূর্ত হয় মুখোশের মুখ জুড়ে। লেখক কুণাল বসু মুখোশ আর স্বপ্নের মধ্যে খানিক সাদৃশ্য দেখেন, "both are extensions of our mind, playful and unpredictable in parts"। সুতরাং মুখোশকে ঘিরে যুগ থেকে যুগান্তরে দানা বেঁধেছে এক উপলব্ধি যা আসলে কৌতুক, বিস্ময়, ধর্ম বিশ্বাস এবং রহস্যময়তার এক বিচিত্র মিশেল।
কে প্রথম মুখোশ তৈরি করেছিল তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। ঐতিহাসিকদের একাংশ বিশ্বাস করেন, মুখোশের সৃষ্টি আসলে রণক্ষেত্রে ব্যবহৃত ঢালের থেকে। সম্মুখ সমরে যোদ্ধারা নিজেদের সুরক্ষার জন্য ঢাল ব্যবহার করত কিন্তু এর ফলে উদ্যত শত্রুকে যেমন দেখতে সমস্যা হতো তেমনই তাদের একটি হাত সর্বদা আটকে থাকত ঢালটিকে ধরবার জন্য। সমাধানের রাস্তা হিসেবে উঁকি দেওয়ার জন্য ঢালের উপর তৈরি হলো দু'টি গর্ত। দুটো হাত খালি রাখবার তাগিদে যোদ্ধারা এবার মাথায় বেঁধে নিল ঢাল আর তারপর শত্রুদের ভয় দেখানোর জন্য, ঢালের সামনের দিকে আঁকা হলো ভয়ানক মুখ। জন্ম নিল মুখোশ বা মাস্ক বা নকাব।
করোনা পরবর্তী পৃথিবীতে মাস্ক বা মুখোশের ব্যবহারিক সংজ্ঞা এখন অন্যরকম। জীবাণুর আক্রমণ প্রতিহত করাই তার কাজ। বহুদেশিয় কোম্পানির লাল রঙা সাবানের মতোই মাস্ক গত কয়েক বছরে হয়ে উঠেছে 'স্বাস্থ অউর তন্দুরুস্তি'-র প্রতীক। কিন্তু পৃথিবী জুড়ে মাস্ক বা মুখোশের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ব্যক্তিত্বারোপ বা impersonification-এর বাসনা অথবা প্রয়োজনের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। খুব স্বল্প পরিসরে ভাবলে, মুখোশ হয়তো নেহাতই এক খেলনার উপকরণ যার মধ্যে মিশে থাকে এক শিশুসুলভ আনন্দের প্রকাশ কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ছদ্মমুখের ব্যবহার দেখা গেছে সামাজিক ও ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডে, অভিনয়, নৃত্য প্রভৃতি শিল্পের সুচারু উপস্থাপনায়, গুপ্তচরবৃত্তি অথবা সামরিক প্রয়োজনে কিংবা ক্রীড়াঙ্গনের এক অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে।

যে চেহারা আমাদের পরিচয়বাহী, তাকে অন্তরাল করতে মুখোশের ব্যবহার সেই প্রাচীনকাল থেকে যার বিকাশ মূলত 'স্কাল আর্ট' বা 'করোটি শিল্পকলা' হিসেবে খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে প্যালেস্টাইন বা কান্নান অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। মৃত মানুষের করোটির উপরে মাটির প্রলেপ এবং রঙ লাগিয়ে তৈরি করা হতো এই ধরনের মুখোশ। এখান থেকে ক্রমশ তা ছড়িয়ে পড়ে মধ্য প্রাচ্যসহ পৃথিবীর অন্যান্য অংশে। উত্তর আমেরিকার ইস্টার্ন উডল্যান্ডস এবং দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত দেশ পাপুয়া নিউ গিনির উপজাতিদের মধ্যেও চলন ছিল এ ধরনের মুখোশের। বিশ্বাস ছিল সমাজের জ্ঞানী মানুষের প্রজ্ঞা সুরক্ষিত থাকবে মুখোশের মধ্যে আগামী প্রজন্মের জন্য। এই মুখোশ হবে তাদের রক্ষাকবচ। 'স্কাল আর্ট'-এর খুব কাছাকাছি মুখোশ হলো 'ডেথ মাস্ক', যার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে প্রাচীন মিশরে ফারাওদের মমিতে। এর সব থেকে পরিচিত উদাহরণ ১৯২২ সালে আবিষ্কৃত রাজা তুতেনখামেনের মমি। সোনা এবং নানা মূল্যবান পাথরে তৈরি সেই মুখোশ থেকে মাত্র ষোল বছরে মৃত রাজার চেহারার খানিক অনুমান করতে পেরেছিলেন প্রত্নতত্ত্ববিদরা। এছাড়াও কলাম্বিয়া, পেরু, মেক্সিকো, আফ্রিকা, মেসোপটেমিয়া, থাইল্যান্ড, চিন এবং ইওরোপের বেশ কিছু দেশে 'ডেথ মাস্ক'-এর চলন ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। গ্রিসে, পাতালের দেবী পার্সেফোনের নামাঙ্কিত মুখোশ রাখা হতো মৃতের মুখের উপর,পরলোকের যাত্রাপথ সুগম করবার লক্ষ্যে। ঠিক একই ধরনের সামাজিক আচার দেখা গেছে ইতালি, রোম অথবা পলেনেশিয়া অঞ্চলের দেশ পাপুয়া নিউ গিনিতে। রেনেসাঁসের ইতালিতে গির্জায় টাঙানো হতো মৃতের মুখোশ। রোমানদের অন্তিম যাত্রায় পরিবারের সদস্যদের মুখ ঢাকা পড়ত পূর্ব পুরুষের মুখের আদলে তৈরি মুখোশে। পাপুয়া নিউ গিনিতে মৃতজনের নামে উৎসর্গীকৃত মুখোশ ভেলায় করে ভাসিয়ে দেওয়া হতো সাগরের জলে। বিবিধ সামাজিক রীতিগুলির মধ্যে যে সাধারণ সূত্রটি দেখা যায় তা আসলে মৃতের আত্মার ইহলোক থেকে পরলোকের যাত্রাপথে সুমঙ্গলবার্তা প্রদানের অভিপ্রায়।

ধর্মীয় বিশ্বাস বা সংস্কার এবং তার দ্বারা চালিত রীতি রেওয়াজের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে মুখোশের ব্যবহার। ইওরোপের বেশ কিছু দেশ যেমন জার্মানি, ইতালি এবং অস্ট্রিয়াতে শীত শেষে, বসন্ত আগমনে অমঙ্গলকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে মাস্ক পরিহিত মানুষ। এর মধ্যে অস্ট্রিয়ার ইমস্ট-এর উৎসব ভারী মজাদার। মুখোশ পরে এক দঙ্গল ছেলে সুগন্ধি পাউডার আর জল ছিটিয়ে দেয় দর্শকদের গায়ে। কেউ বা ঝাঁটা হাতে চিমনি বেয়ে ওঠে তাকে সাফ সুতরো করার তাগিদে। সবারই কামনা দুষ্ট বা অমঙ্গলের হাত থেকে রেহাই পেয়ে এক সুস্থ জীবন যাপন।
এশিয়া মহাদেশের দিকে তাকানো যাক। ভারত, শ্রীলঙ্কা এবং তিব্বতের সমাজ জীবনেও মুখোশের বড় প্রভাব রয়ে গেছে যা প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাস ও লোকাচারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। শিবের মুখোশ নবদ্বীপের লৌকিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অংশ। চৈত্র মাসে শিবপার্বতীর বিয়ের সময় এই মুখোশ তৈরি করা হয়। লৌকিক শৈব সংস্কৃতির সঙ্গে এই মুখোশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটিকে মুখোশ বলা হলেও আসলে এটি মাটি দিয়ে তৈরি মূর্তি। বহুবর্ণশোভিত এই মুখোশ লৌকিক শিল্পের অন্যতম নিদর্শন। কাঁচা মাটি দিয়ে ছাঁচে ফেলে এটি তৈরি করা হয়। রোদে শুকিয়ে সাদা রং করে আঁকা হয় চোখ-নাক-কান। মাথায় সোনালি রঙের টোপর পরানো হয়। তার উপরে থাকে ফণা তোলা সাপ। চতুর্দোলায় সাজিয়ে নিয়ে বাড়ি-বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। ভিক্ষা করে এনে সেই টাকা দিয়ে আয়োজন করা হয় শিবের বিয়ের।
দেশের উত্তর পুবে মাজুলি দ্বীপ। ব্রহ্মপুত্র নদের মাঝে অবস্থিত, প্রায় ৮৮০ বর্গ কিমি দ্বীপ বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসারের ফলে বৈষ্ণব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কেন্দ্রস্থল। এই দ্বীপে ষোলো শতক থেকে মুখোশ তৈরির ঐতিহ্য বিকাশ লাভ করেছে। 'রাস লীলা' এবং 'ভাওনা'-র মতো প্রাণবন্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, স্ট্রিট থিয়েটার সদৃশ উপস্থাপনায় মুখোশ বা 'মুখোতা' ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ ভারতেও নানা ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডে মুখোশের ব্যবহার চলে আসছে বহু শতাব্দী ধরে। কেরলের 'কুটিয়াট্টম' সংস্কৃত থিয়েটার, গুরুভায়ূ মন্দিরে প্রধান দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত 'কৃষ্ণনাট্টম' নৃত্যনাট্য এবং তামিল গ্রামাঞ্চলে 'কাট্টাইকুট্টু' লোকনৃত্য— এ সবেরই প্রাণ হাতে তৈরি মুখোশ।
শ্রীলঙ্কায় মুখোশধারী পুরোহিতকে পাওয়া যাবে চিকিৎসকের ভূমিকায়। লৌকিক বিশ্বাস, কঠিন রোগ নিরাময়ের একমাত্র ভরসা তিনিই। আঠারোটি কুঠুরি নিয়ে তৈরি একটি কুঁড়েঘরের সামনে রাখা হয় অসুস্থ মানুষকে। প্রতিটি কুঠুরিতে বাস এক একটি ভূত বা রাক্ষসের যারা আঠারোটি ভিন্ন ভিন্ন রোগের কারণ। পুরোহিতমশাই একে একে আঠারোটি কুঠুরিতে প্রবেশ করেন এক এক রকমের মুখোশ পরে এবং রোগের বিনাশের পুজো চলে। অবশেষে, আঠারোটি মুখোশ একসঙ্গে পরে একটি নৃত্য পরিবেশন করেন। বিশ্বাস, যদি নাচগুলি সঠিকভাবে সঞ্চালিত হয়, তবে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে।

তিব্বতি সমাজেও মুখোশের বহুল ব্যবহার দেখা গেছে যা মূলত রোগীর সুস্থতা কামনা এবং অসুস্থতা নিরাময়ে ব্যবহৃত হতো। এছাড়াও, সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের লেখা নাটক, যার মূল বিষয় গৌতম বুদ্ধের জীবনযাপনের উপদেশ, অভিনীত হতো মন্দিরে। উজ্জ্বল রঙের মুখোশ পরে অভিনেতারা এতে অভিনয় করতেন। আজও, তিব্বতি মন্দিরের নৃত্যশিল্পীরা মুখোশাবৃত হয়ে অমঙ্গলের দানবকে তাড়িয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানায়। এই পারফরম্যান্সের অন্যতম প্রধান চরিত্র 'যম' (হিন্দু নন, পরিচয়ে বৌদ্ধশাস্ত্র সম্ভূত), যিনি নরকের রাজা এবং বিচারক। একই ধরনের আচার দেখা যায় চিনা নববর্ষে যেখানে ব্যবহৃত হয় দীর্ঘকায় ড্রাগন মাস্ক।
সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, বিশেষত নাটক এবং নৃত্যের পরিবেশনে মুখোশের ব্যবহার পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বিভিন্ন জনজাতির মধ্যেই রয়েছে। এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায় বিনোদন। চরিত্র বিন্যাসের প্রয়োজনে নট-নটীদের মুখে ওঠে বিবিধ মুখোশ। প্রাচীন গ্রিক এবং রোমান থিয়েটারের অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ মাস্ক বা মাস্কা। সুবিশাল অ্যাম্ফিথিয়েটারে বসে অভিনেতাদের মুখের ভাব অভিব্যক্তি ইত্যাদি যাতে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় সেজন্য মুখোশের আকার শুধু বড় হতো না, মুখ গহ্বরের সামনে লাগান থাকত এক ধরনের ধাতব খণ্ড যা মুখোশের ভেতর থেকে অভিনেতার স্বর প্রক্ষেপণে সহায়তা করত। নাটক উপস্থাপনার ক্ষেত্রে মুখোশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল সেই সময়।
গ্রিক ট্র্যাজেডি সাধারণত শুধুমাত্র তিনজন অভিনেতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, যারা মুখোশের সাহায্যে শত শত ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে পারে। ইতিহাসবিদরা ২০ ধরনের 'ট্র্যাজেডি' মুখোশ এবং ৪০টিরও বেশি 'কমেডি' মুখোশের ব্যবহার দেখেছেন। নিয়ম ছিল, নাটক মঞ্চায়নের সময়ে মুখোশগুলি তাদের মঞ্চ প্রবেশের ক্রমানুসারে মঞ্চের আড়ালে সাজানো থাকবে যাতে অভিনেতারা বুঝতে পারেন পরবর্তী কোন চরিত্রটি এসে দাঁড়াবে আলোয়।
ইওরোপিয় নাটকে মুখোশের জনপ্রিয়তা মধ্যযুগ জুড়ে অব্যাহত ছিল তার মূল কারণ 'মাউন্টব্যাঙ্কস' বা গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বেড়ানো ফেরিওয়ালারা। মুখোশ পরে, গল্প বলে বা নানারকম অভিনয়ের মাধ্যমে সম্ভাব্য ক্রেতার চিত্ত বিনোদন করে পণ্য বিক্রি করত এরা। এছাড়াও মুখোশ ব্যবহৃত হতো নাটকের অভিনয়ে। সন্তদের অলৌকিক জীবনচরিত এবং বাইবেলের ঘটনা নিয়ে নাটক তখন খুব জনপ্রিয় ছিল। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে মূকাভিনয় পরিচিতি লাভ করে। ফরাসি শব্দগ্রন্থি 'মামার’স প্লে' থেকে এর উদ্ভব যার অর্থ 'নির্বাক নাটক'! ক্রিসমাস মরসুমে এবং লেন্টের আগের কার্নিভাল মরসুম জুড়ে মুখোশধারীরা ঘরে ঘরে গিয়ে নাটক এবং প্যান্টোমাইম উপস্থাপন করত। তাদের মুখে থাকত মুখোশ অথবা রঙের মেকআপ।

বহু শতাব্দী ধরে জাপানে মুখোশের অস্তিত্ব রয়েছে। সামন্ত যোদ্ধারা লোহার তৈরি এবং পশুর চামড়ার আস্তরণ লাগানো হেলমেটের মতো মুখোশ 'কবুতো' পরতেন। জাপানি নাচের মুখোশ আজও তাদের নাটকে ব্যবহৃত হয়। 'গিগাকু' (প্রাচীন চিনা রাজ্য গোর-এর সঙ্গীত থেকে যে নামের উৎপত্তি) বিশ্বের প্রাচীনতম মুখোশের মধ্যে একটি। গিগাকু নাটক ৬১২ খ্রিস্টাব্দে চিন থেকে জাপানে আসে। 'নো' ( Noh) থিয়েটার জাপানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নৃত্যনাট্য যা ষোড়শ শতাব্দী থেকে বিদ্যমান। নো নাটকের অভিনেতার মুখোশ সাধারণত কয়েকশ বছর ধরে বংশানুক্রমে হস্তান্তরিত হয়। প্রতিটি মুখোশ শিল্প ও শিল্পীর এক অসামান্য কাজের স্বাক্ষর রাখে। পাঁচটি মৌলিক ধরনের মুখোশ তৈরি হয় — পুরুষ, মহিলা, বয়স্ক, দেবতা এবং দানব। একটি নো মাস্ক পরে নৃত্যের জন্য প্রস্তুত হতে বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় প্রয়োজন। মুখোশ হালকা হলেও যেহেতু তা সম্পূর্ণ মুখ ঢেকে রাখে এবং চোখের ছিদ্র খুব ছোট হয়, তাই দীর্ঘ অনুশীলন ছাড়া এই নাচ পরিবেশন কঠিন। নাচের জটিলতায় মনোনিবেশ করতে প্রয়োজন দুর্দান্ত শৃঙ্খলাবোধ।
আফ্রিকা এবং মধ্য আমেরিকার দেশগুলির সংস্কৃতির সঙ্গে মুখোশের সংযোগ গভীর। একটি লোককাহিনি থেকে, অনেকে ধারণা করেন পৃথিবীর প্রথম মুখোশ হয়তো তৈরি হয়েছিল মধ্য আফ্রিকার কঙ্গোতেই। কাহিনিটি এক ছোট্ট মেয়ের। সে প্রত্যেকদিন বায়না করে মায়ের সঙ্গে ঝরনার ধারে যাবে। বকাঝকা সার! সে মোটেই কথা শোনবার পাত্রী নয়। প্রত্যেকদিন সে পিছু নেয় মায়ের। অবশেষে, মা তাঁর বিশাল বপু জলের হাঁড়িতে আঁকেন একটি ভয়ঙ্কর মুখ আর তাই দেখে মেয়ে ভয় পেয়ে অনুসরণ করা বন্ধ করে। হতে পারে এ নেহাতই কল্পকাহিনি। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক মতে, আফ্রিকান উপজাতিদের মধ্যে মুখোশের প্রচলন এবং তার গঠন বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি। আফ্রিকান মুখোশ আকার, ডিজাইন এবং উপকরণের নিরিখে বৈচিত্র্যময়। কিছু মুখোশ ডিম্বাকৃতি, কিছু গোলাকার, কিছু হৃদয় আকৃতির, কিছু বর্গাকার। অনেকেই অলংকৃত রঙিন পুঁতি, শাঁস, চুল, ধাতু, চামড়া, কাপড় বা কাঁচ দিয়ে। আকারে বেশ কয়েক ফুট উঁচু কাঠামো থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রাকৃতি - যা দুল বা পোশাকের মতো পরিধান করা যায়। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে মাস্কের গঠন প্রকৃতি বদলে যায় আর তা হয়ে ওঠে একটি গ্রামের 'সিগনেচার'।

দুর্ভাগ্যবশত, এই শিল্পের অনেক কাজই হারিয়ে গেছে। ষোড়শ শতাব্দীতে যখন পর্তুগিজ, ডাচ এবং ইংরেজরা আফ্রিকা আক্রমণ করে, তখন অগণিত আফ্রিকাবাসীকে ধরে নিয়ে তারা বিদেশে পাঠায় দাসবৃত্তির জন্য। ফলত উপজাতিদের অনেক রীতি-রেওয়াজ ও মুখোশের মতো লোকজ শিল্প বিলুপ্ত হয়ে যায়। এর উপর ছিল ইওরোপিয় মিশনারিদের খ্রিস্টান ধর্মে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা। তাদের 'বিধর্মী' মুখোশ ব্যবহার থেকে নিরুৎসাহ করে সেগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। আসে শিল্প বিপ্লব। যে হাত একসময় তৈরি করত কারুকাজ শোভিত মুখোশ, সেই হাত মেশিন চালাবার কাজে ব্যবহৃত হতে থাকে। হারিয়ে যেতে বসে মুখোশ শিল্প।
মেসোআমেরিকা বা মধ্য আমেরিকা অঞ্চলে হাজার হাজার বছর ধরে, ওলমেক, জাপোটেক, মায়ান, টলটেক এবং অ্যাজটেক গোষ্ঠীদের বসবাস। সময়ের সঙ্গে বিকশিত হয়েছে এক বিরল সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং অসাধারণ স্থাপত্য শৈলী। ঐতিহাসিকরা বিশ্বাস করেন, এখানে যে মুখোশ দেখা যায় তা আসলে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে মধ্য আমেরিকা হয়ে উত্তর আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল বরাবর এবং পূর্বদিকে আটলান্টিক উপকূলে ছড়িয়ে পড়ে। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায়, একসময় মৃতদের মুখে মুখোশ পরানোর রীতি ছিল। ১৯৫২ সাল নাগাদ ৬০ ফুট মায়ান পিরামিডের মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিকরা যে রাজার মৃতদেহ আবিষ্কার করেন তার মুখে পরানো ছিল এক অপূর্ব মুখোশ, যার মধ্যে পাওয়া যায় আগ্নেয় শিলা থেকে উৎপন্ন অ্যালবাইট নামের বহু মূল্যবান এক ধরনের সাদা খনিজ। এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে মাস্ক ব্যবহারের চল ছিল। ইস্টারকে কেন্দ্র করে যে ব্রাজিল কার্নিভাল হয় সেখানে এখনও মুখোশের ব্যবহার দর্শনীয়।
গ্রামবাংলায় মূলত রামায়ণ, মহাভারত, পৌরাণিক অথবা একবারেই লোকায়ত বা গ্রামীণ চরিত্রদের আদলে তৈরি হয় মুখোশ। নানা চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত মুখোশ পরে মঞ্চে অভিনয় ও পুজো-পার্বণে নৃত্য পরিবেশিত হয়। যে কোনও অনুষ্ঠানে নৃত্য-অভিনয়ের সঙ্গে মুখোশের এক ধরনের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। এপার বাংলার পুরুলিয়া অঞ্চলে যেমন দেখা যায় ছৌ নাচের মুখোশ, তেমনই মালদা অঞ্চলে বহুল প্রচলিত গম্ভীরা নাচের মুখাবরণ। ওপার বাংলায় ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, কুমিল্লা, রাজশাহী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, যশোর, বগুড়া, রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলে আজও কিছু কিছু মুখোশের প্রচলন রয়েছে। যেমন, মুণ্ড মূর্তির মুখোশ, ওলাই চণ্ডীর মুখোশ, বড়াম চণ্ডীর মুখোশ, বড়খা গাজীর মুখোশ, ধর্ম ঠাকুরের মুখোশ, সত্য নারায়ণ সত্য পীরের মুখোশ, পীর গোরাচাঁদের মুখোশ, ওলা বিবির মুখোশ, ভৈরবের মুখোশ, ঘাটু দেবতার মুখোশ, মানিক পীরের মুখোশ ইত্যাদি।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সমাজ, জনজাতির কাছে মুখোশের আবরণ, এক ধরনের আভরণও বটে। নিজের মুখের উপরে এ যেন আরেকটি সত্ত্বার প্রতিস্থাপন। নিষ্প্রাণ হয়েও সে যেন বাঙ্ময়। অভিনেতার সঙ্গে চরিত্রের এক নিঃশব্দ, সুপ্ত বন্ধনে আবদ্ধ সে। কবি বিমল চন্দ্র ঘোষের কবিতায় যেন মেলে সেই সুপ্ত বন্ধনের সমর্থন-
“মুখোশেরা যাদুকর মুখ নেই তবু কথা বলে / হাত নেই সম্পদ বিশাল / যাদুমন্ত্রে ধরে রাখে,/
বিনাপায়ে হেঁটে যায় পায় যদি বাধামুক্ত পথ / জঠরে জটিল মনোরথ!”

এখন মুখোশের গুরুত্ব ক্রমহ্রাসমান। আর পাঁচটা বিনোদনের পাশে তার দীনহীন উপস্থিতি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুখোশচিত্র শিল্পকে একটি জাতির পূর্ণাঙ্গ লোকসংস্কৃতির মূল্যবান উপকরণ বলে চিহ্নিত করেছিলেন – কিন্তু সেই স্থান সে কতখানি ধরে রাখতে পেরেছে তা তর্ক সাপেক্ষ। সামাজিক বা ধর্মীয় সংস্কার অথবা বিনোদনের অঙ্গ হিসেবে নয়, অবনমিত হয়ে থেকে যাবে সে মিউজিয়াম গ্যালারি আর ড্রয়িং রুমের শোভাবর্ধনের অংশ হিসেবেই কেবল।
তথ্য ঋণ
১) Masks Around The World || Shaaron Cosner, Ann George
২) মুখোশ : অনন্য চিত্রকলা || হাসান মাহমুদ রিপন “যুগান্তর” অনলাইন , বাংলাদেশ
৩) Living Culture of Masks || SHILPA SEBASTIAN R
৪) Stories Behind the Mask || MADHUR TANKHA
৫) Blog on Majuli Raasyatra || PRABALIKA M. BORAH
৬) Ask Mask || Tamal Bhattacharya




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp