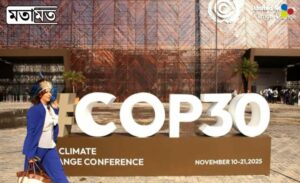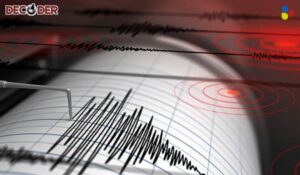সুন্দরবনের বর্ষা: ভেঙে যাওয়া গ্রাম ও হারানো চাষের উৎসবগুলি
Monsoon in Sundarban: গত দশবছরে বৃষ্টির ছবিটা পালটে গেছে। কালবৈশাখী নেই বললেই চলে। কাঁকড়িতলায় ধান ছিটিয়ে ধান বোনা এখন গল্পকথা। আমন মরশুমে ধান চাষ পিছিয়ে যাচ্ছে এক দেড়মাস কারণ, বৃষ্টি শুরুই হচ্ছে অনেক দেরিতে।
জলের দেশ, বৃষ্টির দেশ সুন্দরবন। দ্বীপে দ্বীপে বাঁধঘেরা গ্রাম। বাঁধের একদিকে নোনাজল আরেকদিকে মিষ্টিজলের পুকুর, খালবিল, হাওর। বৃষ্টি তো আকাশ থেকে নামে না, পৃথিবী থেকে ওঠে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নির্দেশে ও পরিকল্পনায় সুন্দরবন জরিপ করে সম্ভাব্য বার্ষিক দশ লক্ষ টাকা রাজস্বের হিসেব মাথায় রেখে শুরু হয়ে যায় জঙ্গল কেটে বসত ও চাষবাসের পরিকল্পনা। সেসময় আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যাদের জঙ্গল কাটার জন্য আনা হয়েছিল তারা এখানে বাঘের জঙ্গলে উঁচু গাছে বাসা বেঁধে থাকতেন। ধানী ঘাসের বীজকে ভাতের মতো সেদ্ধ করে খেতেন আর নদীর ধার থেকে তুলে আনতেন গিরিয়া শাক। এই শাক নোনাজলে জোয়ারের সময় ডুবে থাকে। রান্নায় আর আলাদা করে নুন লাগে না। এই শাক, ভাত আর প্রচুর মাছ কাঁকড়া ছিল খাবার। পানীয় জলের উৎস তেমন না থাকায় নোনাজলে তেঁতুল গুলেই অনেকসময় কাজ চালাতে হতো। রাতে মশাল জ্বলত। সারাদিন লাট কাটাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে চলত গ্রামগুলিকে বাঁধ দিয়ে ঘিরে ফেলার কাজ। দ্বীপের উঁচু জায়গায় কাছারিবাড়ি ও জমিদারের অন্যান্য কর্মচারীদের বসতবাড়ি, শস্যগোলা তৈরি হলো আর মাটি কেটে তৈরি হলো বড় বড় পুকুর, দিঘি, খালবিল। মিষ্টি বা পানীয় জল পাওয়া যেত বলে জায়গার নামই হয়ে গেল 'মিঠাপুকুর'। পুকুরের নামে অনেক জায়গার নাম আছে। উঁচু জায়গায় পুকুর কেটে চারপাশ ভালো করে বাঁধ দিয়ে ঘিরে দেওয়া হতে লাগল। এমন অগুনতি জলাশয়ের কিছু কিছুতে মানুষ যেমন মাছ চাষ শুরু করল, তেমনই কিছু জলাশয় ব্যবহৃত হতে লাগল পানীয় জলের উৎস হিসাবে।
সারাবছর ভালো বৃষ্টি হয় সুন্দরবনে, তাই এই জলাশয়গুলি ভরে উঠতে সময় লাগল না। বরং ভরে উপচে সব একাকার হয়ে যেতে লাগল বর্ষাকালে। এরকম জলাশয়গুলোকে ঘিরে নতুন জীববৈচিত্র্য সৃষ্টি হলো সুন্দরবনে। তবে বেশিরভাগ জলাশয়ের জল দো-আঁশলা, কেউ বলে "দুধে-নোনতা" মানে নোনা মিষ্টি মেশানো। এই জলে মাছ বাড়ে খুব ভালো। তখন বিক্রিবাটা নিয়ে এত ভাবনা মানুষের মনে আসেনি। এখন যেমন পান্তাভাতে আলুমাখা বা ভাজা খাওয়া হয়, তখন আলুর কোনও চল ছিল না। আলু বলতে পুঁজিবাদী বাজারে এই যে হলুদ খোসাযুক্ত আলু, যে আলুর চাষ কত মানুষকে ঘরছাড়া করেছে, কত কৃষকের ক্ষতি করেছে, সে ছিল না। তখন ছিল রাঙালু, খামালু এইসব। এখনও টিমটিম করে রাঙালু-খামালুর পাশে বাঁদরমুখী নীলকান্ত সহ কিছু আলুর জাত বীজ কোম্পানির আগ্রাসনের মুখে টিকে আছে। তবে পান্তার সঙ্গে নানারকম মাছের ভাজা, ঝাল, তেঁতুলের টক এইসব খাওয়া হতো। খাওয়া হতো চিতিকাঁকড়া, তেলুয়াকাঁকড়া, রাজকাঁকড়া মাখা; গরম গরম কাঁচালংকা পিঁয়াজ দিয়ে। বৃষ্টি ও জলাশয় ছাড়া গ্রামের ভেতরে এতরকমের মাছ, কাঁকড়া সুন্দরবনবাসী পেত না।

আরও পড়ুন- আজও বাঘের চোখে চোখ রেখে জঙ্গলে পা ফেলেন সুন্দরবনের ‘বাঘ বিধবা’-রা
বৃষ্টির কথা বলতে এসে এই কথাগুলো বলছি কারণ, পৃথিবীর জল বাষ্প হয়ে আকাশে ওঠে, আবার আকাশ থেকে নেমে জলাশয় ও মাটিকে পরিপুষ্ট করে। বর্ষাকালেই তো বজ্রপাতের মাধ্যমে মাটিতে বাঁধা পড়ে নাইট্রোজেন, গাছপালা সতেজ হয় ও দ্রুত বাড়তে থাকে খনিজ সমৃদ্ধ জলে। জলাশয়ও একইভাবে সমৃদ্ধ হয়। সমস্ত জায়গা ভরে ওঠে। মাছ-কাঁকড়া সবাই ডিম পাড়ে। সারা এলাকার খাদ্যশৃঙ্খল রসদ পায়। মানুষ ছাড়াও কতরকমের মাছরাঙার প্রজাতি আছে, পানকৌড়ি, ভোঁদড়, বাঘরোল, দাঁড়াশ, জলঢোঁড়া সাপ, কতরকমের বক আছে; তারা সবাই এই মাছ-কাঁকড়া খেয়ে জীবনধারণ করে। অগুনতি শাক, ঘাসের প্রজাতি ছেয়ে যায় চারিদিকে, যাদের ওপর নির্ভর করে থাকে গবাদি পশু, পাখি, প্রজাপতি, মৌমাছি সহ অসংখ্য প্রাণী। বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদেরা দ্রুত বেড়ে ওঠে অর্থাৎ বৃষ্টি শুধু মানুষের চাষবাস জীবিকা নয় একটা গোটা অঞ্চলের খাদ্যশৃঙ্খলে পেট ভরা খাবার ও পুষ্টি জোগাবার অন্যতম মূল উৎস যা না হলে সকলকেই হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে হতো।
বৃষ্টি বলতে মনে পড়ে, বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে ঝোড়ো হাওয়া চলবে। বৈশাখের শেষ সপ্তাহে শুরু হবে কালবৈশাখী। সেই কালবৈশাখী এখন লুপ্তপ্রায়। চোখে দেখার চেয়ে গানে-ছড়ায়-কবিতাতে কালবৈশাখীকে শোনা যায় বেশি। তাদের দেখা যায় না আর। এই কালবৈশাখীর জন্য অপেক্ষা থাকত। দাদুর মুখে শুনেছিলাম, একদিকে কালো মেঘ উঠছে আরেকদিকে কৃষক হাতে বীজ নিয়ে প্রস্তুত। বৃষ্টি পড়ে মাটি নরম হয়ে জো তৈরি হয়েছে বুঝলেই সরাসরি মাঠে ধানের বীজ ছিটিয়ে বীজ বোনার কাজ শুরু করতে হবে। এই হলো আমাদের ধানের 'কাঁকড়িতলা'। এই সময় মিস করা যাবে না। একটা মজার কথা আছে এই দোখনো সুন্দরবন অঞ্চলে:
"হাগতে বুসিকি চাষ গ্যালা"
মানে এখন যদি সঠিক সময়ে কাঁকড়িতলায় বীজ ছিটিয়ে না বোনা হয় তাহলে চাষে সমস্যা হয়ে যাবে, তাই এসময় হাগুমুতু করতে গেলেও যেন চাষের সময়টা হাতছাড়া হয়ে যায়!
এরপর জৈষ্ঠ্যের শেষদিক থেকে শুরু হবে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বর্ষাকালীন বৃ্ষ্টিপাত। আষাঢ় শ্রাবণ বর্ষাকাল। আষাঢ় মাসে অম্বুবাচী তিথি থেকে ধান চাষের কাজ শুরু হতো। এই হলো আমন মরশুম। দেশের সবচেয়ে বড় চাষের মরশুম। এইসময় সুন্দরবনে উঁচু মাঝারি নীচু জমিতে চাষ হতো দুধেরসর, চামরমণি, কনকচূড়, মালাবতী, মৌলে, হোগলা, হামাই, ঘিওস, কুমড়াগোড়, ট্যাংরা, তালমুগুর, নাঙলমুড়া, ভুঁড়িশাল, খেজুরছড়ি, মরিশাল, নোনাবগড়া এইরকম সব দেশি ধান। এখানে কোনও কোনও ধানের সঙ্গে নোনা শব্দটা পাওয়া যাবে কারণ এ তো নোনামিঠা জল-মাটি-বাতাসের দেশ, এখানকার কৃষকরা তাই নোনা-সহনশীল ধানের জাতও সঙ্গে রেখেছিলেন। এ তাদেরই আবিষ্কার। তার মধ্যে লুপ্তপ্রায় দু'টি জাত হলো- মাতলা ও হ্যামিল্টন। বলা বাহুল্য, এ ধানের নাম সেই হ্যামিল্টন সাহেবের নামে। গোসাবায় তাঁর সমবায়ভিত্তিক কাজকর্মে খুশি হয়ে চাষিরা একটা নোনাসহনশীল ধানের জাতের নাম রেখেছিলেন 'হ্যামিল্টন'।

আরও পড়ুন- মদ, গাঁজা, সিদ্ধিই ভোগ, সুন্দরবনের লোকদেবতাদের ঘিরে থাকা রহস্য আজও অবাক করে
আশ্বিন মাস থেকে ধান কাটা শুরু হতো। এখন সুন্দরবনে মে মাসে সাইক্লোন, সুপার সাইক্লোন, বন্যা হয়। সেসময় ঝড় হতো আশ্বিনে। আশ্বিনে ধান কাটা হচ্ছে শুনে অবাক লাগবে, কিন্তু আশ্বিনে যে দুর্গাপুজো। দুর্গাপুজোয় যিনি ব্রতী হবেন তাঁকে একটা ধান হয় চাষ করতে হবে নয়তো সে ধান যোগাড় করে আনতে হবে। ধানটির নাম 'দুর্গাভোগ'। কী অপূর্ব নাম! দুর্গার ভোগের নিমিত্ত যে ধান সেই তো দুর্গাভোগ। এই নতুন ধানেই তো সাজবে নবপত্রিকা। দুর্গাপুজোর নবপত্রিকায় ব্যবহৃত ধানের নাম তো আর "IR8", "IR36" বা ধরা যাক "JC78896aR" এরকম হতে পারে না। এখন অবশ্য দুর্গাভোগ ধানের চাষ এদিকে কোত্থাও নেই। গ্রামকে গ্রাম ঘুরে ইয়াস সাইক্লোন ও বন্যার ধ্বংসের মাঝে যখন হারিয়ে যাওয়া ধান আর ধানের গল্প খুঁজছি, তখন এই দুর্গাভোগ ধানের খবর প্রথম দিয়েছিলেন অশীতিপর এক কৃষক। কৃষক বললে আমরা লাঙল কাঁধে এক পুরুষের অবয়ব দেখি, অথচ কৃষিকাজের বেশিরভাগটাই করেন মেয়েরা। এই কথাটা আমি শুনেছিলাম তাই এক ঠাকুমার মুখে। বীজ সংরক্ষণের দায়িত্ব আজও তাঁরাই নিয়ে চলেছেন। এছাড়াও আশ্বিন মাসে কাটা হবে 'আশ্বিনেসরু', 'চূর্ণকাটি' ধান। এসব ছিল অসামান্য এক একটা দেশি ধান। উঁচু জমিতে সোনার ফসল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। পুরুলিয়া থেকে সুন্দরবন — কত প্রবীণ চাষির মুখে শুনেছি শুধু ভাত খেতেই কত সুন্দর হতো। মিলের পালিশ করা স্ফটিকস্বচ্ছ সরু চালের স্মৃতিহীন অজ্ঞ জিভের জগতে এসব কল্পকথা। মাস্টারমশাই দেবল দেব, যিনি সারাজীবন ধরে ১,৪৮০ জাতের দেশি ধান সংরক্ষণ করেছেন তাঁর কাছে জেনেছিলাম, সুন্দরবনে যে চূর্ণকাটি ধানচাষের কথা পিসিমার মুখে শুনেছি তা আসলে মানভূমের ধান। সুন্দরবনেও ভালো ফলত।

কার্তিকমাসে কাটা হবে কার্তিকশাল। নামেই তার কার্তিক। আর কাটা হবে ঘেঁচিপাটনাই বা কার্তিকপাটনাই। এসব ধান মাঠ থেকে হারিয়ে গেছে এক বিকট বিপ্লবের দরুণ। তার নাম 'সবুজ বিপ্লব'।
এই যে এতসব ধানের নাম, এত চাষের নাম, এসময় মাঠে কোনও ভারী যন্ত্র নেই, লাঙলে চাষ হতো, মাটির তলার পানীয় জল তুলে সর্বনাশ করে বোরো মরশুমে ধানচাষের কোনও ব্যাপারই ছিল না। চাষবাস যা হবে সব বর্ষার জলে, আর অন্য ঋতুতে হবে নানা জলাশয় থেকে জল নিয়ে।
তখন এত বাজ পড়ত না। বৃষ্টি হলে একেবারে মাঠঘাট ভরিয়ে হতো। আষাঢ়-শ্রাবণ পেরোলে ভাদ্রে হতো 'ছাগল তাড়ানো বৃষ্টি'। এই বৃষ্টি আবার এই রোদ। পৌষ-মাঘের শীত পেরিয়ে "ফাল্গুনে বিকশিত কাঞ্চন ফুল/ডালে ডালে পুঞ্জিত আম্রমুকুল"-এর সময়ে আবার কিছুটা বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি হতো।
গত দশবছরে বৃষ্টির ছবিটা পালটে গেছে। কালবৈশাখী নেই বললেই চলে। কাঁকড়িতলায় ধান ছিটিয়ে ধান বোনা এখন গল্পকথা। আমন মরশুমে ধান চাষ পিছিয়ে যাচ্ছে এক দেড়মাস কারণ, বৃষ্টি শুরুই হচ্ছে অনেক দেরিতে। অম্বুবাচী কেটে যাচ্ছে নির্জলা। ভাবা যায় না। এতে সমস্যা হলো, আমন মরশুমের চাষের শুরু দেরিতে হচ্ছে বলে ওদিকে পাকা ধান গোলায় উঠতেও দেরি হচ্ছে। প্রতিবছর মে মাসে বঙ্গোপসাগরে ক্রমশ সাইক্লোন, সুপার সাইক্লোন তৈরি হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। আয়লা, বুলবুল, ফণী, আম্ফান, ইয়াসের মতো বিধ্বংসী ঝড় বন্যায় তছনছ হয়ে যাচ্ছে উপকূলবর্তী সমস্ত গ্রাম ও চাষের জমি। মিষ্টি জলের জলাশয়ে ঢুকছে নোনাজল। হাজারে হাজারে ছেলেমেয়ে জীবিকা অর্জনের জন্য চলে যাচ্ছে অন্য রাজ্যে। হাতে সেই নোনাসহনশীল ধানের বীজও আর নেই যে বীজ বুনে ধান ফলাবে। কোম্পানির বীজ বেমালুম কেড়ে নিয়েছে নিজেদের দেশি ধানের গোষ্ঠীগত স্বত্ব ও স্মৃতি। যারা জমিকে চাষের জন্য তৈরি করতে পারে তাদের আর এক বিপদ হলো, কার্তিক-অঘ্রাণ মাসে ব্যাপক বৃষ্টি ও বছরের দ্বিতীয় সাইক্লোনের উপদ্রব। ২০২১ সালে ইয়াসের পরে এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগে মাঠের পর মাঠ ধান ডুবে পচে গিয়ে বহু চাষি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হন। পুঁজিবাদের বেপরোয়া আগ্রাসনে পরিবেশ দূষণ সবদিক দিয়ে এত বাড়ছে যে আমরা একটা 'হিট ট্র্যাপ'-এ বন্দি হয়ে আছি। সমুদ্র ঠান্ডা হওয়ার সুযোগই পাচ্ছে না। তার ফল ভুগছে সুন্দরবন সহ পৃথিবীর নানা উপকূল ও ব-দ্বীপ অঞ্চল।
আবার ধানের বীজ রোপণের সময় এত বৃষ্টি হচ্ছে যে বীজতলা পচে যাচ্ছে। এক একজন চাষির দুই তিনবার করে বীজতলা পচে গেছে। অতিরিক্ত গরম, অসময়ে অতিবৃষ্টি বা ধান পাকার সময়ে বৃষ্টির অভাবে ধানের ফলন মার খাচ্ছে। আগড়া বা অপুষ্ট ধান বেশি হচ্ছে ফলে চালের উৎপাদন কমছে। এক্ষেত্রে বাজারি হাইব্রিড ধানগুলো সবচেয়ে বেশি হতাশ করছে চাষিদের। তুলনায় দেশি ধানের বীজে ক্ষতির পরিমাণ কম কিন্তু দেশি ধানের বীজ আর কতটুকুই বা আছে? বেশিরভাগ চাষিই তো কোম্পানির বীজ কিনে চাষাবাদ করেন। বিক্রি পরের কথা। সারাবছর নিজেদের সংসারের খোরাকি জুটবে তো? কৃষকসভায় এখন এই চিন্তা দেখা যায়৷ এবারের গরম আশ্চর্যভাবে শুষ্ক গরম। এর প্রভাব পড়েছে তাল নারকেল গাছে। অতিরিক্ত শুকনো গরমে নারকেলের মঞ্জরী শুকিয়ে গেছে। ফলত ফলন দাঁড়াচ্ছে অর্ধেকেরও কম। আবার মনে পড়ে তরমুজ পেকে যাওয়ার সময় অতিবৃষ্টিতে চাষীর প্রভূত ক্ষতির কথা। সুন্দরবনের বিখ্যাত তরমুজ চাষ উঠে যাওয়ার একটা কারণ এটাও।
চারিদিকে নোনাজলের মধ্যে এই মিষ্টি জলের জলাশয়গুলোই সুন্দরবনের সবচেয়ে বড় বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জায়গা কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত অতিরিক্ত কীটনাশক, ভেনামি চিংড়ি ও পোলট্রির দুর্গন্ধ মুরগি চাষে ব্যবহৃত নানা হরমোন, ওষুধ ইত্যাদি মিলে জল নষ্ট করে চলেছে দিনের পর দিন। মানুষ শুধু রোজগার করবে। নিজের আয়ুর বিনিময়ে পাগলের মতো রোজগারের চিন্তা করবে। এরকম কেন হচ্ছে তা অন্যত্র কোথাও আলোচনা করা যাবে।
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এখানে এসে জল, জঙ্গল, জমি সম্পর্কে মানুষের ধারণা ও সম্পর্ক একেবারে বদলে দিয়েছে। হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার, কার্টোগ্রাফার, উকিল, এপিডেমিওলজিস্ট এবং প্রশাসকদের সঙ্গে নিয়ে তারা সমস্ত নিচু জলা জংলা জায়গাকে 'ওয়েস্টল্যান্ড', 'ম্যাল এরিয়া' আখ্যা দিয়ে প্রোমোটারের কাজ শিখিয়ে গেছে। কীভাবে এইসব জায়গার সব গাছগাছালি কেটে, জল শুকিয়ে মাটি ভরাট করে সেই জমিকে জমিব্যবসার অন্তর্ভুক্ত করে বিপুল টাকায় কেনাবেচা করা যায় এই পদ্ধতি তারা দেখিয়ে গেছে। এইভাবেই পুঁজি সঞ্চয় ও মুনাফার জন্য গ্রাম ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করে শহর গড়ে ওঠে। কলকাতাও আজ যা, তা তার আসল পরিচয় নয়। সুন্দরবনও এখন কলকাতার পথে। সুন্দরবন সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাকার উৎপলেন্দু মণ্ডলের কথায়, "সারা পৃথিবীটা কোলকাতা হয়ে গেলো"।
শহরকে দেখি পুঁজিবাদের এজেন্সি হিসাবে। নানারকম এজেন্সি নিয়ে সে বসে থাকে। সে তার এজেন্সি ও প্রোপাগান্ডা দিয়ে দখল করে পাহাড়, মালভূমি, উপত্যকা, উপকূল, নদী, মহাসাগর, মানুষ সব কিছু। দক্ষিণবঙ্গে কালবৈশাখী কমে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ঝাড়খণ্ডে নির্বিচারে প্রকৃতির উপর পুঁজিপতিদের হস্তক্ষেপ।
এদিকে সুন্দরবনেও বেশ কয়েক দশক হলো জলাশয় ভরাট করে ঘরবাড়ি কারখানা বা কোনও প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজ চলছে। এতে এক একটা গ্রামের নানা জলাশয়ের যে আন্তঃসম্পর্ক তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এর প্রভাব সরাসরি পড়ছে মাছ-কাঁকড়ার প্রজননে। একদিকে কীটনাশক সহ নানারকম জলদূষণ আরেকদিকে জলাশয় দখল হয়ে যাওয়া, বৃষ্টির জল যদি সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে না পারে, যদি নিরাপদ না থাকে তবে এরা বাঁচবে আর কীভাবে, আর এরা না বাঁচলে গোটা খাদ্যশৃঙ্খলেই দেখা দেবে সমস্যা বা ভারসাম্যহীনতা।

আরও পড়ুন- রয়েল বেঙ্গল নয়, সুন্দরবনের এই প্রাণীটির ওপরেই এখন নজর পশুপ্রেমীদের
বৃষ্টি, জল, জলাশয়, জীববৈচিত্র্য, জলীয় রাজনীতি ও এসব কিছুর ইতিহাসকে আলাদা করে দেখা অসম্ভব। জল সংরক্ষণের নানারকম পদ্ধতি আবার অনুসরণ করতে হবে। বোরো মরশুমের ধান বাদ দিয়ে জোর দিতে হবে আউশ ও আমন মরশুমে। কীটনাশকের ব্যবহার একেবারে বন্ধ করতে হবে। এমন দেশি জাতের ধান বাছতে হবে যারা দুইটি ঝড়ের মাঝে (মে বা নভেম্বর) নিরাপদে হতে ও গোলায় উঠে যেতে পারে। ধান বা সবজির বীজতলা করতে হবে মাটি থেকে উঁচু করে বীজবিছানা বানিয়ে, যাতে বীজতলা অধিক বা কম বর্ষায় সহজে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।
বহুকাল হলো পাড়ায় পাড়ায় নলকূপ, অনেক ঘরে ব্যক্তিগত পাম্প ইত্যাদি আসার সঙ্গে সঙ্গে পুকুর ও অন্যান্য জলাশয়ের আদর যত্ন, সম্মান অনেক কমে গেছে। এর মাশুল অবশ্য মানুষকে গুনতে হয় শারীরিক অসুখ, আর্থিক ক্ষতি দিয়ে। সুন্দরবনে শুধু রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবোস, পুঁটি, মৌরলা, ফলুই, শোল, ল্যাঠা, চ্যাঙ মাগুর, শাল তো হয় না। সুন্দরবন তো ভেটকি, দাঁতন, ভাঙন, সেলে, বেলে, পার্শে সহ নানা নোনা মাছেরও দেশ। এইসব জলাশয় বা ভেড়ি, খাল সংস্কারে উৎসাহ দিতে হবে। কাজ করতে করতে মনে হয়, একটু হলেও আবার এসব ভেড়ি খালের প্রতি মানুষের উৎসাহ বেড়েছে। গত চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরে অনেক কিছুই ভুল ও অন্যায় হয়েছে আন্দাজ করে অনেকে ফেরার চেষ্টা করছে। কাজটা সহজ না হলেও অসম্ভব নয়।
বর্ষাকে কীভাবে আবার ফিরিয়ে আনা যায় তা এখনও ঠিক জানা নেই কিন্তু একথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সমুদ্র, নদী, জঙ্গল আর গ্রামের মাটি, বাতাস এরা কেউ আর শুদ্ধ নেই, ভালো নেই। পুঁজিবাদের আগ্রাসন এসব কিছুকে পুঁজিবৃদ্ধির লোভে দূষিত করে ফেলেছে। অথচ এরা সকলে মিলে মেঘ বৃষ্টিকে তৈরি করে, বহন করে। এদের কথা বুঝতে হবে, বলতে হবে। বৃষ্টি যখন যেমন হচ্ছে তাকে সেভাবেই যতটা সম্ভব জলাধারে সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। চাষের পদ্ধতি বদলাতে হবে। বিভিন্নরকমের দেশি বীজ হাতে রাখতে হবে। বন্ধ করতে হবে ভারী যন্ত্রপাতির ব্যবহার। এসবই সম্ভব যদি মানুষ অনুভব করে তার গোষ্ঠী আছে, সে একা নয়। যদি বুঝতে পারে মানুষ একা নয়, আরও লক্ষ কোটি প্রাণ পৃথিবীতে আছে।
অনেক বিষয়ই ছুঁয়ে যাওয়া হলো না এই আলোচ্য পরিসরে, তবু কথা উঠুক। চিন্তার উদ্রেক হোক। কাজ হোক। বৃষ্টি আসুক। ফিরে আসুক ভেঙে যাওয়া গ্রামে বৃষ্টি ও চাষের সব উৎসব যারা আজ কেবল বইতে মুখ লুকিয়েছে। বর্ষা মঙ্গল করুক। ফিরে আসুক বৃষ্টির গান।




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp