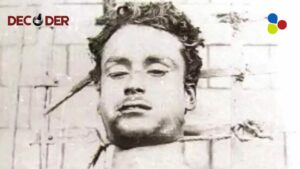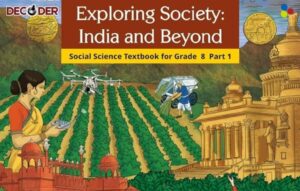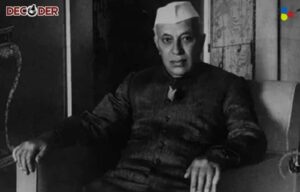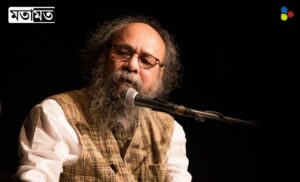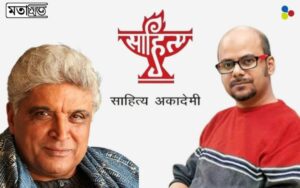গোয়েথালস গ্রন্থাগার: শান্ত দ্বিপ্রহর, হারানো সময় এবং গ্রন্থের সঙ্গে সংলাপ
St. Xavier's Goethals Library: দীর্ঘদিন ধরে ধর্মতত্ত্ব, সমাজবিদ্যা, আদিবাসী জীবন, ভারততত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের নানা গ্রন্থ সযত্নে সংগ্রহ এবং সন্নিবেশ করা হয়েছে এখানে।
১
বড় বড় কাঠের টেবিল। সেই টেবিলে বসে লক্ষ্য করি গ্রন্থাগারের বইপত্র, চেয়ার, প্রদর্শনী, দেওয়াল এবং অনেকগুলি আলমারি। এক একটা আলমারিতে এক এক রকম বই। দেখে তাক্ লেগে যায়। এত বছর ধরে এত বইপত্র, বাঁধানো পত্রিকা, এমনকী নথি-দলিল-দস্তাবেজ সযত্নে রক্ষিত রয়েছে। পড়াশুনোর এমন নিঃশব্দ পরিসর খুব একটা মেলে না। সমস্ত পড়ুয়া এবং বিশেষত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের উদ্দেশ্যে জানাতে চাই যে, তত্ত্বাবধায়ক বা প্রিন্সিপাল কিংবা প্রতিষ্ঠানের মুখ্য আধিকারিকের সূচক পত্র সঙ্গে থাকলেই এই আশ্চর্য গ্রন্থালয়ে প্রবেশ করা যায়। আমার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং প্রাবন্ধিক রাজীব চৌধুরী। আমাকে কেউ তেমন ভাবে চেনে না, আমার কোনও গবেষণাই কস্মিনকালে নেই, ফলে ‘তত্ত্বাবধায়ক’ শব্দটাই অবান্তর, তার ওপর পণ্ডিতদের দেখলেই আমার মনে পড়ে সেই বিখ্যাত প্রবাদ ‘যঃ পলায়তি সঃ জীবতি’।
আলমারি এবং বইপত্রের কথায় পরে আসছি। আমার সবথেকে আকর্ষণীয় মনে হয় লাইব্রেরিতে নানা ধর্ম এবং সংস্কৃতির সহাবস্থান। আগেই বলেছি, লাইব্রেরির চার কোণে আছে চারটি বুদ্ধমূর্তি। কোনওটি সাদা মার্বেলের, কোনওটি কালো মার্বেলের। একটি কালো, সুদৃশ্য, নকশাদার সেগুন কাঠের টেবিলে কাঁচের মধ্যে রাখা রয়েছে পাথরের তৈরি তাজমহল! দরজার কাছেই কাঁচের বাক্সে রাখা আছে ভারতীয় সংবিধানের সেই সুচিত্রিত মূল গ্রন্থটি, যার পাতায়-পাতায় অলংকরণ করে দিয়েছিলেন শিল্পী নন্দলাল বসু। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বরের সেই অবিস্মরণীয় ঘোষণাপত্র। ‘In our constituent Assembly this twenty sixth day of November, 1949, do Hereby Adopt, Enact and Give to ourselves this Constitutions’. গায়ে রোমাঞ্চ হলো। সামনে গিয়ে উল্টো দিকের দেওয়ালের ছবিটি দেখে তাজ্জব বনে গেলাম। সেখানে রাজপুত মিনিয়েচার পেইন্টিংয়ে রয়েছে বালক কৃষ্ণের বাল্যলীলার একটি চমৎকার ছবি। শুধু প্রাচীন বা মধ্যযুগই নয়, হঠাৎ দেখলাম একটি দেওয়ালে ঝুলছে যামিনী রায়ের ছবি। মা ও শিশুর সেই গাঢ় নীল এবং মাটি রঙে চিত্রিত ছবিটির নীচে অবশ্য ছবির প্রাপ্তিতথ্য খুব কিছু স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। যদিও ভারতীয় সংবিধানের ক্ষেত্রে, একটি ফলকে লেখা আছে, ‘THE ORIGINAL CONSTITUTION OF INDIA’-র এই বিশেষ সংস্করণটি গোয়েথালস লাইব্রেরিতে উপহার দেওয়া হয়েছে ২০২৩ সালের ৭ জুলাই, স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে। উপহারটি পাঠিয়েছে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক। একপাশের দেওয়ালে কয়েকটি কাঠের চৌকোণাকার পাটাতন। দেয়ালে ঝুলন্ত। তার ওপর বহু পুরনো অস্ত্রশস্ত্র। একেবারে সাবেক আমলের। কিছু ধারালো হাতিয়ার। যেমন তরোয়াল, ছুরি, কুক্রি বা ভোজালি। কিছু পুরনো আমলের আগ্নেয়াস্ত্র। পিস্তল গোছের। কয়েকটি স্প্রিং লাগানো ছুঁড়ে মারার অস্ত্রও আছে। এগুলি কবেকার বা ইতিহাস কী, কেউ বলতে পারেননি।
আরও পড়ুন-সাঁ সুসি থিয়েটার এবং আরেকটা কলকাতা
২
একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, এটি শুধু গ্রন্থাগারই নয়, নানা ধরনের শিল্পসামগ্রীর একটি সংরক্ষণাগারও বটে। পাশের ঘরে বড় বড় পানপাত্র বা শিল্পসামগ্রী প্যাকেটের মধ্যে রাখা আছে, জানি না, হয়তো আগামী দিনে এগুলি প্রদর্শন করা হবে। এই প্রসঙ্গে বলতে হয় নানা পাণ্ডুলিপির কথাও। আগেই বলেছি, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের কিছু পাণ্ডুলিপি এই গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। এছাড়াও বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য পুস্তক এবং জীর্ণ, প্রভূত পুরাকালের পাণ্ডুলিপিও গ্রন্থালয়ে রক্ষিত আছে। আলমারির মধ্যে পাণ্ডুলিপির বাক্স বা পেটিকা কাঁচের বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে, তার সঙ্গের বিজ্ঞপ্তি – ‘Palm leaf manuscript’। কোনওটিতে কাপড়ে মোড়া ‘Ancient manuscript’। জানি না, এগুলির মধ্যে ঠিক কোন পুঁথি সংরক্ষিত আছে। এই গ্রন্থাগার মূলত যে কালপর্ব তার রক্ষণাবেক্ষণের অভ্যন্তরে সযত্নে রেখেছে, সেটি হলো আঠারো বা উনিশ শতকের নানা সামগ্রী। প্রকৃতপক্ষে বলা চলে ঔপনিবেশিক আমলের নানা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, দলিল-দস্তাবেজ, ছবি এবং পাশ্চাত্যের চোখে ভারত, কলকাতা এবং পূর্ব ভারতের নানা বিবরণ, নথিপত্র এখানে সংরক্ষিত আছে। লাইব্রেরিটির একটি নিজস্ব ‘ক্যাটালগ’ আছে। সেখানে বলা আছে, দীর্ঘদিন ধরে ধর্মতত্ত্ব, সমাজবিদ্যা, আদিবাসী জীবন, ভারততত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের নানা গ্রন্থ সযত্নে সংগ্রহ এবং সন্নিবেশ করা হয়েছে এখানে। সেইসব গবেষক, পড়ুয়া এবং সারস্বত বিদ্বজ্জনের নাম তালিকায় দেখলাম, ফাদার রবের আঁতোয়ান এবং ফাদার পি. ফালোঁ-র নাম জ্বলজ্বল করছে। এই সুযোগে একটা কথা বলে নেওয়া ভালো। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি বুদ্ধদেব বসুর নেতৃত্বে এবং উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল ‘তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ’। সেই সাহিত্যবিভাগে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সাহিত্য-দর্শন এবং কাব্যতত্ত্ব বিষয়ে সুপণ্ডিত এক ঝাঁক মেধাজীবী শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন, ফাদার আঁতোয়ান এবং ফাদার ফালোঁ। এই ‘ক্যাটালগ’ থেকে জানা যাচ্ছে, পাঁচটি আলাদা আলাদা খণ্ডে এবং বিন্যাসে এই গ্রন্থাগারে আছে ‘Daniel’s Oriental Scenary’। এছাড়াও, James. B. Franses এর ‘Franses’s view of Calcutta’. William wood-এর ‘Panoramic view of Calcutta’ প্রভৃতি। এসমস্ত রঙিন চিত্রকলাগুলি মোটামুটিভাবে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ১৮৩৩, ১৮২৬ এমন সব সময়ে অঙ্কিত। কলকাতার প্রাচীন ইতিহাস, বিশেষত ঔপনিবেশিক পর্বে শহরের নির্মাণ এবং ক্রমবিকাশ নিয়ে যারা অনুসন্ধান এবং গবেষণা করছেন, তাঁদের কাছে এই গ্রন্থাগারটি একটি সোনার খনির মতো।
আরও পড়ুন-সুরা-মাংস-কবরখানার পথ! যেভাবে বদলে যাচ্ছে পার্কস্ট্রিটের সড়ক বাস্তবতা
৩
কয়েকদিন আগে আমি গিয়েছিলাম, দার্জিলিং শহরের সন্নিকটে ‘ঘুম মনাস্টেরি’-তে। এই মনাস্টেরির মধ্যে একটি মিউজিয়ম তথা প্রদর্শনশালা রয়েছে। সেটির নাম ‘DRUK PADMA KARPO MUSEUM’। ঘুম রেলস্টেশন থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত। দোতলায় এক বিশাল বারান্দা। চতুর্দিকে পুণ্য পতাকা। সেই ধ্বজা বা নিশানগুলি নানা রঙের। রয়েছে বুদ্ধের একটি বিশাল মূর্তিও। সেই চত্ত্বর বা বারান্দায় আমি যখন উঠেছিলাম, হঠাৎ বিপুল বাতাসের লণ্ডভণ্ড চলাচল শুরু হলো। এতই তার গতিবেগ আর ঝোড়ো দাপট, যে দাঁড়িয়ে থাকাই কঠিন হয়ে পড়েছিল। এ হলো স্থাপত্যের এক অত্যাশ্চর্য নমুনা। কেননা একতলায়, কিংবা রাস্তায়, এমনকী পাশের পাহাড়ে ঝড়ের এই দামালপনা নেই! প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সেই মিউজিয়ামের প্রধান সমস্যা ছিল ভাষা বা বিজ্ঞপ্তিগুলি সবই তিব্বতি ভাষায় লিখিত। প্রাচীন বিভিন্ন পবিত্র বস্তু, পুঁথির পাতা, বহু শতক প্রাচীন প্রাচীন ধর্মগুরুদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র, পুরনো জনপদের নানা অলংকার, টুপি, বাসন সবই রাখা আছে, কিন্তু ঠিক টীকাভাষ্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আন্দাজে হাতড়ে-হাতড়ে একটু আধটু বুঝছি মাত্র। এই মিউজিয়ামের বাইরে টিকিট কাউন্টারে সমস্যার কথা জানালাম। তাঁরা বললেন, চেষ্টা চালাচ্ছেন, তবে বহু বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্ম দর্শনের শব্দ, ব্যবহার বা অভিজ্ঞতা, এমনকী বস্তু, পরিভাষা বা অনুভব প্রকাশের উপযুক্ত শব্দ তাঁরা হিন্দি, বাংলা বা ইংরেজিতে খুঁজে পাচ্ছেন না। ফলে, দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাঁরা নিরুপায়। খুব সতর্ক হয়ে এগোচ্ছেন। আমি বলতে চাইছি, যে কোনও গ্রন্থাগার বা সংরক্ষণাগারের এ এক নিজস্ব সমস্যা। তাঁদের বস্তুরাজি বা জনপদের ভাষা এক আর সেই মিউজিয়ামে দর্শনার্থী বা গবেষকদের ভাষা বা সংস্কৃতি আলাদা। গোয়েথালস গ্রন্থাগারে এই সমস্যা নেই। সেখানে প্রধানত ইংরেজিতেই সব বিজ্ঞপ্তি লেখা আছে। যদিও এই গ্রন্থাগারে সংস্কৃত, হিন্দি, এমনকী বাংলা বইও অঢেল! বহু যুগ ধরে তারা যেন কাঁচের আড়াল থেকে নজরে পড়ার জন্য হাত নাড়াচ্ছে! বাঙালি মূলত দ্বিভাষিক হওয়ায় (ইদানীং অবশ্য উল্টো একটা প্রবণতা বেশ জোরালো! ‘আই কান্ট রিড বাংলা’ – সদম্ভে জানাচ্ছে আদ্যন্ত বাঙালি কলকাত্তাইয়া খুদেরা। বুক কেঁপে ওঠে! একভাষিক বাঙালি প্রজন্ম কি তবে দূরে নয়? বাংলা বইয়ের ইংরেজি তর্জমা হবে সব? আশা করি, ততদিন বাঁচব না।)
যেমন ধরুন, গোয়েথালস লাইব্রেরির একটি আলমারির গায়ে জানানো হয়েছে, এই অংশে সাধারণভাবে ধর্ম এবং ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থরাজি আছে। আছে ধর্মতত্ত্বের তুলনামূলক বিচার সংক্রান্ত বইপত্র। ম্যাক্সমুলার প্রমুখের গ্রন্থ যেমন আছে, বৈদিক এবং অন্যান্য ভারতীয় নানা ধর্ম এমনকী তান্ত্রিক, আগম, পুরাণভিত্তিক গোষ্ঠীর ধর্মাচরণের বিষয়েও বইপত্র আছে। পুরো গ্রন্থাগার এইভাবে বিষয়, প্রসঙ্গ এবং ভাবমূল বা থিম অনুযায়ী সজ্জিত আছে।
আরও পড়ুন- জেভিয়ার্সের অন্দরে লুকিয়ে গোয়েথালসের নিজস্ব রত্নকক্ষ
৪
আলমারির বইপত্র দেখতে দেখতে কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ চোখে পড়ল, যা, আমি নিশ্চিত, ঔপনিবেশিক বাংলা এবং ঔপনিবেশিক ভারতের বহু সাম্প্রতিক গবেষণার রসদ জোগান হতে পারে। যেমন ধরা যাক, বার্ণিয়ের রচিত ‘ট্র্যাভেলস ইন দ্য মোগল এম্পায়ার’। তারপর একটি শেষ গ্রন্থ যার নাম ‘The Art of Indian Asia’. খুবই গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক গবেষণার ক্ষেত্রে ‘History of cholera in India’. অথবা ১৮৯৯ সালের মাসিক ক্যাথলিক জার্নাল ‘সোফিয়া’। দু'টি বইয়ের কথা বলে আপাতত প্রসঙ্গ পালটাব। একটির নাম ‘Notes on the Zoology of the W.P. India’ এবং অন্যটি ‘The Butterflies of India Burmah & Ceyton’।
হাঁটতে হাঁটতে অবাক বিস্ময়ে ঘরের শেষ প্রান্তে পৌঁছলাম। বাক্সের মধ্যে কাঁচের তলায় সযত্নে সাজানো আছে প্রচুর পুরনো গ্রন্থ। তার এক একটি পৃষ্ঠা দেখলেই মন ভরে যায়। সেসময়ের মুদ্রণ, এমনকী ছবির ধূসর অথচ শিল্পিত রেখাকৃতগুলি চোখ টেনে নেয়। কোনওটি ছাপা হয়েছে ১৮০০ সালে, কোনওটি ছাপা হয়েছে ১৯৭৪ সালে!
গ্রন্থাগার থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছলাম দ্রুতগামী, নিয়ন আলোর পার্ক স্ট্রিটে। মনে হল, এ আবার কোন শহর? এতক্ষণের আঠার-উনিশ শতক তখনও চোখে লেগে আছে। একেই হয়তো বলে ‘টাইম ট্র্যাভেল’। মোদ্দা কথা হল, জ্ঞানচর্চার এই উনিশ শতকী মেজাজ আমার বুকের মধ্যে বাসা বেঁধে ফেলেছে। মায়া যেন ভোলা যাচ্ছে না।



 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp