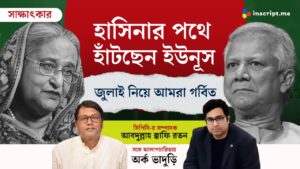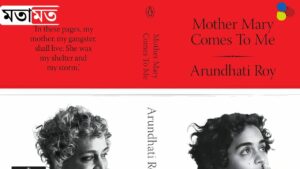থিয়েটারের অঞ্জন : বার্লিন, ব্রেখট আর মৃণাল সেন
Anjan Dutt Interview; জার্মানিতে পুব-পশ্চিম মিলিয়ে অজস্র থিয়েটার দেখে প্রথমেই আমার যেটা মনে হয়েছিল— ওইর’ম স্কেলে ওইভাবে আমরা ভাবতে পারি না। থিয়েটারে এত খরচা হচ্ছে!
অঞ্জন দত্তের থিয়েটার নিয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারিতা করেছেন অভিজিৎ বসু৷ এই দীর্ঘ কথোপকথন ঠিক সাক্ষাৎকার নয়, বরং হয়ে উঠেছে অঞ্জনের থিয়েটারের দর্শন, রাজনীতি, শিল্পভাবনা এবং জীবনের টুকরো টুকরো নানা রঙের মিশেলে একটি দুর্দান্ত আড্ডা। রইল দ্বিতীয় পর্ব। অনুলিখনে সৌরভ সেন।
অভিজিৎ বসু : সার্ত্রের পরেই কি পেটার ওয়াইস করলেন?
অঞ্জন দত্ত : সার্ত্রের নাটকের খবর পৌঁছল আলিয়ঁস ফ্রঁসেজে। ওরা তখন অনেক কিছু কাজটাজ করত। ম্যাক্স মুলার ভবনও অনেক কিছুতে জড়িত থাকত। আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ আমায় ডেকে পাঠিয়ে ওদের সঙ্গে কাজ করার প্রস্তাব দিল। কিছুটা খরচাও দেবে ওরা। ঠিক করলাম জাঁ জেনে-র নাটক করব। ওরা একটু দ্বিধায় ছিল যে জাঁ জেনের নাটক দর্শক টানবে কিনা।
ফের আমার মধ্যেকার সেই ডিরেক্টরটা থিয়েটার করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এটা হলো কলামন্দির বেসমেন্টে। দু-তিনটে শোয়েই লোকজন এমন চিৎকার-চেঁচামেচি আরম্ভ করে দিল যে আর হলো না। কিন্তু কলকাতায় যে জাঁ জেনে হচ্ছে, বিকল্প ভাবনার মানুষজন ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন। এবার ম্যাক্স মুলারের লোকজন আমাকে জার্মান নাটক করার জন্য বললেন। জার্মান নাটক কোনটা করা যায়, হাতড়াচ্ছি। ম্যাক্স মুলারের ডিরেক্টর রোলান্ড শাফনার আমাকে পেটার ওয়াইসের একটা নাটক পড়তে দিলেন : The Persecution and Assassination of Jean-Paul Marat as Performed by the Inmates of the Asylum of Charenton Under the Direction of the Marquis de Sade; ইয়া লম্বা একটা নাম, ছোট করে ‘মারা/সাদ’ (Marat/Sade)। এটা মিউজিকাল, বহুস্তরীয় এবং বাস্তবতায় মোড়া। পড়ে তো মাথা খারাপ হয়ে গেল! ঠিক করলাম, করবই। প্রযোজনার অর্থ ওরা দিল। ১৯৮০-তে আমরা করলাম। আকাডেমিতে ফার্স্ট শো করতে গিয়ে তো ‘অশ্লীল, অশ্লীল’ বলে বন্ধ করে দিল। তাহলে কি কোনও হল্ পাওয়া যাবে না! শাফনার সাহস জুগিয়ে কোনও মুক্তমঞ্চে করার পরামর্শ দিলেন। বললেন— তাহলে আমরা এমন একটা জায়গা খুঁজি যেখানে কোনও অথরিটি নেই, যা চাইব আমাদের করতে দেবে।
পড়ুন প্রথম পর্ব- থিয়েটারের অঞ্জন : বাদল সরকারই আমার থিয়েটারের শিক্ষক
রডন স্ট্রিটে একটা পুরনো ওষুধের কারখানা পড়েছিল। সেটা ভাড়া করা হলো। তেরপল-টেরপল দিয়ে ঠিকঠাক করে মাটিতে কাঠের একটা সিটিং এরিয়া করা হলো, এরিনা-র মতো, যেখানে দর্শক বসবে। ছিল সাদাটে আলো। ছিল ব্যান্ড, ছিল গান।
মারা আর সাদ। আমার দলেরই একটা ছেলে, ভালো অভিনয় করছিল, সে সাদ করল। ঠিক করলাম মারা-র চরিত্র আমিই করব। প্রথম নাটক ‘স্বীকারোক্তি’-তে আমি অভিনয় করিনি, একটুখানি ঢুকে বেরিয়ে আসার ছিল, সেটা করেছিলাম। জাঁ জেনের সময়েও আমি করিনি খুব একটা। একটা গার্ড, মাঝে-মাঝে দূর থেকে আসে। ওই গার্ডটা আমি করতাম। এ-ই প্রথম কোনও বড় রোল নিয়ে আমি নামলাম, আমার তৃতীয় নাটকে, জাঁ-পল মারা-র চরিত্রে।
এই নাটকটি বাদলবাবু দেখতে এসেছিলেন। শুনেছিলাম, ওঁর নাকি ভালো লেগেছিল। অনেকেই দেখতে এল। মৃণাল সেন দেখতে এলেন এবং আমাকে না-জানি কেন পছন্দও করলেন। বললেন— চলো, একটা ফিল্ম করা যাক!
এ-ই আমি সিনেমাতে গেলাম।

অভিজিৎ : একজন অভিনেতা, নির্দেশক বা শিল্পী হিসেবে আপনার জীবনে সবথেকে ইম্পর্ট্যান্ট দু'জন মানুষ মৃণাল সেন এবং বাদল সরকার, একথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি।
অঞ্জন : যদি নাগালের মধ্যে থাকা মানুষ হন, তাহলে মৃণাল সেন, বাদল সরকার। আর ভাবনাগত জায়গা থেকে অবশ্যই আমার ওপর প্রভাব ফেলেছেন বব ডিলান, লি স্ট্র্যাসবার্গ, পিটার ব্রুক।
আরও পড়ুন- ‘মৃণাল সেনের চোখে দেখেছি আমার শহর’: কথাবার্তায় অঞ্জন দত্ত
অভিজিৎ : হাত বাড়ালেই এই দু'জনকে পেয়েছেন। এঁদের মধ্যে মৃণাল সেন যতদিন বেঁচেছিলেন, স্নেহভাজন আপনাকে পুত্রসম, বন্ধুসম চিরকাল ভালোবেসেছেন। অথচ বাদলবাবুর সঙ্গে এত ভালো একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক হওয়া সত্ত্বেও কোথায় যেন থমকে গেল সম্পর্কটা! একটু বলুন, যদি অসুবিধে না হয়।
অঞ্জন : অন্যদের মুখে শুনেছি, তিনি আমার সম্পর্কে একটু হতাশ ছিলেন। এক্ষেত্রে আমারও দোষ আছে। যাঁর কাছ থেকে এতকিছু শিখলাম, তাঁর দলে ঢুকলাম না। তাঁর থার্ড থিয়েটারের অংশ হলাম না। তবে ভেতরে-ভেতরে আমি সবসময় বাদলদাকে অন্তর থেকে ভালোবেসে এসেছি, বলতে পারিনি। বাদলদাও হয়তো আমাকে ভালোবাসতেন।
বাদলদা শেষজীবনে ওঁর কাছাকাছি থাকা একজনকে বলেছিলেন— অঞ্জন তো সিনেমা করে, অঞ্জন তো গান করে, অঞ্জন কেন সিনেমাতে গেল! সে বলেছে, ওকে তো রোজগার করতে হবে। তখন তিনি বলেছেন— হ্যাঁ, ও তো পড়াতে পারত, অনেক কিছু করতে পারত, ওর অনেক ক্ষমতা আছে, অন্য কিছু না করে বায়োস্কোপ করতে গেল কেন? এটা একটা ফ্যাক্টর ছিল, একটা অভিমান। কোথাও গিয়ে আমার দিক থেকেও একটা প্রবণতা ছিল বাদলদাকে এড়িয়ে চলার, যাতে ডিরেক্ট কনফ্রন্ট করতে না হয়। শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে এটা হতে পারে যে, আমি একজনের কাছ থেকে শিখেটিখে নিয়ে তাঁর রাস্তাটা ফলো না করে অন্য দিকে চলে গেছি। বাদলবাবু সিনেমার লোকেদের সঙ্গে মিশতেন, কিন্তু তাঁদের তো শেখাননি কিছু, আমায় শিখিয়েছেন। মৃণাল সেন তো অ্যাক্টিং করে শেখাননি, বাদল সরকার অ্যাক্টিং করে শিখিয়েছেন। তো সেই একটা মান-অভিমানের জায়গা থেকে এবং সেটা শুধু বাদল সরকার নন, অন্যান্য যাঁরা থিয়েটার করেছেন, যেমন প্রবীর গুহ ও অনেকের সঙ্গেই আমার গভীর সম্পর্ক হয়নি। তাঁদেরও হয়তো আমার প্রতি একটু অভিমান আছে যে অঞ্জন দত্ত এড়িয়ে চলে, সে শুধু নিজের সাফল্যের দিকেই তাকিয়ে থাকে! কিন্তু আমি এভাবেই চলি। আমি যে-রাস্তাটায় বিশ্বাস করি সেদিকেই যাব। এই থার্ড থিয়েটারের সঙ্গে আমার একটা মান-অভিমানের জায়গা আছে। আমি বোঝাতে পারিনি তাদের, অথচ তারা তো অপরিচিত নয়! তাদের শ্রদ্ধা করি।
অভিজিৎ : কোথাও একটু এড়িয়ে গেছেন?
অঞ্জন : আমি এড়িয়ে গেছি। বাদলবাবুরও অভিমান ছিল। নইলে ‘মারা/সাদ’ দেখতে এলেন, অন্য কোনও নাটকে এলেন না কেন? থিওসফিকাল সোসাইটিতে কীসব কোলাজ করছি, বাদল সরকার এসেছিলেন দেখতে, চুপ করে বসে দেখেছেন, অথচ অন্যান্য নাটক কেন দেখতে আসেননি? সিনেমা কেন দেখতে যাননি? একটা মান-অভিমানের ব্যাপার ছিল, আমার মনে হয়। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে সত্যিই ভালোবেসেছি এবং তাঁর কাছ থেকে যতটা পাওয়ার তা নিয়ে আমি আমার দিকে চলেছি।
অভিজিৎ : এটা খানিকটা এলভিস প্রিসলির গানের মতন : You were always on my mind...
অঞ্জন : যখন আমি কাউকে কিছু শিখিয়েছি, কোনও দলের ছেলেদের হোক বা বাইরের, ওয়ার্কশপ করেছি, বাদল সরকারের নাম সর্বত্র বলেছি। আমরা তো তাঁর দিকেই তাকিয়ে থেকেছি! নাট্যকার হিসেবে ওঁর যে-জায়গা, তার উল্লেখ আমি বহু জায়গায় করেছি। আর আমি কে! অমল পালেকর, গিরিশ কারনাডরা তাঁকে যে-স্থান দিয়েছেন, সেখানে আমি কে বলার যে ‘তিনি আমার কাছে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার’! একটা প্রচ্ছন্ন ভুলবোঝাবুঝি হয়ে গেছিল, যেটা থেকে তিনি বলেছিলেন “সিনেমায় চলে গেল কেন!” কোথাও একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং।
অভিজিৎ : এটা মেটাবার কোনও সুযোগ আসেনি?
অঞ্জন : অনেক পরে একটা জায়গা এসেছিল যখন অপর্ণা সেন তাঁর ধারাবাহিক টেলি-নাটক ‘আনডায়িং সিটি’ করছেন, আমার মেইন রোল, একটা ফিকশনাল গল্পের মধ্য দিয়ে কলকাতাকে ধরার চেষ্টা, মোট আটটা পার্ট। কলকাতার আর্কিটেকচার, ইতিহাস, আন্দোলন ইত্যাদি। এর মধ্যে একটা পার্ট ছিল বাদল সরকারকে নিয়ে। এতেই প্রথম আমি ওঁর সঙ্গে অ্যাক্টিং শেয়ার করি। একটি মেয়ে এসেছে বিদেশ থেকে, তাকে আমি কলকাতা ঘোরাচ্ছি। একটা সময়ে বলি, “আমি তোমাকে একজনের কাছে নিয়ে যাব, তিনি বাদল সরকার, তাঁকে দর্শন করা দরকার।” এবার বাদল সরকার পুরো গল্পের বেশ খানিকটা টেনে নিলেন, ফের আমি টেকওভার করলাম। একটা, কী দুটো এপিসোড— আমার ঠিক মনে নেই। চিড়িয়াখানাতে প্রথম শট-টা ছিল। বাদলদা খুবই শান্তভাবে এলেন, আমি চুপচাপ রয়েছি, বাদলদা সিগারেট খাচ্ছেন, আমিও। বললুম— বাদলদা, আমরা একটু রিহার্সাল করব? বললেন— হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করবে। রীণাদি বলল— তোমরা রেডি? রিহার্সাল করতে পারবে?
শুটিং হলো। দু-তিনটে শট হয়ে গেল, আমি গেলাম ফিরে, মেয়েটাকে পৌঁছে দিলাম, আমার সিকুয়েন্স শেষ। তারপর বাদলদাকে ছেড়ে চলে এলাম, জিজ্ঞেস করিনি কীর'ম হয়েছে। কিন্তু হয়েছিল চমৎকার, ভারী সুন্দর। কোনও সমস্যাই হয়নি। চলে তো এলাম, কিন্তু আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল।
আমি এখনও মনে করি যে, তিনি আমায় যতটুকু সময় দিয়েছিলেন সেটা আমাকে মানুষ এবং অভিনেতা হতে অসম্ভব সাহায্য করেছিল। তাঁর মতো শিক্ষক আমি গোটা ভারতবর্ষে আর খুঁজে পাইনি। যদি আমি বেপরোয়া হয়ে থাকি, সাহসি হয়ে থাকি, থিয়েটারে যদি কোনও নিয়ম ভেঙে থাকি, তার সবটাই বাদলদার কাছ থেকে পাওয়া। তিনি শিখিয়েছিলেন— প্রশ্ন তোলা-ই জরুরি, সমাধান দেওয়া নয়।

অভিজিৎ : আপনার জার্মানি যাওয়ার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে যদি একটু বলেন। থিয়েটার ইন জার্মানি। ইউরোপের থিয়েটার ইউরোপে বসেই দেখছেন!
অঞ্জন : আমি তখন কলকাতায় ‘মারা/সাদ’ করেছি, ম্যাক্স মুলারে বেশ আলোড়ন হয়েছে, আমি সিনেমা করছি ‘চালচিত্র’ এবং পরের নাটক ভাবছি কী করব। তখন জার্মানি থেকে বিখ্যাত আধুনিক নাট্যকার এবং ফিল্মমেকার টাংক্রেড ডর্স্ট কলকাতায় এলেন। তাঁর কাজকর্ম নিয়ে এখানে আলোচনা ইত্যাদি হবে। তখন ম্যাক্স মুলারের সেই ডিরেক্টরই আমায় বললেন, তুমি টাংক্রেড ডর্স্টের একটা নাটক করো। তখনো আমি টাংক্রেডের নাটক কী-কী আছে জানি না, একটারও ইংরেজিতে ভাষান্তর নেই, ম্যাক্স মুলারে কেউ আমায় গল্পগুলো অন্তত বলুক! যাই হোক, আইস্ এজ্ (Ice Age) বলে একটা নাটক আমাকে নাড়া দিল। ম্যাক্স মুলারের রাজু রামন (এস ভি রামন) পুরোটা জার্মান থেকে ইংরেজি করে আমায় বলছে, আমি লিখে নিচ্ছি। ডায়লগগুলো ইংরেজিতে লিখছি, তারপর বাড়িতে এসে সেই ইংরেজির ভিত্তিতে বাংলাটা লিখলাম।
বিশ্ববিখ্যাত নোবেলজয়ী লেখক নুট হামসুন— ‘হাঙ্গার’, ‘গ্রোথ অফ দ্য সয়েল' যাঁর লেখা— একবার হিটলার তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিল এবং হিটলারের সঙ্গে একটা টি-পার্টিতে তিনি চা খেতে গেছিলেন। এটা তাঁর জীবনে একটা বিতর্কিত ঘটনা হয়ে গেল। শেষজীবনে হামসুনকে অ্যাসাইলামে থাকতে হয়েছিল। সেখানে বৃদ্ধ নুট হামসুন যেমন আছেন, তেমনি তাঁর সঙ্গে আছে একটা আলট্রা-টেররিস্ট ছেলে, সে-ও পাগল হয়ে গেছে। যু্দ্ধোত্তর পরিস্থতিতে দু'জনেই রাস্তা প্রায় হারিয়ে ফেলেছে। ছেলেটা আাবার যুদ্ধকালীন প্রতিরোধ-বাহিনীতে বোমাটোমা বানাত! কিন্তু তাদের মধ্যে অদ্ভুত একটা বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছে এবং এই বিষয়টাতে আমি অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে পড়ি। আর আমি যে-ধরনের নাটক করি তাতে এটা আমাকে টানবে, বলা বাহুল্য।
আমি এটাকে প্রসিনিয়ামের উপযোগী করে নিয়ে ভীষণ গোছানোভাবে উপস্থাপন করেছিলাম। ভেরি ওয়েল ডিজাইনড্ পারফর্মেন্স। তীব্র সাদা, সবকিছু সাদা, তার স্ক্রিন সাদা, পোশাক সাদা, ক্লিনিকাল একটা আবহে হাসপাতাল-নার্স-ডাক্তার সব সাদা-সাদা-সাদা, সর্বত্র সাদা, লাইট সাদা। আবার দর্শক আছে কালোয়, একেবারে অন্ধকারে। সঙ্গে ছিল খুব সাজানো একটা পাগলাগারদ। সত্যি বলতে কী, পেটার ওয়াইস করার পরে পাগলাগারদ নিয়ে এই নাটকটাই যেন অবধারিত ছিল! আর অভিনয়ও হয়েছিল খুব বাস্তবধর্মী আর বিশ্বাসযোগ্য।
পড়ুন দ্বিতীয় পর্ব- থিয়েটারের অঞ্জন : লিয়ার আমার জীবনে অবশ্যম্ভাবী ছিল

খুবই গোছানো প্রোডাকশন, আমার নাটক এত গোছানো চট করে কেউ ভাবতে পারবে না। অনেক খরচা করিয়েছিলাম। তা ট্রাংক্রেড আমাদের রিহার্সালটা দেখলেন। তারপর ফাইনালটা স্টেজে দেখে ওঁর প্রচণ্ড ভালো লেগে গেল। তখন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। আমার অভিনয়ও ওঁর খুব ভালো লেগেছিল। বিরাট ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন কলকাতার কাগজে, হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড-এ বোধহয়, কলকাতায় তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে। আমার ওপর বিশেষভাবে বলেছিলেন, একটা ছেলেকে আবিষ্কার করলাম— চমৎকার অভিনেতা— কী দারুণ তার অভিনয়— এই বয়সে এত ভালো অভিনয়, কাউকে দেখিনি। আমাকে আলাদা করে হোটেলে ডেকে টাংক্রেড বললেন
— তুমি জার্মানি যাবে? যেতে চাও?
— হ্যাঁ, আমি জার্মানিতে গিয়ে থিয়েটার দেখতে চাই।
— থিয়েটার করবে?
— আমি তো ভাষাটা ভালো করে জানি না।
— ভাষা জানো না তো আমার নাটকটা করলে কী করে! পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তুমি কী করছ।
— আমায় হেল্প করে দিয়েছে।
— বোবা-র রোল করবে?
— হ্যাঁ, করতে পারি।
— দেখছি তাহলে। যদি যেতে চাও বলো, আমি তোমার একটা ব্যবস্থা করে দেব। ওখানে গিয়ে তোমাকে থিয়েটার করতে হবে। অ্যাক্টিংয়ে যদি চান্স না পাও তাহলে ব্যাকস্টেজে কাজ করবে?
— হ্যাঁ, করব।
— তোমায় তাহলে বছর-তিনেকের জন্য যেতে হবে।
— হ্যাঁ-হ্যাঁ, হান্ড্রেড পারসেন্ট।
— ঠিক আছে, আমি দেখছি।
এই দেখছি-দেখছি করতেই ক’বছর গেল। ‘চালচিত্র’ অ্যাওয়ার্ড পেল। ‘খারিজ'-এ মৃণালদা আবার আমায় নিলেন। বুদ্ধদেববাবু ‘গৃহযুদ্ধ’-তে নিলেন। এগারো মাসের মধ্যে এসব হচ্ছে। পরপর তিনটে— সার্কিটে সবাই বলছে ভীষণ ভালো, অঞ্জনের অভিনয় দারুণ ভালো! এসবের মধ্যেই হঠাৎ টাংক্রেডের কাছ থেকে খবর এল— হ্যাঁ, হয়ে গেছে। তবে তিনি যেখানে থাকেন সেই মিউনিখে হয়নি; হয়েছে ওয়েস্ট বার্লিনে, তখন তো ইস্ট-ওয়েস্ট ছিল, এটা ১৯৮৩/’৮৪-র কথা। খবর যেটা এল— পশ্চিম বার্লিনে একটা থিয়েটারের দল আছে, ‘থিয়েটার ম্যানফ্যাকটুর’, যারা এইরকম বিদেশ থেকে লোকটোক নেয় ব্যাকস্টেজে কাজ করার জন্য। ব্যাকস্টেজ হেল্প হিসেবে। তারা ভারত নিয়ে আগ্রহী। ওরাই রাজি হয়েছে। ওয়েস্ট জার্মানির, কিন্তু তারা সোশালিস্ট।
তদ্দিনে কলকাতা আমার খুব ভালো লাগছে। একবার ভাবছি যাব, আবার কখনও ভাবছি সিনেমা করব। দোটানায় পড়লাম— পরপর তিনটে ছবি— অ্যাওয়ার্ড পেয়ে গেছি— কী করব? মৃণালদা তখন বললেন— না, তুমি যাও। তুমি যখন এটা চাইছ, তুমি যাও। তিন বছর ঘুরে এসো। কিচ্ছু হবে না, এখানে তিন বছর বাদেও তুমি পার্ট পাবে।
আমি গেলাম। ওখানে আমদের ডিরেক্টর ছিল মাঝবয়সি অটো, কলকাতায় আমার কাজকর্মের কথা জেনে খুশি, আবার সোশালিস্ট নই বলে গোঁসাও ছিল তাঁর। কাজ থেকে যখন আমায় ছাড়ত তখন আমি থিয়েটার দেখতে চলে যেতাম। ওখানে থিয়েটারকর্মী হিসেবে আমার একটা কার্ড ছিল, সেই কার্ড দেখিয়ে আমি যে-কোনও থিয়েটারে ঢুকে পড়তে পারতাম। একটা নির্দিষ্ট স্লট থাকত, সেই স্লটে থিয়েটার দেখতাম বিনা পয়সায়। পূর্ব জার্মানিতে দেখতে গেলে সামান্য কিছু দর্শনী দিতে হতো, কিন্তু পশ্চিম জার্মানিতে ফ্রি। আমার থিয়েটারের জায়গাটা ছিল ক্রয়েৎসবার্গ। স্টেশন ছিল ফ্রিডরিখস্ত্রাস, সেখান থেকে ইউ-বান মেট্রোতে পরের স্টেশনেই আমি ঢুকে যেতাম ইস্ট বার্লিনে। একটা স্টেশন, পনেরো মিনিটও না।
আরও পড়ুন- চিত্রাঙ্গদা: ঋতুপর্ণর আত্মকথনে জেগে থাকেন অঞ্জন দত্ত
অভিজিৎ : এদিক থেকে ওদিকে যাওয়ার অনুমতি থাকত?
অঞ্জন : ভারতীয় নাগরিক বলে আমি পারতাম। জার্মানরা বা অনেকেই এভাবে যেতে পারত না। নিয়ম ছিল সকাল আটটায় আমি ঢুকে যেতে পারি, কিন্তু সন্ধে আটটার মধ্যে আমাকে ইস্টের ফ্রিডরিখস্ত্রাসে ফিরে আসতেই হবে।
ইস্ট বার্লিনে পৌঁছেই যদি দৌড় লাগাই তবে দশ মিনিটের মধ্যেই ব্রেখ্টের বার্লিন অনসম্বল। আর হাঁটলে 'পরে বড়জোর মিনিট কুড়ি। কিন্তু কোনওদিনই বার্লিন অনসম্বলের প্রোডাকশন শেষ অব্দি দেখা হয়নি। কারণ, শেষ হতে-হতে রাত ন’টা। কাজেই ইন্টারভ্যালের ঠিক পরেই পালিয়ে আসতে হতো।
জার্মানিতে পুব-পশ্চিম মিলিয়ে অজস্র থিয়েটার দেখে প্রথমেই আমার যেটা মনে হয়েছিল— ওইর’ম স্কেলে ওইভাবে আমরা ভাবতে পারি না। থিয়েটারে এত খরচা হচ্ছে! ডিজাইন নিয়ে এত ভাবনা! বিখ্যাত সব অভিনেতা, ফিল্মের অভিনেতারা করছে। এত খরচা করে থিয়েটার করছে, এত ভিড় করে লোকে থিয়েটার দেখছে এবং প্রত্যেকটা থিয়েটারেই কিছু-না-কিছু ক্লাসিক হচ্ছে, যদিও জার্মান ভাষায় হচ্ছে, ক্লাসিকগুলো হয় পড়া বা শোনা। থিয়েটার নিয়ে আমার ভাবনার খুব কাছাকাছি, কিন্তু যেন বহু-বহু দূরে, এত বড় একটা স্কেলে ওসব হচ্ছে! এমন— যেখানে কেউ জামাকাপড় পরে নেই; এমন— যেখানে থিয়েটারের গোটা ব্যাকড্রপটা হচ্ছে একটা কাঁচ, আয়না— অডিয়েন্স নিজেকে দেখছে! একটা নাটক পড়ে যেগুলো মনে হতো, চোখের সামনে সেসব সত্যি হতে দেখছি! একটা ঘোড়া চলে এল, লাল রংয়ের, বিরাট! অভিভূত হয়ে দেখছি। আর কী বলিষ্ঠ অভিনয়! তখন ছিলেন একহার্ড শাল, ব্রেখটের জামাতা, তাঁর প্রযোজনায় ককেশিয়ান চক সার্কেল আমি দেখেছি। থ্রিপেনি অপেরা দেখেছি, বোধহয় হাইনে মুলারের করা, হাইনে মুলার আবার ইস্টের।
ব্রেখটিয় থিয়েটার সম্পর্কে কলকাতায় বসে আমি যা শুনে এসেছি, এ তো তার সম্পূর্ণ বিপরীত! কলকাতায় বলা হয় ব্রেখট হচ্ছে পোস্টার ড্রামা, ব্রেখট মানে এলিয়েনেশন, কত কী! এ তো দেখছি হলিউড মিউজিকালের থেকেও এগিয়ে— নাচ করছে, গান করছে, গুলি করছে, পড়ে যাচ্ছে, কাঁদছে— কত কী! এরকম ব্রেখট! এত স্কিলড্, এত ভালো গান-টান! হতবাক হয়ে যাচ্ছি। ব্রেখটিয় থিয়েটার কি এরকম? জীবনে কল্পনা করতে পারিনি। কিন্তু সেখান থেকে একটা কিছু বেরিয়ে আসছে, খুব বড় কিছু, সেটাই এপিক থিয়েটার। এপিক থিয়েটার মানে এই নয় যে পুওর থিয়েটার।
আমি দেখলাম এই থিয়েটারটা আমার পক্ষে করা সম্ভবই নয়। মিউনিখে গিয়েও কিছু অভিজ্ঞতা হলো। সেখানে টাংক্রেড আমাকে তাঁর বাড়িতেই রাখলেন। একমাসের ছুটি পেয়েছিলাম। আমার তখন একেবারে দিশেহারা অবস্থা। তিনি বললেন,
— তোমার এই অবস্থা কেন?
— আমি পারব না থিয়েটার করতে।
— সে কী! তুমি তো থিয়েটার করতেই এলে!
— এই থিয়েটার আমার পক্ষে সম্ভব নয়, এ এত বড় মাপের যে আমাদের দেশে এ জিনিস খাটবে না।
— তাহলে কী করবে?
মিউনিখে তখন জার্মান সিনেমার নবতরঙ্গ। রাইনহার্ড হাউফ, আলেকজান্ডার ক্লুগ, মার্গারেট ভন ট্রটা— এঁরা সব আছেন। রাইনহার্ড হাউফের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, তাঁর বাড়িতে যাচ্ছি। রাইনহার্ড তখন বললেন— চলো, তুমি দেখো সিনেমা কীভাবে হয়। এবার আমি গিয়ে দেখছি, ঠিক মৃণাল সেন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্তরা যের’ম ভাবে সিনেমা করেন, সেভাবেই এঁরা করছেন! ঘরের মধ্যে, রাস্তার মধ্যে এখানে যেভাবে সিনেমা হয়, ওখানেও সের’মভাবে হচ্ছে, হয়তো স্কেলটা একটু বেটার। হয়তো দুটো ভ্যানিটি ভ্যান রয়েছে, বা আরও কিছু। কিন্তু মোটের ওপর একই রকমের। এমন নয় যে ‘খারিজ’ এক স্টাইলে হচ্ছে আর আলেকজান্ডার ক্লুগের ছবিটা একদম অন্য স্টাইলে হচ্ছে। এটা আমার বেশ ভাল্লাগছে। রাইনহার্ড হাউফ আর টাংক্রেড ডর্স্টের বাড়িতে প্রচুর ভিডিওর কালেকশন। সেইগুলো দেখতে-দেখতেই আমি এই প্রথম সারা পৃথিবীর সিনেমা নিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠলাম। হলিউড আমি জানি, কিন্তু ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো, গোদার, জার্মান সিনেমা, ফাসবিন্দার, ব্যাটেলশিপ পটেমকিন আমি এ-ই প্রথম দেখলাম। মৃণাল সেন, সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, সঙ্গে হারজগ, আন্তোনিওনি, আন্দ্রে ওয়াইদা, ইতালিয়ান সিনেমা, সেইসঙ্গে প্রচুর অপুরস্কৃত ছবি। দিনে তিন-চারটে করে ভিডিও দেখে ফেলছি এবং বুঝতে পারলাম, আমি ফিরে গিয়ে এইটা করতে পারি আমার মতো করে। একটু অন্যরকম কিছু করব। পপুলার, ব্রেখ্ট, মিউজিকাল— এসব মাথায় ঘুরছে। সিনেমা করব। রাইনহার্ডকে বললাম, তোমার বন্ধু মৃণালকে একটা চিঠি লিখে দাও যে আমি সিনেমা শিখতে চাই, যাতে গিয়ে একটা কাজ পাই। রাইনহার্ড বললেন, তুমি গিয়ে বলো, তোমার তো পরিচিত। বললাম— না, তুমি প্লিজ লিখে দাও। খুব রাগ করবেন। রাইনহার্ড তখন লিখে দিয়েছিলেন— মৃণাল, তোমার অ্যাক্টর সিনেমা বানাতে চায়, তুমি ওকে একটু হেল্প করো।

আরও পড়ুন- মৃণালের অঞ্জন অঞ্জনের মৃণাল
তো আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে বললাম, আমি আর থাকব না। সুতরাং আর মাইনেও আমি পাব না। দেশে ফিরে এলাম। এসে মৃণালবাবুর কাছে গিয়ে চিঠিটা দেখালাম। মৃণাল সেন হাঁ করে তাকিয়ে বললেন,
— এইটার জন্যে তুমি জার্মানি গেছিলে? এটা আনার জন্য?
— না-না, আমি তো গিয়ে বুঝেছি ব্যাপারটা।
— কী বুঝলে তুমি?
— থিয়েটার হবে না। এটা করতে হবে।
‘নাইফ ইন দ্য ওয়াটার’, পোলানস্কি, ইনি-উনি-তিনি— মৃণাল সেন অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, আমি বলে চলেছি— আন্তোনিওনি যেভাবে শট নেন... মৃণাল সেন চুপ করে তাকিয়ে আছেন।
— এসব কোত্থেকে শিখলে? তুমি কি ওখানে গিয়ে ফিল্ম-স্কুল, সিনেমা...
— না-না, আমি ওখানে থিয়েটার দেখেছি, প্রচুর দেখেছি।
আমি বলে যাচ্ছি— ভুবন সোম, কলকাতা-৭১, এটা-ওটা। হঠাৎ মৃণালদার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হলো। ইতালিয়ান নিউ ওয়েভ নিয়ে, জার্মান নিউ ওয়েভ নিয়ে, কোনটার কে ডিরেক্টর, ইনি কে, উনি কে, তিনি কে। আমিও ঝটপট উত্তর দিয়ে যাচ্ছি। শেষে বললেন, পাগল! ঠিক আছে, তুমি এসো, একটা অ্যাসিস্ট করো। আর পার্টও থাকবে।
কিন্তু ম্যাক্স মুলার ভবন তখন আমাকে ছাড়বে না। তারা তো আমায় প্লেনভাড়া ইত্যাদি খরচা দিয়ে পাঠিয়েছিল, যদিও ওখানে আমি নিজের রোজগারের টাকায় চালিয়েছি, কিন্তু শর্ত ছিল যে ফিরে এসে ম্যাক্স মুলারে নাটক করতে হবে। কী শিখে এসেছি সেটা ওদের দেখাতে হবে! তা দেখলাম, চুক্তি মোতাবেক আমাকে মোট ছ’টা নাটক করতে হবে। এজন্য ওরা অবশ্য টাকা দেবে। তখন আমি বেছে-বেছে ছ’টা নাটক করলাম।
অভিজিৎ : কোন সময় এটা?
অঞ্জন : ১৯৮৬ থেকে ’৮৯, এর’ম সময়ে। বছরে কমবেশি একটা করে। ভীষণ অ্যাবস্ট্র্যাক্ট, লোকের মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য শেষের ক’টা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। দুটো নাটক করেছিলাম এখানকার, মানে কলকাতা বা পশ্চিমবাংলার পটভূমিতে। ‘ডল্’স হাউস’, একটা বাড়ির চত্বরে হয়েছিল, খুব নাম করেছিল। আরেকটা ‘লাইন ওয়ান’— কর্ড লাইন নামে হয়েছিল, এর অরিজিনাল মিউজিক ডিরেক্টর জর্জ ক্রানজ্-কে এখানে ডেকে পাঠালাম। জর্জ এল কলকাতায়, দু'জনে মিলে এই মিউজিকাল ‘কর্ড লাইন’ করলাম, জর্জ ট্র্যাক-টা করল আর আমি কথাগুলো লিখলাম। এগুলো আমি করেছিলাম এবং এগুলোর খুব নাম হলো। এই সময়েই সিনেমায় পরপর কাজ আসতে লাগল— শিল্পী, মহাপৃথিবী, যুগান্ত। আবার আমি সিনেমা করতে আরম্ভ করলাম। ততদিনে আমার নাটক সম্পর্কে কিছু লোকের একটা ধারণা হয়েছে। ’৯৩ থেকে আমি গান করছি।
চলবে...




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp