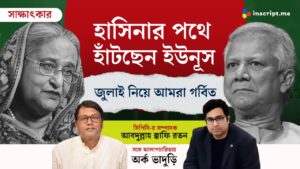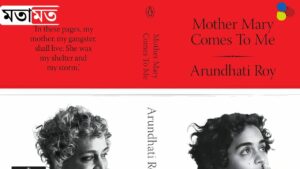থিয়েটারের অঞ্জন : লিয়ার আমার জীবনে অবশ্যম্ভাবী ছিল
Anjan Dutt Interview: আমার থিয়েটার মানুষকে কী দেবে? একটু অন্যরকম থিয়েটারের মাধ্যমে কিছু তরুণকে একটু সাহস জোগাতে পারে মাত্র। এর বেশি হয়তো কিছু নয়।
অঞ্জন দত্তের থিয়েটার নিয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারিতা করেছেন অভিজিৎ বসু৷ এই দীর্ঘ কথোপকথন ঠিক সাক্ষাৎকার নয়, বরং হয়ে উঠেছে অঞ্জনের থিয়েটারের দর্শন, রাজনীতি, শিল্পভাবনা এবং জীবনের টুকরো টুকরো নানা রঙের মিশেলে একটি দুর্দান্ত আড্ডা। রইল তৃতীয় ও শেষ পর্ব। অনুলিখনে সৌরভ সেন।
অভিজিৎ বসু : নাটক সংক্রান্ত আরেকটি প্রসঙ্গ। আপনি খুব সচেতনভাবেই কোনও দল করেননি।
অঞ্জন দত্ত : দলের নাম একটা আমাদের করতে হয়েছিল কর্পোরেশন ইত্যাদির নিয়মকানুনের ঠ্যালায়। বাদল সরকারের কাছ থেকে এসেছি বলে দলের নাম ছিল ‘ওপেন থিয়েটার’। দলে নিয়মের কোনও কড়াকড়ি ছিল না, একেবারেই ঢিলেঢালা। একজনের কাকা না জ্যাঠা, তাকে করা হয়েছিল সেক্রেটারি। যারা একটা নাটকে করল, তারা পরেরটাতে না-ও থাকতে পারে। আগের নাটকে না থাকলেও পরের নাটকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকতেই পারে। এমনি করেই শেখর দাশ, রাজা সেন, বিপ্লব দাশগুপ্তরা বিভিন্ন সময়ে কাজ করেছেন।
অভিজিৎ : পিছন দিকে ফিরে একটা প্রশ্ন। আপনি একদা বলেছিলেন যে, দল ব্যাপারটা আপনি এড়িয়ে গেছেন কারণ দলে ঢোকা মানে দলের মতাদর্শগত যে কাঠামো, সেই অনুযায়ী একজন অভিনেতার গড়ে-ওঠাটা হয়ে ওঠে। তাহলে কি আপনি ব্যক্তিমানুষ হিসেবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে ভর করেই গড়ে উঠতে চেয়েছেন?
অঞ্জন : হ্যাঁ। আমার নাটকটা যদি ব্যক্তি আর সমষ্টির ক্রাইসিস হয় এবং যেখানে আমার কাছে ব্যক্তি বড়, তাহলে আমার নাটক কী করে একটা সমষ্টির হয় যেখানে একটা সমষ্টির লোক হয়ে আমি ব্যক্তিকে বড় করছি! থিয়েটারে আমি ওই সমষ্টিতে বিশ্বাস করিনি। আমি ‘দল’ কনসেপ্টটায় বিশ্বাস করি না। আমি পার্টিতে বিশ্বাস করি না। আমি কোনও সংগঠনে বিশ্বাস করি না। হ্যাঁ, সংগঠনের দরকারও থাকে, সংগঠনের কিছু ভালো দিকও আছে। কিন্তু সংগঠন দিনের পর দিন ব্যক্তিমানুষের স্বাধিকারকে খর্ব করে যাচ্ছে। আমার যে-নাটক করতে ইচ্ছে করছে তার বদলে আমাকে সেইর’ম নাটক করতে হবে, দলের ছেলে যের’ম আছে! দলে একটা নির্দিষ্ট বয়সের ছেলে আছে, তবে কি আমি একটা বয়স্ক লোকের নাটক করতে পারব না? দলে একটা মাত্র মেয়ে, তাহলে চারটে মেয়ের নাটক করতে পারব না? এ তো ভারী মুশকিল! আরেকটা কথা— অভিনেতাকে তো গড়ে-উঠতে হবে, দল করে কী হবে? সারাক্ষণ দল আর সংগঠন, যে-কারণে গ্রুপ থিয়েটারের কনসেপ্টে আমার আপত্তি ছিল। এই দলে কাজ করলে ওই দলে কাজ করা যাবে না। বহুরূপীতে করলে বহুরূপীর হয়েই থাকতে হবে এবং প্রায় সবাইকে শম্ভু মিত্রের ধারায় অভিনয় করতে হবে! এটা একেবারেই অর্থহীন এবং ভীষণ ক্ষতিকারক। আবার উৎপল দত্তের দলে হয়তো সবাই বামপন্থী অথবা বামপন্থী একটি পার্টিতে বিশ্বাস করলে ভালো। এটা আমি মানতে পারিনি।
তবে এটা ঠিকই, গ্রুপ থিয়েটারের উৎপত্তি হয়েছে একটা বিশেষ ধারার রাজনীতি থেকে। কিন্তু এক দলের লোক আরেক দলে কাজ করতে পারবে না, এটা কী ধরনের নিয়ন্ত্রণ? শতাব্দীতেও তাই-ই। কেন এটা হবে? আমার মনে হয়েছিল, শতাব্দীতে যদি আমি থেকে যাই, আমিও নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাব। আমি এটা বলছি বটে, কিন্তু বাদলদার জন্য কষ্ট হচ্ছে।
পড়ুন প্রথম পর্ব- থিয়েটারের অঞ্জন : বাদল সরকারই আমার থিয়েটারের শিক্ষক

অভিজিৎ : আপনি কি মনে করেন যে ব্রেখটের এপিক থিয়েটারের ধারণাই স্ট্রাকচারের দিক থেকে সবচেয়ে পলিটিকাল? আপনার থিয়েটার পলিটিকাল হলেও ‘নট অ্যাবাউট পলিটিক্স’। একটু যদি ভেঙে বলেন।
অঞ্জন : ব্রেখটের থিয়েটার আমার কাছে সবথেকে বেশি পলিটিকাল মনে হয়নি, সবথেকে বেশি আধুনিক মনে হয়েছে। মানে, থিয়েটারের ক্রমবিকাশ ব্রেখটে এসে একটা চূড়ান্ত ধাপে পৌঁছেছে, তারপরে আরও উঠেছে, থিয়েটার অফ ক্রুয়েলটি হয়েছে, থিয়েটার অফ দি অ্যাবসার্ড হয়েছে। অতীতের গ্রিক থিয়েটার, এলিজাবেথান থিয়েটার, ন্যাচেরালিজম হয়ে এটা-ওটা-সেটা হওয়ার পর শেষে এপিক থিয়েটার যা আনল, তারপর যা-যা হয়েছে সবই এপিক থিয়েটার-ভিত্তিক, এপিক থিয়েটারের মধ্যেই সেসব রয়েছে। এপিক থিয়েটার হচ্ছে থিয়েটারের সবথেকে আধুনিক ফর্ম। কখনই সবথেকে বেশি পলিটিকাল আমার মনে হয়নি, মনে হয়েছে সবথেকে আধুনিক। এরপরে আর আমি ব্রেখটকে ছাড়তে পারিনি। আমার মধ্যে ব্রেখট ঢুকে গেছে, আমার শেক্সপিয়রে, আমার রবীন্দ্রনাথে, সব জায়গায়। পলিটিকাল ব্রেখট আমাকে একেবারেই আলোড়িত করেনি। এখানেই ব্রেখটের মজা। যে-কারণে বাদল সরকারের কন্ট্রাডিকশান আর ব্রেখটের কন্ট্রাডিকশান আমার কাছে এক। বাদল সরকারের ভোমা বা মিছিল-ও চমৎকার ভাবে লেখা। টেক্সটের বাইরে তো বাদলদা বেরোতে পারেননি। বলা হচ্ছে অফস্টেজের কথা। কিন্তু মিছিল স্টেজে করা যায়, ভোমা-ও স্টেজে করা যায়। ব্রেখট রাজনীতির যে-কথাগুলো বলেছেন সেটা যদি সোশালিজমের কথা বলে, সোশালিজম পাওয়ারে এলে সেটা সোশালিজমের বিরুদ্ধে বলে, সোশালিজম যখন করাপ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন সেটা ভীষণ প্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে। কী করে হচ্ছে! তিনি সোশালিজম চাইছেন বলে লিখছেন আর্তুরো উই। যখন রাইটিস্টরা পাওয়ার থেকে সরে গিয়ে লেফটিস্টরা আসার পর সেই একইরকম করাপশান, তখন আর্তুরো উই ফের প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল, কারণ এটা পাওয়ার আর করাপশান নিয়ে লেখা। অনেকটা শেক্সপিয়রের মতন।
আরও পড়ুন-‘মৃণাল সেনের চোখে দেখেছি আমার শহর’: কথাবার্তায় অঞ্জন দত্ত
অভিজিৎ : ক্ষমতাকে প্রশ্ন করলেই সেটা পলিটিকাল হয়ে দাঁড়ায়।
অঞ্জন : হ্যাঁ, সেটা পলিটিকাল, ওইটুকুই। ব্রেখটের মধ্যে ব্যক্তিমানুষ সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। গুড পার্সন অফ সেজওয়ান-কে ব্যক্তিমানুষের সংকট হিসেবে দারুণভাবে উপস্থাপিত করতে পারি। গ্যালিলিও-কেও তাই-ই। ব্যক্তিমানুষের সংকটকে ঘিরে ব্রেখটের অনেকগুলো নাটকই করা যায়। সেই সুযোগ তিনি দিয়ে গেছেন। একটা টেক্সটও বদল না করে, ব্যক্তিমানুষ আর সমাজের মধ্যেকার সংঘাত আমি ব্রেখটের যে-কোনও নাটক থেকে বের করে এনে দিতে পারি। এই যে-দ্বন্দ্ব, সেটা ব্রেখটের মধ্যে সতত হাজির, সেটা দ্বন্দ্ব বা সৌন্দর্য যা-ই বলুন না কেন! হয়তো তিনি থিয়েটারের বাইরে একজন সোশালিস্ট। কিন্তু আমার মনে হয় ওঁর কাজে তিনি বলেছেন ক্ষমতা আর রাজনীতির কথা, আঙুল তুলেছেন ক্ষমতার দিকে। এটা কিন্তু রাজনৈতিক। সেদিক থেকে ব্রেখটের থিয়েটার অবশ্যই রাজনৈতিক থিয়েটার। এটা আমার কাজেও আমি করার চেষ্টা করেছি, কোনওরকম রাজনৈতিক গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় না দিয়ে।
স্ট্রাকচারের দিক থেকে গোদার আমাকে টেনেছিলেন, ব্রেখট টেনেছিলেন, কিন্তু গোদার হয়তো অতিবাম রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন, আমি করিনি সেটা।
অভিজিৎ : পিটার ব্রুক বলেছেন, সিনেমা সবসময়ে অতীতকে নিয়ে থাকে, সিনেমার কোনও বর্তমান নেই। আর থিয়েটার সবসময়ে বর্তমানকে নিয়ে, বর্তমানে হচ্ছে। আপনিও থিয়েটারকে বলেছেন ‘লাইভ আর্ট, মোমেন্টারি এক্সপেরিয়েন্স’। এটা জানতে চাই আপনার কাছে।
অঞ্জন : হ্যাঁ। কারণ থিয়েটার হচ্ছে ‘তখন এবং এখন’ (then and now), তার আর অতীত বলে কিছু নেই। ‘তখন-এখন’— সেটা ঘটছে, তাকে সমকালীন সময়ে এসে দাঁড়াতে হবে, চলমান সময়ের প্রতিচ্ছবি হতে হবে— হতে পারে সেটা শেক্সপিয়রের নাটক, হতে পারে সেটা মহাভারত বা অন্য কিছু। এখনকার সময়ে দাঁড়িয়ে, একটা টেক্সট অথবা স্ট্রাকচারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি এখনকার সময়কে দেখছি। সেটা আর রেখে দেওয়া যাবে না ভবিষ্যতে ফিরে-দেখার জন্য, কিন্তু যে-কোনও বড় সিনেমাকে আপনি রেখে দিয়ে ফিরে-ফিরে দেখতে পারেন। এটা বাদল সরকারই আমাকে শিখিয়েছিলেন যে একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটা নির্দিষ্ট স্থানে বিশেষ কিছু ঘটবে। হয়ে গেল, তো শেষ! তার রেশ নিয়ে থাকতে পারো তুমি। কিন্তু ফের ওই অভিজ্ঞতা, ওই উপলব্ধি হবে না। পরের শনিবারে আবার অন্য জায়গায় আমরা সমবেত হব, তখন সেটা একটা অন্য অভিজ্ঞতা হবে।
অভিজিৎ : সেই একই জায়গায় সমবেত হলেও তো অন্য অভিজ্ঞতা!
অঞ্জন : হ্যাঁ, কখনই এক হবে না।
বাঁধাধরা পদ্ধতিতে দিনের পর দিন হুবহু একইভাবে হতে পারে না। যান্ত্রিক ভাবে হয় না। মেপেজুপে ওই একই জায়গা থেকে একইভাবে একই রংয়ের আলো এক বিশেষ চরিত্রের বা একাধিক চরিত্রের ওপর ফেলে যাওয়া— এটা বদলাতেই পারে, আজকে এটা হতে পারে, কাল ওটা হতে পারে। একদিন এমন একটা অভিনয় হলো যে সেটা আর অন্যদিন অভিনেতা আনতে পারল না। কিচ্ছু করার নেই তার। সেইদিন মানসিক পরিস্থিতি এমন ছিল যে করে দিয়েছে। অথবা, একটা প্রোডাকশন দেখে একজন দর্শকের এমন অনুভূতি হলো ওইদিনকার আবহে যে পরে যখন সেটা আবার দেখতে গেল, সেই আস্বাদ পেল না। সিনেমায় সেটা নয়, যা একবার হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে। ওটা আর কিছু করা যাবে না। ভুল হলে ভুলটা নিয়েই থাকতে হবে। সিনেমা আর বদলানো যায় না।
অভিজিৎ : ২০১২-তে আপনি গ্যালিলিও করেছিলেন। এখন অবধি গ্যালিলিও-ই কি আপনার সবচেয়ে সফল প্রযোজনা? মানুষের উচ্ছ্বাস, প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে?
অঞ্জন : সবথেকে সফল প্রযোজনা 'মারা/সাদ’, আমার তৃতীয় নাটক। ওইর’ম সময়ে ওইর’ম একটা প্রোডাকশন দেখতে প্রচুর লোক আসত। আমি মারা-র চরিত্রে করতাম, সেটাও ছিল বেশ কঠিন কাজ। এরপর আমি রাখব ইবসেনের ‘ডল’স্ হাউস’, যেটা প্রিয়া সিনেমার উল্টোদিকে একটা বাড়ির চাতালে হয়েছিল, দর্শক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ভাড়া-করা কাঠের চেয়ারে বসত। অভিনয় হতো চাতাল আর লাগোয়া দুটো ঘরে, যার বিশাল দুটো জানলা ছিল। আলো করেছিল সিনেমার ক্যামেরাম্যান সম্বিত বোস। ঘরের আলো উঠোনে এসে পড়ত, লোডশেডিং করা হতো মোমবাতি জ্বালিয়ে। আমি পার্ট করিনি। আমি মনে করি, আমার স্ত্রী ছন্দার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় এটি।
এর পরে আমি রাখব কিং লিয়ার-কে, তারপর আসবে গ্যালিলিও।
অভিজিৎ : গ্যালিলিও-তে ব্রেখটের যে-টেক্সট, সেটা তো সবার কাছেই এক— আপনি, শম্ভুবাবু, বহুরূপী...
অঞ্জন : আর যাঁরা-যাঁরা করেছেন, হরিমাধব মুখোপাধ্যায় এবং অন্যরা...

অভিজিৎ : আপনি যে একটা জায়গায় আলাদা হচ্ছেন, সেটা কি ইন্টারপ্রিটেশানের ভিত্তিতে? না কি আপনি এত বছর ধরে যে-থিয়েটার শিখেছেন, সেটা প্রয়োগের মাধ্যমে?
অঞ্জন : প্রথম কথা, টেক্সটকে আমি কীভাবে পড়ছি। একই টেক্সট নানাভাবে পড়া যায়। তারপর আমি তাকে যেভাবে দেখছি। বিভিন্নজন এটাকে বিভিন্নভাবে দেখতে পাবে। তারপর কীভাবে প্রয়োগ করছি, তখন ফর্মের ব্যাপারটা আসছে। যত বড়মাপের টেক্সট হবে, সময়ান্তরে তত তার নানারকম মানে বেরোবে। এ ব্যাপারে শেক্সপিয়র অগ্রগণ্য। যে-নাটকের ভাষ্য একটাই, সেটা ভালো নাটক নয়। রবীন্দ্রনাথকেও আমি অন্যভাবে দেখতে চেষ্টা করেছি।
অভিজিৎ : বিসর্জন?
অঞ্জন : সহিংসতা আর ধর্মবিশ্বাসের বাইরে চলে যেতে চেয়েছি। বিসর্জনকে ব্যক্তিমানুষ ও সমষ্টির সংকটের মধ্য দিয়ে দেখতে চেয়েছি আমি। কতটা পেরেছি জানি না।
বিসর্জন করলাম একটা কারণে যে সবাই বলছিল, অঞ্জন ভারতীয় থিয়েটার করে না। তখন ভাবলাম, বাদল সরকার করব, না রবীন্দ্রনাথ করব? দেখলাম, একটা চিরকালীন ক্লাসিক করা উচিত। রবীন্দ্রনাথকে ধরে আমি বদলাতে পারি কিনা ভাবছি— তাসের দেশ, রক্তকরবী, এটা-সেটা মাথায় ঘুরছে, কখনও মনে হচ্ছে যে রক্তকরবী করার থেকে সারারাত্তির করলেই ভালো হয়, একটা দ্বন্দ্ব চলছিল, যদিও নাটক হিসেবে সারারাত্তির অনেক শ্রেয়। তারপর মনে হলো, একটা বড় স্কেলে বড় জায়গা নিয়ে করার কথা। দক্ষিণপন্থী উত্থান তখন একটা চূড়ান্ত জায়গায় যাচ্ছে। তখন এই জয়সিংহ এবং রঘুপতির যে ক্রাইসিস, একটা গোষ্ঠীর মধ্যে আটকে রাখা, ওই গোষ্ঠী-পলিটিক্স থেকে বেরিয়ে আসা— ঠিক করলাম এটা নিয়েই হোক! এখানে রবীন্দ্রনাথকে অন্যভাবে দেখতে চেয়েছি।
অভিজিৎ : পোস্ট-মডার্নিস্টদের মতো বলবেন, দি অথর ইজ ডেড? তাহলে লেখক হিসেবে বাদল সরকার— নেই?
অঞ্জন : অবশ্যই। কিন্তু তাঁর নাটকে তিনি এমন কিছু দিয়ে গেছেন, তাঁর মৃত্যুর পরেও যেটা হতে পারে। লেখক অনেক কিছু ভেবে লেখেন। ব্রেখট বলে দিচ্ছেন, যদি ভালো না লাগে নাটকটা, তাহলে সমাজকে পাল্টান। এবার সমাজ পাল্টে গিয়ে যখন বদমায়েশি হচ্ছে, আবার যদি ভালো না লাগে নাটকটা, তাহলে সমাজকে পাল্টান, অন্য সমাজকে। কমিউনিজম এসে গেছে বলে সব ভালো হয়ে গেছে, তা তো নয়, কমিউনিজম এলে গোলমাল যদি হয়, আবার ওই কথাটাই এসে যাবে। সমাজ যতক্ষণ না পাল্টাবে, নাটকটাও পাল্টাবে না। যতরাজ্যের যুদ্ধবিগ্রহ, হানাহানি, ব্যভিচার চলতেই থাকবে। এটা সমাজের যে কোনও অবস্থায় সম্ভব, হিটলারের সময়ে সম্ভব, যে কোনও সময়ে।
অভিজিৎ : কমিউনিস্ট জমানাতেও?
অঞ্জন : হ্যাঁ, স্টালিনের সময়েও সম্ভব এবং যখনই বড় কোনও ক্রাইসিস এসেছে তখনই সমাজের কথা বলতে গিয়ে সিনেমা, থিয়েটার সব— গ্রিক ট্রাজেডি বা পুরনো কিছুকে আঁকড়ে ধরেছে। তখন টেক্সটের মোড়ক বা বেশভূষার মধ্য দিয়ে যে যার পলিটিক্স বলতে আরম্ভ করে। সরাসরি বললে ধরা পড়ে যাবে। যেমন হিটলারের সময়ে গ্রিক ট্রাজেডির আধিক্য। আন্তিগোনের মানেটা সম্পূর্ণ পাল্টে যাচ্ছে, তখন আর ঈশ্বর-মানুষের ক্রাইসিস নয়, তখন ক্রেয়ন আর আন্তিগোনের ঝামেলা। বড় টেক্সটের গুণ কালজয়ী হওয়া । যে-থিয়েটার সেই চিরকালীনতাকে ধরতে পারে না, সে-থিয়েটারের অবস্থা খুব খারাপ।
আরও পড়ুন-পাল্টে যাওয়া জীবনজগৎ বাস্তবতায় কেন মৃণালকে খুঁজেছেন অঞ্জন?
অভিজিৎ : গ্যালিলিও কি এই ধরনের টেক্সট?
অঞ্জন : আলবাত। গ্যালিলিও তো এক বিজ্ঞানীর গল্প নয়, প্রশ্ন হল সত্যি কথাটা বলতে পারছে কি পারছে না। সত্যি কথা বলতে গেলে তাকে সিস্টেমের বিরুদ্ধে যেতে হবে। সে সেটা পারল না, হেরে গেল, তারপর বন্দি অবস্থায় সত্যটা লিখে ফেলল। আন্দ্রেয়া দেখা করতে গেলে লেখাগুলো তাকে পাচার করল। আন্দ্রেয়া বলছে, তুমি বেঁচে রইলে বলে সত্যি কথাটা পেলাম। ব্রেখটের লেখায় গ্যালিলিও বলছে : আমি না লিখলে কুড়ি বছর বাদে আর-কেউ লিখত। লিখতই। আমি কুড়ি বছর আগে এটা ভেবেছিলাম। তখন মৃত্যুভয়ে লিখিনি। আমি বিজ্ঞানকে কুড়ি বছর পিছিয়ে দিয়েছি।
অনবদ্য! এইটাকে ধরেই আমি কাজটা করতে চেয়েছিলাম। আবার এক জায়গায় আন্দ্রেয়া বলে ওঠে, দুর্ভাগা সে-দেশ, যে-দেশে বীরের এত অভাব। গ্যালিলিওর উত্তর ছিল, দুর্ভাগা সেই দেশ, যেখানে হিরোর প্রয়োজন হয়। হিরোর প্রয়োজন কেন, মানুষ করতে পারছে না কেন?
এভাবে না পড়লে জিনিসটা কাজ করে না।
অভিজিৎ : আমরা এবার আপনার সাম্প্রতিকতম নাটক ‘আরো একটা লিয়ার’-এ আসছি। গোটা ছয়েক শো তো হলো। নিরাভরণ মঞ্চ, একটা চাকালাগানো চেয়ার, শেক্সপিরিয়ান থিয়েটার, জ্যাকবিয়ান টেক্সট, সঙ্গে চরিত্রগুলো গোটা মঞ্চকে একটা জ্যামিতিক স্পেস হিসেবে ব্যবহার করছে, পাশাপাশি তারা তাদের স্থানাঙ্ক পরিবর্তন করে বিভিন্ন প্যাটার্ন তৈরি করছে। আধুনিক মঞ্চ-নকশা, অভিনয়, বিভিন্ন প্রয়োগ মিলে এত আধুনিক একটা জিনিস ঘটছে যে-টেক্সটকে ভিত্তি করে, সেটা আবার চারশো বছরের পুরনো। যথাসম্ভব আধুনিক একটা ধাঁচে এই টেক্সটকে ধরা হচ্ছে। কিছু বলুন এ নিয়ে।
অঞ্জন : থিয়েটারের সেটাই কাজ। যত আধুনিকভাবে, যত গোড়াঘেঁষা জায়গা থেকে এগনো যায়, থিয়েটার ততই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। মানবশরীরকে নিয়ে জড়িয়ে থাকে থিয়েটার। বাদল সরকারে ফিরছি। একজন দেখছে, আরেকজন করছে, ব্যাস, আর কিচ্ছু দরকার নেই, মেকআপ ইত্যাদি কোনও কিছু। তিনি বারণ করছেন। এই ঝেড়ে-ফেলা থেকে শুরু করেছি, তারপর মেকআপ রেখেছি। সেট-সেটিংয়ের বদলে মানুষগুলো মুভমেন্ট দিয়ে বুঝিয়ে দেবে। এই ন্যাড়া স্টেজ দিয়েই আমি শুরু করেছিলাম, মেন উইদাউট শ্যাডোজ-এ। বাদলবাবুরা মানবশরীর দিয়ে স্পেসটাকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতেন। সেই টেকনিকে খানিকটা ফিরে যাওয়া, আর আধুনিক প্রেক্ষাপটে দেখতে চাওয়া। টেক্সট আর মানবশরীর ছাড়া, আর কিছুর দরকার নেই। এইরকম একটা জায়গা থেকে আমি করেছি। আমি যা শিখেছি সেটা প্রয়োগের চেষ্টা করেছি।
অভিজিৎ : ব্রেখটিয় পদ্ধতিতে প্ল্যাকার্ড লাগানো হচ্ছে, দর্শককে যেন মনে করানো হচ্ছে— দ্যাখো বাপু, তুমি কিন্তু একটা নাটকই দেখছ!
অঞ্জন : প্ল্যাকার্ডের মধ্য দিয়ে সিনের মানেটাও কিন্তু দর্শক বুঝে নিতে পারে। কারো একটা উক্তি বা বিখ্যাত কোনো গানের লাইন। পিঙ্ক ফ্লয়েড, বব ডিলান, হিটলার বা মার্ক্স— যে-কারো। থিয়েটারে তো শুধু থিয়েটারের লোক নেই, থিয়েটার সকলকে শামিল করে নেয়, সিনেমা-টিনেমা সবকিছুই আস্তে-আস্তে প্রভাব ফেলেছে থিয়েটারে। তাই বাইরের পৃথিবীটাকে একঝলক আনার চেষ্টা।
অভিজিৎ : প্রথম শোয়ে দেখেছিলাম দুই অ্যাক্টের মাঝে রক গিটার বাজছে। পঞ্চম শোয়ে দেখলাম মিউজিকের ব্যবহার বাড়ানো হয়েছে। দর্শকদের একটু ঝাঁকুনি দেওয়ার জন্য?
অঞ্জন : মিউজিকটা লাউড, মেকআপটাও বিচ্ছিরি, জামাকাপড়গুলো কেমন যেন যাত্রা-টাইপের— হচ্ছেটা কী? চারপাশে অস্বস্তিকর একটা পরিবেশ, কারণ সমাজে একটা অস্বস্তি, কেউ স্বস্তিতে নেই। পলিটিক্স ইত্যাদি সবকিছু অস্বস্তিকর। সেইজন্যেই করা যে দর্শকও যাতে স্বস্তিতে না থাকে। দর্শককেও একটা বিরক্তিকর জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। যখন শেষকাল আসছে, দর্শক ভাবছে, এবার শান্তি। সবশেষে দর্শক বেরিয়ে আসছে তৃপ্তি অথবা প্রশ্ন নিয়ে। এইটাই করার চেষ্টা।

অভিজিৎ : গত শোয়ে দেখলাম মুখ-মুখোশের লড়াই। নাটকের শেষ দৃশ্যের আগে আপনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুখের রং তুলে দিলেন। এটা কীসের দ্যোতক? লিয়ার স্টেজ থেকে নেমে আসছেন, নাকি অঞ্জন দত্ত মঞ্চকে বিদায় জানাচ্ছেন?
অঞ্জন : এটা আমরা শেষ দুটো শোয়ে করেছি। প্রথমে এটা ছিল না। আফশোস থেকে গেল, প্রথম থেকে এটা করলাম না কেন! এটা সম্পূর্ণ একটা অন্য ডাইমেনশনে নিয়ে যাচ্ছে। লিয়ার তো একটা ভাঁড়ের মতো ঘুরছিল, অবশেষে মানুষ হলো। মানুষ হয়ে মানুষের কাছে চলে গেল।
অভিজিৎ : ডিসপ্লেসমেন্টের অডিও-ভিস্যুয়াল’টা এবার কিন্তু খুব সুন্দর ভাবে দুই অর্ধ জুড়ে দেখানো হলো। দর্শকদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া কিন্তু দারুণ।
অঞ্জন : ডিসপ্লেসমেন্ট হলো, তারপর নাটকটা আবার ফিরে যাচ্ছে। প্রথমে ইন্টারভ্যালের আগে এটা হতো, কিন্তু মুশকিল হলো, ভিডিওর এফেক্ট উধাও হয়ে যাচ্ছিল ইন্টারভ্যালে। তখন আমরা ভাবলাম, ইন্টারভ্যালের আগে আদ্ধেকটা দেখাব, তারপর আস্তে করে ফেডআউট করে যাবে, তারপর যখন ফের পর্দা উঠল, আবার ফেরত এল।
অভিজিৎ : আপনার লিয়ারে এডগার— যে সততার প্রতীক, তাকে কালো করে দিয়েছেন; আর শঠ এডমান্ড— সে সাদা। এই বাইনারির তাৎপর্য?
অঞ্জন : আমি চেয়েছিলাম এডমান্ড বেশ ঝলমলে হোক। ও অসভ্যের প্রতীক, ম্যাকিয়াভিলিয়ান বদমায়েশ, নব্য নাৎসিরা যেমন। অন্যদিকে এডগার গরিব, কালো, সে ভিখিরিদের দলে ঢুকেছে। দলের অ্যাক্টররা এর মধ্যে অবশ্য সাদা-কালোর দ্বন্দ্ব দেখতে পাচ্ছে। অভিনেতারা অবশ্যই ভাবনাচিন্তা করুক!
অভিজিৎ : লিয়ার স্বাভাবিক ভাবেই ‘লিয়ার’-ময়, কিন্তু এই নাটকে সবক’টি চরিত্রকেই যথেষ্ট জায়গা দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে গ্লস্টার। এটা নিয়ে যদি বলেন!
অঞ্জন : এটা টেক্সটেই আছে। গ্লস্টারের চরিত্রটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ, যেন লিয়ারের অপর সত্তা। যেহেতু নাটকের নাম কিং লিয়ার, তাই লোকে ভাবে গ্লস্টার এত প্রাধান্য পাচ্ছে কেন?
অভিজিৎ : বছরখানেক আগে আপনি যখন লিয়ার করবেন বলে ঘোষণা করলেন, তখন ফেসবুকে বলেছিলেন যে যারা আসবে বলে আপনি আশা করেন, তারা যেন টেক্সটটা পড়ে আসে।
অঞ্জন : এটা যদি স্যামুয়েল বেকেট হত আমি বলতাম না। কিন্তু শেক্সপিয়র তো স্কুলেও পড়ানো হয়! পাঠ্য হাতের কাছেই পাওয়া যাবে। তিন মেয়ে, সোনা-রুপোর গল্প এটা নয়, তাই পড়ে এলে ভালো হয়। এটা অত্যন্ত চড়া দাগের নাটক।
অভিজিৎ : নাটকের শেষে এসে এই করাপ্ট, বদমায়েশ, লম্পট রাজাকে কি কোনওভাবে সহানুভূতি দেখালেন?
অঞ্জন : মানুষ আসলে কী, সেই খোঁজ চলেছে গোটা নাটকটা জুড়ে। সবকিছু হারিয়ে একটা খারাপ, বদমায়েশ লোকের আত্ম-উপলব্ধির গল্প। চারপাশে মানুষের বিপর্যয় অনুভব করে আস্তে-আস্তে সে মানুষ হয়ে উঠছে জীবনের শেষ পর্যায়ে। আমার কাছে এটা লিয়ার রাজার আধ্যাত্মিক এক যাত্রা বলা যায়।

পড়ুন দ্বিতীয় পর্ব- থিয়েটারের অঞ্জন : বার্লিন, ব্রেখট আর মৃণাল সেন
অভিজিৎ : লিয়ারকে বেছে নেওয়া কারণ হিসেবে আপনি বলেছিলেন, এই ভরা করাপ্ট সময়কে ধরতে গেলে লিয়ারই হচ্ছে সেরা টেক্সট। সেটাই একমাত্র কারণ? নাকি অঞ্জন দত্তের শেষ (ঘোষিত) মঞ্চাবতরণের জন্য লিয়ারই সবচেয়ে জুতসই চরিত্র?
অঞ্জন : শেষ নাটক হিসেবে প্রথমে ভেবেছিলাম ওয়েটিং ফর গোডো-র কথা। তারপর ভাবলাম ক্র্যাপ’স্ লাস্ট টেপ, একক অভিনয়ের নাটক। শেষে মনে হলো, একটা বড় মাপের চরিত্র করা উচিত। বর্তমান সময়ে মানুষের আত্মানুসন্ধান, নিজেকে খোঁজার ব্যাপারটা উধাও হয়ে গেছে। শান্তির মানে সহনশীলতা, ধৈর্য, ক্ষমা, সংযম। এগুলো হারিয়ে ফেলে দলাদলি, মারামারি, হানাহানি। ধিক্কারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সবকিছু হারিয়ে অবশেষে ধীরে-ধীরে নেমে আসে শান্তি। এই গল্পটা আমি কিং লিয়ারে পেয়েছিলাম।
অভিজিৎ : এই সফরটার মধ্যে একটা beyond আছে...
অঞ্জন : আমি চাই এটা দেখে দর্শকেরও একটা আত্মিক বিকাশ হোক! কী রেখে যাচ্ছি আমরা? প্রকৃতিকে ধ্বংস করে নির্মাণের স্পর্ধা। লোভ, ঘৃণা আর বিপর্যয়। যা চলছে, তাতে তো হিপি মুভমেন্ট ভালো ছিল! পৃথিবীর কী হবে? কোন দিকে চলেছে দুনিয়া?
মানুষ কতটা যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে, এই দিয়ে পথ-চলা শুরু করেছিলাম ‘মেন উইদাউট শ্যাডোজ’-এ। যাত্রাশেষে বলতে পারি, মানুষ যদি চুপচাপ নিজেকে অনুসন্ধান করে, অনুতাপে ভুগে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ায় অসুবিধা কী? আমি ক্ষমাশীলতায় মহত্ত্ব আরোপ করতে চেয়েছি। চারপাশে যখন স্থিতাবস্থা কায়েম হয় তখন সহিংসতার প্রয়োজন হয়তো থাকে, কিন্তু এখন এমনিতেই সমাজ এত হিংসাত্মক যে এখন প্রশমনের দরকার।
অভিজিৎ : বৃহত্তর এক আত্মিক পরিসরে উত্তরণ ঘটছে লিয়ারের। সেদিক থেকে দেখলে এই সিদ্ধান্তে বোধহয় আসা যায়, লিয়ার আপনার নাট্যজীবনের একটি অনিবার্য প্রযোজনা।
অঞ্জন : সমাজ-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বললে তা-ই। ‘মারা/সাদ’-এ সাদ মারা-কে বলে : তোমার বিপ্লব একটা যৌন উত্তেজনা! এই উত্তেজনার পর কী? কী হবে মারা-র? সাদ বোঝাতে চাইছে : তুমি ভুল করছ। একজন বলে : ফরাসি বিপ্লব ঠিক। আরেকজনের মন্তব্য : কোনো লাভ নেই, যারা বিপ্লব করছে সেই লোকগুলো পরের দিন কী করে দ্যাখো! দু'দিন সবুর করো।
আমার কাছে ভায়োলেন্স কোনও উত্তর হতে পারে না।
অভিজিৎ : শেষবারের মতো আপনি মঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, সেই লগ্ন আসন্ন। অভিনেতা হিসেবে না হোক, নির্দেশক হিসেবে আপনাকে কি এরপর আমরা পাব? বাংলা থিয়েটারের যে দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, তাতে একটি স্বতন্ত্র ও স্থায়ী অবস্থান আপনি অর্জন করেছেন। এই মুহূর্তে আপনার কী মনে হচ্ছে— যা করেছেন তা যথেষ্ট, না আরও কিছু করার ছিল?
অঞ্জন : আমার থিয়েটারের জগৎ সীমিত কারণ আমি কম কাজ করেছি। সিনেমা, থিয়েটার, গান অনেক কিছুই করেছি, সবকিছু যে খুব বড় স্কেলে করতে পেরেছি তা নয়। কোনও একটা জিনিসকে ধরে থাকলে আমি জানি আমাকে কিছু নিম্নমানের কাজ করে নিজেকে জাস্টিফাই করে ভালো কাজ করতে হবে। আমার এই ছোট সফরে এই কম্প্রোমাইজ আমি করিনি, কখনও বিশ্রি কিছু করিনি। এজন্য আমার কাজ সংখ্যায় কম, কিন্তু তার মান বোধহয় ভালোই।
অভিনেতা হিসেবে নিজেকে মঞ্চে না রেখে শুধু থিয়েটার ডিরেক্ট করাটা আমার পক্ষে মুশকিল। শুরুর দিকে শেখার জন্যে শুধু ডিরেক্ট করেছি। কিন্তু তারপর সবসময়েই আমি অভিনয় করছি। শুধু নির্দেশক হিসেবে কাজ করতে আমি অপারগ।
আমার থিয়েটার মানুষকে কী দেবে? একটু অন্যরকম থিয়েটারের মাধ্যমে কিছু তরুণকে একটু সাহস জোগাতে পারে মাত্র। এর বেশি হয়তো কিছু নয়।
আমার কোনও প্রভাব কি বাংলা থিয়েটারে আদৌ পড়েছে? বাংলা থিয়েটারে কি কারও মাথাব্যথা ছিল আমাকে নিয়ে? যেখানে বাদল সরকারই হারিয়ে গেছেন, আমার শিক্ষক হারিয়ে গেছেন, সেখানে আমি কে?
হয়তো স্বল্পসংখ্যক কিছু মানুষ আমায় মনে রাখবেন। এই-ই যথেষ্ট।




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp