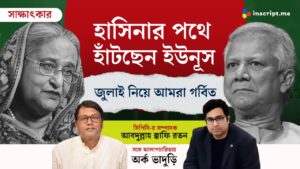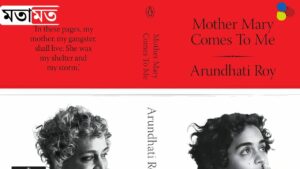থিয়েটারের অঞ্জন : বাদল সরকারই আমার থিয়েটারের শিক্ষক
Anjan Dutt Theatre: কে আমি? কেন আমি? কী করছি? এই যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ মাইসেল্ফ— আমার লজ্জা, আমার ভয়, আমার বিশ্বাস, আমার অবিশ্বাস, এইসব— এইগুলো খেলার ছলে এমনভাবে শিখিয়েছিলেন বাদল সরকার যে এসবে আমি খুব সড়গড় হয়ে উঠেছিলাম...
অঞ্জন দত্তের থিয়েটার নিয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারিতা করেছেন অভিজিৎ বসু৷ এই দীর্ঘ কথোপকথন ঠিক সাক্ষাৎকার নয়, বরং হয়ে উঠেছে অঞ্জনের থিয়েটারের দর্শন, রাজনীতি, শিল্পভাবনা এবং জীবনের টুকরো টুকরো নানা রঙের মিশেলে একটি দুর্দান্ত আড্ডা। আজ প্রথম পর্ব। অনুলিখন- সৌরভ সেন।
অভিজিৎ বসু : নমস্কার অঞ্জনদা, অনেক ধন্যবাদ আমাদের সময় দেবার জন্য। গোড়া থেকেই শুরু করা যাক! আপনার বেড়ে-ওঠা দার্জিলিং হিলস্ স্কুলে, আর আপনি জন্মেছেন এক বনেদি বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারে। এইরকম পরিবেশে অভিনয়, নাটক— এই ব্যাপারগুলো কীভাবে আপনাকে প্রভাবিত করল?
অঞ্জন দত্ত : দার্জিলিংয়ে জুনিয়র স্কুলে পড়ার সময় থেকেই আমি অভিনয় করি। খুব ভালো লাগত করতে। তারপর সিনিয়র স্কুলে থাকতেও সব নাটকে অভিনয় করেছি। স্কুলও খুব উৎসাহ জোগাত। যখন আরও সিনিয়র হয়ে গেলাম তখন প্রধান চরিত্র করতাম। স্কুলের থিয়েটার খুব সিরিয়াসলি হতো, মিউজিকাল হতো। শেক্সপিয়র, মলিয়ের, হ্যারল্ড পিন্টার করেছিলাম। ডাম্ব্ ওয়েটার করেছিলাম, এখনও মনে আছে। জুলিয়াস সিজার, টুয়েলফথ্ নাইট বা টেম্পেস্ট-এ আমি মেইন রোল করেছি।
অভিজিৎ : কলকাতায় যখন এলেন তখন নাটক নিয়ে আপনার যথেষ্ট জানা-বোঝা হয়ে গেছে!
অঞ্জন : হ্যাঁ, মানে অভিনয় করতে-করতে একটা ষোল বছরের ছেলের যতটা হয় আর কী! তবে আমি ভালো করতে পারতাম।
অভিজিৎ : আপনার সিরিয়াস লার্নিং অফ থিয়েটার বাদল সরকারের কাছে। ওই বয়সে ওর’ম একটা সিদ্ধান্ত নিলেন কী করে যে, আমি একজন প্রফেশনাল মানুষের কাছে অভিনয় শিখব? এই মাপের একজন সিনিয়র টিচারের কাছে নিজেকে একদম সঁপে দিলেন! আপনি তো এনএসডি-তেও যেতে পারতেন। সর্বভারতীয় স্তরে আপনার সমসাময়িক যাঁরা, তাঁরা তো প্রায় সকলেই সেখান থেকে বেরিয়েছেন। আপনি ওদিকে গেলেন না, এদিকে থাকলেন। এটা কি সচেতন সিদ্ধান্ত?
অঞ্জন : না, একেবারেই সচেতন নয়। আমি তো অভিনয় করতে চাইছি এবং মূলত সিনেমায় অভিনয় করতে চাইছি। ১৯৭০-এ আমি কলকাতায় আসি, ’৭২-এ যখন কলেজে ঢুকি তখন আমি ঠিক করে ফেলেছি যে আমি সিনেমায় অভিনয় করব। বাবা আইনজীবী ছিলেন, বাবার ইচ্ছে ছিল আমি বার অ্যাট ল’ হই। কিন্তু আমি কিছুতেই ল’ পড়ব না। সেটা নিয়ে বাড়িতে খানিক অশান্তিও হয়েছিল। এনএসডি বা এফটিআইআই-তে যেতে দিতে বাবা রাজি হলেন না, সিনেমা-থিয়েটারে ডিসকারেজ করলেন। পুনেতে তখন রোশন তানেজা-র মতো শিক্ষক, অসাধারণ এক মানুষ, কত বড়-বড় অ্যাক্টরদের শিখিয়েছেন এবং পরবর্তী কালে নাসির, শাবানা, ওম পুরী, স্মিতা এঁরা বেরিয়েছে। যাই হোক, আমি আশুতোষ কলেজে ঢুকলাম। বাবার ইচ্ছে ছিল সেন্ট জেভিয়ার’স্, কারণ বাবা সেখানকার প্রাক্তনী।
অভিজিৎ : আশুতোষে কোন সাবজেক্ট?
অঞ্জন : ইংলিশ। সেটাই সহজে পড়ে ফেলতে পারব বলে আমার মনে হয়েছিল।
তখন আমি খুঁজে চলেছি কলকাতায় কার কাছে অ্যাক্টিং শেখা যায়। তখন ওই ফার্স্ট ইয়ার, কী সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। নামমাত্র পড়াশুনো করছি। ঘনিষ্ঠ সঙ্গীসাথি, বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই নকশালবাড়িকে সমর্থন করছে। আমরা তখন ’৭০-এর দশকের ইউরো-আমেরিকান প্রভাবে ভেসে যাচ্ছি— ধোঁয়া, গাঁজা এসব— রক অ্যান্ড রোল মিউজিক ইত্যাদি— সেই কলকাতাটা আমার ওপর ভর করল— কলকাতার ওই স্পেস-টা ছিল, উদ্দেশ্যহীন ভেসে যাওয়ার— এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি করতাম— মেডিকেল কলেজ, সেন্ট জেভিয়ার’সের হস্টেলে— মেডিকেল কলেজের হস্টেলটা ছিল জুতসই জায়গা— এদের-ওদের সঙ্গে ঘুরছি। তো, তখন আমি জানতে পারলাম যে একজন আছেন, নাম বাদল সরকার, তিনি বিভিন্ন জায়গায় অ্যাক্টিং ওয়ার্কশপ করান। আমি তখন খুঁজে-খুঁজে বাদল সরকারের বাড়ি গেলাম।

অভিজিৎ : তারপর?
অঞ্জন : তিনি প্রথমে একদমই আগ্রহী হননি। আমাকে বললেন তিনি কোথায় একটা অ্যাক্টিং ওয়ার্কশপ করাচ্ছেন, সেখানে যেতে। আমি ওভাবে অনেকের সঙ্গে শিখতে চাইনি। আমি বলেছিলাম তিনি যদি আলাদা করে আমাকে প্রাইভেট টিউশন দেন! তিনি বেশ বিরক্ত হয়ে আমার কাছ থেকে অনেক টাকা চেয়ে বসলেন!
আরও পড়ুন-চিত্রাঙ্গদা: ঋতুপর্ণর আত্মকথনে জেগে থাকেন অঞ্জন দত্ত
আমি বাড়ি গিয়ে মায়ের কাছে কান্নাকাটি করলাম, মা অল্প কিছু টাকার বন্দোবস্ত করে দিলেন, প্রায় দেড় হাজার টাকা, ’৭০-এর দশকের গোড়ায় যেটা ছিল অনেক টাকা। আমি ওঁকে গিয়ে বললাম— এটা অ্যাডভান্স, এবার আমাকে শেখান। আমার বয়স তখন উনিশ-কুড়ি হবে। তিনি মুচকি হেসে ওঁর কাছে মাঝে-মাঝে যেতে বললেন। একটুখানি রেখে সেই টাকার প্রায় পুরোটাই আমার হাতে দিয়ে বললেন, মাকে গিয়ে ফেরত দিয়ো। সেই যে আমি ওঁর কাছে কিছুদিন গিয়েছিলাম, আমার অভিনয়-জীবনের গোটা পুঁজিটাই ওই ক’দিনের অর্জন। আমি যা কিছু শিখেছি, ওই ক’দিনেই।
অভিজিৎ : সেই ‘ক’দিন’টা কত?
অঞ্জন : নিখুঁত মনে নেই, তবে মাসকয়েক হবে। বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, বিভিন্ন খেলা, বিভিন্নতার মধ্য দিয়ে— কখনও তাঁর দলের থিয়েটারের শো হচ্ছে সেটা আমায় দেখাচ্ছেন, কখনও আলাদাভাবে। তিনি বুঝতেই পেরেছিলেন যে অভিনেতা হওয়ার একটা ইচ্ছে, একটা খিদে আমার আছে। তাই অনেক যত্ন নিয়ে, অনেক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে আমাকে পুষ্ট করেছিলেন। ওঁর কাছে শিখতে গিয়ে জেনেছিলাম তিনি থার্ড থিয়েটার করেন, ‘শতাব্দী’ নামে ওঁর থিয়েটার-দল আছে, তিনি গ্রোটোস্কির সঙ্গে মিশেটিশে এসেছেন পোল্যান্ডে, রিচার্ড শেখনারের খুব প্রিয়পাত্র, জুলিয়েন বেকের লিভিং থিয়েটারের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ। স্তানিস্লাভ্স্কির বইতে যা সব পড়েছি, সেই কনসেনট্রেশন, অবজারভেশন, ইমাজিনেশন ইত্যাদি, সেসব কিন্তু তিনি আমায় শেখাননি। তিনি দিতেন অন্য স্তরের একটা ট্রেনিং, যারা অ্যাক্টর হতে চায় না তাদেরও বোধহয় শিখলে কাজ দেবে। কিন্তু অ্যাক্টর হতে গেলে, একটা কমপ্লিট হিউম্যান বিয়িং হতে গেলে যেটা অত্যন্ত জরুরি তা হচ্ছে, নিজেকে জানা। প্রথমত এবং প্রধানত নিজেকে জানা। কে আমি? কেন আমি? কী করছি? এই যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ মাইসেল্ফ— আমার সোশাল রিয়েলিটি কী, আমার সঙ্গে তার কানেকশন কী, আমার লজ্জা, আমার ভয়, আমার বিশ্বাস, আমার অবিশ্বাস, এইসব— এইগুলো খেলার ছলে এমনভাবে শিখিয়েছিলেন যে এসবে আমি খুব সড়গড় হয়ে উঠেছিলাম।
একটা জিনিস আমি বাদল সরকারের সঙ্গে কাজ করতে-করতে বুঝে গেছিলাম যে, থিয়েটার আমাকে করতেই হবে। থিয়েটার না করলে হবে না। বাদল সরকারের স্ট্রিট থিয়েটার খুব উত্তেজিত করেছিল আমাকে। কিছুদিন নিজেরা ওইসব করার চেষ্টা করেছিলাম বন্ধুবান্ধব মিলে কিন্তু আমি প্রসিনিয়ামে চলে এলাম। আমার কাছে আলাদা করে অফ্-প্রসিনিয়াম খুব উন্নত থিয়েটার বলে মনে হয়নি। মানে বাদলদার কাজকে এতটুকু অশ্রদ্ধা না করেও বলছি, আমার কাছে নাটকের টেক্সটের মতন সেই নাটককে মঞ্চে দেখতে চাওয়াটাও গুরুত্বের ছিল। বাদলদার কাছে অফ্-প্রসিনিয়ামে যাওয়াটা দার্শনিক দিক থেকে জরুরি ছিল।
অভিজিৎ : যাকে বলে ‘ব্রিংগিং থিয়েটার অন দ্য স্ট্রিট’?
অঞ্জন : হ্যাঁ, যেখান থেকে থার্ড থিয়েটারের জন্ম। কিন্তু আমি তাতে জয়েন করিনি, শতাব্দীতেও যাইনি। আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে থিয়েটার করতে আরম্ভ করি, নিজে। কারণ বাদল সরকার আমাকে স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করতে শিখিয়েছেন এবং তার সঙ্গে আরও অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়েছেন।

অভিজিৎ : এই যে একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা আপনার হয়েছে বাদলবাবুর সঙ্গে কাজ করে, সেটা কোনও ইন্সটিটিউটে গিয়ে তো আপনার হতো না...
অঞ্জন : এভাবে হতো না কিন্তু একজন অভিনেতার একটা সঠিক প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যাওয়া উচিত। যখন নাটক করতে এলাম, আমার চারপাশে তখন দিকপাল মানুষদের থিয়েটার আমি দেখছি। উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র, অজিতেশের নান্দীকার প্রভৃতি। কিন্তু তারা যেভাবে বিদেশি নাটকের বঙ্গীকরণ করেছে, তাতে আমার আপত্তি আছে। অর্থাৎ যে-কালজয়ী টেক্সট ফরাসি বিপ্লব নিয়ে হচ্ছে, বাঙালি দর্শককে সহজে বোঝানোর জন্যে ভারতীয় কোনও বৈপ্লবিক পটভূমিকায় তা ফেলা যাবে না, ফরাসি বিপ্লব নকশালবাড়ি নয়। বিদেশি চরিত্র যদি বাংলায় কথা বলে তাহলে অসুবিধেটা কোথায়? উৎপল দত্তের লেনিন তো বাংলায় কথা বলছে! শেক্সপিয়রের মার্চেন্ট অফ ভেনিসে কেউ তো ইতালিয়ান ভাষায় বলছে না! সবাই তো ইংরেজিতে বলছে। নাটকে সাহেব চরিত্ররা বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারে, যা সিনেমায় সম্ভব নয়। এটা নাটকের সবথেকে বড় সুবিধে। নাটকের দর্শক অনেক কিছুকে কল্পনা করে নিতে পারে। এটাই নাটকের জোরের জায়গা।
দ্বিতীয় পর্ব- থিয়েটারের অঞ্জন : বার্লিন, ব্রেখট আর মৃণাল সেন
অভিজিৎ : আপনি সিনেমার অভিনেতা হতে চেয়েছিলেন এবং সেই অভিনয়টা শিখতে গিয়ে বাদলবাবুর সঙ্গে আপনার যোগাযোগ। আবার বাদলবাবুর কারণেই থিয়েটার!
অঞ্জন : থিয়েটার। সিনেমাটা না হয়ে থিয়েটারটা হলো।
অভিজিৎ : কিন্তু এগুলো পুরোটাই ঘটছে একটা ইচ্ছে থেকে, একটা খিদে থেকে। একটা ছোট্ট প্রশ্ন, আপনি থিয়েটারটাকে একজন পরিচালকের দৃষ্টিতে কবে থেকে দেখতে শুরু করলেন?
অঞ্জন : পরে। বাদল সরকার বলেছেন, থিয়েটার আর সিনেমার তফাত হচ্ছে যে একটা দল যারা নাটক করছে, আরেকটা দল যারা নাটক দেখছে— একটা বিশেষ দিনে, বিশেষ জায়গায়, বিশেষ সময়ে একত্রিত হবে এবং কিছু একটা ঘটবে! এটা সিনেমায় হবে না। এটা আমি আমার উনিশ বছর বয়সে বুঝতে পেরে গেছি। আমার কাছে যেটা ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে— কী ঘটছে বিশেষ জায়গায়? আবার রোজ কিন্তু একই জিনিস হচ্ছে না, বদলে-বদলে যাচ্ছে। এই বদলে যাওয়াটাও থিয়েটার।
আরও পড়ুন-অঞ্জনের প্রিয় বন্ধু: শিকড়হীন আর শিকড়গাঁথাদের সংলাপ
বাদলবাবুর সঙ্গে মিশে, লেখাপড়া করে যেটা আমি বুঝলাম যে একটা নাটক, একটা টেক্সট, একজনের লেখা নাটক— বানিয়ে-বানিয়ে কথা হবে না— বানিয়ে-বানিয়ে ‘ভোমা’-ও হচ্ছে না, ‘মিছিল’-ও হচ্ছে না, সব একটা ‘লেখা জিনিস’, বানিয়ে-বানিয়ে কিছু হচ্ছে না। হয় সেটা ককেশিয়ান চক সার্কেল হচ্ছে, বা হয় সেটা অন্য কিছু হচ্ছে, বা ভোমা হচ্ছে। কাজেই সেটা একটা টেক্সট, আর টেক্সট নিয়ে কাজ হচ্ছে। এবার পরস্পরের মধ্যে মুখোশ খোলা হচ্ছে, না পরস্পরের কাছে আসছে, কত দূরে যাচ্ছে, সেটা আমার কাছে আর ফ্যাক্টর হচ্ছে না। সুতরাং টেক্সট আমার কাছে ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে গেল! তাহলে সেই টেক্সটটা কী? বাদল সরকার বলছেন— অভিনেতার দল যে-ইনফর্মেশনটা বয়ে নিয়ে গিয়ে দেবে দর্শককে, দর্শকও তাতে সংযুক্ত হবে এবং একটা কিছু ঘটবে! কিছুক্ষণের জন্য কিছু ঘটবে— আনন্দ, ইনফর্মেশন দেওয়া-নেওয়া হবে। এই ইনফর্মেশনটা যদি একটা টেক্সট হয়ে যায়! সেটা বিশ্বাস থেকে হবে। দর্শকের বিশ্বাস, অভিনেতাদের যে-দলটা তাদের বিশ্বাস, তাদের ধ্যানধারণা এবং যদি থার্ড থিয়েটারই ধরি, সেটা হচ্ছে পৃথিবীর কষ্ট, মানুষের জীবন, সেই দুঃখ, কষ্ট এবং ক্ষুধা!

অভিজিৎ : তাহলে আপনি বলছেন, টেক্সটটাই সব? শেষ কথা?
অঞ্জন : হ্যাঁ, তা-ই। এবার প্রশ্ন হলো, আমার টেক্সটটা তাহলে কী হবে? আমার টেক্সটটা তো উৎপল দত্তের বিশ্বাস হতে পারে না! উৎপল দত্ত যে টেক্সটটা করছেন সেটা আমার বিশ্বাস না-ও হতে পারে। আমি দেখলাম, মোটেই হচ্ছে না। আমার টেক্সটটা তো শম্ভু মিত্রের বিশ্বাস নয়! আমার যেটা বিশ্বাস, সেই টেক্সটটা খুঁজতে আরম্ভ করলাম আমি। আমার নিজের নাটক নামানোর আগে, দলটল করে একটু এক্সপেরিমেন্ট করলাম আমরা কিছুদিন, বাদলদার ফর্মটা নিয়ে। এবং থিওসফিকাল সোসাইটিতেই। এখান-ওখান থেকে স্কেচ, কোলাজ নিয়েটিয়ে, যেটা বাদলদা করতেন এবং শতাব্দী ও আরও যারা করত, কোলাজ টাইপের থিয়েটার, গান ইত্যাদি। কিন্তু যা করছি তাতে আমি খুশি হতে পারছিলাম না। আমি দেখলাম যে এটা হচ্ছে না, আমার আরও জোরালো টেক্সট দরকার। তাই ১৯৭৮-এ যখন আমি কার্যত প্রথম নাটক করলাম, আমি সেই টেক্সটটাই নিলাম যেটা আমি বিশ্বাস করি। সেই বিশ্বাস থেকেই জাঁ-পল সার্ত্রের ‘মেন উইদাউট শ্যাডোজ’ আমি ঠিক করলাম। এই টেক্সটটা আমার টেক্সট।
আরও পড়ুন-‘মৃণাল সেনের চোখে দেখেছি আমার শহর’: কথাবার্তায় অঞ্জন দত্ত
অভিজিৎ : আপনি কিন্তু প্রথম থেকেই ইউরো-আমেরিকান টেক্সটের কাছেই নিয়ে যাচ্ছেন। মানে আপনি সেই অর্থে যাকে বলে দেশজ থিয়েটার সেদিকে ঘেঁসছেন না, আপনি ক্লাসিক করার কথা ভাবছেন না, আপনি গিরিশ ঘোষ করতে যাচ্ছেন না...
অঞ্জন : এমনকী বাদল সরকার করার কথাও ভাবছি না, যদিও সেটা খুবই উঁচুদরের।
অভিজিৎ : সেই ইউরোপেই ফেরত যেতে হচ্ছে, সঙ্গে কিছুটা আমেরিকাতেও। এটা তো একটা জার্নি! সেই সফরটা কীরকম?
অঞ্জন : আমি সেই স্কুল-বয়স থেকেই ইউরোপিয়ান থিয়েটার পড়তে আরম্ভ করেছি। আর্থার মিলার পড়েছি। কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র আমি, আমার টেক্সটের মধ্যে রয়েছে আর্থার মিলার, আছে জন অসবোর্ন-এর ‘লুক ব্যাক ইন অ্যাংগার’। আমার থিয়েটার পড়তে আরম্ভ করে দিয়েছি, আমার টেক্সটের মধ্যে শেক্সপিয়র, আমার টেক্সটের মধ্যে বেস্ট অফ দ্য থিয়েটার রয়েছে। তাই যখন পাকাপাকিভাবে ঠিক করলাম যে প্রসিনিয়াম থিয়েটার করব এবং প্রসিনিয়ামের যা-যা আমি শিখেছি সেই সমস্ত টেকনিক দিয়ে করব, তো আমার চেহারাটা তখন ডিরেক্টরের চেহারা হয়ে গেল!
এবার, টেক্সট বাছা কার কাজ? — ডিরেক্টরের। সেটাকে ট্রানস্লেট করার কথা কার?— ডিরেক্টরের। আমি ট্রানস্লেট করতে আরম্ভ করলাম, বাংলায়। তো আমি এমন-এমন কাজ করতে লাগলাম যার জন্য কিন্তু আমি মায়ের গয়না বেচে সিনেমার অ্যাক্টর হব বলে কাউকে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলিনি যে আমায় শেখান! সেখান থেকে আমি ক’বছর পরে যখন থিয়েটার করছি তখন একজন নাট্যনির্দেশকের মতোই আমার ভাবনাচিন্তা। আমি একটা টেক্সট চাইছি, আমি ট্রানস্লেট করতে চাইছি, আমিই ঠিক করছি কোনটা করব। কামু, সার্ত্র, কাফকা, না পিরান্দেলো— কী করব? এইসব পছন্দ মাথায় ঘুরছে। এটুকু বুঝতে পারছি যে টেক্সটটা ইম্পর্ট্যান্ট না হলে আমি কী কমিউনিকেট করছি? সেই চিন্তাটাও মাথার মধ্যে বসে আছে। সুতরাং অবধারিতভাবেই আমি তখন ভেবেচিন্তে আমার বিশ্বাসে অস্তিত্ববাদ বা এক্সিস্টেনশিয়ালিজম, তা সেমি-লেফটিস্ট বা যা-ই হোক, আমি যে-থিয়েটারে বিশ্বাস করি, আমার যা বিশ্বাস, মতাদর্শ, মানুষের প্রতি বিশ্বাস— সেই মানুষের সংকট নিয়ে আমি থিয়েটার করতে গেলাম। সার্ত্রের ‘মেন উইদাউট শ্যাডোজ’।
যারা বাদল সরকারের সঙ্গে ঘুরেছে, বাদল সরকারের সঙ্গে কাজ করেছে, বাদলদার নাটক দেখতে গেছে— এমন অনেকে একত্রিত হলাম এবং আমি ট্রানস্লেট করলাম, আমাকে ডিরেক্ট করতে হলো। আমি যদি ডিরেক্ট করি তাহলে অভিনয় করা যাবে না। মানে আমি দুটো কাজ একসঙ্গে করতে পারব না। তখন আমার বয়স কতই বা হবে! ওই বয়সে আমি এটা লিখলাম, ট্রানস্লেট করলাম। অন্যেরা অনেকে হয়তো আমায় পাত্তা দেবে না এবং তাদের থিয়েটারও আমি দেখছি, ঠিক আছে, আমার কিন্তু খুব একটা ভালো লাগছে না। আমি মোটেই উত্তেজিত হচ্ছি না উৎপল দত্তের নাটকে, কেমন যেন গিমিক মনে হচ্ছে! শম্ভু মিত্র দেখে রোমাঞ্চিত নই, সেকেলে লাগছে। তবে হ্যাঁ, নান্দীকারের নাটক বেশ নাড়া দিচ্ছে, কারণ তারা পৃথিবীর নানারকম নাটক করছে। কিন্তু তারা কেন বাংলায় পুরো জিনিসটাকে নিয়ে আসছে! কেন তারা চরিত্রগুলোকে বিদেশি রেখে বাংলা কথা বলছে না? আন্তিগোনে যখন করছে তখন ক্রেয়ন-আন্তিগোনে করছে, কিন্তু যখন ইবসেন বা চেখভ করছে তখন তারা কিন্তু নোরা, লোপাখিন করছে না।
আরও পড়ুন-মৃণালের অঞ্জন অঞ্জনের মৃণাল
বাদল সরকার ভারতের একজন বরিষ্ঠ নাট্যকার। কিন্তু আমি তাঁর নাটকের চাইতেও বড় মাপের নাটক করতে চাইছি। এদেশের নাট্যকার বাছতে হলে আমি বাদলদাকেই পছন্দ করতাম, কিন্তু আমি আরও বড় মাপের কিছু খুঁজছিলাম— সার্ত্র বা অন্য কেউ, যাঁদের কাছ থেকে বাদল সরকারও নিয়েছেন। ইওনেস্কো, বেকেট ছাড়া বাদল সরকারের নাটক হয় না। বেকেট বা ইওনেস্কো গুলে না খেলে ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ লেখা যায় না। ‘মেন উইদাউট শ্যাডোজ’-এ আমার থিয়েটারের বক্তব্য আর এর উপস্থাপনার ভঙ্গির মধ্যে একটা সাযুজ্য থাকতে হবে। ইতোমধ্যে কিছু বই হাতে এসে পড়ছে, ‘টুওয়ার্ডস্ আ পুওর থিয়েটার’, এটা-সেটা, আমি রিচার্ড শেখনারের নাটক দেখে ফেলেছি এরিনা-তে— ‘মাদার কারেজ...’ এসেছে, দেখেছি— বাদল সরকারের সঙ্গে আমরা নাটক করতে গেছি, দেখেছি। পিটার ব্রুকের নামটা শুনেছি, পড়ছি-টড়ছি একটু। কিন্তু একটা মানুষকে নিরাবরণ করে নিঃসীম শূন্যতায় গিয়ে জিজ্ঞাসা : মানুষ মানে কী? আমি কে? এই ‘আমি কে’-র সন্ধানই হচ্ছে ‘মেন উইদাউট শ্যাডোজ’।

তৃতীয় পর্ব- থিয়েটারের অঞ্জন : লিয়ার আমার জীবনে অবশ্যম্ভাবী ছিল
তথাকথিত রাজদ্রোহীদের একটি দল। তারা ধরা পড়েছে আর কিছু নির্যাতক নাৎসি তাদেরকে টর্চার করছে। “বলো তোমাদের লিডার কোথায় আছে, বললে ছেড়ে দেব।” এরা বলবে না, আর ওরা বলাবে! সার্ত্রের গল্পটাতে ‘কে বলবে, কে বলবে না’ এটা থাকছে না, থাকছে কতটা যন্ত্রণা, কতটা নির্যাতন এরা সহ্য করবে। কীভাবে বলাবে? না যন্ত্রণা দিয়ে, নির্যাতন করে। কতদূর অত্যাচার মানুষ শুধু তার বিশ্বাসের জন্য সহ্য করতে পারে, কতটা যন্ত্রণা নিতে পারে— এতেই কি মানুষের পরিচয়? মানুষকে অনাচ্ছাদিত করা হচ্ছে, তার সমস্ত কিছু সরে যাচ্ছে তখন! কেবল রয়ে যাচ্ছে তার শরীর, তার যন্ত্রণা, তার বিশ্বাস।
এ-ই যদি হয়, তাহলে কস্টিউমের কী দরকার? স্টেজের লাইট কী দরকার? কার্টেন ফেলার কী দরকার? মিউজিকেরও তো কোনও দরকার নেই! একেবারে ন্যাড়া। সজ্জাহীন। Bare। যতটা করা যায়। অডিয়েন্সে আলো জ্বালিয়ে দাও! সেখানেও আলো জ্বলুক!
আমরা এমনটাই করেছিলাম। এটা এসেছিল টেক্সট থেকে, আমি যেমনটা বুঝেছিলাম। অডিয়েন্স এসে দেখছে আলো জ্বলছে। আলো নিভছে না। বীভৎস টর্চার। যন্ত্রণা আর অত্যাচার। লোকে স্রেফ নিতে পারল না। মুক্তাঙ্গনে হয়েছিল— প্রচুর লোকের অস্বস্তি— অনেকে নাটক দেখতে-দেখতে বেরিয়ে গেছিল। “বিচ্ছিরি! ভাল্লাগছিল না।”
তা এই ছিল আমার প্রথম নাটক, ‘স্বীকারোক্তি', সাল ১৯৭৮। রীতিমতো টিকিট বিক্রি করে হয়েছিল। আমি তখন স্টেটসম্যান-এ ঢুকেছি। স্টেটসম্যানের নাট্য-সমালোচক ধরণী ঘোষ আমাদের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। আরেক নাট্য-সমঝদার শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিস্তর প্রশংসা করলেন। বুঝলাম, ঠিক রাস্তাতেই আছি।
চলবে...




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp