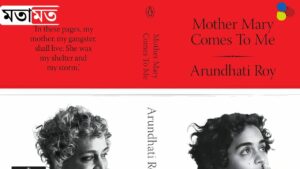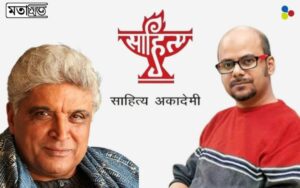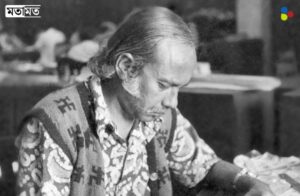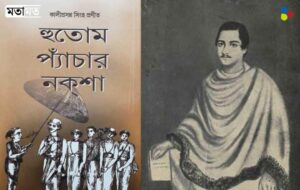বানু মুশতাকের ‘হার্ট ল্যাম্প’: মেয়েলি প্রতিরোধের আশ্চর্য ধরনধারণ
Banu Mushtaq The Heart Lamp Review: জিনাতের মনে হয় মুসলমান হিসাবে তারা শিখে এসেছে মুজাহিদের পুঁজ, ঘা এইসমস্ত কিছু জিভ দিয়ে চেটে পরিষ্কার করলেও জিনাতের ঋণ মিটবে না।
বানু মুশতাকের ‘হার্ট ল্যাম্প: সিলেকটেড স্টোরিস’ (মূল ভাষা: কন্নড়, ইংরেজিতে অনুবাদক: দীপা ভাস্থি, প্রকাশক:পেঙ্গুইন র্যান্ডম হাউস, ইন্ডিয়া) এই বছরের আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কার পেয়েছে। বইটির পেছনের মলাট থেকে জানতে পারি, বইটির মধ্যে সংকলিত গল্পগুলি ১৯৯০ থেকে ২০২৩-এর মধ্যে কন্নড়ে লেখা। একজন সাংবাদিক, আইনজীবি এবং সমাজকর্মী হিসেবে বানু মুশতাক দক্ষিণ ভারতের মুসলিম নারীদের রোজকার যে জীবন দেখেছেন এবং জড়িয়েছেন, গল্পগুলি সেই দীর্ঘ জড়িয়ে থাকা এবং দেখার ভঙ্গি থেকেই উঠে এসেছে। তাই মুশতাকের গল্পগুলি জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছটফটে পোলাপান, ডাকাবুকো দাদি, বুরবক মৌলবী, ঠগ ভাই-বেরাদর, প্রায়-বেচারা স্বামী এবং হরেক কিসিমের মায়েরা যারা সবকিছুর পরেও সংবেদনশীল। বইয়ের পেছনের মলাটে এই হ্যাশট্যাগ জাতীয় বিষয় পাঠক হিসেবে আমাকে খুব আতঙ্কিত করে। বাংলা ভাষায় একটি আত্মকথার হ্যাশট্যাগে দলিত নারী, জীবন সংগ্রাম, ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধিতা ইত্যাদি ইত্যাদি হ্যাশট্যাগ দেখে বই কিনে তিরিশ পাতা পরে গিয়ে পড়েছি যে আত্মকথক গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছেন, তিনি মোটেও নিম্ন বংশজাত নন, যথেষ্ট উঁচুঘর; অবস্থার ফেরে আজ দলিত মাত্র এবং তাঁর মায়ের গায়ের ফর্সা রঙ চিনিয়ে দেয় তাঁর উচ্চ বংশ। তাই পেছনের মলাটের প্রান্তিকতার হ্যাশট্যাগকে আমি খুব সন্দেহের চোখে দেখি, কারণ কেন্দ্রভোগী প্রকাশক খুব ভালো করেই জানেন কোন প্রান্তিকতা কেন্দ্রীয়ভাবে বিক্রয়যোগ্য। সাম্প্রতিক কালে ইংরেজি অনুবাদে পড়া মালায়ালি লেখক এস হরিশের অসামান্য উপন্যাস ‘মুসটাশ্’, আরেকজন মালায়ালি লেখক শীলা টোমির ‘ভাল্লি’, কিংবা কিছু বছর আগেই আন্তর্জাতিক বুকার পাওয়া হিন্দিতে লেখা মণিপুরি লেখক গীতাঞ্জলি শ্রী-এর 'টোম্ব অফ স্যান্ড’ কিংবা নাগা লেখক ইস্টেরাইন কিরের ‘হোয়েন দ্য রিভার স্লিপ্স’ —কারওই বইয়ের পেছনের মলাটে এই হ্যাশট্যাগ জাতীয় শব্দ রেখে বিক্রির চেষ্টা ছিল না। তাই খানিক সন্দেহ নিয়ে এবং খুব বেশি আশা না রেখে বইটি পড়তে শুরু করি।
প্রথম গল্প ‘স্টোন স্ল্যাবস ফর শায়িস্তা মহল’-এর প্রথম আট-দশটা লাইনের পর থেকেই আমাকে বানু মুশতাক পাকড়াও করে ফেলেন। গল্পের শুরুতেই কথক জিনাত জনৈক মুজাহিদের বদলির খবরে খুব খুশি হয়। এরপর জিনাতের মনে হয় পাঠকের সঙ্গে তো মুজাহিদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া দরকার। মুজাহিদকে জিনাতের ঘরওয়ালা হিসাবে পরিচিত করাতে গিয়ে তার মনে হয় ঘরওয়ালি যতটা গ্রহণযোগ্য শব্দ, ঘরওয়ালা কেমন জানি শোনাচ্ছে। মুজাহিদকে নিজের আপিসওয়ালা হিসাবে পরিচিত করাতে গিয়ে তার মনে পড়ে অফিসটাই তো মুজাহিদের, তার নয়। একবার ভাবল যে, মুজাহিদকে যজমান বলে ফেলা যাক। তারপরেই মনে পড়ল, তাহলে তো নিজেকে যজমানের ঝি ভাবতে হয়, ওইটুকু ডিগ্রি আছে তার যেখানে একটা মেয়ের নিজেকে ঝি ভাবলে একটু খারাপ লাগে। ‘পতি’ বলতেই পারত, কিন্তু কে রোজকার জীবনে ‘পতি’ বলে পরিচয় করিয়ে দেয় শুনি! এদিকের লোকজন ‘দেবারু’ বলে একটা শব্দ ব্যবহার করে ঠিকই, কিন্তু সেখানে দেবত্বের মহিমা রয়েছে খানিক, মুজাহিদকে এতটাও উঁচু আসন দেওয়ার কোনও দরকার নেই। এমনিতেই জিনাতের মনে হয় মুসলমান হিসাবে তারা শিখে এসেছে মুজাহিদের পুঁজ, ঘা এইসমস্ত কিছু জিভ দিয়ে চেটে পরিষ্কার করলেও জিনাতের ঋণ মিটবে না। মুজাহিদ যদি মাতাল হতো, বউ পেটাত, বেল্লেলাপনা করে বেড়াত— তারপরেও জিনাতের স্বামীই থাকত।
আরও পড়ুন- বোনেরা চাইছে মুক্তি|| কমলা ভাসিনের বাজনার বোল থেকে কবিতার বোলচাল
এই মজাদার থাপ্পড় দিয়ে যে বই শুরু হয় তা প্রথম থেকেই একটি ব্যাপার পরিষ্কার করে দেয়— গল্পবলিয়ের খপ্পড়ে পড়তে চলেছি, গল্প বলতে বলতে যে দেখাতে থাকবে সেই সব ক্ষত, পুঁজ যা দেখেও না দেখার ভাণ করি আমরা। তাই জিনাতকে যখন মুহাজিদ বাংলোর সামনের কাঁঠাল গাছ, লেবু গাছ, চন্দ্রমল্লিকা, জুঁই, ডালিয়া আর বাংলোর পেছনের কারিপাতা, লতিয়ে থাকা করলা এসবের মাঝে ফেলে চলে যায় রোজ কর্নাটক ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ স্টেশনে গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ করতে জিনাত হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। পিতৃতন্ত্র নিয়ে বাঁকা হাসি আর নারীর নিজস্ব জগতকে পরিমিত গীতিময়তার মাধ্যমে এক আশ্চর্য রাজনৈতিক বোধ পাঠকের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন বানু।
এই রাজনৈতিক বোধ থেকেই জন্ম নেয় ‘ব্ল্যাক কোবরাস’-এর মতো গল্প। আশরাফ এক হতদরিদ্র মাঝবয়সি মা। আশরাফের বর আশরাফকে ছেড়ে অল্পবয়সি এক মেয়ের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। নিজের পোলাপানের জন্য খাবার, ওষুধ এইসব জোগাড় করতে নাজেহাল হয়ে উঠে আশরাফ শেষমেশ যায় সেই গ্রামের ‘মুতাওয়াল্লি’র কাছে। মুতাওয়াল্লি এমন একটি ধর্মীয় পদ, যে পদে আসীন ব্যক্তির দায়িত্ব হলো গ্রামের কোনও মুসলমান অভাবে থাকলে তার রোজকার জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তা সেই মুতাওয়াল্লি আশরাফকে সাহায্য করতে অস্বীকার করে। এই অস্বীকার গ্রামের মেয়েদের ধর্ম রক্ষার্থেই এক হতে বলে এবং ধর্মের জন্যই মেয়েরা প্রতিবাদ শুরু করে। প্রতিবাদের ধরনটাও খুব রাজনৈতিক। এক মহিলা চিল্লে বলে যে, মুতাওয়াল্লির গলায় কালো কালো সব গোখরো। আরেক মহিলা মুতাওয়াল্লিকে ঢিল ছুঁড়ে মারে এবং ভাণ করে মুতাওয়াল্লির দিকে এগোতে থাকা নাপাক কুকুরকে তাড়াতে গিয়েই এই বিপত্তি। ইসলামকে ব্যবহার করেই পিতৃতন্ত্রকে প্রতিরোধের এই গল্প আমাদের তথাকথিত উদারপন্থাকেও ইসলামকে দেখার চোখ পাল্টাতে বলে।

বানু মুশতাকের গল্পের বহুস্তরীয় প্রভাব এখানেই। এমন বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই জন্ম নেয় ‘রেড লুঙ্গি’। রাজিয়া বলে এক মায়ের, তার চেয়েও বেশি করে রাজিয়া বলে এক নারীর গল্প। গল্পের শুরুই হচ্ছে গরমের ছুটি রাজিয়ার মতো নারীর ক্ষেত্রে এক বিভীষিকার সময় বলে। লতিফ আহমেদ আর রাজিয়া থাকে লতিফের পৈতৃক বাড়িতে। রাজিয়ার নিজের ছয়টি সন্তান। গরমের ছুটি পড়লে এই বাড়িতে ছুটি কাটাতে এসে জোটে লতিফের ভাইয়ের ছেলেপুলে, কোনও কোনওবার রাজিয়ার বোনের পোলাপান। রাজিয়ার নিজের ভাষ্য অনুযায়ী এই বাড়িতে আগে থেকেই ছয়খান আজাইরা মাল আছে, আর সব কয়টা দেবরের দু'টা করে, তিনটা করে সন্তান। সব কয়টা একসঙ্গে হাজির হবে গরমের ছুটিতে আর বোনও তো এবার পাঠিয়ে দিয়েছে নিজেরগুলোকে। গোটা দিন ধরে আঠেরোটা বাচ্চা কাঁইমাঁই করে, ছেলেগুলোর বাঁদরামি করে বেশি, রাজিয়ার মাইগ্রেন চাগাড় দিতে থাকে। রাজিয়া ঠিক করে তাকে বাঁচতে হবে। বাঁচার পদ্ধতি হিসাবে রাজিয়ার বেছে নেওয়া বুদ্ধি বানু মুশতাকের রাজনৈতিক মোটিফ স্পষ্ট করে। রাজিয়া ঠিক করে এদের চুপ করাবার একটাই উপায়— খৎনা। আঠারোটা ইবলিশের মধ্যে আটটা মেয়ে হওয়ার কারণে ছাড় পায়, চারটা চ্যাংড়া পিচ্চি-ইবলিশ ছাড় পায় বয়স আট অতিক্রম না করায়। কিন্তু ছয়খানা দামড়া চ্যাংড়াকে পাকড়াও করা হয় এবং রাজিয়ার মর্জিতে সায় দেয় লতিফও। লাল কাপড়, জরি সব কিনে আনা হয় খৎনার জন্য লুঙ্গি সেলাই করতে। কিছু কাপড় বেঁচে গেলে রাজিয়া ঠিক করে বাড়ির আশেপাশের গরিবগুর্বো চ্যাংড়াগুলোকেও পাকড়াও করে খৎনা করাবে। ওদের লুঙ্গিতে খালি জরির কাজ থাকবে না। খৎনার দিন যত এগোতে থাকে দামড়া চ্যাংড়াগুলোর মুখ ও গলার স্বর শুকোতে থাকে। প্রচণ্ড ট্রমাটাইজড হয়ে পড়ে কেউ কেউ। পুরুষ হয়ে ওঠার ধর্মীয় প্রতীককে একজন নারীর নিজের ব্যক্তিগত জীবনের শান্তি বজায় রাখার পদ্ধতিতে পর্যবাসিত করা যে নারীবাদের বিকল্প পাঠক্রমের সন্ধান দেয়, তা বানু মুশতাক আমাদের ভাবতে বলেন। ভাবতে বলেন আপাত মানবিক বহিরঙ্গ নিয়েও। ‘আ ডিসিশন অফ দ্য হার্ট’ গল্পের ইউসুফ কিছুতেই নিজের বউ আখিলাকে তালাক দিতে পারে না। পাঠক হিসেবে আমরা আবিষ্কার করি, ইউসুফ আখিলাকে ভালোওবাসে না, ভয়ও পায় না। তাহলে ইউসুফ তালাক দিতে পারে না কেন? গল্প দেখায়, ইউসুফ বেজায় ভয় পায় আখিলার ভাইদের। তার দৃঢ় বিশ্বাস তালাক দিলেই আখিলার ভাইগুলো তাকে মেরে পাট পাট করে দেবে। টিকে থাকা বিয়ে যে মূলত উভমুখী একটি পিতৃতন্ত্র তা কী সূচারুভাবে দেখিয়ে দেন বানু!
আরও পড়ুন- আন্তর্জাতিক সম্মান জয়! তাও কেন এই তিন ভারতীয়কে অভিনন্দন জানাননি মোদি?
আর এই গল্পজগত বুনতে গিয়ে বানু ভারতীয় কথক ভঙ্গিমাটিকেই বেছে নিয়েছেন। ফলে গল্পের মধ্যে অতীত, বর্তমান এক বাক্যের মধ্যেও আঁটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। একই গল্পের ভিতর তিন-চার রকম আখ্যান ভঙ্গিমা রেখেছেন, ফলে গল্পটি একইসঙ্গে একের এবং অনেকের এই বোধ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। গল্প দুলতে দুলতে এগিয়েছে। এগিয়েছে দুপুরবেলা বাড়ির সব কাজ সেরে, খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে চুল শুকোতে শুকোতে পান চিবুতে চিবুতে যে ভঙ্গিতে কথা বলেন একজন ভারতীয় নারী সেই ভঙ্গিমায়। ফলে গল্পে খুব সোচ্চার কিছু নেই, রয়েছে অনায়াস মেয়েলিযাপন। বানুর আখ্যানের মূল শক্তিই হলো এই মেয়েলিপনা। ‘হার্ট ল্যাম্প’ গল্পের তিন বাচ্চার মা মেহেরুন স্বামী পরিত্যক্তা হওয়ার পর অনেক ভাবার পরে পারিবারিক জীবনের মানে খুঁজে না পেয়ে গায়ে কেরোসিন ঢালে। সেই সময় তার মেয়ে সালমা যখন তার কাছে আকুতি করে আত্মহত্যা না করতে, মেহেরুন আবিষ্কার করে স্রেফ মেয়ের জন্যও সে বেঁচে থাকতে পারে, পুরো একটি জীবন কোনও পুরুষ ছাড়াই। এই মেয়েলিপনার উদযাপনই বানু মুশতাকের সবচেয়ে বড় শক্তি। শেষে এসে আবিষ্কার করি, পেছনের মলাটের ওই হ্যাশট্যাগ জাতীয় কথাগুলিকেই বানু মুশতাকের লেখা বাঁকা হাসি দিয়ে দেখছে। এই সাবাটোজই একটি বইয়ের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সাফল্য।




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp