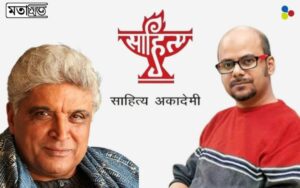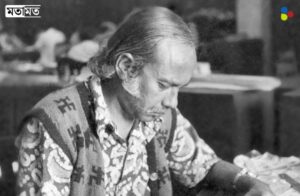শান্তিনিকেতনের বর্ষা: বিপর্যয়কে পূর্ণতায় শমিত করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ
Monsoon in Shantiniketan: রবীন্দ্রনাথও শান্তিনিকেতনে জীবনযাপনের অন্যরকম এক পথ কেটেছিলেন। সেই ধর্মপথের মূল শর্ত ছিল মানুষ প্রকৃতিকে ধ্বংস করবে না, জয় করবে না— প্রকৃতির সঙ্গে সহবাস করবে।
আগে বাঙালি অর্জন ও উপার্জন করত। এখন বাঙালি খরচ করে। আগের অর্জন ও উপার্জনও খরচ হয়ে যাচ্ছে। ভাঁড়ে যে কী থাকছে এখনই বলা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে হারানো সময়ের কাছে বাঙালি যায়! সেই যাওয়ার জায়গায় শান্তিনিকেতন এখন ‘বিবি নম্বর ওয়ান’। ধর্মও হলো জিরাফও হলো। ধর্ম সবার এক নয়। একদলের ধর্ম নিকটবর্তী দেবীপীঠ। শাক্তধর্মের তো এখানে রমরমা। এই মায়ের অঙ্গের এ-খানি পড়েছে ওখানে তো সে-খানি পড়েছে সেখানে। তাই নিয়ে জনধর্ম, পুজোপাঠ, রক্তটীকা। ধর্মের আরেক রূপও অবশ্য আছে। সেখানে ধর্ম আর জিরাফের সমন্বয় আরেক রকম। ধর্মের নাম রবীন্দ্রনাথ জিরাফের নাম নয়াবাদ— এ আবাদ কিন্তু চাষাবাদ নয়। নিও লিবারেল অর্থনীতির সৌজন্য শান্তিনিকেতনে ও তার চারপাশে যে হাই-এন্ড ট্যুরিজম গড়ে উঠেছে আবাদ সেখানে। জিরাফে থাকতে খারাপ লাগার কথা নয়। লম্বা গলা। ভারতের থেকে দূরে সুদূর ইন্ডিয়ায় অন্তর্বর্তী হয়ে থাকা যায়। মাটিতে কী হচ্ছে গলার উপরে তার আঁচ লাগে না তেমন, অভিযোজনের কী মহিমা। তবে উভয়ে থাকতে গেলে ধর্মের খবর লাগে, নিতান্তই খবর— যাপন নয়।
ধর্ম বলতে এখানে সাম্প্রদায়িক বৈধী জনবাদী ধর্মের কথা বলছি না, একেবারে মূলে যেতে চাইছি। ধৃ-ধাতু থেকে আসা শব্দ ধর্ম, যা আমাদের ধারণ করে তাই ধর্ম। শান্তিনিকেতনকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথ এই ধর্মের অনুশীলন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর বাংলা ভাষায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত কমলা বক্তৃতার শিরোনাম ‘মানুষের ধর্ম’। সেই মানুষের ধর্মের মূল কথাই হলো এই প্রাকৃতিক অভিযোজন বাইরের, পশুজগতের মতো পশুমানুষেরও তেমন অভিযোজন হয়েছে। তবে সেখানেই মানুষ থেমে যায়নি। মানুষ, প্রকৃত ধর্মশীল মানুষ, মনের জগতে অভিযোজিত হয়েছে। সেই অনিঃশেষ অভিযোজনই মানুষের অভিযোজন। তাই মানুষের ধর্ম। মানুষের রয়েছে পথ, মানুষ সেই পথ কাটতে কাটতে চলেছে।

আরও পড়ুন- হেমন্তকে এড়িয়ে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ?
রবীন্দ্রনাথও শান্তিনিকেতনে জীবনযাপনের অন্যরকম এক পথ কেটেছিলেন। সেই ধর্মপথের মূল শর্ত ছিল মানুষ প্রকৃতিকে ধ্বংস করবে না, জয় করবে না— প্রকৃতির সঙ্গে সহবাস করবে। এই যে সহবাসের আদর্শ তারই সূত্রে তো ব্রহ্মচর্যাশ্রমে তপোবনশিক্ষার পুনর্নিমাণ ঘটাতে চেয়েছিলেন তিনি। বিশ শতকের একেবারে গোড়ায় যা ছিল পুনর্নির্মাণের স্বপ্ন তাই ক্রমে হয়ে উঠল পুনর্নবীকরণের প্রকল্প। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রকৃতিলগ্ন পরিসরে যেহেতু ছ'টি ঋতুর আসা-যাওয়া ধরা পড়ত সুস্পষ্টভাবে সেহেতু ক্রমেই শান্তিনিকেতনে আয়োজন করা হলো ঋতু উৎসবের। সেই উৎসবের মধ্যে প্রাচীনের রীতি যেমন ছিল, তেমনই মিশে ছিল নবীনের গীতি। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের ঋতু উৎসব মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলেমিশে থাকার ধর্ম। সেই ধর্মপালনে সম্প্রদায় বিশেষের দেব বা দেবী মূর্তি লাগে না।
হালের বাঙালিদের কাছে অবশ্য শান্তিনিকেতনের ঋতুযাপন প্রকৃতির সঙ্গে মিলে-মিশে যাওয়ার উপায় নয়। হাই-এন্ড ট্যুরিজমের দৌলতে গান আছে, পান আছে, রিমিঝিম আদিগন্ত বৃষ্টি আছে আর হাতের কাছে আছে সর্ববিদ্যাবিশারদ গুগল। অন্তর্জাল জানিয়ে দেবে রবিঠাকুরের জীবৎকালে শান্তিনিকেতনে বর্ষা কীভাবে যাপিত হতো। জানিয়ে দেবে এখানে বর্ষার উৎসব কী? বৃক্ষরোপণ আর হলকর্ষণেই এখানে বর্ষায় মাটির গন্ধ এসে লাগে। উগ্রজাতীয়তাবাদী বিশ্বযুদ্ধের পর নেশনতন্ত্রের বিরোধী রবীন্দ্রনাথ ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতে পল্লীপুনর্গঠনের যে কাজ শ্রীনিকেতনে শুরু করেছিলেন, তারই সূত্রে ১৯২২-এ হলকর্ষণের অনুষ্ঠান। শান্তিনিকেতনের রেডিওতে সকালবেলায় এখন যে রবীন্দ্রগীতি বাজে মাঝেমাঝে ‘ফিরে চল, ফিরে চল, ফিরে চল মাটির টানে’ সেই টানেই এই উৎসবের সূচনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘হলকর্ষণ’-এ জানিয়েছিলেন, ‘কৃষির মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছে। পৃথিবীর গর্ভে যে জননশক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল সেই শক্তিকে আহ্বান করেছে। ’ আর বৃক্ষরোপণ? ১৯২৮। পিয়ারসন পল্লীতে একটি বকুল গাছের চারা লাগিয়েছিলেন কবি। তারপর ১৯৩৬ সাল থেকে এই উৎসব নিয়মিত বাৎসরিক অনুষ্ঠানের রূপ পেয়েছিল। নাচ-গান-বৈদিক মন্ত্রে-নৃত্যে ঘেরা সেই সব দিন। বিধুশেখর শাস্ত্রী আর ক্ষিতিমোহন সেন এই দু'জন রবীন্দ্রনাথের উৎসবের পরিকল্পনাকে সাজিয়ে দিতেন আদি-ভারতের মন্ত্র আর উপচারে।

তখন এসবই জীবন যাপনের অঙ্গ। আশ্রমিকদের চিন্তা-ভাবনার বিষয়। পরাধীন দেশে কৃষি-অর্থনীতির তো অন্যরকম মানে ছিল। এখন অবশ্য এসবই শান্তিনিকেতনে ধর্ম ও জিরাফ যাপন করতে আসা পরিযায়ীদের দৃশ্যবস্তু। তা খারাপ কী? অন্য কিছুর থেকে তো এসব দেখা ভালো। ভালোই। বিশেষত শান্তিনিকেতনের বর্ষা! ভুবনডাঙার মেঘলা আকাশ তো এককালের কৃত্তিবাসের কবিদের কী প্রিয় ছিল! বাঙালির সাংস্কৃতিক মানচিত্রের অংশ হয়ে উঠেছিল তা। সুনীলের থেকেও শক্তি বর্ষাযাপনে অনেক বেশি উত্তাল। যখন লেখেন ‘আজানুকেশ ভিজিয়ে নিচ্ছ আকাশ-ছেঁচা জলে’ তখন হয়তো তাঁর মনের চোখের সামনে শান্তিনিকেতনের গোয়ালপাড়া ভেসে উঠেছিল। সেখানে ভারি-ব্যাপক বৃষ্টিই তো দেখার মতো তখন পড়ত। এখনও পড়ে, তবে দেখার নিরাপদ-আশ্রয় দু'পাশে গজিয়ে ওঠা পর্যটন-পরিসরের আবাসগুলি।
আরও পড়ুন- অনন্ত বিরহের বর্ষায় বৃষ্টি লুকোয় যে ‘রেইনকোট’

রবীন্দ্রনাথের ঋতু উৎসবে বাইরের কথার মধ্যে ভেতরের কথাটাই আসল। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন বর্ষাকালে আমাদের নানাখানা মন একখানা হয়ে যায়। সেই একীভূত মন থাকে বলেই তো বর্ষা পাগলিনী রাধার অভিসারের ঋতু। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বর্ষার উৎসবে খরচ আর জমার হিসেব দুয়ের মধ্যে সাম্যাবস্থা আনতে চেয়েছিলেন। লিখেছিলেন,
‘পৃথিবীর দান গ্রহণ করবার সময় লোভ বেড়ে উঠল মানুষের। অরণ্যের হাত থেকে কৃষিক্ষেত্র জয় করে নিলে, অবশেষে কৃষিক্ষেত্রের একাধিপত্য অরণ্যকে হঠিয়ে দিতে লাগল। নানা প্রয়োজনে গাছ কেটে কেটে পৃথিবীর ছায়াবস্ত্র হরণ করে তাকে দিতে লাগল নগ্ন করে। তাতে তার বাতাসকে করতে লাগল উত্তপ্ত, মাটি উর্বরতার ভাণ্ডার দিতে লাগল নিঃস্ব করে। অরণ্যের-আশ্রয়-হারা আর্যাবর্ত আজ তাই খরসূর্যতাপে দুঃসহ।এই কথা মনে রেখে কিছুদিন পূর্বে আমরা যে অনুষ্ঠান করেছিলুম সে হচ্ছে বৃক্ষরোপণ, অপব্যয়ী সন্তান-কর্তৃক লুণ্ঠিত মাতৃভাণ্ডার পূরণ করবার কল্যাণ-উৎসব।’
আমাদের যে মন খরচ করতে চায় সে মন নানাখানা, আর যে মন পূরণ করতে চায় সে মন একখানা। নানাখানা মনের লোভেই আমরা ধর্মেও ছুটি জিরাফেও ছুটি। রবীন্দ্রনাথ কৃষির ক্ষয়কে, অরণ্যের বিপর্যয়কে বৃক্ষরোপণের পূর্ণতায় শমিত করতে চেয়েছিলেন। সেই চাওয়া থেকেই তাঁর বর্ষার শান্তিনিকেতনে এই দুই উৎসব। তথ্য, অন্তর্জালের তথ্য, এসব সত্য বলে না।
এই সত্যের কাছে হাত পাতা চাই এই বর্ষায়। গতর খাটানো যে শ্রমিক, সভ্যতার লোভে রিক্ত হয়ে ওঠা যে পৃথিবীর গতর দু-য়ের জন্যই চাই বৃক্ষরোপণের অবসর। সেই অবসর পেলে তবেই তো আবার ভরে উঠবে ধরা। খরুচে-রিক্ততাদায়ী নব্য-উদার অর্থনীতি সে-অবসর দেয় না। সেই অবসরের পক্ষে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সেই অবসরের পক্ষে ছিলেন কার্ল মার্ক্স। বর্ষা সেই অবসরের, আলস্যের ঋতু।




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp