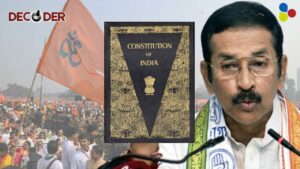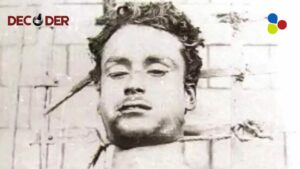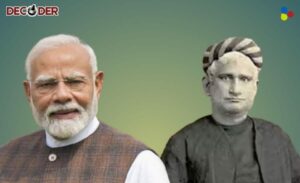নেহরু-নৈতিকতার বিসর্জন! ভারতের বিদেশনীতিতে দ্বিচারিতার যে ছায়া
India's Foreign Policy: যে ভারত একসময় নিরস্ত্রীকরণ, মানবাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে নেতৃত্ব দিত, সে আজ অস্ত্র ও নজরদারি চুক্তির মোহে নিজেদের নীতিগত ভিত্তি বিসর্জন দিচ্ছে।
বর্তমান ভারতের বিদেশনীতি এক সংকটের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। স্বাধীনতার পর ভারতের কূটনৈতিক দর্শন ছিল নীতিনিষ্ঠ, অহিংস এবং গ্লোবাল সাউথের প্রতি সহমর্মিতার ভিত্তিতে। কিন্তু আজকের বিদেশনীতি ক্রমাগতভাবে প্রতিরক্ষা-কেন্দ্রিক, প্রতিযোগিতামূলক ও জোট নির্ভর হয়ে উঠছে। ফলে ভারত একদিকে মার্কিন প্রভাব বলয়ে অংশগ্রহণ করছে, অপরদিকে রাশিয়া ও ব্রিকস-এর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে গিয়ে দ্বৈত ভূমিকার ফাঁদে আটকা পড়ছে। এই নীতির ফলে ভারতের আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব প্রশ্নের মুখে পড়েছে। একসময় জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি এবং প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু প্যালেস্টাইনের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমর্থন করেছিলেন। ১৯৮৮ সালে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে ভারত ছিল প্রথম দেশগুলোর অন্যতম। কিন্তু সাম্প্রতিক গাজা যুদ্ধের সময় ভারত কেবল ইজরায়েলপন্থী অবস্থানই নেয়নি, প্যালেস্টাইনের পক্ষে জাতিসংঘে ভোট দিতেও বিরত থেকেছে। যে নীতি নিয়ে একসময় 'নৈতিক বিদেশনীতি' বলে গর্ব করা হতো, তা আজ অস্ত্র ব্যবসা, নজরদারি প্রযুক্তি এবং কৌশলগত অবস্থানের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছে।
ইজরায়েলের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ২০২৩ সালে প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে, যার বড় অংশই প্রতিরক্ষা ও নজরদারি প্রযুক্তিনির্ভর। পেগাসাস স্পাইওয়্যার থেকে শুরু করে বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা— এইসব চুক্তি ভারতের বিদেশনীতিকে ক্রমেই মূল্যবোধহীন বাস্তববাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এমনকী যখন ইজরায়েলের আক্রমণে গাজায় হাজার হাজার বেসামরিক মানুষ নিহত হচ্ছে, তখনও ভারত নীরব দর্শকের ভূমিকায় থেকে গেল। ভারত সরকার জাতিসংঘের জরুরি অধিবেশনে অস্ত্রবিরতি চেয়ে প্রস্তাব আনা থেকে বিরত থেকেছে, যা আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। জাতিসংঘে ভারতের ভোটদানের প্যাটার্ন ইঙ্গিত দেয় যে ভারত এখন ফিলিস্তিনকে নয়, বরং কৌশলগত অংশীদার ইজরায়েলকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বিশ্লেষকদের মতে, এই অবস্থান ভারতকে আরব বিশ্বে বিশ্বাসযোগ্যতা থেকে বঞ্চিত করছে এবং গ্লোবাল সাউথ-এর মধ্যেও ভারতের নৈতিক অবস্থানকে দুর্বল করে তুলছে। যে ভারত একসময় নিরস্ত্রীকরণ, মানবাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে নেতৃত্ব দিত, সে আজ অস্ত্র ও নজরদারি চুক্তির মোহে নিজেদের নীতিগত ভিত্তি বিসর্জন দিচ্ছে।
আরও পড়ুন- মাস্কের স্টারলিঙ্ক ইন্টারনেট ভারতীয়দের নিরাপত্তা বিকিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত?
নেহরুর সময়ে ভারত আফ্রিকার উপনিবেশ বিরোধী সংগ্রামে ছিল সক্রিয় অংশীদার কিন্তু আজ আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অনেকটাই কৌশলগত এবং চিনা প্রভাব ঠেকানোর লক্ষ্যে প্রভাব বিস্তারমূলক। ২০২৩ সালের জি-২০ সম্মেলনে আফ্রিকান ইউনিয়নকে সদস্যপদ দিয়ে ভারত প্রশংসা কুড়িয়েছে ঠিকই কিন্তু আফ্রিকায় প্রকৃত বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ভারত এখনও চিনের ধারে-কাছে নেই। ফলে ভারতের 'দক্ষিণের নেতা' হিসেবে পরিচিতি এখন আর নিঃসন্দেহ নয়। ব্রিকসের (ব্রিকস একটি আন্তঃসরকারি সংস্থা, যা দশটি দেশ নিয়ে গঠিত— ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন, দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর, ইথিওপিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইরান এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি) ধারণা ছিল একটি বহুমুখী বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার। কিন্তু ভারত এখন একইসঙ্গে কোয়াডের (কোয়াড একটি গোষ্ঠী, যা অস্ট্রেলিয়া, ভারত, জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে গঠিত এবং এটি সদস্য দেশগুলোর মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়) সামরিক সহযোগী এবং ব্রিকসের অংশীদার হয়ে দ্বৈত ভূমিকায় পড়েছে। চিনের আধিপত্য ঠেকাতে ভারত ব্রিকস সম্প্রসারণে দ্বিধা প্রকাশ করেছে, যা রাশিয়া ও গ্লোবাল সাউথের দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের দূরত্ব তৈরি করছে।
আফগানিস্তানে তালিবান ফেরার পর ভারতের অবস্থান দ্ব্যর্থপূর্ণ। একদিকে ভারত তালিবান শাসনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদ জানিয়েছে, নারী শিক্ষার ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং সংবাদমাধ্যমের দমন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। অপরদিকে, দোহা ও মস্কো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তালিবানের সঙ্গে পরোক্ষ যোগাযোগও বজায় রেখেছে— যা আফগান ভূখণ্ডে ভারতীয় কূটনৈতিক ও নিরাপত্তা স্বার্থরক্ষার এক বাস্তবতামূলক পদক্ষেপ হলেও আদর্শগত দিক থেকে দ্বৈততা প্রকাশ করে। ভারত তালিবান সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়নি, তবে কাবুলে টেকনিক্যাল মিশন পুনঃস্থাপন করেছে। এই অবস্থান ‘ব্যাকডোর কূটনীতি’-র পরিচয় দেয়, যেখানে নীতিগত প্রতিবাদ ও বাস্তব নিরাপত্তা-স্বার্থ একসঙ্গে চালানো হচ্ছে। তবে এর ফলে ভারতের পূর্ববর্তী বিশাল উন্নয়ন প্রকল্প— যেমন আফগান পার্লামেন্ট ভবন, জরঞ্জ-দেলারাম মহাসড়ক, ও স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ এখন কার্যত অবরুদ্ধ বা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। ভারতের রাজনৈতিক প্রভাবও সংকুচিত হয়েছে কারণ নতুন আফগান প্রশাসনে পাকিস্তানপন্থী গোষ্ঠীর প্রভাব বেশি। বিশ্লেষকরা মনে করেন, আফগানিস্তান ইস্যুতে ভারতের দ্ব্যর্থপূর্ণ নীতির ফলে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ায় ভারতের কৌশলগত অবস্থান দুর্বল হয়েছে এবং ভারত দীর্ঘমেয়াদি বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে। বর্তমান ভারতের বিদেশনীতি ক্রমেই প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা-কেন্দ্রিক হয়ে উঠছে, যা অতীতের আদর্শভিত্তিক কূটনীতির বিপরীতে একটি নতুন ধারা প্রতিষ্ঠা করছে।
স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (SIPRI) তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ভারতের অস্ত্র আমদানির ৬৫ শতাংশ এসেছে রাশিয়া ও ফ্রান্স থেকে। এই পরিসংখ্যান কেবল প্রতিরক্ষা নির্ভরতার মাত্রাই প্রকাশ করে না, এক গভীর কূটনৈতিক শূন্যতার ইঙ্গিতও দেয়। ভারতের সঙ্গে ইজরায়েল, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক চুক্তি ও যৌথ মহড়া বর্তমানে ভারতের বৈদেশিক সম্পর্কের প্রধান চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। মালাবার (যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে), বরুণ (ফ্রান্সের সঙ্গে), ইন্দ্র (রাশিয়ার সঙ্গে) এবং কোয়াড-এর আওতায় সামরিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা— এসবই নির্দেশ করে যে ভারতের কূটনীতি এখন প্রায়ই প্রতিরক্ষা সহযোগিতার ছায়াতলে আবদ্ধ। বিশ্লেষকরা বলছেন, এই প্রবণতা ভারতকে এক সামরিক জোটনির্ভর রাষ্ট্রে পরিণত করছে, যেখানে স্বতন্ত্র কূটনৈতিক নেতৃত্ব, দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা এবং জাতিসংঘ-ভিত্তিক শান্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ক্রমশ গুরুত্ব হারাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, কোয়াড-এর ক্ষেত্রে ভারত মূলত একটি নিরাপত্তাভিত্তিক জোটের অংশ, যার উদ্দেশ্য চিনের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা। একই সময়ে, ভারত আবার ব্রিকস বা সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের (SCO) মাধ্যমে চিন ও রাশিয়ার সঙ্গেও সংযুক্ত—ফলে দ্বৈত ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে, যা ভারতের বিদেশনীতিতে দ্ব্যর্থতা তৈরি করছে।
ভারতের প্রতিরক্ষা-কেন্দ্রিক বিদেশনীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা হলো নজরদারি ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রযুক্তিতে বিদেশি নির্ভরতা। ইজরায়েলি পেগাসাস স্পাইওয়্যার কেনা, ফ্রেঞ্চ রাফাল যুদ্ধবিমান, রাশিয়ান এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা— এসব প্রযুক্তি ভারতকে প্রতিরক্ষা সক্ষমতায় শক্তিশালী করেছে ঠিকই কিন্তু সমালোচকরা মনে করেন, এসব চুক্তি প্রায়শই অনুগত বিদেশনীতির বিনিময়েই হয়েছে। একই সঙ্গে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে ক্রমাগত উত্তেজনা এবং সীমান্ত সমস্যাও ভারতের প্রতিরক্ষাকেন্দ্রিক মানসিকতাকে বাড়িয়ে তুলছে। চিনের সঙ্গে সীমান্তে গালওয়ান সংঘর্ষ কিংবা পাকিস্তানের সঙ্গে নিয়মিত সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন— এসব ইস্যুতে কূটনৈতিক আলোচনার বদলে সামরিক প্রতিক্রিয়া ক্রমেই বেশি হয়ে উঠছে। এর ফলে নেপাল, বাংলাদেশ, ভুটান কিংবা মায়ানমারের মতো ছোট প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের সম্পর্কেও এক ধরনের অবিশ্বাস তৈরি হচ্ছে, কারণ তারা ভারতকে আর কূটনৈতিক আলোচনার নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসেবে দেখছে না, বরং প্রতিরক্ষাশীল ও চাপ প্রয়োগকারী শক্তি হিসেবে দেখতে শুরু করেছে। এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠে আসে যে, ভারতের প্রতিরক্ষা-কেন্দ্রিক বিদেশনীতি কি একটি কৌশলগত বাস্তবতা, না কি এটি আসলে এক গভীর কূটনৈতিক দুর্বলতার প্রতিফলন? একটি মতানুযায়ী, যেখানে বিদেশনীতি রাজনৈতিক আদর্শ, অর্থনৈতিক আন্তঃনির্ভরতা এবং সাংস্কৃতিক কূটনীতির সমন্বয়ে পরিচালিত হওয়া উচিত, সেখানে শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার ওপর নির্ভরতা একটি একমুখী এবং শেষ পর্যন্ত অস্থিতিশীল কূটনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি করে। বিশ্ব রাজনীতিতে যে দেশগুলো দীর্ঘমেয়াদে নেতৃত্ব দিতে পেরেছে, তারা প্রতিরক্ষা সক্ষমতার পাশাপাশি ন্যায়ভিত্তিক বিদেশনীতি, কূটনৈতিক সংলাপের সংস্কৃতি এবং বহুস্তরীয় সম্পর্ক গঠনের দক্ষতা দেখাতে পেরেছে। ভারতের জন্যও এটাই সময় এই প্রতিরক্ষা-নির্ভর কূটনৈতিক প্রবণতা পর্যালোচনা করে নতুন করে ভাবার যে, নেতৃত্ব শুধু শক্তি নয়, নীতিতেও নিহিত।
চিন-ভারত সীমান্ত পরিস্থিতি বর্তমানে দক্ষিণ এশিয় ভূ-রাজনীতির অন্যতম উদ্বেগজনক ক্ষেত্র। ২০২০ সালের গালওয়ান উপত্যকার সংঘর্ষে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ২০ জন জওয়ানের মৃত্যু এবং চিনেরও অজ্ঞাত সংখ্যক হতাহতের ঘটনার পর উভয় দেশের সম্পর্ক এক গভীর কূটনৈতিক সংকটে পড়ে। দুই দেশ একাধিক দফায় সামরিক ও কূটনৈতিক বৈঠক করলেও প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় (LAC) উত্তেজনা প্রশমিত হয়নি। বরং চিন একতরফাভাবে অরুণাচল প্রদেশের কিছু অংশকে 'ঝাংনান' নামে চিহ্নিত করে নিজেদের মানচিত্রে দেখাচ্ছে, সেখানে সেতু, রাস্তা ও ঘাঁটি নির্মাণ করে স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। এদিকে কাশ্মীর উপত্যকায় ধারাবাহিকভাবে সশস্ত্র সংঘর্ষ, নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান এবং পাকিস্তানের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ রেখায় (LoC) গোলাগুলি চলছে। ভারত-পাক অধিকৃত কাশ্মীর ইস্যুতে কঠোর অবস্থান নিচ্ছে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণার পর জম্মু ও কাশ্মীরের আন্তর্জাতিকীকরণ রোধে কূটনৈতিক প্রচার চালাচ্ছে। তবে, এই অভ্যন্তরীণ সংকট ও চিনের আগ্রাসী ভূকৌশলগত আচরণের মুখে ভারতের প্রতিক্রিয়া প্রায় পুরোপুরি প্রতিরক্ষাকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। ভারত সীমান্তে ফৌজ বৃদ্ধি, রাস্তা নির্মাণ, যুদ্ধাস্ত্র মোতায়েন এবং UAV নজরদারি বাড়ালেও রাজনৈতিক সমঝোতার পথে খুব একটা অগ্রসর হয়নি। LAC ও LoC উভয় এলাকায় ঘন ঘন সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন এবং সীমান্তে বারংবার 'স্ট্যান্ড-অফ' পরিস্থিতি জন্ম নিচ্ছে। একদিকে ভারতের এই প্রতিক্রিয়া প্রতিরক্ষা প্রয়োজনে যৌক্তিক হলেও, অন্যদিকে প্রতিবেশীদের কাছে এটি এক আত্মকেন্দ্রিক, প্রাধান্য প্রয়াসী এবং আস্থাহীন রাষ্ট্রের চিত্র নির্মাণ করছে।
আরও পড়ুন- নেতানিয়াহু ট্রাম্পের নাগালের বাইরে! প্রমাণ ইরান আক্রমণ
নেপাল, ভুটান ও মায়ানমার— এই তিন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গেও ভারতের সম্পর্ক গত এক দশকে জটিল হয়ে উঠেছে। নেপাল ২০২০ সালে নতুন মানচিত্রে কালাপানি, লিপুলেখ ও লিম্পিয়াধুরাকে অন্তর্ভুক্ত করে ভারতের ভূখণ্ডকে নিজেদের বলে দাবি করে। ভারত এই মানচিত্র প্রত্যাখ্যান করলেও, তার আগে কোনও কার্যকর কূটনৈতিক পর্যালোচনা বা আলোচনার উদ্যোগ ছিল না। ভুটানে চিনের অনুপ্রবেশ মোকাবিলায় ভারত কৌশলগত সহায়তা দিলেও রাজনৈতিক সমঝোতার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা সীমিত। মায়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থানের পর ভারত এক 'সতর্ক নীরবতা' বজায় রেখেছে— যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ থেকে বিরত থাকার এক প্রতীক।এই ভূকৌশলগত সংকটগুলোর পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও ভারতের সরকারের হিন্দুত্ববাদী প্রবণতা এবং সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে দমননীতি প্রতিবেশী মুসলিম প্রধান দেশগুলোর মধ্যে ভারতের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ করেছে। বাংলাদেশে সিএএ ও এনআরসি-র প্রভাব, পাকিস্তানে কাশ্মীর নীতির সমালোচনা এবং মলদ্বীপে হিন্দু জাতীয়তাবাদ বিরোধী 'India Out' প্রচার ভারতের আঞ্চলিক গ্রহণযোগ্যতায় চিড় ধরাচ্ছে। প্রাক্তন বিদেশ সচিব শিবশঙ্কর মেনন এক আলোচনায় বলেন,
“Without a credible political process and diplomatic imagination, military assertion alone cannot secure India’s neighborhood.”
এ পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে, ভারতের সীমান্ত এবং নিরাপত্তা ইস্যুতে প্রতিক্রিয়া দ্রুত সামরিকীকরণের রূপ নিচ্ছে কিন্তু রাজনৈতিক সংলাপ ও আস্থাবহ কূটনৈতিক চেষ্টার ঘাটতি ভারতকে এক বিচ্ছিন্ন আঞ্চলিক শক্তিতে পরিণত করছে। বহু বছর ধরে যে 'বড় ভাই' ও নেতৃত্বের ভূমিকা ভারত পালন করেছে, তা আজ অনেক প্রতিবেশীর চোখে পরিণত হয়েছে এক কঠোর, একমুখী এবং প্রভাব বিস্তারী রাষ্ট্রে। ভারত সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নিজেকে 'বিশ্বগুরু অর্থাৎ গ্লোবাল সাউথের নৈতিক নেতা ও বিকল্প শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মোদি সরকারের ভাষণে, জি-২০ সভাপতিত্বের ব্যাখ্যায়, কিংবা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারত নিজেকে উন্নয়নশীল বিশ্বে ন্যায়, টেকসই ও সংযুক্তকারী নেতৃত্বের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরছে। কিন্তু এই আদর্শচর্চার পেছনে বাস্তব কর্মকাণ্ড অত্যন্ত সীমিত এবং প্রায়শই আত্মরক্ষামূলক ও অবস্থাননির্ভর। ২০২৩ সালের জি ২০ শীর্ষ সম্মেলনে আফ্রিকান ইউনিয়নকে স্থায়ী সদস্যপদ দেওয়া ভারতীয় কূটনীতির জন্য তাৎপর্যপূর্ণ কৃতিত্ব হলেও, বৃহত্তর গ্লোবাল সাউথের পক্ষ থেকে উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলো— যেমন ঋণ মকুব, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য জলবায়ু অর্থায়নে নতুন প্রতিশ্রুতি এবং প্রযুক্তি স্থানান্তরের নীতিমালা—এগুলোর কোনওটির ক্ষেত্রেই ভারত বিশেষ কোনও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেয়নি। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর কাঠামোগত সংস্কার সম্পর্কে ভারত মুখে সমর্থন জানালেও, জি-২০ বিবৃতিতে এসব নিয়ে কার্যত কোনও সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার নিশ্চিত করা যায়নি। এ বিষয়ে আফ্রিকার একাধিক প্রতিনিধির অভিযোগ ছিল, ভারত মার্কিন এবং ইওরোপিয় অবস্থানের সঙ্গে আপোস করেই সংহতির নামে শূন্যতাকে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এছাড়া, জলবায়ু ন্যায়বিচারের প্রশ্নেও ভারত দ্বৈত ভূমিকা পালন করেছে। একদিকে নিট শূন্য নির্গমনের লক্ষ্যের কথা বলছে, আবার অন্যদিকে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপে আপত্তি জানিয়েছে। ভারত নিজে ২০৩০ সাল পর্যন্ত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা করেছে, অথচ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশকে সবুজ জ্বালানির অনুশাসনে আনতে আন্তর্জাতিক চাপকে মদত দিয়েছে।
বিশ্লেষকরা বলছেন, ভারত আজ 'নৈতিক নেতৃত্বের ভাষা' ব্যবহার করলেও বাস্তবে তা হয়ে উঠেছে 'চুপিসারে নৈতিক আপোসের রাজনীতি'। গ্লোবাল সাউথ এখন এটিকে সহানুভূতির উৎস নয়, রাজনৈতিক সুবিধাবাদের প্রতীক হিসেবেই দেখছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, অক্সফ্যাম ও থার্ড ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্কের একাধিক প্রতিবেদনে ভারতের এই কৌশলী দ্বিচারিতার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। বিশেষত, ভারতের জি ২০ প্রেসিডেন্সির সময়কালে জারি করা "উন্নয়নশীল বিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবা" বিষয়ক খসড়া চুক্তির অধিকাংশই ছিল রাজনৈতিক ‘ভাষাবিন্যাস’-নির্ভর, যার বাস্তবায়নে নির্দিষ্ট সময়সীমা, তহবিল বা কাঠামো নির্ধারিত হয়নি। এই পটভূমিতে, ভারতের ‘বিশ্বগুরু’ হওয়ার প্রচেষ্টাকে অনেকেই ব্যঙ্গ করে ‘বিশ্ব-বক্তা’ বলেও চিহ্নিত করছেন— যিনি নীতিকথা বলেন কিন্তু দায়িত্ব নিতে চান না। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণনের একটি কথা আজ খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে:
"A foreign policy without moral clarity is a policy of expedience, not leadership."
বর্তমান ভারত ঠিক সেই পথেই হাঁটছে— নৈতিকতাবর্জিত সুবিধাবাদী কূটনীতির পথে। বর্তমান ভারত কূটনীতিকে প্রায়শই প্রতিরক্ষার পরিপূরক হিসেবে দেখছে, অথচ আদর্শ, ন্যায় ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাব প্রকট হয়ে উঠছে। নেহেরুর নীতিনিষ্ঠ কূটনীতির জায়গায় এখন এসেছে প্রতিযোগিতামূলক সামরিক কৌশল।প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামের ভাষায়, "A nation's strength lies not just in the might of its weapons, but in the morality of its policies." আজকের ভারতের জন্য এই বাণী আরও প্রাসঙ্গিক। কারণ অস্ত্র থাকলেও নেতৃত্ব আসে ন্যায় ও নীতির ভিতর দিয়ে, আর সেই পথেই ভারতের নতুন বিদেশনীতি এক বিশ্বাসযোগ্য ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে ফিরে যেতে পারে।
মতামত লেখকের ব্যক্তিগত, এর সঙ্গে ইনস্ক্রিপ্টের কোনও সম্পর্ক নেই




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp