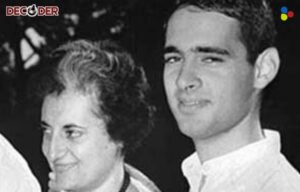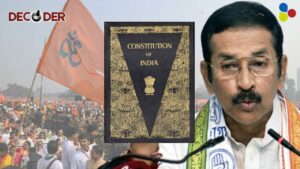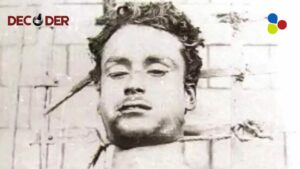রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাবে ধুঁকছে ইউনূস সরকার : আলতাফ পারভেজ
Altaf Parvez Interview: পাকিস্তানের হাতে এমন কোনও নৈতিক পণ্য নেই যেটা বাংলাদেশিদের মুগ্ধ করতে পারে। পাকিস্তানের হাতে এমন কোনও রাজনৈতিক পণ্যও নেই যা বাংলাদেশিদের মুগ্ধ করতে পারে।
ধানমন্ডি ৩২ ভাঙার দিনগুলিতে ঢাকার নানাপ্রান্তে ঘুরে অর্ক দেব কথাবার্তা বলেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা, জুলাই অভ্যুত্থানের সাক্ষী ছাত্রনেতা, বিশ্লেষক, ইতিহাস গবেষকদের সঙ্গে। এই কথপোকথন ডিকোড বাংলাদেশ অনুষ্ঠানেরই সম্প্রসারিত রূপ। এই পর্বে অর্কর অতিথি বিশিষ্ট লেখক, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস গবেষক আলতাফ পারভেজ। এই কথাবার্তায় ধরা রইল বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির চুলচেরা বিশ্লেষণ, রাজনীতির আগামী দিন সম্পর্কে আশা-আকাঙ্খা-উদ্বেগ।
অর্ক: আমাদের দেখা ও কথা হচ্ছে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডের বাড়িটি ভাঙার মুহূর্তে। ফলে আলাপ এখান থেকেই শুরু করতে চাইছি। ৩২ ধানমন্ডি রোডে ভাঙচুরের সময় সেখানে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি এবং অসক্রিয়তার কথা বলছেন অনেকে। এটা দেখে যে কেউ ভাববে দেশে কোনও সরকার নেই। অ্যানার্কি চলছে। তবে, আমি বিদেশি একজন সাংবাদিক। এ বিষয়ে আপনার মতামতটা কী? এই সময়টাকে আপনি কীভাবে দেখছেন?
আলতাফ: আপনার পর্যবেক্ষণ অসত্য বলি কীভাবে! ৩২ নম্বর যখন ভাঙা হচ্ছিল, আমি সেদিন নোয়াখালিতে ছিলাম কিন্তু নজর রাখছিলাম ঘটনাবলীতে। প্রান্তিক জেলাগুলোয় অনেক আগে থেকে সরকার প্রায় অনুপস্থিত। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদ ছয় মাস পেরলো। পরিষদের বড় অংশই গত ছয় মাসে কোনও জেলায় যাওয়ার সময় পায়নি, যেটা জরুরি ছিল। একটা রক্তাক্ত গণঅভ্যুত্থানের পরে নানা ধরনের সংকট থাকে সমাজে। ওঁরা কোথায় জেলা-উপজেলায় গিয়ে মানুষকে ভরসা দেবেন, গণঅভ্যুত্থানের ভিশন নিয়ে বলবেন, ভবিষ্যৎ প্রচেষ্টা সম্পর্কে জানাবেন এবং করণীয় সম্পর্কে শুনবেন— সেই কাজগুলো একদম হয়নি। এই না হওয়ার কারণে এক ধরনের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক শূন্যতা তৈরি হয়েছে। নানা ধরনের নৈরাজ্যবাদী সামাজিক শক্তি সক্রিয় হয়েছে, যারা এখন ক্রমে একটা ‘মব’-এ রূপান্তরিত হয়েছে। তারা একটা ‘ছায়া সরকার’-এর মতো আচরণ করছে। একটা বিকল্প প্রশাসনের মতো অনানুষ্ঠানিক ক্ষমতা দেখাচ্ছে। এই ‘শক্তি’গুলো সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে নানাভাবে। তাদের প্রতিদিনকার বয়ান, শারীরিক উপস্থিতি ও দাপটের মাধ্যমে, খবরদারিত্বের মাধ্যমে সরকারের বিকল্প হয়ে উঠেছে তারা। ফলে যে অর্থে আপনি ঢাকায় সরকার খুঁজছেন, জেলা শহরে সেই খোঁজ আরও প্রবল, তীব্র। ঢাকায় আমরা দেখলাম, একদল মানুষ যা ইচ্ছা করছে তাই করতে পারছে। একে ধরব, একে মারব, কেউ আন্দোলন করছে— এদের পিটিয়ে দাও, কেউ এমন কোনও দাবি দাওয়া তুলল, পছন্দ হচ্ছে না— ওদের তাড়িয়ে দাও। এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে। ফলে আপনার ওই পর্যবেক্ষণে আমি বড় আকারে কোনও দ্বিমত প্রকাশ করব না।
অর্ক: ধানমন্ডি ৩২ ভাঙা আটকানো গেল না কেন?
আলতাফ: এটার অন্যভাবে একটা ব্যাখ্যা হতে পারে। সেটা হলো, গণঅভ্যুত্থানে সরকারের ছয় মাস হলো এবং মোটামুটি এটা অনেকে আপনাকে বলবে যে এরা প্রত্যাশিত মাত্রায় কিছু ডেলিভারি দিতে পারেনি। যে জনপ্রত্যাশা ছিল সরকারের কাছে, সেই প্রত্যাশা অনেকখানিই পূরণ করতে পারেনি। অনেকে এখন অবশ্য বলছেন, প্রত্যাশাই নাকি বেশি ছিল।
এই সরকারের ভেতর বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের প্রতিনিধি আছে। সরকারের ওই প্রতিনিধিরা জাতীয় নাগরিক কমিটি ও বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের ঘনিষ্ট। সরকারের সাফল্য-ব্যর্থতা আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিকভাবে তাদেরও শেয়ার করতে হয়। দূরের মানুষ সরকার, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন, জাতীয় নাগরিক কমিটি— এগুলোকে এক ফ্রেমে ফেলে দেখে। এখন সরকার কিছু ডেলিভারি দিতে না পারার সামাজিক দায়, নৈতিক দায়, প্রশাসনিক দায়, রাজনৈতিক দায় এরকম সকলকে শেয়ার করতে হচ্ছিল। ফলে, আমি মনে করি, ওই ব্যর্থতার জায়গা থেকে কিছুটা দৃষ্টি সরানোরই চেষ্টা করা হয়েছে। এটা খুব স্পনটেনিয়াস হয়েছে, তা আমি মনে করি না। ওখানে বুলডোজার গিয়েছে এবং অনেকটা আগে ঘোষণা দিয়ে ভাঙচুর হয়েছে। সরকার যদি চাইত এটা বন্ধ করতে, ওটা কোনও ব্যাপার ছিল না। ধানমন্ডি ঢাকার একেবারে সেন্ট্রাল জায়গা। এখান থেকে ক্যান্টনমেন্টের দূরত্ব বেশি নয়। পুলিশ আছে, থানা আছে। ফলে এই প্রশ্ন অস্বাভাবিক নয় যে, সরকার এই ভাঙাভাঙি আদৌ থামাতে চেয়েছে কি না। সরকার চাইলে এটা থামানো সম্ভব ছিল।
সরকার না চাওয়ার ব্যাখ্যা এটাই হতে পারে, সরকার তার ওই ব্যর্থতার জায়গাগুলো থেকে কিছুটা রিলিফ পেল। আর রাজনৈতিকভাবে যারা এই ভাঙচুরে যুক্ত তারাও এটা সচেতনভাবে করেছে। আমি বলব, এটা একটা প্রকল্প আর কী। তারা রাজনীতিকে নতুনভাবে মেরুকরণ করতে চাইছে। তারা বনাম আওয়ামী লীগ, অন্যরা যাতে সরে যায়। আমি মনে করি এটার ভিতর দিয়ে বিএনপিকে দূরে সরানোর চেষ্টা আছে। বামপন্থীদেরও দূরে সরানোর চেষ্টা আছে। শ্রমিক-কৃষক-জনজীবনের প্রকৃত ইস্যুগুলো দূরে সরানোর চেষ্টা আছে। অর্থাৎ, রাজনীতিকে নতুনভাবে মেরুকরণ করার একটা প্রচেষ্টা আছে। যারা ভাঙছি এবং যাকে ভাঙছি, মূলত রাজনীতিতে আমরাই দুই পক্ষ— এই বার্তা দেওয়ার চেষ্টা মাত্র।
অর্ক: এই ঘটনাকে সামনে রেখেই জিজ্ঞেস করছি বাংলাদেশের জনতার একাংশ কি ‘রোবটিক মব’ হওয়ার পথে এগোচ্ছে?
আলতাফ: এখানে আমার একটা ভিন্নমত আছে। আমি মনে করি না, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এই হামলাগুলো করেছে। এই ‘মব’ মানে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ নয়। এগুলাকে আমি রাজনৈতিক প্রকল্প আকারে দেখছি। অর্থাৎ, এগুলোর পিছনে রাজনৈতিক গোষ্ঠী আছে। তারা তাদের একটা কর্মী বাহিনীকে এই কাজে লাগাচ্ছে।
অর্ক: স্পষ্ট করে বলুন, কোন রাজনৈতিক গোষ্ঠী?
আলতাফ: এখানে দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলো আছে। তারা অনেক। এটার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নানা ইউটিউবার। এদের একটা অ্যালায়েন্স হয়েছে। রাজনৈতিক অ্যালায়েন্স, ডিজিটাল অ্যালায়েন্স। এরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করছে তাদের তৎপরতার মাধ্যমে। অভ্যুত্থানের পর থেকে ধীরলয়ে দক্ষিণপন্থার উত্থান হচ্ছিল। সেটা এখন অনেকটা প্রকাশ্য দৃশ্যমান।
অর্ক: কিন্তু দেশের বাইরে বসে একজন ইলিয়াস, একজন পিনাকী ভট্টাচার্য দেশের মানুষের স্নায়ুসংবেদ কন্ট্রোল করবেন, একটা ভিডিও গেমের মতো, এটা হতে পারে? এটা কাম্য?
আলতাফ: এটা সম্ভব হয়েছে অন্য কারণে। সরকার যদি সফল হতো তার ছয় মাসের প্রশাসনিক কাজে, তাহলে এইটা কারও পক্ষে সম্ভব হতো না। কিন্তু এখন প্রশাসন প্র্রত্যাশাপূরণে ব্যর্থ হওয়ায় মানুষের ভিতরে প্রচণ্ড একটা হতাশা আছে। তারা ভাবছেন, গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে তো কিছু হলো না, কিছু করা গেল না। ফলে মানুষের ভিতরে একটা উত্তেজনা, হতাশা, ক্ষোভ, অসন্তোষের মিশ্রণ যে মনোভাব তৈরি করে, সেই মনোভাবটা আছে। ওই জমিনের উপর এরা এখন নানা ধরনের কল্পিত প্রতিপক্ষ বা যেই প্রতিপক্ষকে এখন ডিল করার কোনও প্রয়োজন নেই, আর যে কাজগুলো এখন করা দরকার, সেগুলো না করে অন্য কাজের দিকে মনোযোগ নেওয়া এবং রাজনৈতিক মেরুকরণ তৈরি করা এবং আমি বলব, বিএনপিকে অনেকটা সাইডলাইন করা এবং নির্বাচন যাতে বিলম্বিত হয়, সেই চেষ্টা— এইসব মিলে এই ঘটনাগুলো ঘটানো হচ্ছে।
আরও পড়ুন-ক্ষমতায় থাকতে আসিনি, দায়িত্বপালন করে চলে যাব : শফিকুল আলম
অর্ক: আপনি কি মনে করেন যে, ৭২-এর সংবিধান সংস্কারের কিছু আশু প্রয়োজনীয়তা আছে?
আলতাফ: আছে। ১৯৭২ এর সংবিধানের আমূল সংশোধনের জরুরি প্রয়োজনীয়তা আছে।
অর্ক: যে সরকার জনতার বিধান পেয়ে আসেনি, তার কি সংবিধান সংস্কার করার এক্তিয়ার আছে?
আলতাফ: আছে। প্রথমত, এই সরকার জনতার ম্যান্ডেট পেয়েই এসেছিল। এই সরকার গণঅভ্যুত্থানের সরকার। ৫ তারিখে আসলে একটা ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থান হয়েছে এবং একটা জাতীয় ঐক্যমত তৈরি হয়েছে। আপনি তো জানেন, জনগণের সাধারণ ইচ্ছাই আইন। একটা দেশের জনগণ যদি চায়, তাহলে জনগণের চাওয়াটা সংবিধানের চেয়ে অনেক বড় ব্যাপার। বাংলাদেশে অগাস্টের ৫ তারিখে ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থান চেয়েছে বলেই এই সরকার গঠিত হয়েছে। তাহলে জনগণের ইচ্ছার, যৌথ ইচ্ছার অভিপ্রায় হিসেবেই এই সরকার। ফলে এই সরকারের বৈধতা হলো জনগণের যৌথ, সাধারণ ইচ্ছা। আমরা যদি গতানুগতিক আইন দিয়ে সরকারের বৈধতা খুঁজি, তাহলে আমরা ভুল বুঝব। এটা অবশ্যই একটা বৈধ সরকার। কারণ জনগণ তাকে এই জায়গায় এনেছে এবং জনগণ মনে করছে, সংবিধান সংস্কার হওয়ার দরকার। তাহলে সরকার যদি সংবিধান সংস্কারের উদ্যোগ নেয়, সেই উদ্যোগের বৈধতা আছে। প্রশ্ন হলো, সেটা কখন নিতে হবে, কীভাবে নিতে হবে এবং এখন কি সেটার সুযোগ আছে?
অর্ক: আমি বলছি যে, এই মুহূর্তে সরকার যেখানে দাঁড়িয়ে আছে...
আলতাফ: এখন সেই সুযোগ অনেক কমে গেছে। কারণ, ওই যে বললাম, মানে ইতিমধ্যে পরিস্থিতির মোড় পরিবর্তন ঘটেছে। সরকার প্রশাসনিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ওই যে বললাম, জেলাগুলোতে যেতে পারেনি। শিল্প কারখানাগুলো অনেকগুলো বন্ধ হয়ে আছে। কৃষি খাতের জন্য সরকার কিছু করতে পারেনি।
এদিকে ভ্যাট চাপানো হয়েছে। মানুষ দেখছে, তাদের জীবনযাপনের কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। কেবল মুখের কথাই শুনছে তারা— সংস্কার, সংস্কার, সংস্কার। কমিশনগুলো হয়েছে অনেক বিলম্ব করে। কমিশনগুলো তাদের সুপারিশ দিচ্ছে কিন্তু সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে জাতীয় ঐক্যমত দরকার। যে জাতীয় ঐক্যমত ৫ তারিখে ছিল, এখন সেটা নেই। ৫ তারিখের পরে এই যে জাতীয় ঐক্যমত ভেঙে গেছে, এতে সরকার এবং সরকার সংশ্লিষ্ট ছাত্র বা অন্য যে রাজনৈতিক শক্তি আছে তাদের অবদানই বেশি। ঐক্য ভেঙে যাওয়ার পরে এখন আর সংস্কারকে এগিয়ে নেওয়া বাস্তবে সম্ভব না। এখন কেবল নির্বাচিত সরকারই সেই সংস্কারগুলো এগিয়ে নিতে পারে। নির্বাচনের আগে এগুলো কার্যত প্রায় অসম্ভব।

অর্ক: প্রফেসর ইউনূস তো নির্বাচনের দুটো সময় ইঙ্গিত করছেন। একটা ডিসেম্বর, অন্যদিকে জুন।
আলতাফ: নির্বাচন খুব দ্রুত হওয়া উচিত। ডিসেম্বরের আগেই হওয়া উচিত। বাংলাদেশে এখন দ্রুত নির্বাচন না হলে চরম অনিশ্চয়তা দেখা দেবে। অরাজকতা দেখা দেবে। সহিংসতা, সংঘর্ষ আরও বেড়ে যেতে পারে।
অর্ক: সরকারের বাধ্যবাধকতাগুলি কী কী? ধরুন, মাজার ভাঙা হলো। সরকার নিন্দা করল কিন্তু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হলো কি?
আলতাফ: সরকার যেভাবে গঠিত হয়েছে, যাদের নিয়ে গঠিত হয়েছে, তাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ঘাটতি আছে। প্রশাসন পরিচালনার, জাতীয় প্রশাসন পরিচালনার দক্ষতার ঘাটতি আছে এবং সরকারের ভেতর সমন্বয়ের অভাব আছে। সবচেয়ে বড় কথা, দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা আছে। মানে অভিমতটা স্পষ্ট নয় যে, আমরা কবে চলে যাব এবং আমরা কী করব? আমার মনে হয়, সরকারের বড় এক অংশ অনেকটা সময় থাকতে চায়। আর একটা অংশ দ্রুত চলে যেতে চায়। এই যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব, এটাই সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা। অপশক্তিগুলো এই টানাপড়েনের সুযোগ নিচ্ছে।
অর্ক: আপনার কি মনে হয় ক্ষমতাকাঠামোর অভ্যন্তরে গণ্ডগোল আছে, মানে ক্ষমতার সংঘাত আছে ভেতরে?
আলতাফ: বড় ঘটনা হলো সরকারের দক্ষতার, প্রশাসনিক দক্ষতার এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ঘাটতি। সরকার সংশ্লিষ্টরা এমন সব মন্তব্য করেছে যা জাতীয় ঐক্য ভাঙার ক্ষেত্রে নেতিবাচক অবদান রেখেছে এবং যখনই জাতীয় ঐক্য ভেঙে গেছে তখনই গণঅভ্যুত্থান তার মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হতে শুরু করেছে। এটা বিভক্ত হয়ে গেছে। গণঅভ্যুত্থান তার রাজনৈতিক লক্ষ্য, সামাজিক ভরসা, সামাজিক প্রত্যাশা হারিয়ে ফেলেছে। সমাজে নানা ধরনের সংঘাত বেড়ে গেছে। দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে বামপন্থী, বিএনপির সঙ্গে জামাতের, সরকারের সঙ্গে বিরোধী দলের দূরত্ব বেড়েছে। রাজনৈতিক সংঘাতগুলো নানা স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে।
অর্ক: বাংলাদেশের ছাত্র জনতা বারবার বলেছে, শেখ হাসিনাকে তারা চায় না। আওয়ামী লীগকে তারা চায় না। এখনও চায় না। কিন্তু ঘটনাপরম্পরায় মনে হচ্ছে না কি যে জাতির নার্ভ কন্ট্রোল করছেন সেই শেখ হাসিনাই?
আলতাফ: আমি মনে করি এটা ভারতের সরকারের একটা প্রচণ্ড ব্যর্থতা, উস্কানি এবং কিছুটা ঔদ্ধত্য যে তারা শেখ হাসিনাকে এখানকার বিষয়ে উস্কানি হয় এমন কথা বলতে দিচ্ছে। তারা তো জানবেন, তিনি যা বলছেন এটা বাংলাদেশে একটা হিংসা তৈরি করবে, অস্থিরতা তৈরিতে সহায়তা করবে। তাদের কি কোনও রিয়েলাইজেশন নেই যে কী ঘটে গিয়েছে বাংলাদেশে?
আরও পড়ুন-একাত্তর আঁকড়েই এগোবে চব্বিশ: নাহিদ ইসলাম
অর্ক: গাজীপুরে যে ঘটনা ঘটল। ভাই ভাইকে মারছে। সহ-নাগরিককে মারছে। তিনি তো যতদিন আয়ু ততদিন বলার চেষ্টা করবেন। বাংলাদেশের মানুষ মানুষকে রক্তাক্ত করবে আরও?
আলতাফ: তিনি চাইলেই এ রকম সহিংস পরিবেশ আরও উস্কে দিতে পারেন, এভাবে দেখছি না। আমি এইটা মনে করি না যে, তিনি বললেন বলেই সহিংসতা হবে। আমি মনে করি যে, এই সহিংসতাটা আমরা রুখতে পারতাম। আমাদের সরকার উদ্যোগী হলে তিনি যত চেষ্টাই করুন এই সহিংসতা এড়ানো যেত। দমন করা যেত, বাধা দেওয়া যেত। কিন্তু ওঁর বক্তব্যও উস্কানি তৈরি করবে। কারণ অনেকে সেটাকে ব্যবহারও করবে।
অর্ক: অনেকেই মনে করেন বাংলাদেশের নতুন সরকারের প্রতিনিধিরা বিএনপি-র সঙ্গে দূরত্ব রাখছে অথচ জামাতের প্রতি একটু যেন সদয়, এই অভিযোগ সত্য মনে করেন?
আলতাফ: আপাত দৃষ্টিতে সত্যতা আছে। একটা অনুমান আছে, এখানে যদি সুষ্ঠু একটা ভোট হয় বিএনপি ক্ষমতায় যাবে। কিন্তু বিএনপি অতীতে যখন ক্ষমতায় ছিল সেটা নিয়ে ছাত্র জনতার অভিজ্ঞতা খুব বেশি সুখকর না। বিএনপি একটা পরিবারতান্ত্রিক দল এবং অতীতে বিএনপির শাসনামলে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যার কারণে সুশাসনের অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত ছিল নাগরিক। অনেক হতাশার দিক আছে বিএনপির অতীত শাসনে। ফলে ছাত্র জনতার মধ্যে একটা হতাশা বা উদ্বেগের দিক আছে বিএনপিকে নিয়ে। এসব হলো অতীতের দিক।
এবার ৫ অগাস্টের পর বিএনপি অনেক উদারনৈতিক, মডারেট এবং সমন্বয়বাদী প্রবণতা দেখাচ্ছে। তবে যেহেতু বিএনপি নিয়ে অতীতের অভিজ্ঞতাগুলো আছে সেই কারণে বিএনপিকে পুরো আস্থায় নেওয়ার একটা সংকট এখনও আছে, দূরত্ব আছে। আবার সাংগঠনিকভাবে মাঠ পর্যায়ে জামাত ইসলামসহ দক্ষিণপন্থী অন্যান্য দলের বেশ সবল উপস্থিতি বা বিকশিত উপস্থিতি আছে। গণঅভ্যুত্থানের পরপর জামায়াতের সঙ্গে বিএনপির একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে। জামায়াত মনে করছে নির্বাচনটা দেরি করে হলে ভালো, যেহেতু নির্বাচন হলেই বিএনপি ক্ষমতায় চলে আসবে, তার ইমিডিয়েট কোনও লাভ নেই। ফলে নির্বাচন যদি আরও ক্রমাগত পিছনো যায়, সে সাংগঠনিকভাবে আরও একটু সবল হতে পারে। ইতিমধ্যে ছাত্ররাও মনে করছে নির্বাচন যদি পিছনো যায়, আমরা যদি একটা দল গঠন করতে পারি, আমাদের দল দাঁড়ানোর একটা সময় দরকার। দল গঠন করলেই হবে না, মাঠ পর্যায়ে আমাদের সাংগঠনিকভাবে দাঁড়াতে হবে। তাহলে নির্বাচনটা যতদূর দেরি হওয়া যায়, তত ভালো। তাহলে দেখুন, ত্রিমুখী স্বার্থের হিসেবে জামাতের যে রাজনৈতিক লক্ষ্য, জাতীয় নাগরিক কমিটির যে রাজনৈতিক লক্ষ্য, দুটো কাছাকাছি। ইন্টারেস্টের জায়গাটা ম্যাচ করছে এই দুই পক্ষের, সরকারেরও। ফলে এই সরকারের সঙ্গে বিএনপির দূরত্ব বেশি, জামাতের দূরত্বটা কম। সরকার সংশ্লিষ্ট ছাত্ররা মনে করছেন তাদের রাজনৈতিক দল বিকশিত করার জন্য সময় দরকার। জামাতও মনে করছে তাদের সময় দরকার এবং প্রয়োজনে আমরা দুই পক্ষ অ্যালায়েন্সও করব। এসব কারণে নির্বাচনকে একটু বিলম্বিত করে সংস্কারের কথা বেশি বলা হচ্ছে।

অর্ক: বাংলাদেশের কৃষক-শ্রমিকের কী অবস্থা এই মুহূর্তে?
আলতাফ: কৃষকের অবস্থা খুব খারাপ। আগেও এদেশে কৃষি খুব প্রায়োরিটিতে ছিল না কিন্তু ছয় মাস একদম প্রায়োরিটিতে নেই। যিনি কৃষি মন্ত্রক চালান, তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্ব। তিনি একজন মেজর জেনারেল। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবস্থা ভালো নেই। ফলে কৃষি মন্ত্রক দেখার মতো, নিশ্চিতভাবে অনুমান করা যায়, মাননীয় উপদেষ্টার হাতে যথেষ্ট সময় নেই। আরেকটি দিক হলো, কৃষি উপকরণের যে বাজার, মনে করুন, আলুর চাষ হবে, আলুর বীজের যে বাজার, এরকম প্রত্যেকটা উপকরণের বাজার কর্পোরেট মাফিয়াদের দখলে। ফলে কৃষক আবাদের আগেই সর্বস্বান্ত হচ্ছে। আর আবাদের পরে, যেমন, ঢাকায় এখন ১০০ টাকায় ৬ কেজি আলু, এত সস্তা। এর মানে হলো ওই আলুচাষি শেষ। সরিষার ক্ষেত্রেও তাই, পেঁয়াজের ক্ষেত্রেও তাই, ধানের ক্ষেত্রেও তাই। পণ্য আবাদ করতে গিয়ে কৃষক উপকরণের বাজারে সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওই উপকরণ ব্যবসায়ীদের কেউ কিছু বলছে না। এ হলো কৃষিখাতের চুম্বক দৃশ্য।
আর শিল্পে প্রথমত যারা বিনিয়োগকারী তারা তো রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় বিনিয়োগ করবে না। তারা দেখবে একটা নির্বাচিত সরকার আসুক, দেশ ঠিক হোক, তখন বিনিয়োগ করবে। অস্থির সমাজে তো কেউ টাকা ঢালবে না। কিন্তু ইতিমধ্যে যে শিল্পকারখানাগুলো রয়েছে, এরকম মালিকদের অনেকে আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ ছিল, তারা পালিয়ে গেছে, অনেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হয়ে গেছে, খেলাপি ঋণ বাড়ছে। ওই মালিকরা নেই, কারখানায় মজুরি দেওয়া হচ্ছে না, বেতন হচ্ছে না। এরকম প্রায় ৫০-৬০ টা বড় কারখানা গাজীপুর শিল্পাঞ্চলে বন্ধ। ফলে হাজার হাজার শ্রমিক বেকার। শিল্পাঞ্চলগুলো হয়ে গেছে একটা টাইম বোমা। একদিকে নতুন বিনিয়োগ হচ্ছে না, আরেকদিকে বিদ্যমান কারখানা বন্ধ।
যেহেতু নির্বাচিত সরকার নেই, ফলে শ্রমিক কৃষকদের কাছে তার দায়বদ্ধতা নেই। এসব খাতে কী হলো না হলো কিছু যায় আসে না সরকারের। নির্বাচিত সরকার থাকলে এমপি-কে তো দায়বদ্ধ থাকতে হতো। ধরুন, এখন তো গাজীপুর এলাকার কোনও এমপি নেই, তো গাজীপুরে কী হচ্ছে, সেখানকার শিল্পাঞ্চলে, কৃষিপাড়ায় কী হচ্ছে এটা তো দেখার কেউ নেই।
আরও পড়ুন-বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হিংসায় নিহত ২৩? এই মৃত্যুর বাস্তব কারণগুলি আসলে যা
অর্ক: আপনি বলছেন ঢাকাকেন্দ্রিক সরকার চলছে?
আলতাফ: ঢাকাকেন্দ্রিকও নয়, এটা জাস্ট মতিঝিল, রমনা কেন্দ্রিক। কয়েকটি থানার মধ্যে ঘোরাফেরা। সচিবালয় যে থানায় আর জাতীয় নাগরিক কমিটি যে থানায়।
অর্ক: এই জন্যই কি যখন ত্রাণ দিতে যাচ্ছে সরকারের প্রতিনিধিরা তখন সেটা তিন দিন ধরে খবর হচ্ছে যেন সেটা কত অভাবনীয় ব্যাপার?
আলতাফ: একটা অভিজ্ঞতার কথা বলছি। ত্রাণের জন্য ছাত্ররা যে টাকা তুলে নিয়েছিল, সেই টাকাটা ওরা নোয়াখালি কুমিল্লায় না নিয়ে ইউনূস সরকারের ফান্ডে জমা করেছে। অর্থাৎ, সেটা বিতরণের জন্যও সময় নেই কারও। ছাত্রনেতাদের ত্রাণের টাকাটা নোয়াখালিতে পৌঁছে দেওয়ারও সময় হয়নি।
অর্ক: এটার মূল কারণ কী?
আলতাফ: অনভিজ্ঞতা। বা তাদের পেছনে যারা গাইড করছে, তাদের ভুল গাইডেন্স। শেষ বিচারে, আমি বলব, তারা ভুল পরামর্শের শিকার।
অর্ক: আমরা ২২ পরিবার তত্ত্বের কথা পড়েছিলাম, হাসিনাও তো এমন কিছু এস আলম তৈরি করেছিলেন। তারা বিদেশে টাকা পাচার করেছে। রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগ করেছে। এই টাকা কি ফিরিয়ে আনা বাংলাদেশের এই বর্তমান সরকারের পক্ষে সম্ভব? তাহলে তো বাংলাদেশকে আর বিশ্বব্যাংকের কাছে হাত পাততে হয় না।
আলতাফ: সে তো বটেই। পাচার হয়েছে কয়েকশ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশে গত ১৫ বছর নির্বিঘ্নে যেটা হয়েছে সেটা হলো লুণ্ঠন এবং সেই লুণ্ঠনের টাকাটা এখানে বিনিয়োগও হয়নি, সেটা চলে গেছে। ছাত্র জনতার প্রত্যাশা ছিল এই সরকার সেই সম্পদ ফিরিয়ে আনবে। শুরুতে মনে হচ্ছিল কিছু উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আমি যদি সাধারণ জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে বলি, এই আশা খুব কম লোকই করে যে এই সরকার সেগুলা ফিরিয়ে আনতে পারবে। মনে হয় না সরকারের প্রায়োরিটিতে এগুলি আছে আর।
অর্ক: বাংলাদেশের উপর একটা পাকিস্তানের ছায়া পড়েছে— এটা একটা শক্তিশালী মিডিয়া ন্যারেটিভ। পাশাপাশি তরুণতম প্রজন্ম, যারা পররাষ্ট্রনীতি হিসেবে ভারতের আধিপত্য বা আগ্রাসনের বিরোধিতা করে তারা পাকিস্তানের কালচারে ঝুঁকে পড়ে এমন দাবিও শুনি। এই দাবি দাওয়ার সারবত্তা আছে কি না বলুন?
আলতাফ: নেই। আমি এতে একমত না। গণঅভ্যুত্থান যে হলো আসলে এর একটা বড় পটভূমি হলো ভারতের ভূমিকা। আমি বলব এটা অনেক বড় পটভূমি— যেটা এখনও যথেষ্ট মনোযোগ পায়নি। মানুষের জন্য এটা একটা হতাশা, ক্ষোভ, প্রতিদিনকার বেদনার দিক ছিল যে, বাংলাদেশের নির্বাচনের নিয়তি এসে ভারত ঠিক করে দিয়ে যাচ্ছিল। চুক্তি হচ্ছে ভারতের সঙ্গে, দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হচ্ছে জল নিয়ে কথা নেই। ভারতের ট্রেন, ভারতের ট্রানজিট, উলফা ইত্যাদি নিয়ে কথা হয় কিন্তু জল বাদ। ১৫ বছর সম্পর্কটা একেবারেই ভারসাম্যহীন ছিল। একতরফা ছিল। সীমান্ত হত্যাকাণ্ড মানুষকে প্রতিদিন পীড়িত করত। ভারত ব্যাপারটাকে এরকম বেদনার পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল।
ভারত আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছে। ভারতকে নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা বোধ ছিল। কোনও ঘাটতি ছিল না তাতে। আপনি ২০ বছর আগে দেখুন, ১৫ বছর আগে দেখুন। কিন্তু গত ১৫ বছর সবকিছু ওলটপালট করে দিয়েছে। এই যন্ত্রণার কারণে ভারত সম্পর্কে মানুষ এখন প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ এবং শেখ হাসিনাও এটা উপলব্ধি করছেন না যে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে তারা কোথায় নিয়ে গেছেন। মনে করুন, বাংলাদেশে কীভাবে নির্বাচন হবে দিল্লির পররাষ্ট্র মন্ত্রকের বিদেশ সচিব ঠিক করে দিয়ে যাচ্ছিলেন। মানুষ চোখে দেখছিল এসব। ১৭ কোটি মানুষ। কিছু বলতে পারছিল না। এই যে অপমান, এইটা সে ভুলতে পারে না।
একটা পর্যায়ে ৫ অগাস্ট হল। গণঅভ্যুত্থান হলো। স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশের মানুষ বৈদেশিক সম্পর্কের জায়গা থেকে এখন অন্য বন্ধু খুঁজবে, অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক করবে— এরকম একটা জায়গা থাকতে পারে। কিন্তু আমি আপনাকে দায়িত্ব নিয়ে বলছি, বাংলাদেশে পাকিস্তানের তেমন কোনও প্রভাব নেই। কারণ এটা পাকিস্তানের ব্যর্থতা হতে পারে বা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকারও হতে পারে। এরকম ভাবা যেতে পারে যে, পাকিস্তান একটা মুসলিম দেশ, বাংলাদেশও একটা মুসলিম দেশ। বোধহয় দুটো মুসলিম দেশের ভিতরে এখন ভারতকে পাশ কাটিয়ে একটা বড় ধরনের সম্পর্কের উত্থান ঘটবে। কিন্তু, পাকিস্তানের হাতে এমন কোনও নৈতিক পণ্য নেই যেটা বাংলাদেশিদের মুগ্ধ করতে পারে। পাকিস্তানের হাতে এমন কোনও রাজনৈতিক পণ্যও নেই যা বাংলাদেশিদের মুগ্ধ করতে পারে। যদি আমরা দু'জনে ডেটা নিতে পারতাম, তাহলে আমার বক্তব্যটা বোঝাতে পারতাম। ৫ অগাস্টের পর বাংলাদেশের বিপুল পর্যটক পাকিস্তানে যাচ্ছে, এমন কিছু হচ্ছে না। পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যও খুবই নগণ্য, খুবই নগণ্য। তাহলে সম্পর্কের প্রভাবটা কীভাবে পড়বে? অভ্যুত্থানের পরে, গণঅভ্যুত্থানের পরে পাকিস্তান-বাংলাদেশ সম্পর্কে বড় ধরনের ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছে বাস্তবে এমন কোনও প্রমাণ নেই এবং আমি কোনও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও দেখি না। বাংলাদেশ অবশ্যই বৈদেশিক সম্পর্কে নতুন বন্ধু খুঁজছে, কমরেড খুঁজছে, বাণিজ্যের জন্য সহযোগী খুঁজছে কিন্তু সেটা পাকিস্তান নয়। পাকিস্তানের নৈতিক কর্তৃত্ব নেই, অর্জন নেই, অগ্রসর রাজনৈতিক মডেল নেই। এমনকী পাকিস্তানের নেতৃত্বের কোনও হেজেমনিও নেই বাংলাদেশে। ফলে এই সম্পর্ক নিয়ে ভারত যেভাবে বলছে তার বাস্তব কোনও জমিন নেই। বরং আমি বলব পাকিস্তানের বর্তমান রেজিম, ইমরান খানকে যেভাবে কারাগারে বন্দি করে রেখেছে, পিটিআই-এর প্রতি যে আচরণ করছে সেটাই বাংলাদেশের মানুষকে ক্ষুব্ধ করছে। যারা রাজনীতি সচেতন তারা এই ঘটনা জানেন। উভয় দেশের মিল যদি বলেন, পাকিস্তানে দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক অস্থিরতা আছে, বাংলাদেশ হয়তো একই ধরনের অস্থিরতায় ঢুকছে। তবে বাংলাদেশের কিছু কিছু রাজনৈতিক শক্তি পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করার জন্য আকাঙ্খা পোষণ করে। কিন্তু চেষ্টা করেও এতে খুব বেশি সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ ১৯৭১-এর স্মৃতি বাংলাদেশিদের মাঝে এখনও জীবন্ত। যদিও নতুন প্রজন্ম চলে এসেছে, ১৯৭১-এর প্রজন্মের মানুষ খুবই কম কিন্তু পাকিস্তান এখনও অনুতপ্ত হয়নি ১৯৭১-এর ভূমিকার জন্য। পাকিস্তান এখনও ফর্মালি ক্ষমাপ্রার্থনা করেনি। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের ১৯৭১ পূর্ব বিপুল পাওনা আছে, সেটার মীমাংসা হয়নি। ফলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে পাকিস্তান আসলেই এমন কিছু ভূমিকা রাখেনি যেটায় বাংলাদেশ মুগ্ধ হবে, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্য পাগল হয়ে যাবে।
অর্ক: বৈষম্যবিরোধীদের একাংশের আচরণে মনে হচ্ছে যেন মুজিবের রক্ষী বাহিনীর ছায়া দেখা যাচ্ছে, এমন অভিযোগও আসছে।
আলতাফ: বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন বা জাতীয় নাগরিক কমিটিতে এখন যারা আছেন নেতৃত্ব পর্যায়ে, ওঁরা পুরো জনতার তো নয়ই, এমনকী পুরো ছাত্র সমাজেরও প্রতিনিধিত্ব করেন বলে আমি মনে করি না। ছাত্র সমাজের ভেতর নানা উপদল আছে। যারা গণঅভ্যুত্থানে একসঙ্গে ছিল কিন্তু এখন যার যার মতো আলাদাভাবে রাজনীতি করছে। নেতৃবৃন্দের কথা বললে, আমি তাদের ব্যাপারে এইটুকুই বলব, তাদের কিছু কিছু আচরণে আমার মনে হয়েছে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাব, রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ঘাটতি এবং বাংলাদেশের সমাজের অতীত রাজনৈতিক ইতিহাস জানা-বোঝার ঘাটতি আছে। কোন আচরণের প্রভাব কী হবে, প্রতিক্রিয়া কী হবে, ফলাফল কী হবে, এইটা বোঝার ঘাটতি থেকে তারা বিভিন্ন ধরনের আচরণ করছেন। যার ফল হিসেবে তারাই দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বা হতে পারেন। তাতে তাৎক্ষণিকভাবে সমাজেও এক ধরনের অস্থিরতা বাড়বে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তাদের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের এটা ক্ষতি করবে। এসব প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতাজনিত ঘাটতি।
অর্ক: জর্জ সোরেসের ছেলে দিন কয়েক আগে বাংলাদেশ ঘুরে গেলেন। অনেকে মনে করেন, এই সরকার আসলে মার্কিন মদত পুষ্ট সরকার। আপনার কী মত?
আলতাফ: আমি একদম একমত না। কারণ এই অভ্যুত্থানে যারা যুক্ত ছিল তাদের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক বন্ধুত্ব, চলাচল, যোগাযোগ ছিল। অভ্যুত্থান যখন প্রতিদিন একটু একটু করে হচ্ছে, কারফিউর মধ্যে আমি নিয়মিত বেরিয়েছি, অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। দীর্ঘদিন থেকে বাংলাদেশের মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস এখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, নির্বাচন আয়োজন এগুলোর পক্ষে বলেছেন, এতে কোনও সন্দেহ নেই। সেটা ইওরোপের অনেক দেশও বলেছে। কিন্তু এর মানে এই না যে গণঅভ্যুত্থানের মার্কিন ইনভলভমেন্ট আছে বা ছিল। হয়তো উৎসাহ ছিল। শেষের দিকে কোনও না কোনও পর্যায়ে তাদের উৎসাহ বেড়ে গিয়ে থাকতে পারে। তাদের সুবিধাপ্রাপ্ত কেউ কেউ হয়তো আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। সেটা দিয়েই অভ্যুত্থান ঘটেনি। একটা জিনিস ঘটে যাচ্ছে, আমি হাজির হলাম, আমি উৎসাহ দিলাম, যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে এরকম ব্যাপার ছিল। তবে এরপর থেকে তারা ক্রমাগত এসেছে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে নেতৃবৃন্দ আসছেন। তারা অধ্যাপক ইউনূসকে সাহায্যের আশ্বাস দিচ্ছেন কিন্তু খেয়াল করুন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাহায্য উল্লেখযোগ্য মাত্রায় আসেনি এখনও।
অর্ক: এলে বাংলাদেশকে কি চিনের কাছে অর্থসাহায্য চাইতে হতো? দ্বিতীয়ত, আপনি যেটা বললেন, এইটা যুক্তরাষ্ট্র মদত পুষ্ট সরকার কি না?
আলতাফ: এতটা রুক্ষ কথা বলতে চাই না। যুক্তরাষ্ট্র এই সরকারের প্রতি উৎসাহ দেখাচ্ছে এটুকু বলা যায়। আমি মনে করি এটা আমাদেরই গণ অভ্যুত্থানের সরকার। ছাত্র-জনতার পছন্দের সরকার কিন্তু সেই সরকার ডেলিভারি দিতে পারছে না। তাদের কাছে প্রত্যাশা যা ছিল, সেটা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে।
অর্ক: বাংলাদেশের রাস্তায় রাস্তায় শরীরে ক্ষত নিয়ে মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ক্ষত গণঅভ্যুত্থানের ক্ষত। এরকম মানুষের সংখ্যা কয়েক হাজার। শহিদ পরিবার রয়েছে। তারা ন্যায়বিচারের জন্য অপেক্ষমান।
আলতাফ: রাইট। অবশ্যই বিচার আগে হতে হবে। এ বিষয়ে কিন্তু বাংলাদেশে দক্ষিণ-বাম-মধ্য কারও কোনও ভিন্নমত নেই। যে অন্যায় হয়েছে, অন্যায়ের বিচার দ্রুতলয়ে হওয়া উচিত। কিন্তু সেটা কি দ্রুতলয়ে হচ্ছে? হচ্ছে না। এই যে বললাম মানুষের হতাশার এটাও একটা কারণ। বিচার দ্রুতলয়ে হচ্ছে না। সবচেয়ে বড় কথা, বিচার তো হতে হবে ন্যায়বিচার। অপরাধী যিনিই হন, তাঁকে সুষ্ঠ বিচারের মধ্যে দিয়ে শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু সেই সুষ্ঠ বিচারের জন্য ফরেনসিক এভিডেন্সগুলো রাখা দরকার ছিল। সাক্ষ্য প্রমাণ রাখা দরকার ছিল। অনাচারের সাক্ষ্য প্রমাণ সংরক্ষণ করার ব্যাপার ছিল। ১৫ বছর কী ঘটছে এবং শেষ দুই মাসে কী ঘটেছে, তালিকা থাকা দরকার, সব রকম নথি, ডিজিটাল এবং ফিজিক্যাল।
এ ক্ষেত্রেও আমি বলব বড় একটা গাফিলতির ব্যাপার ঘটেছে। এগুলো অনেক সময় বেসরকারি উদ্যোগেও রাখার ব্যাপার ছিল। সে ক্ষেত্রেও আমাদের ঘাটতির ব্যাপার ঘটেছে। ফলে আহত মানুষের, সে কোথায় আহত হয়েছে, কীভাবে হয়েছে, কারা তাকে আহত করল, কারা নিহত হলো, এই তথ্যপ্রমাণগুলো সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের ঘাটতি আছে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঘাটতি আছে। শহিদ পরিবারের পুনর্বাসন-সহায়তার ক্ষেত্রেও ঘাটতি আছে। সম্প্রতি প্রথম আলোতে তথ্য বেরিয়েছে, বিপুল মানুষ এখনও এই ধরনের সহায়তার বাইরে পড়ে রয়েছে। সায়েন্টিফিক্যালি ওরা সার্ভে করে বের করেছে কত শতাংশ। এটা তো একটা সংস্কারের প্রধান অগ্রাধিকার হওয়া উচিত, তাই না? এইটা তো বিয়ন্ড সংস্কার, এটা একটা সরকারের প্রধান প্রায়োরিটি হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু আমরা এগুলো করতে পারিনি।

আরও পড়ুন-বাংলাদেশের আয়নাঘর আসলে কেমন? ছবি, ভিডিও ইনস্ক্রিপ্টের হাতে
অর্ক: বাংলাদেশের বাম রাজনীতির ভবিষ্যৎ কী?
আলতাফ: এ দেশে বাম রাজনীতির ভবিষ্যৎ আছে। প্রবলভাবে আছে। আমরা তো আইএমএফ রেজিমের মধ্যে ঢুকে গেছি। আইএমএফ-এর প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী এখন ভ্যাট ইত্যাদি বাড়ছে। আগামীতে আইএমএফ-এর ইনফ্লুয়েন্স বাড়বে। তাছাড়া সম্পদ বন্টন পুনর্বন্টনের কোনও ব্যাপার নেই আজ আর। ভূমি সংস্কারের আলাপ নেই। কৃষি সংস্কারের আলাপ নেই এবং কীভাবে সম্পদ পাচার হয়েছে সেটা তো দেখা গেছে।
গত ১৫ বছরে যে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল, সেই কাঠামো যদি আবারও থেকে যায় ভবিষ্যতে, তার মানে, ধনবৈষম্য তো আরও প্রকট হবে। আপনি জানেন বোধ হয়, বাংলাদেশের উপর তলার ১০ ভাগ মানুষের হাতে জাতীয় সম্পদের ৪১ ভাগ আর নিচের তলার ১০ ভাগের হাতে ১.৩ ভাগ রয়েছে। তাইলে আগামীতেও যদি এই কাঠামো থাকে সেটা বাম রাজনীতির জন্য একটা উর্বর ভূমি।
অর্ক: বাম রাজনৈতিক দলগুলো সময়ের এই চাহিদা পূরণের জন্য প্রস্তুত? নেতৃত্ব রয়েছে?
আলতাফ: একদমই প্রস্তুত না। এখানে কিছু কর্মী রয়েছে। পরিশ্রমী। তারা কাজ করছে। কিন্তু নেতৃত্ব পর্যায়ে শুধু ব্যর্থ না, আমি বলব প্রায় পুরোই ব্যর্থ। তারা গণঅভ্যুত্থানকে বুঝতেও অনেকাংশে ব্যর্থ ছিল। বাংলাদেশের এখনকার গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়কে বুঝতেও অনেকাংশে ব্যর্থ হচ্ছেন। কল্পনা করুন, একটা কম্পিউটার অনেক পুরনো অ্যাপলিকেশন দিয়ে চলছে। সেই কম্পিউটারের মতো তাদের অবস্থা। বাজারে উইন্ডোজ ১০ চলে এসেছে। এখন উইন্ডোজ ৪/৫ দিয়ে তো মেশিন চালালে হবে না। সমস্যাটা হলো রাজনৈতিক প্রজ্ঞার, দূরদৃষ্টি এবং পরিকল্পনার। বামপন্থী অনেক ইয়ং ট্যালেন্ট বের হচ্ছে। কিন্তু তাদের দলগুলোয় যথাযথ জায়গায় যথাযথ মর্যাদা ও কাজ দেওয়া হচ্ছে না।
অর্ক: বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের একটা অংশ সরকারের ভিতরে, একটা অংশ বাইরে থেকে কাজ করছে। আন্দোলনে একটা অংশ কি কোণঠাসা এখন?
আলতাফ: প্রশ্ন হলো, ওরা কালেক্টিভলি পারফর্ম করতে পারল কি পারল না? পারছে না। আমি বলব, কালেক্টিভলি তারা প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। তাদের দিক থেকে যুক্তি হলো, সরকারে আমরা মাত্র তিনজন। কিন্তু এও তো সত্য, প্রায় পুরো উপদেষ্টা পরিষদ তারাই বাছাই করেছে। ইউনূস সাহেবকে তারাই বাছাই করেছে। পুরো ক্যাবিনেটের পারফর্মেন্সের দায় তাদের না নিয়ে উপায় নেই। বৈষম্য বৃদ্ধি ঠেকাতে পারেনি ওরা।
অর্ক: শেখ হাসিনার পলায়নের আগের ছ’মাস পর পরিস্থিতিটাকে কীভাবে ব্যখ্যা করবেন? বাংলাদেশ স্বৈরাচার থেকে নৈরাজ্যের দিকে চলে গেল কি?
আলতাফ: আমি এইভাবে ফ্রেম করব না। বাংলাদেশ স্বৈরাচার থেকে এখন একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে, যেখানে মানুষ শঙ্কিত যে তাদের গণঅভ্যুত্থানের সম্ভাবনাটা হাতছাড়া হয়ে যায় কি না। মানুষ শঙ্কিত যে, তারা একটা দক্ষিণপন্থার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে কি না। মানুষ শঙ্কিত যে, যারা অর্থনৈতিক সংকটে পড়তে যাচ্ছে কি না, একটা অর্থনৈতিক মন্দায় পড়তে যাচ্ছে কি না। মানুষ শঙ্কিত যে, নির্বাচন আদৌ হবে কি না। এরকম অনেকগুলো অনিশ্চয়তা এবং শঙ্কা সক্রিয়। কিন্তু এটা আমি এখনও মানতে চাই না যে আমরা নৈরাজ্যের যুগে ঢুকে গেছি। আমার ধারণা, এখানে অনেকগুলো বাজে অভিজ্ঞতা, অনেকগুলো সহিংস পরিস্থিতির পরেও বাংলাদেশের সমাজে একটা অন্তর্গত শক্তি আছে। দেখুন ৯০-এ আমরা অভ্যুত্থান করেছি, অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু ২০২৪-এ আবার আমরা জেগেছি। আমি বলব এই অন্তর্গত শক্তির জোরে এখানে একটা শুভশক্তি আবার গণঅভ্যুত্থানকে রক্ষার জন্য ধীরে ধীরে সংগঠিত হবে, এটা আমার বিশ্বাসের অংশ।
অর্ক: সামরিক অভ্যুত্থানের কোনও সম্ভাবনা আছে?
আলতাফ: না, বাংলাদেশের সামরিক অভ্যুত্থানের আপাতত কোনও সম্ভাবনা নেই। হলে আমি আশ্চর্য হব কারণ বাংলাদেশের যে সমস্যা এখন আমরা দেখছি, মানুষ রাজনৈতিকভাবে সমাধান চায় তার। রাজনৈতিক সরকার এগুলোর সমাধান করতে সক্ষম এবং বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর, সশস্ত্র বাহিনীর যে নেতৃত্ব, তারা ইতিমধ্যে যে সিগন্যালগুলো দিয়েছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, তারা মনে করছে রাজনৈতিক সমস্যা রাজনীতিবিদরা সমাধান করবেন। বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী যদি ক্ষমতা নিত ৫ অগাস্টই নিতে পারত। তারা তো রাজনীতিবিদের ডেকে নিয়ে বলেছে, "আপনারা সরকার গঠন করুন," এইটাই তো একটা স্পষ্ট বার্তা।
অর্ক: কিন্তু সেনা হেফাজতে মৃত্যু, এ তো খুব লজ্জাজনক?
আলতাফ: এটা প্রত্যাশিত নয়। আমি ডিফেন্ড করছি না এটা। অনাকাঙ্খিত, অপ্রত্যাশিত, নিন্দনীয় কিন্তু এরকম মৃত্যুর ঘটনা এখন আগের চেয়ে অল্প। এইটাকে আমি একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখতে চাই।
অর্ক: মাজার ভাঙাকে?
আলতাফ: হ্যাঁ। মাজার ভাঙাকে নয়, এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটা পরিকল্পিত। সরকার সেটা ঠেকায়নি বলেই মানুষ মনে করছে।
অর্ক: এই সরকার কেন দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে না এসব বিষয়ে?
আলতাফ: এইটাই ইউনূস সরকারের ব্যর্থতার দিক যে, মাজারগুলো ভাঙা থামাতে পারেনি। আমি মনে করি, এইটা একটা বড় ব্যর্থতার দিক এবং এই যে হিংসাকে গ্রাম পর্যন্ত যেতে দেওয়া হলো, এই যে দক্ষিণপন্থী শক্তির উত্থানের শর্ত তৈরি করা হলো, তাতেই তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেওয়া হলো।
অর্ক: বাংলাদেশ কবে নির্বাচন পাবে?
আলতাফ: আমি ডিসেম্বরের-জানুয়ারির পরে কল্পনাই করতে পারি না।
অর্ক: জামাত, চরমোনাই, হেফাজত, ধর্মকেন্দ্রিক দলগুলি কত শতাংশ ভোট বা ক'টা আসন পেতে পারে?
আলতাফ: এইটা আসলে অনুমান করা কঠিন। আমি এম্পিরিকাল ডেটা ছাড়া কথা বলতে অনিচ্ছুক। আমাদের গত ১৫ বছরে এই ধরনের কোনও এম্পিরিকাল এক্সপেরিয়েন্স নেই। যেহেতু স্থানীয় সরকার, জাতীয় দুই ধরনের নির্বাচনই ভালোভাবে, সুষ্ঠভাবে হয়নি। আমি মনে করি যে আপনি যেইসব শক্তির কথা বললেন তারা খুব বেশি আসন পাবে না। সব মিলে ৫০-এর নীচে থাকবে।
অর্ক: তার মানে তারেক রহমান দেশে ফিরছেন দায়িত্ব নিতে?
আলতাফ: উদ্বেগের দিক আছে অন্যদিকে। বিএনপি যদি ২৫০ বা ২০০ এর বেশি আসন পায়, আমি বলব উদ্বেগের দিক ওইটা। কারণ এক দলের এত বেশি আসন পাওয়ার পরে কী ঘটে সেটা আপনি ভারতে দেখেছেন।
অর্ক: বাংলাদেশে কি একটা ওয়ান/ইলেভেনের দিকে যাবে আবার? ছাত্ররা যে নতুন দল করবে বলছে, এর কি শক্তিশালী বিরোধী দল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে?
আলতাফ: কিছুদিন পর বোঝে যাবে সেটা। কিন্তু বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মানুষ চায় ওরা শক্তিশালী একটা বিরোধী দল হয়ে উঠুক। সংস্কারের এজেন্ডা নিয়ে ওরা রাজনীতি করুক। আমি নৈরাশ্যবাদী নই, আবার খুব আশাবাদীও না। আমি পর্যবেক্ষণ করার পক্ষপাতি। মানে এখনও পর্যন্ত ওরা যে খুব বেশি আশাবাদী হওয়ার মতো কিছু করতে পেরেছে সেটাও না, আবার সব আশা ধূলিসাৎ করে দিয়েছে এমনটাও বলা থেকে বিরত থাকছি। তবে আমি কোনও কিংস পার্টি চাই না।
অর্ক: যেভাবে দল গড়া হচ্ছে সেটাকে কিংস পার্টি বলা যায়?
আলতাফ: সেই রকম একটা দুর্ভাবনা আছে। কারণ অধ্যাপক ইউনূস সাহেব এই সম্ভাব্য দল নিয়ে অনেক পজিটিভ কথাবার্তা বলছেন যেটা বলা ঠিক হয়নি। মানে যদি কিংস পার্টি হয় তাহলে, বিএনপি নির্বাচনের সময় বলবে যে আমি অন্যায়ের শিকার, আমি প্রশাসনের অনৈতিক প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, নির্বাচন স্বচ্ছ হচ্ছে না। তাহলে নির্বাচনী ব্যবস্থাকে আমরা আবার বিতর্কিত জায়গায় এনে ফেললাম।
অর্ক: আমরা আপনাদের কল্যাণে সিরাজ সিকদারের কথা জানতে পেরেছি। ‘মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী’ একটা অভূতপূর্ব বই। সোহরাওয়ার্দীর কথা পড়ছি এখন। ইতিহাসটা বুঝতে পারছি ব্যক্তিনিরপেক্ষ ভাবে। ভবিষ্যতে কি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যান্য নায়কদের কথা, অন্যান্য চরিত্র যাদের কথা আমরা তত জানি না, অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘটনা যেগুলির একটু যেন আড়াল করেই প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তোলা হয়েছে, সেসব আমাদের সামনে আসার সম্ভাবনা রয়েছে?
আলতাফ: বিপুল সম্ভাবনা আছে। ল্যাটিন আমেরিকায় সিমোন বলিভারকে চেপে রাখা হতো, এখন ল্যাটিন আমেরিকার মানুষ বলিভারকে মাটির নিচ থেকে খুঁড়ে বের করেছে, বলিভারপন্থীরা ক্ষমতা পেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ একটা জাতির জীবনের এত বড় ঘটনা, সেটা যে দেশেরই হোক। বাংলাদেশের মানুষ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ করেছে। এটা ছিল জনযুদ্ধ। কৃষক-শ্রমিকরা অংশ নিয়েছেন তাতে। সেই মানুষগুলো পরিবারের কাছে তাদের যুদ্ধের কাহিনি বলে গেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এই জমিনে প্রোথিত করে রেখে গেছে মানুষ, এটাকে উপড়ে ফেলা সম্ভব না, আমি খুবই আবেগ থেকে বলছি এমন না। এটা একটা সায়েন্টিফিক ব্যপার, সমাজবিজ্ঞানের ব্যাপার যে এই জাতি তার ওই প্রধান গৌরবের জায়গা ছাড়বে না।
অর্ক: তার মানে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখনেরও একটা সংস্কার প্রয়োজন?
আলতাফ: অবশ্যই এবং সেটা তো আমরা লিখতাম, অন্যরা লিখত। সেন্সরশিপের কারণে পারিনি। ডিজিটাল অ্যাক্টের কারণে পারিনি। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখার নামে মূলত লেখা হচ্ছিল আওয়ামী লীগের ইতিহাস। ভিন্ন কিছু লিখলে ডিজিটাল আইনে নানা সমস্যা তৈরি হয়েছে। লেখক, কার্টুনিস্ট, গায়ক, সাংবাদিকরা জেলে গেছেন বা পালিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আমরা ইংরেজিতে বিদেশিদের লেখা বই কিনে পড়তাম, এটা আমাদের দুর্ভাগ্যের দিক। ভারতীয়রা মুক্তিযুদ্ধের অনেক ভারতীয় ভাষ্যও বের করেছে কিন্তু আমাদের এখানে এরকম ইতিহাসবিদ, অনুসন্ধানকারী রয়েছেন যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, প্রকৃতির ইতিহাস লিখতে সক্ষম। আমি মনে করি, গণঅভ্যুত্থানের পর সেই শর্ত তৈরি হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সামনে আসবে, আসা উচিত, আসার সম্ভাবনা অন্তত রয়েছে এবং ইতিমধ্যে সিরাজ শিকদারের কথা তো এসেছে, অন্যান্য বড় বড় মুক্তিযোদ্ধাদের, সংগঠকদের কথাও চলে আসবে। আসবেই।
বিশেষ কৃতজ্ঞতা:
অর্ক ভাদুড়ি
স্নিগ্ধেন্দু ভট্টাচার্য




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp