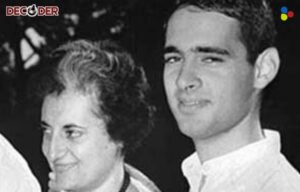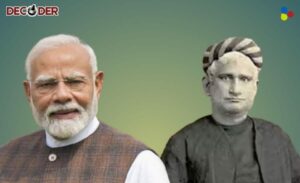প্রাইড মান্থ, প্রান্তিক অস্তিত্ব ও ঋতুপর্ণ ঘোষ
Rituparno Ghosh: মৃত্যুর ১১ বছর পরেও যখন দেখি এখনও ঋতুপর্ণ ঘোষকে অনেকেই তাঁর যৌনপরিচয়ের নিরিখে বিচার করছেন, তখন হতাশ লাগে! তাঁর তৈরি কুড়িটি চলচ্চিত্রের মধ্যে বসবাস করছে অজস্র মানুষের জীবনচিত্রমালা।
একটি প্রশ্ন করতে চাই। তার আগে বলি, ২০২৪-এ ঋতুপর্ণ ঘোষের মৃত্যুর এগারো বছর পূর্ণ হল। সারাজীবন অজস্র সাক্ষাৎকার দিয়েছেন ঋতুপর্ণ। তাঁর ইংরেজি সাক্ষাৎকারগুলি শীঘ্রই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হতে চলেছে। কয়েক দিন আগে, এ-তথ্য যখন আমরা জানতে পারলাম তখন অনেকের বিবিধ মন্তব্যের মধ্যে একটি মন্তব্য বিশেষভাবে নজর কাড়ল। ঋতুপর্ণ ঘোষের আসন্ন প্রকাশিত বইটি সম্পর্কে সোশ্যাল মিডিয়া-য় একজন লিখছেন: ‘গে-দের নিয়ে [বই] না করে পুরুষদের নিয়ে কিছু করুন’।
এখন কী মাস চলছে? জুন? প্রাইড মান্থ? এখানে আমাকে ‘প্রাইড’ শব্দটি নিদারুণ ভাবায়। একজন ব্যক্তি তাঁর যৌনপরিচয় সগর্বে স্বীকার করবেন। প্রত্যক্ষভাবে বলবেন। এ এক স্বাভাবিক স্বাধীনতার চিহ্ন। কিন্তু এটুকুতেই কি সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে ‘প্রাইড’ কথাটির সর্বাত্মক মহিমা? যে এবং যাঁরা সমাজের ভিন্ন যৌনপরিচয়ের মানুষ, তাঁদের আত্মস্বীকৃতির একটি দরজামাত্র হয়ে থাকবে শব্দটির অর্থ?
মুশকিল হল, সমাজের বহুধা অংশে ‘যৌনতা’ বিষয়টি এখনও ভ্রান্ত ও অস্পষ্ট। আচ্ছা, সঠিক ভাবে বলতে পারেন, নিজের একেবারে ভিতরে আমরা যখন তাকাই, যে আত্মা আমাদের শরীরের মধ্যে ছুটে বেড়াচ্ছেন, সে আসলে কে? ‘পুরুষ’? না ‘নারী’? নাকি কেবল একটি অস্তিত্ব!
আরও পড়ুন: সমাজের চোখে ‘অস্বাভাবিক’, যে অভিমান আজীবন বয়ে বেড়ালেন ঋতুপর্ণ
আমরা প্রত্যেকে সেই একক অস্তিত্বকেই প্রকাশ করতে-করতে এগোচ্ছি মাত্র! মজার বিষয় হল, মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। আর সমাজ মানেই সেখানে নিয়ম। কিন্তু প্রকাশ-ইচ্ছের তো কোনও সমাজ নেই। নেই কোনও নিয়মের নিগড়। তাই, তথাকথিত কোনও ‘মেয়ে’-র আচরণের মধ্যে পুরুষচিহ্ন বা একটি ‘ছেলে’-র কথার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা নারীভাব সেই পৃথক-পৃথক ব্যক্তির কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও স্বাচ্ছন্দ্যের হলেও, চারপাশের সমাজচক্ষু তা মেনে নিতে চায় না।
এ-প্রসঙ্গে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, আজ থেকে বহু বছর আগে ‘সংবাদ প্রতিদিন’-এর ‘রোববার’-এ প্রকাশিত একটি লেখায় ঋতুপর্ণ ঘোষের বলা কয়েকটি কথা। ঋতুপর্ণ বলেছিলেন,
‘পুরুষ’ এবং ‘নারী’— এই দুটি বিপরীত শব্দের মাঝখানে এক অসীম প্রান্তর, যেখানে বসবাস করেন অর্ধনারীশ্বরতার নানা প্রতিভু।"
‘মেয়েলি ছেলে’ বা ‘ব্যাটাছেলের মতো মেয়ে’— এই পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু ‘অর্ধনারীশ্বরতার নানা প্রতিভু’? এখানেই গণ্ডগোল বাঁধে! আসলে, শারীরিকভাবে একজন ব্যক্তির সমাজপরিচয়-ই কেবল তাঁর সত্তার সবটুকু নয়। মন যেমন পরিবর্তনশীল। যৌনতার দৃষ্টি ও অনুভবও তেমনই পরিবর্তনময়। কিন্তু এই সহজ সত্যটুকু সমাজ মানতে চায় না। কারণ সমাজের আকর স্বভাব হল সবাইকে কোনও-না-কোনওভাবে চিহ্নিত করে দেওয়া। একজন ভিন্ন যৌনতার মানুষকে ‘গে’, ‘লেসবিয়ান’, ‘ট্রান্সজেন্ডার’, ‘বাইসেক্সুয়াল’ প্রভৃতি আরও ভিন্ন-ভিন্ন অভিধায় একবার ফেলে দিতে পারলেই সমাজ নিশ্চিন্ত হয়!

কিন্তু মন কি একটি নির্দিষ্ট অভিধার মধ্যে বাস করে আজীবন? বোধহয় করে না। এমন তো হতেই পারে, একজন ব্যক্তি এই সব ক-টি যৌনঅভিধার বাইরে এখন নতুন এক ভিন্নতায় নিজেকে দেখতে পাচ্ছেন। সমাজ যেহেতু তাঁর এই ‘নতুন পরিচয়’-কে এখনও অবধি চিহ্নিত করতে পারেনি, তাই তাঁকে মেনে নেবে না।
এখানে একটি বইয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে চাইব। বইটির নাম: ‘মনোলগ: দুই বাংলার লেসবিয়ান কথন’। পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের কুড়ি জন লেসবিয়ান-এর সাক্ষাৎকার একত্র করে মীনাক্ষী সান্যাল, মালবিকা ও সুমিতা বীথি-র সম্পাদনায় বইটি বেশ কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে। বইটিতে চব্বিশ বছর বয়সী একজন লেসবিয়ান মহিলা নিজের যৌন-অভিমুখ সম্পর্কে জানাচ্ছেন:
‘‘…আগে আমি শুধু মেয়েই ভাবতাম নিজেকে, এখন মনে হয়, রোজ আমি মেয়ে হতে চাই না, এক-একদিন আমার অন্য কিছু হতে ইচ্ছে করে। … সাজগোজ তো মেয়েদের মতোই করি, রোজই, কারণ ওরকম সাজতে আমার ভালো লাগে, কিন্তু ভেতরের ফিলিং-টা এক-একদিন এক-একরকম হয়।”
খেয়াল করতে অনুরোধ করব ‘রোজ আমি মেয়ে হতে চাই না, এক-একদিন আমার অন্য কিছু হতে ইচ্ছে করে’। এই ইচ্ছেটাই কিন্তু ওই মেয়েটির ব্যক্তিগত যৌনপরিচয়, যা রোজ পালটে-পালটে যাচ্ছে। আমাদের বোধের মধ্যে বা চেনা-জানার মধ্যে তাঁর সংজ্ঞারূপ যদি না ধরা দেয়, আমরা চেষ্টা করতে পারি তাঁকে বুঝতে, কিন্তু তাঁকে পরিচিত কোনও যৌনতার অভিধাবাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া আসলে মানবিক সভ্যতার বিপরীত অবস্থান, যা জেনে বা না-জেনে প্রায়শই আমরা করে থাকি।
নিজের ব্যক্তিগত যৌনপরিচয় প্রসঙ্গে ঋতুপর্ণ ঘোষ স্বীকার করেছিলেন:
‘আমার স্বভাবপ্রণোদিত ‘অস্বভাবিকতা’ নিয়ে আমি বাস করেছি আমার একাকিত্বের বন্দিজীবনে— আর আমার সামনে ছিল সমাজের এক বিরাট কারাগার। যেখানে ঐতিহাসিকভাবে যে কোনও নতুন প্রথাকেই প্রবেশ করতে হয়েছে দণ্ডিত বিদ্রোহীর মতো, অনেক হিংসা এবং রক্তপাতের মূল্যে।’
হ্যাঁ বন্দিত্বের জীবন। তাচ্ছিল্য। অপমান। কিন্তু সেই জীবনভূমিতে দাঁড়িয়েই ঋতুপর্ণ ঘোষ তাঁর দিকে ছুটে আসা এই অনুভবগুলিকে কোনওদিনই মেনে নেননি। মাথা নোয়াননি তার কাছে। অন্য একটি সাক্ষাৎকারে ঋতুপর্ণ এও বলেছিলেন: ‘আমি নিপীড়িত, আমি অবহেলিত, আমি প্রান্তিক, আমি মনে-মনে কখনো আমার এই অবস্থানটাকে ঠাঁই দিইনি, বা সমর্থনও করিনি। আমার চিরকাল মনে হয়েছে যে এই আকাশ-বাতাস-পৃথিবী আর পাঁচজনের মতো আমারও।’
আরও পড়ুন: সমপ্রেমের আলোয় রবীন্দ্রনাথের ‘চিত্রাঙ্গদা’-কে নতুন করে দেখেছিলেন ঋতুপর্ণ
তাই, ‘আমি প্রান্তিক’, এটাই কি আমার একমাত্র পরিচয় হতে পারে? আমরা এখনও অনেকেই ঋতুপর্ণ ঘোষ নামটির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যৌনপরিচয়ের প্রান্তিকতাকে গুলিয়ে ফেলি! ‘আরেকটি প্রেমের গল্প’, ‘মেমোরিজ ইন মার্চ’ এবং ‘চিত্রাঙ্গদা’ তিনটি ছবির বিষয়ই সমপ্রেম আর এই তিনটি ছবির সঙ্গেই প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন ঋতুপর্ণ ঘোষ। এই সংযুক্তিকে তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা-পরিচয়ের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে অধরা থেকে যাবে ঋতুপর্ণ ঘোষের শিল্পসত্তার সূক্ষ্ম দিকগুলি। কারণ, তাঁর পরিচয়ের প্রধান অংশ জুড়ে ছিল সৃষ্টিময়তা। একটু আগে উল্লেখ করা, তিনটি ছবির প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: So, do you see yourself as entering into LGBT activism?’ ঋতুপর্ণ ঘোষের সচেতন ও তীব্র উত্তর ছিল এরকম: ‘No. An artist need not be an activist, and art doesn’t really need to be political all the time.’
মৃত্যুর এগারো বছর পরেও যখন দেখি এখনও ঋতুপর্ণ ঘোষকে অনেকেই তাঁর যৌনপরিচয়ের নিরিখে বিচার করছেন, তখন হতাশ লাগে! তাঁর তৈরি কুড়িটি চলচ্চিত্রের মধ্যে বসবাস করছে অজস্র মানুষের জীবনচিত্রমালা। ধ্বংসপ্রাপ্ত, নিঃসঙ্গ, একাকী ব্যক্তির ভাগ্যপরিহাস। বহু নিস্তব্ধ দৃশ্যসংকেত। সিনেমা নিয়ে কী কী ভাবতেন তিনি? কীভাবে ভাবতেন? তাঁর ব্যক্তিজীবন ও সিনেমাজীবন ঠিক কোথায় একাকার হয়ে যেত? এগুলিই বোধহয় তাঁর মৃত্যুর এতদিন পরে আমাদের ভাববার বিষয়!
ঋতুপর্ণ-র সিনেমা ও তাঁর মনের বিচিত্র পথচিহ্নগুলি সন্ধান এ-লেখার উদ্দেশ্য। ‘ঋতুপর্ণ: নির্জন সিনে-মন’, এই নতুন কলামটি সেই চেষ্টাতেই জারি থাকবে।




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp