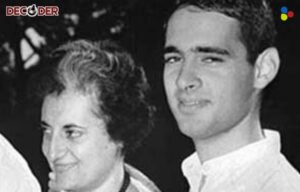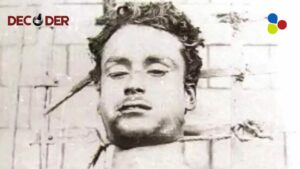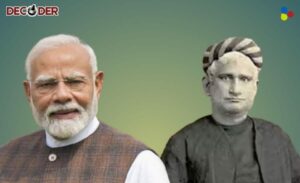বিজ্ঞাপনের মায়াজগৎ! যে নিশিডাক তাচ্ছিল্য করতে পারেননি খোদ রবীন্দ্রনাথও
Rabindranath Tagore: মজার ব্যাপার, এত সব সামগ্রীর মধ্যে মস্তিষ্কবিকৃতি রোগের মহৌষধের বিজ্ঞাপনেও মিলল রবিকবির উপস্থিতি। পাগলের মহৌষধের বিজ্ঞাপনে তিনি লিখলেন, ‘আমি ইহার উপকারিতা বহুকাল যাবৎ জ্ঞাত আছি।’
পঞ্চাশের কবি আশির দশকে এসে লিখলেন, 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে'। হাল আমলের জনপ্রিয়তম কবিদের বিজ্ঞাপনে দেখতে পাওয়াটা আজ আর বিরল কোনও ঘটনা নয়। কী ভাবছেন, এসব হালের আমদানি? যুগের হাওয়া? তেমনটা ভাবলে কিন্তু ভুল হবে। খোদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কিন্তু একাধিক বিজ্ঞাপনের মুখ হয়ে উঠেছিলেন তাঁর সময়ে। এমনকী বিজ্ঞাপনের জন্য লিখেছিলেন জিঙ্গলও।
পণ্য বিক্রয় করতে হলে প্রথমেই যেটা প্রয়োজন, তা সম্পর্কে উপভোক্তাকে জানানো। আর সেই বিজ্ঞাপনের প্রাথমিক উদ্দেশ্যই সেই প্রচারকাজ। প্রাচীন মিশর থেকে গ্রিস কিংবা রোমে প্যাপিরাস ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন দেওয়ার চল ছিল। নিরুদ্দেশ বার্তা জানানোর জন্যও ব্যবহার হত এই বিজ্ঞাপন। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের জন্য দেওয়াল লিখন বা রক পেইন্টিংয়ের চলও মেলে সেই সময় থেকেই। প্রাচীন চিনে প্রাচীনতম যে বিজ্ঞাপনটি পাওয়া যায়, তা অবশ্য ছিল মৌখিক, যা ক্লাসিক কাব্যভাষায় রচিত হয়েছিল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ক্রমশ পুঁজিবাদী অর্থনীতির এক বিরাট শক্তি হয়ে উঠল এই বিজ্ঞাপনই। প্রাক-মুদ্রণ পর্বে বিভিন্ন ট্রেডমার্ক ব্যবহার, রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ঘোষণা যাকে টাউন ক্রিয়ার বলা হত সেসময়ে, আর তাছাড়া ছিল সাইন বোর্ড পদ্ধতি।
তবে মুদ্রন যন্ত্রের আবিষ্কার সেই বিজ্ঞাপনের ইতিহাসে বিশাল বদল নিয়ে এল। ১৬-১৭ শতকে সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমূল বদলে গেল বিজ্ঞাপনের গ্রহ-নক্ষত্র। ষোড়শ শতকে ভেনিসে প্রথম সাপ্তাহিক গেজেট প্রকাশিত হয়। ক্রমে তা ইতালি, জার্মানি এবং হল্যান্ডে ছড়াতে দেরি হয়নি। বাংলায় প্রথম সংবাদপত্র আসতে আসতে অবশ্য আরও দেরি। সেই ১৮১৮ সালে সমাচার দর্পণ, যা শ্রীরামপুরের ব্যপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে প্রকাশ করা শুরু হয়। খবরের কাগজে বাংলা হরফে প্রথম বিজ্ঞাপন কিন্তু ছাপা হয়ে গিয়েছিল তার আগেই, ১৭৭৮ সালে 'ক্যালকাটা ক্রনিক্যাল' নামক ইংরাজি পত্রিকায়। সেই বিজ্ঞাপনটি অবশ্য ছিল বাংলা ব্যকরণ বিষয়ক এক বইয়ের, যার প্রকাশক ছিলেন পঞ্চানন কর্মকার নামে এক ব্যক্তি। কার্যত তিনিই ছিলেন বাংলা মুদ্রণের পথপ্রদর্শক। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলা হরফ নির্মাণের কলাকৌশল আয়ত্ত করেছিলেন পঞ্চানন। চার্লস উইলকিনসন নামে এক সাহেবকে হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ বই ছাপার জন্য বাংলা টাইপফেস তৈরিতে সাহায্যও করেন তিনি। আর সেই পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতেই ধীরে ধীরে বাংলায় প্রকাশিত হতে থাকে নানা পণ্যের বিজ্ঞাপন।
আরও পড়ুন: বিষয়ভাবনায় অভিন্ন হয়েও যেভাবে হাইনের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ
এরই মধ্যে সময় গড়াল। দেশ জুড়ে হইহই করে শুরু হয়ে গেল স্বদেশি আন্দোলনের ধারা। ব্রিটিশদের শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধ গর্জে উঠল গোটা দেশ। বিলিতি দ্রব্য বর্জনের হিড়িক থেকে বাদ গেল না বাঙালিও। একের পর এক দেশি জিনিসের খবরাখবর এ সময়ে উঠে আসতে লাগল বিজ্ঞাপনে। ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানির তৈরি দেশি নিম সাবান মার্গো, নিম টুথপেস্ট থেকে শুরু করে নানা স্বদেশি পণ্য জায়গা করে নিতে শুরু করল বিজ্ঞাপনের পাতায়।

এই সময়ে বিজ্ঞাপনের দুনিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে পড়লেন খোদ কবিগুরু। যতদূর জানা যায়, ১৮৮৯ সাল থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে প্রায় নব্বইটি সংস্থার হয়ে বিজ্ঞাপনে কোনও না কোনও ভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি। বিদেশি ও দেশীয় এয়ারলাইন্স, ভারতীয় রেল থেকে শুরু করে গোদরেজ সাবান, বোর্নভিটা, কুন্তলীন কেশ তেল, রেডিয়ম ক্রিম, বাটা-র জুতো, ডোয়ারকিন হারমোনিয়াম, সমবায় বিমা, ছাপাখানা, কটন মিল, ফটো-স্টুডিয়ো, রেকর্ড, বই, মিষ্টির দোকান, ঘি, দই, কাজল-কালি, পেন্টওয়ার্ক, এমনকী মস্তিষ্কবিকৃতি রোগের মহৌষধ কী ছিল না সেই তালিকায়। কোথাও তিনি লিখেছেন, কোথাও তিনি তাঁর লেখা পঙক্তি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন, তো কোথাও মুখ দেখিয়েছেন স্বয়ং। আনন্দবাজার পত্রিকা, অমৃতবাজার, দ্য স্টেটসম্যান, প্রবাসী, তত্ত্ববোধিনী, ক্যালকাটা গেজেট-এ, আর বিদেশে দ্য গার্ডিয়ান, দ্য গ্লোব-এর মতো পত্রিকাতেও ছাপা হয়েছে সেসব। কেউ কেউ মনে করেন অবশ্য বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থসংগ্রহই ছিল এ সময়ে তাঁর বিজ্ঞাপন জগতে আসার অন্যতম কারণ।
সেসময় অন্যতম একটি প্রসাধনী সামগ্রী ছিল কুন্তলীন তেল। যে সংস্থাটি আবার সাহিত্যিকদের বিশেষ কদর করে পুরস্কার ঘোষণাও করেছিল। সেই কুন্তলীন তেলের প্রচারে জিঙ্গল লেখেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। “কেশে মাখ ‘কুন্তলীন’/রুমালেতে ‘দেলখোস’ /পানে খাও ‘তাম্বুলীন’/ ধন্য হোক্ এইচ বোস।’ শুধু কবিতাই নয়, তেলের খরিদ্দার হিসেবে তার সঙ্গে ছিল এক লাইনের প্রশংসা-বাক্যও— "কুন্তলীন ব্যবহার করিয়া এক মাসের মধ্যে নূতন কেশ হইয়াছে।"

যে মসির জোর স্বদেশিকতার এত ধ্বনি, অথচ দেশে তখন সমস্ত লেখালিখিই হত বিলিতি কালিতে। এই সুযোগে আত্মপ্রকাশ করল দেশি ঝর্না কলম ও কালিপ্রস্তুতকারক সংস্থা সুলেখা। সেই সুলেখা কালির বিজ্ঞাপনে খোদ রবীন্দ্রনাথের র হাতের লেখায় ছাপা হল— ‘কাজলকালি ব্যবহার করে সন্তোষ লাভ করেছি, এর কালিমা বিদেশি কালির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।’

১৯২১ সালে দেশীয় কোম্পানীর উৎপাদিত গোদরেজ সাবানের বিজ্ঞাপনে দেখা গেছে কবিকে। সেখানে কবি লিখেছেন, ‘I know of no foreign soaps better than Godrej’s and I will make a point of using Godrej’s soap.’ পরে আনন্দবাজার পত্রিকায় এই বিজ্ঞাপনটি বাংলাতেও ছাপা হয়। সেখানে লেখা ছিল, ‘গোদরেজ সাবানের অপেক্ষা ভালো কোনো সাবান আমার জানা নাই। আমি ভবিষ্যতে শুধু এই সাবানই ব্যবহার করিব স্থির করিয়াছি।’

রবীন্দ্র-সাহিত্যেরও কম ব্যবহার হয়নি সে সময়কার বিজ্ঞাপনের ভাষায়। তা ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন খোদ রবীন্দ্রনাথই। ইন্ডিয়ার পূর্ব রেলওয়েতে বিজ্ঞাপন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল কবির শ্যামলী কাব্যের বিখ্যাত ‘হঠাৎ দেখা’ কবিতার প্রথম দু'টি লাইন— ‘রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা, ভাবিনি সম্ভব হবে কোনো দিন।’

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, এত সব সামগ্রীর মধ্যে মস্তিষ্কবিকৃতি রোগের মহৌষধের বিজ্ঞাপনেও কিনা মিলল রবি-কবির উপস্থিতি। এস.সি. রায় এন্ড কোং-এর ডাক্তার উমেশচন্দ্র রায়ের পাগলের মহৌষধের বিজ্ঞাপনে তিনি লিখলেন, ‘আমি ইহার উপকারিতা বহুকাল যাবৎ জ্ঞাত আছি।’

এখানেই শেষ নয়। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞাপনের তালিকা কিন্তু আরও দীর্ঘ। তখনকার স্টুডিও এস ঘোষের বিজ্ঞাপনে কবিগুরুর ছবি ব্যবহার করা হয়েছিল এবং সেখানে কবি লিখেছিলেন, ‘এস ঘোষ আমার যে দু'টি ফটোগ্রাফ তুলেছেন তা অতি সুন্দর ও সুনিপুণ। দেখে আমি বিস্মিত ও সন্তুষ্ট হয়েছি। তাদের ব্যবসায়ে তারা যে যথেষ্ট সফলতা লাভ করবেন তাতে আমার সন্দেহ নেই। ’

শুধু যে দেশীয় পণ্যের বিজ্ঞাপনেই রবীন্দ্রনাথ প্রকট হয়ে উঠলেন, তা কিন্তু নয়। তাকে আখছার দেখা যেতে লাগল বিভিন্ন বিদেশী পণ্যের বিজ্ঞাপনেও। ব্রিটেনের তৈরি স্বাস্থ্যকর পানীয় ‘বোর্ন-ভিটা’র বিজ্ঞাপনে নিজের ছবির পাশে তার স্বাক্ষরিত এক লাইনে পণ্য সম্পর্কে মতামত জানালেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি লিখলেন, ‘বোর্ন-ভিটা সেবনে উপকার পাইয়াছি।’ সেই বিজ্ঞাপন ছাপা হল তখনকার কাগজ-সংবাদপত্রে।

শুধু বোর্ন ভিটা নয়। 'কে এল এম রয়াল ডাচ' এয়ারলাইন্সের জন্যেও একটি বিজ্ঞাপন লিখে দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। রয়াল ডাচ এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ আবার সেই বিজ্ঞাপন 'গুরুদেবের বিমান যাত্রা' শিরোনামে বিশ্বভারতী পত্রিকাতেও প্রকাশও করলেন। ইনস্যুয়েরেন্স কোম্পানি, হারমোনিয়াম, বাটা-সহ একাধিক সংস্থার বিজ্ঞাপনে তখন রবীন্দ্রনাথেরই রমরমা।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার জন্য টাকা সংগ্রহের তাগিদে তিনি যতই বিজ্ঞাপন করুন না কেন, নীতি-নৈতিকতার ব্যপারে বরাবরই কঠোর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। একবার ভারতীয় একটি ব্লেড সংস্থা বিজ্ঞাপন বার্তার জন্য দ্বারস্থ হলেন রবীন্দ্রনাথের। রবির তখন একহাত লম্বা দীর্ঘ শ্বেতশুভ্র দাড়ি। সাধের সেই দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে রবীন্দ্রনাথ নাকি সস্নেহে বলেছিলেন, “এই দাড়ি নিয়ে আমি যদি বিজ্ঞাপন করি তাহলে কেউ কি তোমাদের ব্লেডের ধারে আস্থা রাখবে? না আমাকে করবে বিশ্বাস?”
আরও পড়ুন: তরুণ কবিদের মধ্যে আদৌ জেগে আছেন রবীন্দ্রনাথ?
নিজে বিজ্ঞাপনের অংশ হয়েছেন অসংখ্যবার। পাশাপাশি তাঁর বিভিন্ন রচনায় বারবার উঠে এসেছে বিজ্ঞাপনের উল্লেখ। এমনকী নিজের কাজের বিজ্ঞাপন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি রবীন্দ্রনাথ। আসলে আদ্যোপান্ত আধুনিকতম মানুষটি বোধহয় তখন থেকেই মালুম করতে পেরেছিলেন, আগামী যে যুগ আসতে চলেছে, তাতে রাজত্ব করবে বিজ্ঞাপনই। পরিবর্তিত পৃথিবীতে যে চিৎকার না করে মানুষকে আর কোনও কথাই শোনানো যাবে না, তা ভালোই বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। তবে বিজ্ঞাপনের মতো বাণিজ্যবান্ধব প্রচারপদ্ধতি যে একদিন মানুষের মুখটুকুকে ঢেকে দিয়ে মুখোশটাকেই জাগিয়ে রাখবে কেবল, তেমন প্রত্যাশা করেছিলেন কি তিনি আদৌ? কে জানে!




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp