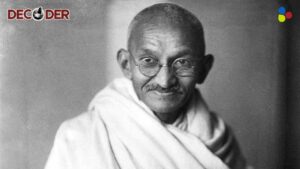২০৩০-এ মানুষের কাছে সুখের ধারণাটুকুও থাকবে না? || কথাবার্তায় রত্নাবলী রায়
সাধারণভাবে সরকারি ক্ষমতাকেন্দ্রগুলি জনস্বাস্থ্য বলতে শরীর ও শারীরিক স্বাস্থ্যকে যতখানি গুরুত্ব দেয়, মানসিক স্বাস্থ্যকে ঠিক ততটা গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না, অথবা প্রয়োজন আছে বুঝেও সচেতনভাবেই এড়িয়ে যায়। কোভিড পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের গণউদ্যোগের সমন্বয়ে, জনস্বাস্থ্য সম্মেলনের মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে, জনস্বাস্থ্য মোর্চা বা পিপলস অ্যালায়েন্স ফর পাবলিক হেলথ। এই জনস্বাস্থ্য সম্মেলন কোভিড পরিস্থিতিতে মানসিক মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকার নিয়ে একটি দলিল গ্রহণ করেছে। এই বিষয়ে অশেষ সেনগুপ্তর সঙ্গে কথা বললেন মানসিক স্বাস্থ্য অধিকার আন্দোলনের দীর্ঘদিনের কর্মী রত্নাবলী রায়। সেই ভিডিও কথোপকথনের অংশবিশেষ দ্বিরালাপে অংশগ্রহণকারীদের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত হল।
অশেষ: মানসিক স্বাস্থ্য, তার অধিকার এবং মানসিক স্বাস্থ্য আন্দোলন নিয়ে ধারণাগুলো এখনও সম্ভবত খানিক অস্পষ্ট। আপনি যদি আলোচনার শুরুতেই মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য আন্দোলন- এই বিষয়টা বুঝিয়ে বলেন, তবে আমাদের পরবর্তী আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যেতে আরও সুবিধা হবে। শারীরিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পর্কটাকে মানসিক স্বাস্থ্য অধিকার আন্দোলন কীভাবে দেখে, সেটাও যদি একটু পরিষ্কার করে বলেন ভালো হয়।
রত্নাবলী: আমার একটা অভিজ্ঞতা রয়েছে। একটা দেখা আছে। মানসিক স্বাস্থ্য ও মনোরোগের সঙ্গে একটা জীবনযাপন রয়েছে। আমি মূলত এই জায়গা থেকেই কথা বলছি। আমাদের কল্পনায় মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক রোগ- এই দুটো সমার্থক। বিধিবদ্ধভাবে মানসিক স্বাস্থ্য বলতে, আমাদের প্রত্যেকের ভেতরের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ায় যে লক্ষণগুলো প্রকাশিত হয়, সেগুলো কিছু স্কেল দিয়ে মাপা হয়। ডিএসএম ফাইভ বা আইসিডি ইলেভেন- এরকম কিছু মাপকাঠিতে এই মাপগুলোর মানেকে ব্যখ্যা করা হয়। সেটা সম্পূর্ণ একটা আলাদা আলোচনার বিষয়।
সর্বভারতীয় স্তরে, আমরা কয়েকজন, এই কথাটাই বারবার বলার চেষ্টা করি যে, মানসিক স্বাস্থ্য মানে শুধু এটা নয়, এটুকু নয়। মানসিক স্বাস্থ্য প্রতিটা মুহুর্তে আছে, প্রতিটা জায়গায় আছে। এই এখন যে আমরা আলোচনা করছি, এখানেও আছে। আপনার পছন্দমতো কোনও একটা বই পড়লে, সিনেমা দেখলে বা ভালো কোনও খবর পেলে আপনার আনন্দ হয়। এই আনন্দ উপভোগ করার মধ্যেও মানসিক স্বাস্থ্য আছে।
আরও পড়ুন: ‘হ্যামলেট’-এর মতোই আমরা প্রত্যেকে চাইছি প্রতিশোধ: কৌশিক সেন
এখন মানসিক স্বাস্থ্য বোঝাতে গেলে, একটা বায়োমেডিক্যাল হেজিমনি দিয়ে বোঝানো হয়। মানে, মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়টা, অধিকাংশের ভাবনায় শুরুই হয় সাইকিয়াট্রিস্টের চেম্বার থেকে। যেন, মানসিক স্বাস্থ্য মানেই মানসিক রোগ।
মাথার ওপরে নিশ্চিত ছাদ, এক প্লেট ভাত-ডালের নিশ্চয়তা- এর মধ্যে যে মানসিক স্বাস্থ্য আছে, সেগুলোকে বাদ দিয়ে যদি কিছু মাপের, কিছু খোপের মধ্য দিয়ে যদি মানসিক স্বাস্থ্যকে দেখা এবং দেখানো হয়, তাহলে, মানসিক স্বাস্থ্যের পরিসরটাকেই খুব খাটো করে ফেলা হয়, লঘু করে দেওয়া হয়।
চিকিৎসকরা বলতে পারেন, বলেন, যে, আমার এই দাবিটাও বায়োমেডিক্যাল অ্যাপ্রোচের ওপর দাঁড়িয়ে বলা। অবশ্যই আমি বায়োমেডিক্যাল অ্যাপ্রোচের ওপর দাঁড়িয়ে বলছি। বায়োমেডিক্যাল অ্যাপ্রোচটা না জানলে আমি সামাজিক, অর্থনৈতিক- এরকম বিভিন্ন কার্যকারণের মিশেলের কথা বলতে পারতাম না। যে বিষয়টা এখানে বলা জরুরি, সেটা হলো, আমরা কি প্রাত্যহিক জীবনের যে কোনও বিপর্যয়, যে কোনও অসুখকে প্যাথোলোজাইজ করব?
আরও পড়ুন: দৃষ্টি ফিরে পাবে অন্ধ! অসাধ্যসাধন থেকে একহাত দূরে দাড়িয়ে ওঁরা
ধরা যাক, মুর্শিদাবাদের একটি গ্রামে, চার সন্তানের একজন মা, প্রত্যেক সকালে পাঁচ কিলোমিটার হেঁটে জল আনতে যান। বাড়ি ফিরে, উনুনে আঁচ দিয়ে রান্না বসাতে হয়, কারণ তাঁর ছেলেমেয়ে স্কুলে যাবে। তারপরে সংসারের অন্যান্য কাজে হাত দিতে হয়। তাঁর স্বামী কখনও কাজে যান, কখনও যান না, সেটা যেতে চান না বলেও হতে পারে, কাজ পাননি বলেও হতে পারে। এই স্বল্প এবং অনিয়মিত রোজগারের টাকায় তাঁকে সংসার চালাতে হয়। এরপরে কখনও কখনও স্বামী গায়ে হাত তোলেন। কিন্তু মহিলা নিজেকেই বোঝান, স্বামী তো আসলে তাঁকে ভালোই বাসেন। কিন্তু তারপরে, তাঁর গায়ে-হাতে-পায়ে ব্যথা হয়, তিনি জল আনতে যেতে পারেন না, ঘড়ির কাঁটা ধরে সংসারের কাজগুলো করতে পারেন না, তাঁর দশ বছরের মেয়ে যখন তাঁর ছোট ছেলের দেখভাল করে, তখন তাঁর যদি কান্না পায়, তখন এই গোটাটা 'অবসাদ’ দিয়ে বোঝা যাবে না।
মানসিক স্বাস্থ্যকে দেখার যে বায়োমেডিক্যাল হেজিমনি, তাকে প্রশ্ন করার দরকারটা এইখানে। এর মানে বায়োমেডিক্যাল অ্যাপ্রোচ বা মডেলকে খাটো করা নয়, এর সঙ্গে অন্য পারিপার্শ্বিকতাকেও চিন্তাভাবনার মধ্যে আনা। একটা কোনও ওষুধের প্রেসক্রিপশন দিয়ে এই মানুষটির মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থাকে নির্দ্দিষ্ট করা যাবে না। সেখানে বাকি বিষয়গুলোকেও হিসেবের মধ্যে আনতে হবে। এই থ্রিসিক্সটি ডিগ্রি অ্যাপ্রোচটাই মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়। মানসিক স্বাস্থ্য আর মানসিক রোগ এই দুটো একই ব্যাপার- এমনটা একেবারেই নয়।
আমাদের দেশে বা বিশ্বে কোনও একটামাত্র আন্দোলন নেই। অনেকগুলো অভিমুখ আছে। একটা অভিমুখ, যাঁরা বায়োমেডিক্যাল অ্যাপ্রোচটাকে একেবারেই মুখ্য নয়, বরং গৌণ বলে মনে করেন। এঁদের জন্য একটা লেবেল বরাদ্দ হয়ে গেছে। মূলত সাইকিয়াট্রিস্টরাই এই নামে এঁদের চিহ্নিত করেন। 'অ্যান্টি-সাইকিয়াট্রি' মুভমেন্ট।
আরেক ধারার আন্দোলন হচ্ছে, ভুক্তভুগী মানুষদের আন্দোলন। আমি নিজে এই ধারাটির সঙ্গে যুক্ত। এখানে, আমাদের মূল কথা হলো, ভুক্তভুগী মানুষের কথা শোনার অভ্যাস করতে হবে। কেন্দ্রে রাখতে হবে মানবাধিকার, লিঙ্গ ও যৌনতার প্রশ্ন। এই সবকিছুকে একসঙ্গে বিবেচনা করে, তারপরে হয়তো একটা 'প্রেসক্রিপশন’ দেওয়া যেতে পারে। ধরা যাক, জীবনযাপনে অন্যরকম যৌনতায় বিশ্বাসী কাউকে যদি স্বাভাবিকতার খোপে পোরার চেষ্টা করা হয়, সেটা তাঁর অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়। চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান তখন একরকম এর দ্বাররক্ষার কাজ করে। দরজার ভেতরে কার প্রবেশাধিকার আছে বা কার নেই, সেটা ঠিক করে, তার স্বাভাবিকতার বোধ দিয়ে। আমরা এই দারোয়ানিটাকে প্রশ্ন করছি, বিজ্ঞানকে বাতিল করছি না। আমরা ক্ষমতার আধিপত্যকে প্রশ্ন করছি। আমাদের দাবিটা সহযোগিতার। রোগীর সঙ্গে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে প্রেসক্রিপশনে পৌঁছনো, রোগীর অধিকারকে বাতিল করে নয়।
এই প্রসঙ্গে একটা অন্য কথাও বলা দরকার। আমাদের পরিচিতদের মধ্যে অনেকেই ইউনিভার্সাল হেলথকেয়ার-এর দাবি করেন। এই দাবিতে যে আন্দোলন তার একদম সামনের সারিতে আছেন তাঁরা আমরা শারীরিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এই দাবিটা যতটা জোরালোভাবে করা দরকার মনে করছি, তারাই কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এই দাবিটা করছি না, করতে পারছি না। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পৃক্ততার বিষয়টা সম্পর্কে আমরা যারা স্বাস্থ্য আন্দোলনের শরিক বলে নিজেদের দাবি করছি, তারাও সবসময় খুব বুঝে উঠতে পারছি না। এ-ব্যাপারে সদিচ্ছার অভাব আছে, এমন নয়। অভাবটা সম্ভবত নেতৃত্ব দেওয়ার প্রশ্নে, বোঝাপড়ায়। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের মধ্যে এই সম্পৃক্ততার ব্যাপারটা যদি ঘটিয়ে তোলা যেত, তাহলে হয়তো আমাদের রাজনৈতিক অবস্থানটা আরও জোরালো হত।
অশেষ: মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকার আর আন্দোলনের প্রশ্নে আমরা আবার আলোচনায় ফিরব। তার আগে, সাম্প্রতিক একটি বিষয় নিয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করে নিই। সাম্প্রতিকতম বাজেটে মানসিক স্বাস্থ্যের উল্লেখ এবং তার জন্য অর্থ বরাদ্দর বিষয়টাকে আপনি 'টোকেনিজম' বলে অভিহিত করেছেন। এর মধ্যে কোনওরকম আশার আলোই দেখতে পাচ্ছেন না?
রত্নাবলী: প্রথমত, আমি যখন 'টোকেনিজম’ বলছি, তখন আমি কোনও আশার আলোই দেখতে পাচ্ছি না, এই পূর্বানুমানের মধ্যে একরকম বাইনারি আছে। আমি এরকম কোনও বাইনারিতে বিশ্বাস করি না। বাজেট নিয়ে ক্রিটিকাল হওয়া, সেটা এরাজ্য থেকে হয়তো আমি করেছি, কিন্তু জাতীয় স্তরে আরও অনেকেই করেছেন, তার মানে এই নয় যে, আমি কোনও আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না। বলা যেতে পারে, সরকারের থেকে আমাদের প্রত্যাশা আরও অনেকটা বেশি। এবার, আমরা কি আমাদের আশাগুলোকেই একটা খাটো মাপে বেঁধে ফেলব? যদি সেটা হয়, তাহলে, এর থেকে বেশি কিছু আমরা কখনওই ভেবে উঠতে পারব না।
আর সমালোচনার জায়গা তো আছেই। ২০২১-এ অতিমারী পরিস্থিতিতে বাজেট পেশের সময়ে মানসিক স্বাস্থ্যের কোনও উচ্চারণও ছিল না। এবং মানসিক স্বাস্থ্যের এই উল্লেখ না থাকা নিয়ে, বিভিন্ন মহল থেকে অনেকেই অসংবেদনশীলতার অভিযোগ তুলেছিলেন। যে সময় মানুষ ন্যূনতম খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের সংস্থান করতে পারছেন না, বাইরে কাজ করা শ্রমিকরা বাড়ি ফিরতে পারছেন না, শিশুরা নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছেন, আত্মহত্যার ঘটনা বাড়ছে- তখন যদি বাজেটে মানসিক স্বাস্থ্যের উল্লেখমাত্রও না থাকে, তাহলে সেটা অসংবেদনশীল তো বটেই। এই নিয়ে কোনও সন্দেহর অবকাশ থাকে না।
২০২১-এর বাজেটের এই প্রতিক্রিয়ার ফলে ২০২২-এর বাজেটে মানসিক স্বাস্থ্যের যেটুকু উল্লেখ পাওয়া গেল, সেটা বড়জোর একটা আপৎকালীন ব্যবস্থা বলা যায়। অতিমারী পরিস্থিতিতে যাঁরা চাকরি হারিয়েছেন, অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন, একটা দীর্ঘস্থায়ী উদ্বেগের চক্রে প্রবেশ করেছেন, তাঁদের জন্য টেলি-মেন্টাল হেল্থ সেন্টারের মাধ্যমে কাউন্সেলিং-এর ব্যবস্থা হলো। কিন্তু ২৩টি টেলি-মেন্টাল হেলথ সেন্টার- এই সংখ্যাটা নির্দিষ্ট হলো কী করে? পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সারা দেশে, মোট ২৫ কোটি মানুষ কোনও না কোনও মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত, সেখানে এক কোটি মানুষ পিছু, একটি টেলি মেন্টাল হেলথ সেন্টারের বরাদ্দ করার হিসেবটা হলো কীভাবে? এগুলো কোন কোন রাজ্যে হবে? কারা এটা পরিচালনা করবেন? তাঁদের কী প্রশিক্ষণ থাকবে? যিনি ফোনে নিজের সমস্যার কথা বলতে চাইবেন, তিনি কি সবসময় খুব গুছিয়ে নিজের সমস্যা বলতে পারবেন? মানুষের কথা শুনেে, তাঁদের সঙ্গে কথা বলে উপশম দেওয়ার কাজটা খুব সহজ নয়। তার ওপর, একটা বড় অংশের মানুষ ডিজিটাল মাধ্যমে অভ্যস্ত নন, আরও অনেকের সেই মাধ্যম ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় আর্থিক সংগতি নেই। স্মার্টফোন ব্যবহারের অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাও থাকতে পারে। আমি শুধু এই প্রশ্নগুলো তুলতে চেয়েছি। এবং এই বাজেটের এই বন্দোবস্তকে একটা আপৎকালীন ব্যবস্থাই বলছি। কারণ মানসিক স্বাস্থ্যের সার্বিক উন্নতির জন্য যা যা করা দরকার, তার একটাও এটা দিয়ে মিটবে না।
প্রান্তিকতম মানুষটির কাছে, তার মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে, এই ২০২২-এও, আমরা কি, ‘মানসিক স্বাস্থ্য নিরাময়যোগ্য’- এরকম একটা স্লোগানকে সামনে রেখে এগোব? না কি, তাঁর অধিকার, মাথার ওপর ছাদের অধিকারের কথা বলব!
সরকারি কাঠামোর মধ্যেই যদি এই ভাবনাগুলো না থাকে, এবং বৈষম্যের ধারণা থাকে, তাহলে বাজেটে সেই না-থাকা এবং থাকাগুলোই তো প্রতিফলিত হবে!
আরও পড়ুন: আমার গ্রামবাংলার গল্প পড়ে বিদেশি পাঠকরা মুগ্ধ: অমর মিত্র
অশেষ: কিছুদিন আগে অন্য এক আলোচনা প্রসঙ্গে আপনি কোভিড পরিস্থিতির মোকাবিলায় যুদ্ধের মেটাফর ব্যবহার করার কথা বলেছিলেন। আপনার বক্তব্য ছিল, শব্দচয়নের এই রাজনীতি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এই যে যুদ্ধ-জিগিরের কোভিড ভাষ্য, তা নিয়ে কোনও পরিচিত দলীয় রাজনৈতিক অবস্থান থেকেও তেমন কিছু শোনা যায়নি। এই কোভিড ভাষ্য, যুদ্ধ-জিগির ইত্যাদি নিয়ে মানসিক স্বাস্থ্য আন্দোলনের বক্তব্যটা ঠিক কী?
রত্নাবলী: যুদ্ধের মেটাফর, যুদ্ধ-জিগির ব্যক্তিগতভাবে আমাকে খুবই অস্বস্তিতে ফেলে। কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলায় রাষ্ট্রের কাছে যখন কোনও পরিকল্পনা থাকে না, তখনই তার যুদ্ধ-জিগিরের প্রয়োজন পড়ে। যুদ্ধের মেটাফর নিয়ে এলে দেশবাসীর প্রশ্ন করার অধিকারটাকেই বাতিল করে দেওয়া যায়। মনস্তাত্ত্বিকভাবে, দেশবাসীর প্রতি দায়িত্বের প্রশ্নটাকে পিছনে ঠেলে দেওয়া যায়। বরং রাষ্ট্রের প্রতি দেশবাসীর দায়িত্ব- এরকম একটা ধারণাকে সামনে নিয়ে আসা সম্ভব হয়। সরকারি স্তরে অপরিকল্পনা বা পরিকল্পনার অভাব গোটাটাকেই খুব পরিকল্পিতভাবে যুদ্ধ-জিগির দিয়ে আড়াল করা হল। পরিস্থিতি মোকাবিলায় যৌথতা তৈরি করার বদলে, ব্যক্তিমানুষকে ঘরবন্দি থাকার নিদান দেওয়া হল। এই গোটাটাই করা হল একটা আধিপত্যের অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে, ক্ষমতার দাপটে।
চিকিৎসক, নার্স, অন্যান্য চিকিৎসা-কর্মী, চিকিৎসা পরিষেবা যাঁরা দেন- তাঁদেরকে 'কোভিড ওয়ারিয়র' নাম দিয়ে যে উদযাপন করা হল, তার আড়ালে তাঁদের ব্যক্তিগত ভয়, অস্বস্তি এগুলোকে কোনও গুরুত্ব দেওয়া হল না, গ্রাহ্যের মধ্যেই আনা হল না। তাঁদের কারও কিছু হলে, 'এমনটা তো হতেই পারে'- এরকম একটা ভাব করে ছেড়ে দেওয়া হল। এঁদের 'ডিজপোজেবল' ভাবাটাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য যুদ্ধ-জিগিরটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।
অশেষ: পরিকল্পনা আর ব্যয়বরাদ্দ নিয়ে আমাদের কথা প্রসঙ্গে একজন বলেছেন, মানসিক স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়বরাদ্দের সম্পূর্ণটাও খরচ হয় না। এই অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে টেলিমেন্টাল হেলথ সেন্টারের সিদ্ধান্তের পিছনে নীতিপ্রণয়নকারীদের ঠিক কী ধরনের ভাবনা থাকতে পারে?
রত্নাবলী: এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। গত বছরে, চল্লিশ কোটি টাকা মাত্র বরাদ্দ ছিল। শেষ পর্যন্ত খরচ হয়েছে, তার অর্ধেক, কুড়ি কোটি টাকার আশেপাশে কোনও একটা পরিমাণ। এটা হলে সরকারের একটা সুবিধে হয়, বরাদ্দ টাকাটা যখন খরচ হচ্ছে না, তার মানে এত টাকা বরাদ্দ করার কোনও প্রয়োজন নেই। ফলে সরকারের পক্ষে এটা ভাবা এবং ভাবানো সহজ ও সম্ভব হয় যে, এই টাকাটা এই খাত থেকে সরিয়ে প্রতিরক্ষা-খাতে বরাদ্দ করা এবং খরচ করা বেশি যুক্তিযুক্ত।
এখানে একটা অন্য বিষয় মাথায় রাখা দরকার। স্বাস্থ্য রাজ্যের এক্তিয়ারের বিষয়। তাই শুধু বরাদ্দ নয়, সেই বরাদ্দটা কোন খাতে, কেন, কীভাবে খরচ করা হবে, সেটাও একটা পরিকল্পনার বিষয়। শেষ ইউপিএ সরকারের সময়, ১১০০ কোটি টাকা, মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু সেই সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে একটি টাকাও খরচ হয়নি। কারণ কীভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে, তার কোনও নীল খসড়া তৈরি হয়নি। এটা কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ নয়। এখানে, অ-সরকারি ও সামাজিক সংগঠনগুলোর সহযোগিতায় কীভাবে এই সচেতনতা বৃদ্ধির কাজটা হতে পারে, সেটা নিয়ে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। কারণ সরকারি নীতিনির্ধারকরা, অ-সরকারি ক্ষেত্রের মানুষদের কাছ থেকে নীতি-সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে কোনও মতামত শুনতে আগ্রহী নন। অ-সরকারি সংগঠনগুলোকে দেখা হয় শুধুই গৃহীত নীতিকে কার্যকর করার কাঠামো হিসেবে। নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অ-সরকারি সামাজিক সংগঠনগুলোর অভিজ্ঞতা যে খুবই কার্যকর হতে পারে, সে ব্যাপারে সরকারি স্তরে খুব স্পষ্ট আপত্তি আছে, এটা দীর্ঘদিন ধরেই আছে। সেজন্যই আমরা যখন মানসিক স্বাস্থ্য আইনের খসড়া লিখছিলাম, তখন আমরা মানসিক স্বাস্থ্য আইনের আওতায় যে নীতি প্রণয়নকারী কমিটিগুলো আছে, সেগুলোতে অ-সরকারি ও সামাজিক সংগঠনের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছি। ঘটনা হচ্ছে, আজ পর্যন্ত কোনও নীতি প্রণয়নকারী কমিটি হয়নি।
অশেষ: এই যে ২০২২-এর বাজেটে, টেলিমেন্টাল হেলথ সেন্টারের উদ্যোগকে মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি সরকারের যথেষ্ট যত্নের পরিচায়ক বলে অনেকে মনে করছেন, সেটাকে আপনি আপৎকালীন ব্যবস্থার বেশি কিছু মনে করছেন না। অথচ, প্রায়োগিক অভিজ্ঞতায়, মানসিক স্বাস্থ্যের বেশিরভাগটাই কাউন্সেলিং এবং ওষুধ। আপনি এর আগে মানসিক স্বাস্থ্যকে বোঝার ক্ষেত্রে বায়োমেডিক্যাল হেজিমনিকে একমাত্র করে দেখার বিরুদ্ধে আপনার যুক্তিগুলো বলেছেন। কিন্তু ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে যে ঘটমানতা, তার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রকরণ ঠিক করাই যদি মানসিক স্বাস্থ্যের চিকিৎসা হয়, তাহলে, সাম্প্রতিক সরকারি ঘোষণা এবং প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা এদুটো বেশ সাযুজ্যপূর্ণ। সেখানে, আপনি বা আপনার মতো করে যাঁরা ভাবছেন, বলছেন, তাঁরা তাঁদের শক্তি সংগ্রহ করবেন কোথা থেকে? কীভাবে?
রত্নাবলী: এটা ইন্টারেস্টিং। এখানে আমাকে প্রথমে নিও-নরম্যাল শব্দবন্ধটাকে এক্সপ্লেন করতে হবে। নিও-নরম্যাল মানে, এককথায়, যেখানে কোনওরকম প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষের কোনও দায় নেই। পুরো দায়টাই ব্যক্তির। ব্যক্তিকেই সবকিছুর সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। মানিয়ে নিতে হবে। এটা কিন্তু মনস্তত্ত্ব চর্চার মূল বিষয় নয়। মনস্ততত্ত্ব চর্চার মূল বিষয় হলো, বিভিন্নতাকে উদযাপন করা। আমরা আমাদের সুবিধার্থে মনস্তত্ত্বকে একটা অস্ত্র হিসেবে, একটা সবখোল চাবি হিসেবে ব্যবহার করি, যেখানে সবকিছুকেই আমরা ‘মেনে নেওয়া’ আর 'মানিয়ে নেওয়ার’ বিষয় করে তুলি। প্যানিক এবং অ্যাংজাইটি অত্যন্ত স্বাভাবিক একটা প্রতিক্রিয়ার ধরন। তার সঙ্গে আমাদেরই বা 'মানিয়ে নিতে’ হবে কেন? সেটার কার্যকারণ সম্পর্ক বুঝে সেটার মোকাবিলা করতে হবে তো! সেটা কতখানি বাস্তব, কতটা ব্যক্তির নিজের মধ্যের অস্বস্তি- সেটা বোঝা এবং বুঝিয়ে বলাই তো মনোবিদ্যা নিয়ে যিনি চর্চা করছেন, তাঁর কাজ। আমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ, বিশেষ করে আমি অনুত্তমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলব, যিনি বিভিন্নতার উদযাপনটাতেই জোর দেন; প্যানিক, অ্যাংজাইটি হবে না- এরকম একটা দাবির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কথা বলেন। বাইরের জগতের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করার নিদানের বিরুদ্ধে কথা বলেন।
তাই মেনে নেওয়া, মানিয়ে নেওয়ার নিদানগুলো মনোবিদ্যা চর্চার সংকীর্ণতা বলে দেখলে ভুল হবে। এটা অনুশীলনের সংকীর্ণতা। প্রয়োগের সংকীর্ণতা। এটা আমরা যাঁরা এই সংকীর্ণতাকে অনুশীলন করি, তাঁদের সমস্যা। আমরা এখন আর রোগীর এজেন্ট হিসেবে কাজ করি না, আমাদের অ্যাজেন্ডা পুশ করতে চাই।
আর একটা কথা আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে চাই। যাঁরা মনোবিদ্যা চর্চার সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের পরিষ্কার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন। (এখানে রাজনীতি মানে, দলীয় রাজনীতি নয়, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি) রাজনৈতিক ঘটমানতা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। এই কথাটা এর আগে আমি যখন লিখেছিলাম, তখন অনেক বিতর্ক হয়েছিল। বলা হয়েছিল, মনোবিদ্যা চর্চার শর্ত হচ্ছে নন-জাজমেন্টাল থাকা। আমি খুব পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, নিজস্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা আর নন-জাজমেন্টাল থাকার মধ্যে কোনওরকম বিরোধ নেই। রাজনৈতিক বোধের গভীরতা নন-জাজমেন্টাল হতে কোনও অসুবিধে সৃষ্টি করে না। বরং ওই গভীরতাটা জরুরি। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতার কারণে যদি কেউ মনে করেন সমকামিতা অপরাধ, তাহলে রোগীর সঙ্গে কথোপকথনে সেটা বারংবার বেরিয়ে আসবে।
অশেষ: আরেকটা প্রশ্ন যেটা ছিল, কোভিড পরিস্থিতিতে মানসিক স্বাস্থ্য আন্দোলনের বক্তব্য কী ছিল? এই প্রসঙ্গে একজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন, লকডাউন, আইসোলেশন, কোয়ারেন্টিন ইত্যাদি পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে কী মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষ থেকে কিছু বলার দরকার ছিল?
রত্নাবলী: অবশ্যই ছিল। কোয়ারেন্টিন আর আইসোলেশন- এই দুটো কথার মধ্যে একটা ভাবাবেগগত ভিন্নতা আছে। কোয়ারেন্টিন আমাকে করতে বলা হয়। আইসোলেশন আমি নিজে করি। একটা চয়েসের প্রশ্ন, পছন্দের স্বাধীনতার প্রশ্ন এখানে রয়ে যায়। তাই, এই দুটো শব্দের মানে এক নয়। একটার বদলে আরেকটাকে ব্যবহার করা যাবে না। রাষ্ট্র বারবার কোয়ারেন্টিনের কথা বলেছে। যাঁরা 'দায়িত্বশীল নাগরিক' হয়ে থাকতে চেয়েছেন, তাঁরা আইসোলেট করেছেন। এটা তাঁদের নিজস্ব পছন্দ এবং সিদ্ধান্ত।
আইসোলেশনে যে মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যা হয়েছে, তার ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। এবং সেখানে, প্রতিবন্ধকতা আছে, এমন মানুষদের যে কী হেনস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছে, তার অজস্র বয়ান পাবলিক ডোমেনে আছে। কে ভেন্টিলেটর পাবে, আর কে ভেন্টিলেটর পাবে না, তার মধ্যে আমরা একটা বড় বৈষম্য দেখেছি। সেখানে প্রতিবন্ধী মানুষকে ডিসপোজেবল ভাবা হয়েছে। যাঁর একাধিক প্রতিবন্ধকতা আছে, যাঁকে অন্যরা সাহায্য করেন, এরকম মানুষ দিনের পর দিন না খেতে পেয়ে মারা গেছেন। তাঁর খাবারের অভাব ছিল না। কিন্তু তিনি নিজের হাতে, মুখ পর্যন্ত খাবার তুলে খেতে পারেন না। ফলে তিনি মারা গেছেন। এই বাস্তবতাগুলো নিয়ে আমরা একদমই আলোচনা করিনি।
বেহালায়, বাবা এবং তাঁর প্রতিবন্ধকতা-যুক্ত সন্তান বিষ খেয়ে মারা গেলেন। এর থেকে করুণ ভাষ্য আর কিছু হতে পারে না। প্রতিবন্ধকতা-যুক্ত মানুষদের এই কথাগুলো কি মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষ থেকে ততটা জোরালোভাবে বলা গেছে? না। এবং সেটা আমাদের অক্ষমতা। আরও অনেক জোরালো গলায় সেই কথাগুলো বলতে হবে। যাঁরা আমাদের আজকের এই কথোপকথন পড়বেন, এর সংহতিতে, তাঁদেরও সকলকে একসঙ্গে জোর গলায় এই প্রশ্নগুলো তুলতে হবে। আসলে মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয় বরাবরই দূর একটা গ্রহ হিসেবে রয়ে গেছে। এবং সেটাকে বিশেষজ্ঞদের এক্তিয়ারভুক্ত একটা বিষয় বলে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। সাধারণ মানুষকে যে এ-ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে সেই প্রচারটা হয়নি।
অশেষ: আজকে কম্পিউটেশনাল কগনিশন বলে যে অ্যাকাডেমিক ডিসিপ্লিনটা, সেটা বহুলাংশে সাইকোলজির ওপরে নির্ভর করে। অঙ্ক, রাশিবিদ্যা, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ইত্যাদি বিষয়গুলোর সঙ্গে সাইকোলজি চর্চার ইন্টার-ডিসিপ্লিনারিটি এখন যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে আপনি যখন সাইকোলজিকে , সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সঙ্গে ইন্টারসেকশনাল হতে হবে, সাইকোলজির পাঠক্রমকে ইন্টার-ডিসিপ্লিনারি হতে হবে- এই দাবি করছেন, সেটা মান্যতা পেতে অসুবিধে হচ্ছে। এই দু'রকমের ছবি সামনে আসছে কেন?
রত্নাবলী: এটার উত্তর খুব সহজ। শোনা যায়, অবিভক্ত রাশিয়ায় বিরোধী কন্ঠস্বরকে দমন করার বিরোধিতা করছেন, এমন মানুষদের 'স্কিৎজোফ্রিনিক' বলে দাগিয়ে দেওয়া হতো। মানে, বিরোধিতাকে নস্যাৎ করার জন্য সাইকোলজিকে, সাইকিয়াট্রিকে একটা পলিটিক্যাল ওয়েপন, একটা রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। বিগ ডেটার ক্ষেত্রেও একই রকম। ধরুন আপনি ফোনে বললেন শুঁটকি মাছ খাব, এবার আপনার স্মার্ট ফোনে, বিবিধ প্রকারের শুঁটকি মাছ এবং সেগুলো কোথায় পাওয়া যাবে, তার বিজ্ঞপ্তি আসতে থাকল। এভাবে কারও থেকে অনৈতিকভাবে সংগৃহীত ডেটা দিয়ে তাঁকে সাইকোলজিক্যালি ম্যানিপুলেট করার ঘটনা এখন যথেষ্ট পরিচিত। একটি সাইকিয়াট্রিক ফার্মা কোম্পানি, তাদের ওষুধের বিজ্ঞাপন করেছিলেন, ‘রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে চান? তাহলে এই ওষুধ ব্যবহার করুন।’ এবং সেখানে একজন মহিলার ছবি। মহিলার ছবির ব্যবহার, বিজ্ঞাপনের ভাষার ব্যবহার, এগুলো সবকটাই সাইকোলজিক্যাল ম্যানিপুলেশনের উদাহরণ। সাইকোলজিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে, আমাদের আচরণবিধি, আমাদের ভাবনাচিন্তাকে বেঁধে ফেলা হচ্ছে।
ইন্টার-ডিসিপ্লিনারিটি নিয়ে সমস্যা থাকবেই। আমার ডাক্তার বন্ধুরা আমাকে প্রায়শই বলেন, চেম্বারে একজন রোগী যখন আসছেন, তখন তাঁর সমস্যার মূল কারণ জানলেও, তাঁকে তখনই কোনও উপশম দিতে গেলে, সেই মূল সমস্যার দিকে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। তাঁদের বক্তব্য, এটা নিয়ে চিকিৎসকদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। সেটা সমাজনির্মাণের কাজে যাঁরা আছেন, তাঁদের পক্ষে করা সম্ভব হতে পারে। সেখানে আমার বা আমাদের বক্তব্য, হ্যাঁ, শুরুতেই হয়তো তাঁর মূল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। কিন্তু সেটা খুঁজতে হবে। খুঁজতে গেলে শুনতে হবে। সেটার জন্য অন্য কোথাও রেফার করেন যে প্রত্যাশা নিয়ে, সেটা চিকিৎসককেই দিতে হবে। কেউ কেউ সেটা করেনও।
ডেটা কীভাবে বুঝব, বুঝতে চাইব, সেই প্রশ্নটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। ধরুন, নির্বাচন-পরবর্তী হিংসা। এটা কি পরিমাণগতভাবে মাপা সম্ভব? আমি মনে করি, হিংসা-কে মাপা সম্ভব। এটা নির্ভর করে কোন তথ্যকে আপনি কীভাবে দেখছেন, কীভাবে কোডিফাই করছেন, তার ওপর। ক'টা বাড়ি পুড়ল, বই-পত্র কত নষ্ট হলো, কতজন মারা গেলেন, ক'টা এফআইআর হলো, ক'টা হলো না, কারা প্রতিবাদ করলেন, কারা করলেন না, কারা চুপ করে থাকলেন- এগুলো সবই পরিমাপের তথ্য। সিম্পটম, রোগলক্ষণ-কে কোডিফাই করাই একমাত্র তথ্য নয়।
অশেষ: ইন্টার-ডিসিপ্লিনারিটির প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন জুড়ে দিই। এই সমস্যার জন্য সাইকোলজির পাঠ্যক্রমও কি দায়ী নয়? ভারতে বা ভারতের বাইরেও, সাইকোলজির যে পাঠ্যসূচি হয়, তাতে তো এই ক্ষেত্রের যা প্রসার হয়েছে, তা প্রায় ধরাই পড়ে না!
রত্নাবলী: এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। দেখুন, মেডিক্যাল কারিকুলামেও একটা ফান্ডামেন্টালিজম আছে। মেডিক্যাল কারিকুলামে জেন্ডার পড়ানো হয় না। মেডিক্যাল কারিকুলামে সেক্সুয়ালিটিকে বায়োমেডিক্যাল অ্যাপ্রোচ দিয়ে দেখা হয়। শিশ্ন-র দৈর্ঘ্যই সেখানে আপনার লিঙ্গ নির্ধারণের শেষ কথা। আমরা তার থেকে অনেক এগিয়ে এসেছি। আমরা এখন এইভাবে দেখাটাকেও চ্যালেঞ্জ করি। মেডিক্যাল সায়েন্স হোক বা সাহিত্য বা ইতিহাস– কোনও পাঠ্যক্রমই কি খুব প্রাসঙ্গিক? এক ধরনের ফান্ডামেন্টালিজম কারিকুলামে থাকে। কিন্তু সেটা থাকা সত্ত্বেও, কেউ কেউ তার বাইরে গিয়ে ভাবেন, কথা বলেন। এই পাঠ্যক্রম যে পরিবর্তন করা দরকার, সেই প্রয়োজনের বোধটা অ্যাকাডেমিয়াকে ভালো করে বোঝাতে হবে। আগে তো পাঠ্যক্রমে মানবীচর্চা ছিল না, এখন তো মানবীচর্চা এসেছে। যাদবপুরে এখন একটা কোর্সে জেন্ডার অ্যান্ড ম্যাডনেস পড়ানো হচ্ছে। দশ বছর আগেও কি এই ধরনের কোর্সের কথা কেউ ভাবতে পারতেন! প্রথাগত পাঠ্যক্রমে একরকমের গতানুগতিক গোঁড়ামি আছে। কিন্তু তার বাইরেও অনেক ধরনের বিকল্প পাঠ্যক্রমে পড়ানো হচ্ছে। সেগুলোর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা দরকার। আর এই প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ্যক্রমকে পরিবর্তন করার একটা প্রয়াসও পাশাপাশি থাকা উচিত। পাশাপাশি এটাও মাথায় রাখা উচিত যে, আমাদের দেশে মাত্র একহাজার সাইকোলজিস্ট আছেন। যাঁদের বেশিরভাগই শহরে থাকেন। ফলে গ্রামে কোনও প্রতিবন্ধকতা-যুক্ত মানুষকে ডিসএবিলিটি সার্টিফিকেট দেওয়ার মতোও কেউ নেই। সার্টিফিকেট না থাকার ফলে তাঁর পক্ষে সরকারি প্রকল্পের সুবিধে পাওয়াও সম্ভব হয় না। প্রাতিষ্ঠানিক বন্দোবস্তের মধ্যেও এরকম একটা দুষ্টচক্র চলতেই থাকে!
অশেষ: ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের সিইও, ক্লস শোয়েব-এর বই, দ্য গ্রেট রিসেট-এর বক্তব্য অনুযায়ী, ২০৩০ নাগাদ আমরা এমন একটা অবস্থায় পৌঁছব, যেখানে আমাদের বেশিরভাগেরই নিজস্ব মালিকানায় কিছু থাকবে না, অথচ সকলেই খুশি থাকবেন, সুখী হবেন। আপনি শুরুতে মানসিক স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে ট্যানজেবিলিটির কথা বলছিলেন। ধরা-ছোঁয়া যায় এরকম কিছু। সেখানে ক্লস শোয়েব-এর এই বক্তব্য প্রসঙ্গে আপনার মতামত জেনে আজকের কথোপকথন শেষ করব।
রত্নাবলী: হ্যাপিনেস-এর কোয়েশ্চেনেয়ার দেখলে, একজন বুঝতে পারবেন, এটা মাপা হয় ঠিক কী করে। সুখ-কে এরকম আলাদা করে দেখতে চাওয়ার মধ্যেই তো সমস্যাটা আছে। খুব সহজে বলা যায়, হ্যাপিনেস, সুখ-এর ধারণার একটা নির্মাণমাত্র।
আধুনিক রাষ্ট্রকে হ্যাপিনেস-এর কারখানা হিসেবে বিশ্বাস করানোর একটা চেষ্টা থাকে। আপনার প্রশ্নের উত্তরে, আমি অন্য একটা তথ্য দিই। ২০৩০-এ অবসাদ, ডিপ্রেশন, একটা মহামারীর আকার নেবে। এটাও একটা তথ্যভিত্তিক ভবিষ্যতের ধারণা। ফলে, ২০৩০-এ এমনটাও একটা সম্ভাবনা যে, বেশিরভাগ মানুষ, একটা বড় অংশের মানুষের কাছে, হ্যাপিনেস-কে বোঝার অনুভূতিটুকুও থাকবে না। হ্যাপিনেসের প্রসঙ্গটাই অবান্তর হয়ে দাঁড়াবে।
এবার কোন তথ্যটা আমরা বিশ্বাস করব, বিশ্বাস করে কোন অবস্থান নেব, সেটা পাঠকদের জন্য রাখা থাক।




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp