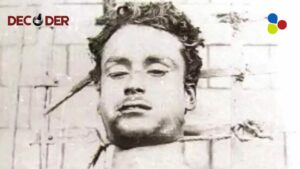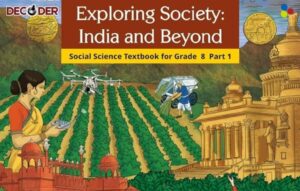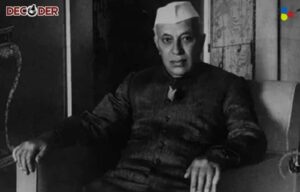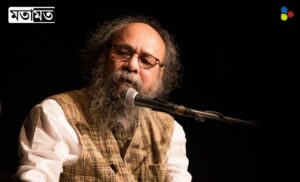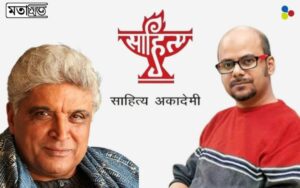জাপানি জুডো ক্ষীণ সুতোয় বেঁধে দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ, সত্যজিতকে
Rabindranath Tagore Judo: ‘যখন ছোটো ছিলাম’ বইয়ের মধ্যে স্পষ্টতই লেখা আছে, সত্যজিৎ জুডো দেখেছিলেন প্রথম, রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে, একেবারে শৈশবে, শান্তিনিকেতনে। সালটা ১৯৩৪।
১
গ্রীষ্মের দাবদাহের মধ্যে যেন দেখতে পাই সেকালের শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের রুদ্রদৃষ্টি। প্রবল তাপপ্রবাহে তিনি, হাতপাখা নাড়তে নাড়তে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সারা দুপুর জুড়ে লিখে চলতেন।
শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথের কর্মক্ষেত্র। তবে সেই কর্মক্ষেত্রেও কত নতুন ভাবনা, নতুন প্রয়োগ এবং নতুন নানা অভিমুখকে তিনি আমদানি করেছেন, আজকে সে কথা ভাবলে বিস্ময়ে চমকে উঠতে হয়। এখন বিদ্যালয় স্তরে ‘স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা’ পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যবইতে নানাভাবে শেখানো হয়, সেখানে বিস্তারিতভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, শেখানো হয় শরীর চর্চা এবং আত্মরক্ষার কৌশল। ভাবতে অবাক লাগে, কত বছর, কত দশক আগে রবীন্দ্রনাথ এইসব খুঁটিনাটি জিনিসের পত্তন করেছিলেন তাঁর বিদ্যালয়ে। অভিনব ছিল তাঁর দৃষ্টি এবং প্রজ্ঞা।
এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা ছিল বিদ্যালয় নয়, এক ধরনের বিকল্প শিক্ষার আশ্রম গড়ে তোলা। যে কারণে লক্ষ্য করবেন, শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন লেখায় রবীন্দ্রনাথ ক্রমাগত বলে চলেন, আত্মঅভিব্যক্তি আর মুক্তির কথা। সাধারণভাবে বিদ্যালয় বলতে আমরা যা বুঝি, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তার একেবারে উল্টোদিকে। তিনি কোনও জ্ঞানচর্চার পিঞ্জরে শিক্ষার্থীদের বদ্ধ করে, তথ্য গেলাতে চাননি। সেজন্যই তাঁর লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীর মনে একধরনের মুক্তির আস্বাদ তাঁর বিদ্যালয়ের মাধ্যমে সৃষ্টি করা। এখানেই স্কুল পালানো ছেলে রবীন্দ্রনাথের ব্যতিক্রমী এক অবস্থান। ১৯২৪ সালে তাঁর মনোভঙ্গির একটি দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে চিন দেশে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় –
‘When I was very young I gave up learning, and ran away from my lessons. That saved me, and I owe all that I possess today to that courageous step taken when I was young. I fled the classes which gave me instructions, but which did not inspire. One thing I have gained, a sensitivity of mind to the touch of life and nature’.
১৯২৪ সালে উচ্চারিত এইসব বাক্য অবশ্য চিরদিনই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত ‘সহজ পাঠ’ প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ডে লক্ষ্য করে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়, শিশুমনে বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ নির্মাণ বারংবার ফিরে আসছে।
শিক্ষা পরিকল্পনাতেও রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব এবং শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের এক সুসম সহাবস্থান চেয়েছিলেন। মিশেল ফুকো যাকে বলছেন ‘Discipline and punish’ সেই অমানবিক ছাত্রনিপীড়ন ব্যবস্থার বদলে রবীন্দ্রনাথ খুঁজে আনলেন এক নতুন অভিপ্রায়, নতুন শিক্ষাচিন্তা। শিশু এখানে কখনই ‘তোতা-কাহিনী’র পাখির মতো শেকলে বদ্ধ নয়। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন প্রকৃতির সৌন্দর্য আর জীবনের ছন্দের এক স্বাভাবিক মিলন। তাঁর স্বপ্ন ছিল এই বিদ্যালয়টিকে কেন্দ্র করে, বিচিত্রবিদ্যার সমাহার। ‘কলেজ পাশ করা’ শিক্ষা যা ডিগ্রি এবং বেতনমুখী, তার বদলে এক সৃষ্টিশীলতায় ভরা শিশু বিকাশ কেন্দ্র ছিল তাঁর অভিপ্রেত। ‘সহজ পাঠ’-এর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সেই সুদূরের প্রতি আমন্ত্রণ, যে অদেখা-অচেনা পৃথিবী ভরে গেছে শিশুর নানা কল্পনায়। নানা কল্পনা পূরণে। ফলে সুদূরের আহ্বান আর কল্পলোকের ইশারায় শৈশবের উড়ানকে নির্দিষ্ট করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর আশ্রম শিক্ষায় এভাবেই শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্য-সংগীত আর আনন্দ অভিব্যক্তির বিস্তৃত আয়োজন। একটি ভাষণে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ –
‘… সুতরাং আমার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমি মুক্তির এই তিন মাত্রাকেই প্রাপনীয় করে তোলার চেষ্টা করেছি – মনের মুক্তি, হৃদয়ের মুক্তি আর চিন্তাশক্তির মুক্তি’।
শুধু ভাবালুতা অবশ্য নয়, আত্মসৃষ্টি এবং আত্মচর্চার নানা নতুন দিকও তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। নিখিল এশিয়ার বিবিধ মাত্রা ছিল তার অন্যতম। গল্পটিকে অবশ্য আমরা রবীন্দ্রনাথ নয়, প্রথমে ঘুরিয়ে দেখতে চাইব সত্যজিৎ রায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে।
আরও পড়ুন- নিজের বইয়ের ‘অন্ত্যেষ্টি সৎকার’ করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ
২
সত্যজিৎ রায় তাঁর আত্মজীবনীর সংক্ষিপ্ত পরিসরে নানা অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতা এবং অতুলনীয় সব ব্যক্তিত্বকে হাজির করেন। তার মধ্যে একটি হল তাঁর জুডো শেখার ইতিবৃত্ত। ‘যখন ছোটো ছিলাম’ বইয়ের মধ্যে স্পষ্টতই লেখা আছে, সত্যজিৎ জুডো দেখেছিলেন প্রথম, রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে, একেবারে শৈশবে, শান্তিনিকেতনে। সালটা ১৯৩৪। ‘পৌষমেলা’ দেখতে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন সত্যজিৎ। সত্যজিৎ লিখছেন,
"রবীন্দ্রনাথ জাপানে গিয়ে জুডো দেখে ঠিক করেন শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের এই জিনিসটা শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। কিছুদিনের মধ্যেই জুডো এক্সপার্ট তাকাগাকি চলে আসেন শান্তিনিকেতনে, আর জুডোর ক্লাস শুরু হয়ে যায়। কী কারণে জানি না, এই ক্লাস বছর চারেকের বেশি চলেনি। শেষে তাকাগাকি শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায়, আর বালিগঞ্জের সুইনহো স্ট্রিটে আমারই এক মেসোমশাই ডাঃ অজিতমোহন বোসের বাড়ির একতলাটা ভাড়া নিয়ে সেখানে জুডো শেখানোর ব্যবস্থা করেন।"
আমাদের আলোচনার মূল চরিত্র শিন্জো তাকাগাকি (১৮৯৩-১৯৭৭) আবির্ভূত হয়ে গেছেন। সত্যজিৎ তাঁর কাছে জুডো শিখতে গিয়েছিলেন সেই ১৯৩৪ সালেই। তাঁকে সেখানে নিয়ে যান তাঁর স্কুলমাস্টার ছোটকাকা সুবিনয় রায়। সত্যজিৎ তাঁর স্মৃতিগুলিকে বিশদে উন্মোচন করেছেন। ‘ডোবা বাঁশঝাড় তাল নারকেল ভরা মাঠ পেরিয়ে তবে সুইনহো স্ট্রিট’ [একালের পাঠক, তুলনা করবেন। বিশেষত যারা সুইনহো স্ট্রিটের আশেপাশে থাকেন বা ওই রাস্তায় প্রায়শই যাতায়াত করেন]। এই জুডো শেখানো হতো পুরু সাদা কাপড়ের তৈরি জ্যাকেট, বেল্ট আর পাজামা পরে। দশ ইঞ্চি পুরো গদির ওপর চলত নানা কসরত।
সত্যজিৎ রায় পরিণত বয়সেও মনে করতে পারেন দুটো প্যাঁচের নাম – শেওই-নাগে আর নিপ্পন নিও। আরও উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থীদের ‘ওভালটিন’ খাইয়ে বাড়ি পাঠাতেন তাকাগাকি। জানি না, অস্ত্রহীন এই আত্মরক্ষার কৌশল সত্যজিৎকে পরবর্তীকালেও প্রভাবিত করেছিল কিনা। পাঠক-পাঠিকারা অনেকেই মনে করতে পারবেন, ‘বোম্বাইয়ের বোম্বেটে’ উপন্যাসে (১৯৭৬) ফেলুদার কুং-ফু সম্পর্কে আগ্রহ এবং বাড়িতে সেইসব চর্চার প্রসঙ্গ আছে। অনুশীলনে তিনি ভিক্টর পেরুমলকে বেশ ইম্প্রেস করতেও পেরেছিলেন। ফেলু মিত্তিরের এইসব কীর্তিকলাপের অন্তরালে কতদূর বসে আছেন তাকাগাকি – সেকথা কি কেউ বলতে পারে?
৩
শিন্জো তাকাগাকি-র কলকাতা তথা এ-বঙ্গে আসার কাহিনিটিও দীর্ঘ। লেখা বাহুল্য, তার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। এই ভারতবর্ষে জুজুৎসু বা জুডোচর্চার পথিকৃৎও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ১৯২৯ সালে কানাডা থেকে দেশে ফেরার সময় রবীন্দ্রনাথ জাপান হয়ে ফিরছিলেন। জাপানে জুডো বা জুজুৎসুর চর্চা দেখে তাঁর বেশ ভালো লাগে এবং শান্তিনিকেতনে তাঁর বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই লড়াই এবং আত্মরক্ষার পদ্ধতি প্রচলনে তিনি উৎসাহী হন। আমরা বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তায় শরীরচর্চার এই দিকটিও ছিল। ভারতবর্ষে সে সময় ব্রিটিশ সরকার অস্ত্র-আইন প্রচলন করেছিল। ফলে, অস্ত্রশস্ত্রহীন এই রণকৌশল শান্তিনিকেতনে চর্চার একটা ‘রাজনৈতিক’ দিকও হয়তো ছিল। প্রথমত, আত্মপরিচয় উদ্ঘাটনে এই কৌশল বেশ উল্লেখযোগ্য, কেননা এর প্রধান উৎসভূমি হলো প্রাচ্যের জাপান। অন্যদিকে, শুধু আত্মরক্ষাই নয়, প্রয়োজনে আক্রমণের এই কৌশল হয়তো ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।
রবীন্দ্রনাথ জাপানের বিখ্যাত কাগজ-ব্যবসায়ী কুনিহিকো ওকুরাকে একজন জুজুৎসু বা জুডো শিক্ষককে শান্তিনিকেতনে পাঠাতে অনুরোধ করেন এবং সেই সূত্রেই দ্বিতীয় জুজুৎসু শিক্ষক হিসেবে শান্তিনিকেতনে আসেন তাকাগাকি। বিশ্বভারতীর বার্ষিক রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, ‘তাকাগাকি ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসে’ শান্তিনিকেতনে প্রশিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছেন। তখন বিশ্বভারতী চরম অর্থসংকটে ভুগছে। তৎসত্ত্বেও এই বিশেষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে সর্বতোভাবে সমর্থন এবং সহযোগ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাকাগাকির স্ত্রী মাকি হোসি শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯৩০-এর নভেম্বর মাসে। অর্থাৎ ঠিক একবছর পরে। তিনি সম্পর্কে ছিলেন বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর শ্যালিকা। অন্যদিকে, শ্রীমতী মাকি হোসিও বিশ্বভারতীতে প্রধানত জাপানি ফুল সাজানো, বৃক্ষপালন পদ্ধতি ‘ইকেবানা’ শেখাতেন এবং জুডোও শেখাতেন। তাকাগাকি এবং মাকি হোসির পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলে রবীন্দ্রনাথ (৬ অক্টোবর, ১৯৩১) তাঁর নামকরণ করেন ‘উজ্জ্বল সূর্য’ – জাপানি ভাষায় সেই সূত্রেই শিশুর নাম ‘আকিরা’। এর আগে ১৯৩০ সালের নভেম্বর মাসে ‘বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি’-তে একটি শিক্ষা সম্মেলনে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা যোগ দিয়েছিল। সেখানে তারা জুজুৎসু বা জুডোর একটি প্রদর্শন অনুষ্ঠান করেছিল। সেই অনুষ্ঠানে তাকাগাকি এবং মাকি হোসিও উভয়েই পুরো অনুষ্ঠানটি তত্ত্বাবধান করেন। কোনও কোনও ছাত্রীর স্মৃতিচারণে এই সফরের নানা টুকরো স্মৃতি পাওয়া যায়। সে সময়ের ছাত্রী নিবেদিতা বসু লিখেছেন – ‘তাকাগাকি ছিলেন একটু গম্ভীর প্রকৃতির। তাঁর স্ত্রী ছিলেন হাসিখুশি। দু'জনেই সকলের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতেন’। মাকি হোসি তাঁর স্মৃতিকথা ‘ভারতভ্রমণ কাহিনি’-তে এই বেনারস শহরের প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের উল্লেখ করেছেন।
রবীন্দ্রনাথের এত উৎসাহ এবং উদ্যোগের পরও অবশ্য জুজুৎসু বা জুডো শান্তিনিকেতনে খুব জনপ্রিয় হয়নি। প্রধানত ছাত্রীরাই এই বিদ্যাশিক্ষায় উৎসাহ দেখিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ শুধু শান্তিনিকেতনেই অবশ্য এই চর্চাকে আবদ্ধ রাখতে চাননি। নানা ক্ষেত্রে এবং পরিসরে তাকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। হয়তো, এই কারণেই তাকাগাকি এবং রবীন্দ্রনাথ যৌথভাবে একটি জুজুৎসু প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন নিউ এম্পায়ার মঞ্চে ১৯৩১ সালের ১৬ মার্চ। নিউ এম্পায়ার তখন কলকাতার এক অভিজাত মঞ্চ। সেই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ উদ্যোগ নেন জুজুৎসু কসরতের পিছনে একটি বাংলা গানের উপস্থাপনা যাতে হয়! এমন একটি পরিকল্পনা সত্যিই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে একমাত্র সম্ভব। জাপানের এক বিশেষ রণকৌশল প্রদর্শন অনুষ্ঠানের পিছনে বাংলা রবীন্দ্রসংগীত! নথিপত্র জানাচ্ছে ‘সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান’ গানটি প্রথম নিউ এম্পায়ারে গাওয়া হয়েছিল। জুজুৎসু শিখতে ছাত্র এবং বিশেষত ছাত্রীরা সংকোচ করছে, এই প্রসঙ্গ হয়তো গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের মনে কাজ করছিল। সে সময়ের অভিভাবকরা, ছাত্রীদের ক্ষেত্রে সত্যিই জুডোর বিষয়ে বিরূপ ছিলেন। মাত্র সাতজন ছাত্রীকে বাড়ি থেকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। পরে এটি ‘চিত্রাঙ্গদা’র গান হিসেবে গৃহীত হয়। এক-একটি গান এভাবেই, এক নয়, বিচিত্র অনুষঙ্গকে জড়িয়ে প্রবাহিত হতে পারে।
আরও পড়ুন- দেশের নামে উগ্রতার দ্বন্দ্ব দিয়ে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজেও
৪
এত চেষ্টা করেও অবশ্য জুজুৎসু মোটেই জনপ্রিয়তা পেল না। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘রবীন্দ্রজীবনী-৩’ থেকে জানা যাচ্ছে আর্থিক অনটনের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ জুজুৎসু প্রশিক্ষকের জন্য দু-বছরের মেয়াদে প্রায় বারো-চোদ্দ হাজার টাকা ব্যয় করেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্র মহলে তৎসত্ত্বেও এই বিদ্যার কোনও কদর হল না। মেয়াদ শেষ হবার মুখে, রবীন্দ্রনাথ কলকাতার তৎকালীন মেয়র সুভাষচন্দ্র বসুকে লেখেন –
‘…দুই বৎসরের মেয়াদ আগামী অক্টোবরে পূর্ণ হবে। কোচিন প্রভৃতি দূরদেশ থেকে শিক্ষার্থী এসেছে কিন্তু বাংলা থেকে কাউকে পাইনি। যে ব্যয়ের বোঝা আমার পক্ষে অত্যন্ত গুরুভার তাও সম্পূর্ণ হয়ে এল অথচ আমার উদ্দেশ্য অসমাপ্ত হয়ে উঠলো। জাপান থেকে এরকম গুণীকে পাওয়া সহজ হবে না। … এখন এই লোকটিকে তোমাদের পৌর শিক্ষা বিভাগে নিযুক্ত করবার কোনো সম্ভাবনা হতে পারে কিনা আমাকে জানিয়ো। যদি সম্ভব না হয় তাহলে এঁকে জাপানে ফিরে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবো।…’
পরিতাপের বিষয় দু'টি। প্রথমত সুভাষচন্দ্র কোনও ব্যবস্থাই করতে পারলেন না। দ্বিতীয়ত শান্তিনিকেতনে এমন কেউ ছিলেন না যিনি জুজুৎসু বিদ্যাটি তাকাগাকির কাছ থেকে মোটামুটি শিখে নিয়ে শান্তিনিকেতনে প্রশিক্ষণ চালিয়ে যেতে পারেন। ফলে, শান্তিনিকেতনে জুডো চর্চার সমাপ্তি এভাবেই ঘনিয়ে উঠল। শান্তিদেব ঘোষ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় এই জাপানি শিক্ষককে উল্লেখ করেছেন এইভাবে – ‘গুরুদেব জাপানি যুযুৎসু-পালোয়ান টাকাগাকীকে শান্তিনিকেতনে আনিয়ে যুযুৎসু শিক্ষার প্রবর্তন করেন।…’ [রবীন্দ্রসংগীত/ পৃ: ২০৩]।
কাহিনি এখানে শেষ নয়। সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে, একই রকম একটি প্রস্তাব লিখে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী মেয়র বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে পাঠান। এইরকম এক কালপর্বে, অনুমান করি, তাকাগাকি কলকাতায় জুডো শেখাবার আখড়া তৈরি করেন।
আরও আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে, সত্যজিৎ রায় তখন বালক হিসেবে কল্পনা করতেই পারেননি, পরবর্তীকালে তিনি বিশ্বভারতীতে গিয়ে শিল্পশিক্ষা করবেন এবং চলচ্চিত্রকার হিসেবে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী হিসেবে বানাবেন রবীন্দ্রনাথের ওপর একটি স্মরণীয় তথ্যচিত্র! মানবজীবন কত বিচিত্রপথে মোড় নেয়। পাশাপাশি, জুডো বা জুজুৎসুর সূত্রে বাঙালির দুই যুগপুরুষ ব্যক্তিত্ব এক ক্ষীণ সুতোয় বাঁধা রইলেন। সেই বা কম কী! শেষে উল্লেখ করে যাই, তাকাগাকি পরবর্তীকালে আফাগানিস্তান সরকারের মাধ্যমে কাবুলে জুজুৎসু বা জুডোর ‘ইনস্ট্রাক্টর’ পদে বহাল হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তিনি নেপালেও এই বিদ্যাচর্চা শুরু করান।
রবীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টির কোনও মূল্য অবশ্য তৎকালীন কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেয়নি। এতবছর পর ‘স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা’-র পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যবইগুলোই দেখে, আবারও রবীন্দ্রনাথের প্রতি কুর্নিশের সংখ্যা বাড়ল। মনটা মন্থর ও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল, তৎকালীন সমাজ, শিক্ষানিয়ন্ত্রক এবং অভিভাবকদের অবজ্ঞা দেখেও। রবীন্দ্রনাথের প্রতি এই অবজ্ঞা আসলে এক সংকীর্ণতা। অবজ্ঞা নাকি অজ্ঞতা? উত্তর মেলে না!



 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp