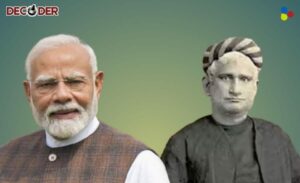গুগি: আমাদের লোক, আমাদের লেখক
Ngũgĩ wa Thiong'o: পুরো উপন্যাসটি গুগি লিখেছিলেন টয়লেট পেপার ব্যববহার করে কারণ তাঁকে রাষ্ট্র জেলের ভিতর লেখার জন্য খুবই অল্প পরিমাণ কাগজ বরাদ্দ করতো। ১৯৭৮ সালে তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দিলেও একের পর এক রাষ্ট্রবিরোধী মামলায়...
গুগি সম্ভবত সেই বিরল অস্বস্তিকর মানুষদের একজন যাঁকে ইওরোপিয় মননকেন্দ্রিক পশ্চিমি সাহিত্য জগত না পারে গিলতে, না পারে উগরাতে। গুগির সাহিত্য ও সাহিত্যের রাজনীতি সংক্রান্ত চিন্তাভাবনাকে উদযাপন করতে হলে, তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে এতদিনে ইওরোপ নিজের উদারপন্থাকে জাহির অবশ্যই করে ফেলত। অসামান্য সাহিত্য রচনার পাশাপাশি নোবেল পুরস্কার পাওয়ার জন্য আরও যে যে টেমপ্লেট লাগে, সবই গুগির ছিল। গুগি নিজের রাষ্ট্র কেনিয়ায় ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রের শাসকবিরোধী নাটক লেখা ও মঞ্চস্থ করার জন্য গ্রেফতার হয়েছেন। কেনিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ড্যানিয়েল আরাপ মৈ ক্ষমতার অপব্যবহার করে গ্রেফতারের পর বিনা বিচারে গুগিকে এক বছর আটকে রাখেন। জেলে থাকাকালীন গুগি লিখে ফেলেছেন লেখক হিসেবে তাঁর জেল দেখার অভিজ্ঞতা। জেলে থাকাকালীনই তিনি লিখতে শুরু করেন তাঁর জনজাতির ভাষা গিকুয়ুতে। শেষ করেন গিকুয়ুতে তাঁর প্রথম উপন্যাস, ইংরেজি অনুবাদে যার নাম ‘ডেভিল অন দ্য ক্রস’। ঔপনিবেশিক শোষণে বিধ্বস্ত একটি দেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন যে ঔপনিবেশিক কাঠামো থেকে বেরোতে পারে না এবং সেই কাঠামোকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক মুখোশে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র গ্রাস করতে শুরু করে দেশটির প্রতিটি উপাদানকে। মাটি, কৃষি, খনি, জল, বন থেকে শুরু করে প্রতিটি মানুষের স্বাধীন অস্তিত্ব বিপন্ন করে সেই ঔপনিবেশিক কাঠামোর রাষ্ট্র।
উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ওয়ারিঙ্গা গ্রামীণ কেনিয়ার এক গঞ্জ ছেড়ে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে এসে রোজকার জীবনে নারী হিসেবে ব্যবহৃত হতে হতে আবিষ্কার করে যে, তাঁর ব্যক্তিগত যন্ত্রণা জাতই হয়েছে রাজনৈতিক শোষণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থেকেই। পুরো উপন্যাসটি গুগি লিখেছিলেন টয়লেট পেপার ব্যববহার করে কারণ তাঁকে রাষ্ট্র জেলের ভিতর লেখার জন্য খুবই অল্প পরিমাণ কাগজ বরাদ্দ করত। ১৯৭৮ সালে তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দিলেও একের পর এক রাষ্ট্রবিরোধী মামলায় তাঁর জীবন অতিষ্ঠ করে তোলা হয়। চাপ সহ্য করতে না পেরে ১৯৮২ সালে গুগি বাধ্য হন তাঁর দেশ কেনিয়া ছেড়ে যেতে। প্রথম কিছু বছর ব্রিটেনে থাকার পর থিতু হন আমেরিকায়। অধ্যাপনা করেছেন ইয়েল এবং নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে। দেশে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করে আমেরিকায় বিয়ে করেন মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ নিজেরিকে। মৈ-এর শাসনাবসানের পর কেনিয়াতে ২০০৪ সালে নিজের বইয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ফেরেন। অজানা দুষ্কৃতীদের হাতে হোটেলে আক্রান্ত হন, কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচেন। গুগির স্ত্রী নিজেরি যৌন হেনস্থার শিকার হন। গুগি ‘গার্ডিয়ান’-কে ২০০৬ সালে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানান যে, সেই আক্রমণ তাঁর কাছ থেকে কেনিয়াকে চিরতরে কেড়ে নেওয়ার জন্যই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে করা হয়েছিল। তৃতীয় বিশ্বের একটি পূর্বতন উপনিবেশ এবং সার্বিকভাবে ব্যর্থ একটি রাষ্ট্রের অসামান্য লেখক গুগি তাঁর জীবনে লেখার জন্য রাষ্ট্রের দ্বারা গ্রেফতার, বন্দি থাকাকালীন সাহিত্য সৃষ্টি, দেশ থেকে নির্বাসন, দেশে সহিংস হামলা সবকিছুরই সম্মুখীন হয়েছেন যা সধারণত এই প্রেক্ষিতের একজন লেখককে ইওরোপ-কেন্দ্রিক সাহিত্যমহলে খুব অনায়াসে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। এইসবের পরেও গুগি পশ্চিমের কাছে অপ্রতিরোধ্য এক অস্বস্তি হয়ে রইলেন জীবনের শেষ দিন অবধি। যে অস্বস্তির চোটে তাঁর মতো লেখককেও নোবেলের জন্য বিবেচনা করা হয় না। এই অস্বস্তিকর গুগিই আমাদের লোক।
১৯৩৮ সালে ব্রিটিশ শোষিত কেনিয়ার মোটামুটি অবস্থাপন্ন চাষা থিয়ং-ও ডুকুর তৃতীয় স্ত্রী ওয়ানজিকু ওয়া গুগি জন্ম দিলেন এক পুত্র সন্তানের। ছেলের ব্যক্তি নামটি বাপের মতো, ঠাকুর্দার মতো রাখতে চাইলেন না ডুকু। নয়া-কেনিয়ায় এই জাতীয় নামের চেয়ে ইওরোপিয় খ্রিস্টান নামের সম্ভ্রম দিন দিন বাড়ছে। ব্যাপ্টাইজেশনের সময় ছেলের নাম রাখা হলো জেমস। কেনিয়ায় ততদিনে ইংরেজি ভাষা ও ইওরোপিয় শিক্ষাব্যবস্থা দেশকে মিটিয়ে একটি ঔপনিবেশিক কাঠামোর রাষ্ট্রব্যবস্থা শুধু গড়ে তুলেছে। খ্রিস্টধর্ম ও ইওরোপিয় জ্ঞান চর্চা দুই-ই সেই রাষ্ট্রের ব্যক্তির বৈষয়িক ও স্বীকৃতির পক্ষে অনুচ্চারিতভাবে আবশ্যক করে তোলা হচ্ছে। কেনিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামীরা নিজেদের লড়াইয়ের অংশ হিসেবে গিকুয়ু ভাষার স্কুল চালাচ্ছেন, অন্তত প্রাথমিক শিক্ষাটুকু যাতে জনজাতির প্রথম ভাষায় পায় ছাত্রছাত্রীরা। এই স্কুলগুলোতেও ইংরেজ সরকার নজর রাখছে এবং ১৯৫২ সালে পুরোপুরি নিজেদের শিক্ষাবোর্ডের অধীনে নিয়ে আসছে জরুরি অবস্থার সুযোগ নিয়ে। আধুনিক শিক্ষার জন্য গিকুয়ু ভাষা অচল, এই যুক্তিতে স্কুলগুলোর প্রথম ভাষা করা হলো ইংরেজিকে। জেমস এরকমই একটি স্কুলে পড়ত। জেমসের স্মৃতিতে তাঁর ছোটবেলার স্কুলের ভাষা নিয়ে চাপ মাত্রাভেদে এখনকার শহুরে বাঙালি মধ্যবিত্তের ভীষণ চেনা ঠেকবে। জেমসদের স্কুলে থাকাকালীন জেমসরা ক্লাসের বাইরেও নিজেদের মধ্যে গিকুয়ু ভাষায় কথা বলার অনুমতি পেত না। একটা গোটা দিনে কোনও কোনও ছাত্র ক্লাসে শিক্ষক না থাকাকালীন ফিসিফিস করে নিজের দেশের ভাষায় সহপাঠীকে কিছু বলল কিনা, শৌচালয়ে গিয়ে নিজের ভাষায় কিছু বলে ফেলল কিনা, এইগুলো ধরার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ এক অদ্ভুত ব্যবস্থা রেখেছিল। ব্যবস্থাটিতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে ইওরোপিয় কাঠামোর মূল অভিমুখ। শিক্ষকরা একজন ছাত্রকে বেছে নিয়ে তাঁর হাতে একটি বোতাম ধরিয়ে দিতেন। তাঁকে বলা হতো সে যেন কাউকে স্কুলে গিকুয়ু কোনও শব্দ উচ্চারণ করতে শুনলেই বোতামটা তাঁর হাতে দিয়ে দেয় এবং তাঁকে বলে সে-ও যেন একই পদ্ধতি অনুসরণ করে আরেকজনের হাতে বোতামটা তুলে দেয়। দিনের শেষে যার হাতে বোতাম পাওয়া যেত তাঁকে ধরা হতো বোতামটা সে কার হাত থেকে পেয়েছে। এভাবে সারাদিনে একটা গিকুয়ু শব্দ উচ্চারণ করা ছাত্রদের একত্রিত করা হতো। তারপর তাদের সঙ্গে রুটিন মেনে দিনের পর দিন ইওরোপিয় ডিসিপ্লিন মেনে প্যান্ট খুলিয়ে সবাইকে দেখিয়ে তিন থেকে পাঁচটি বেতের ঘা দেওয়া হতো, কিংবা কোনও কোনওদিন গলায় একটা ধাতব পাত ঝুলিয়ে সারা স্কুলে ঘোরানো হতো। সেই পাতে লেখা থাকতো, “আমি একটা গাধা” বা “আমি একটা বেকুব”— এই জাতীয় কোনও কথা। আর এর বিপরীতেই ছিল ইংরেজি ভাষায় কথা বলা এবং লেখার জন্য চূড়ান্তভাবে পুরস্কৃত করা। জেমস একটা অদ্ভুত পরিবেশে বড় হচ্ছিল। বাড়িতে মা, বড়-মা, মেজো-মায়ের কাছ থেকে যা যা গল্প শোনে সেগুলোর সঙ্গে কোনও মিলই পায় না স্কুলে শেখা গল্পগুলোর। বাড়ির গল্পের সিংহ, চিতা, খরগোশরা স্কুলের গল্পের অলিভার টুইস্ট বা টম ব্রাউনের দুনিয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না। দোলাচল নিয়ে বড় হতে থাকে জেমস। ইংরেজি ভাষায় দখল বাড়তে থাকে, সড়গড় হতে থাকে ইওরোপিয় সাহিত্যে।
জেমসের ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা ও ইওরোপিয় সাহিত্যের পুঁজি জেমসকে অভিজাততম অ্যালিয়ান্স হাই স্কুলে পৌঁছে দেয়। তারপর ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পড়াশোনা এবং ফিরে এসে নাইরোবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে পেশা জীবন শুরু। এর মধ্যে ১৯৬৩ সালে কেনিয়া ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয় এবং জেমস খেয়াল করেন তারপরেও শিক্ষা ও সাহিত্য ইওরোপিয় মডেল অনুসরণ করেই চলতে থাকে। এসবের ফাঁকে জেমস পড়ে ফেলছেন ফ্র্যানজ ফ্যাননের “ব্ল্যাক স্কিন, হোয়াইট মাস্কস”। স্পষ্ট হচ্ছে তাঁর কাছে চর্চার পরেও ইংরেজি ভাষা ও ইওরোপিয় সাহিত্য নিয়ে তাঁর এত অস্বস্তি কেন হয়। আর এই সমস্ত কিছু নিয়ে ১৯৬৯ সালে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক জেমস, তাঁর আরও দুই সহকর্মীর সঙ্গে একত্রিত হয়ে একটি আকাডেমিক পেপার পড়লেন যা আজ ঐতিহাসিক এক দলিল হিসেবে চিহ্নিত হয় সমস্ত পূর্বতন-উপনিবেশগুলির সাহিত্যচর্চার অভিমুখের ক্ষেত্রে। পেপারটির নাম ‘অন দ্য অ্যাবলিশন অফ দ্য ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট’। তাঁরা প্রস্তাব করলেন পূর্ব আফ্রিকার সাহিত্যকে আধুনিকভাবে জন্মাতে গেলে দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যেভাবে ইওরোপিয় মডেলে সাহিত্যের ধারা গড়ে উঠেছে, তাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে হবে। প্রাক-ঔপনিবেশিক মৌখিক সাহিত্যের যে ধারা এবং অনান্য আফ্রিকান ভাষার সাহিত্যের যে ধারা তার সঙ্গে সাহিত্যকে সংশ্লিষ্ট হতে হবে। এই সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে যেতে যেতে জেমস আবিষ্কার করছিলেন যে তিনি আসলে জেমস নন। তিনি নিজেকে যা ভাবেন তিনি সেই অস্তিত্বের নামেই নিজেকে পরিচিত করাতে চাইলেন। খুব অল্পদিনের জন্য নিজের নাম হিসাবে ব্যবহার করতেন নিজের মায়ের নামটি উলটে দিয়ে গুগি ওয়া ওয়ানজিকু। তারপরে থিতু হলেন সেই নামে যে নামে তাঁকে দুনিয়া চেনে। গুগি ওয়া থিয়ং-ও। ‘ওয়া’ শব্দটি গিকুয়ু ভাষায় খুব গুরুত্বপূর্ণ। ‘ওয়া’-র অর্থ বাংলায় করলে দাঁড়ায় নিজেকে নিজের ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করা। আর এই সংযোগের জন্য যা সবচেয়ে জরুরি বলে মনে করেছিলেন গুগি ওয়া থিয়ং-ও তা হলো মননকে ‘ডিকলোনাইজিং’ করতে থাকা সব সময়, বিউপনিবেশিয়ানমান একটি মননই পারে আমাদের সাহিত্যকে নতুনভাবে জন্ম দিতে। ১৯৮৬ সালে লেখা ক্লাসিক হয়ে যাওয়া তাঁর তত্ত্বের বই 'ডিকলোনাইজিং দ্য মাইন্ড: দ্য পলিটিক্স অফ ল্যাংগুয়েজ ইন আফ্রিকান লিটারেচার’-এ তাই তিনি স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন বিখ্যাত আফ্রিকান-ইংরেজি ভাষার লেখকদের ঐতিহ্য অনুসরণ করে তিনি আরও একজন আফ্রিকান-ইংরেজি লেখক হতে চান না আর। তিনি গিকুয়ু ভাষাতেই লিখবেন। তাঁর পরিচয় হোক তিনি গুগি ওয়া থিয়ং-ও, গিকিয়ু ভাষায় লেখেন, তিনি আফ্রিকাকে ধারণ করেন। তিনি তাঁর দেশকে লেখেন, ইওরোপের গণ্ডি টেনে দেওয়া রাষ্ট্র নামক ছদ্ম-দেশের পরিসরকে অগ্রাহ্য করে। এই আত্মানুসন্ধানী গুগিই আমাদের লেখক।




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp