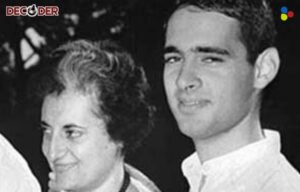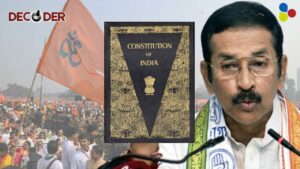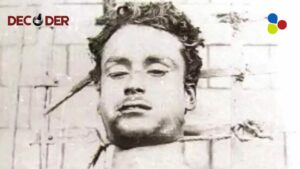ভয় ও বিভেদ ছড়ানোর নতুন মাধ্যম এখন ইউটিউবাররাই?
YouTube: ইউটিউবের অ্যালগরিদম প্রায়শই এই ধরনের কন্টেন্টকে আরও বেশি দর্শকের কাছে পৌঁছে দেয়, যা তথ্যের ভুল ব্যবহারকে ত্বরান্বিত করে।
ইউটিউব এখন ডিজিটাল বিপ্লবের এক নতুন দিগন্ত। এটি মানুষের জীবনে নতুন কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ এনে দিয়েছে। কিন্তু এই প্ল্যাটফর্মে অবাধ তথ্য প্রবাহের অপব্যবহার জন্ম দিচ্ছে নানা নতুন চ্যালেঞ্জের, যা জাতীয় নিরাপত্তাকেও সংকটে ফেলছে। সাম্প্রতিককালে ভারতীয় ট্র্যাভেল ভ্লগার জ্যোতি মালহোত্রার পাকিস্তানি গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদের ঘটনা আবারও সামনে এনেছে ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে তথ্যের অপব্যবহারের গুরুতর ঝুঁকি। অভিযোগ উঠেছে, 'ট্রাভেল উইথ জো' চ্যানেলের এই ইউটিউবারকে ব্যবহার করে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই ভারতের সামরিক বাহিনীর গতিবিধি, সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর ক্যাম্পের অবস্থান এবং অন্যান্য সংবেদনশীল তথ্য সংগ্রহ করছিল। ফরেনসিক বিশ্লেষণে জ্যোতির মোবাইল থেকে বিএসএফ ক্যাম্প, রাডার ইনস্টলেশন সম্পর্কিত ভিডিও, সংবেদনশীল সীমান্ত অঞ্চলের দৃশ্য এবং পাকিস্তানি হাইকমিশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মুছে ফেলা কথোপকথন উদ্ধার হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। জ্যোতি ছাড়াও পঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশ থেকে আরও বেশ কয়েকজন ইউটিউবারকে একই অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ঘটনা প্রমাণ করে, জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে ইউটিউবারদের ভূমিকা কতটা মারাত্মক হতে পারে।
ইউটিউব: এক ডিজিটাল বিপ্লব
২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও, ইউটিউবের জনপ্রিয়তা বাড়তে শুরু করে ২০১০ সালের মাঝামাঝি থেকে— অর্থাৎ যখন থেকে স্মার্টফোন ও দ্রুতগতির ইন্টারনেটের প্রসার ঘটে। এটি এখন শুধু একটি ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম নয়, বরং লক্ষ লক্ষ মানুষের আয়ের উৎস এবং তথ্যের এক নতুন দিগন্ত। ইউটিউব পার্টনার প্রোগ্রাম (ওয়াইপিপি) চালু হওয়ার পর নির্মাতারা সরাসরি ভিডিও থেকে আয় করার সুযোগ পান, যা এটিকে পেশা হিসেবে জনপ্রিয় করে তোলে। ২০১১ সালে লাইভ স্ট্রিমিং ও ইউটিউব অ্যানালিটিক্স এবং ২০১৭ সালে 'সুপার চ্যাট' ও 'চ্যানেল মেম্বারশিপ'-এর মতো নতুন আয়ের সুযোগ যুক্ত হলে এটি আরও গতি পায়। ২০২২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সারা বিশ্বে ৫০ কোটির বেশি ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে এবং প্রায় ৬.৬ কোটি ইউটিউব ক্রিয়েটর আছেন। প্রতি মিনিটে ৫০০ ঘণ্টার বেশি ভিডিও আপলোড হয় এবং বর্তমানে এটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সার্চ ইঞ্জিন, গুগলের পরেই এর অবস্থান।
আরও পড়ুন-ভারতের ইউটিউব রাজধানী এই গ্রাম! অবাক করবে ইউটিউবারদের উত্থান কাহিনি
ইউটিউব : কর্মসংস্থান ও অর্থনীতিতে
ইউটিউব বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রচলিত চাকরির বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা থাকা সত্ত্বেও ইউটিউবে সৃজনশীলতা ও পরিশ্রমকে কাজে লাগিয়ে মানুষ আয়ের সুযোগ তৈরি করতে পারছে। এটি একটি বিস্তৃত কর্মসংস্থানের বাস্তুতন্ত্র তৈরি করেছে, যেখানে সরাসরি ইউটিউবার বা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ছাড়াও ভিডিও এডিটর, গ্রাফিক ডিজাইনার, স্ক্রিপ্ট রাইটার, কন্টেন্ট ম্যানেজার, সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার, অডিও ইঞ্জিনিয়ার, লাইটিং টেকনিশিয়ান সহ বহুমুখী সাপোর্টিং পেশার সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ পূর্ণকালীন চাকরির সমতুল্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে।
শুধু কর্মসংস্থান নয়, যেকোনও দেশের জিডিপিতেও ইউটিউবের অবদান অনেকখানি। গুগল অ্যাডসেন্সের মাধ্যমে ইউটিউবারদের আয় কেবল তাদের ব্যক্তিগত উপার্জন নয়, বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য একটি বিশাল ও কার্যকর বাজার তৈরি করেছে। ব্র্যান্ডগুলি এখন জনপ্রিয় ইউটিউবারদের মাধ্যমে তাদের পণ্যের প্রচার করছে, যা ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং নামে পরিচিত। এছাড়াও, ভিডিও উৎপাদন, সম্পাদনা, অ্যানিমেশন, অডিও রেকর্ডিং, লাইটিং, সাউন্ড ডিজাইন এবং স্টুডিও সেটআপের মতো সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলির বিকাশে ইউটিউবের ভূমিকা অপরিসীম। অক্সফোর্ড ইকোনমিক্সের গবেষণা অনুযায়ী, ২০২২ সালে ইউটিউবের ক্রিয়েটিভ ইকোসিস্টেম শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপিতে ৪৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অবদান রেখেছে এবং ৪.৩ লাখের বেশি পূর্ণকালীন কর্মসংস্থানের সমান কাজ সৃষ্টি করেছে। ভারতে, ২০২২ সালে এই ইকোসিস্টেম জিডিপিতে প্রায় ১৬,০০০ কোটি টাকার বেশি অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলেছিল এবং ৭.৫ লক্ষের বেশি পূর্ণকালীন কর্মসংস্থানের সমতুল্য কাজ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। যেসব দেশে ডিজিটালাইজেশন দ্রুত বাড়ছে এবং তরুণ জনসংখ্যা বিশাল, সেখানে ইউটিউব একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ইঞ্জিন হিসেবে কাজ করছে।
ইউটিউব: ডানপন্থী দলগুলির রাজনৈতিক স্বার্থে
ইউটিউব এখন রাজনৈতিক ক্ষমতা বদলের এক শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ডানপন্থী দলগুলি নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর সাহায্য নিয়ে জনমতকে প্রভাবিত করতে ইউটিউব প্ল্যাটফর্মের অপব্যবহার করছে।
• জার্মানির কট্টর ডানপন্থী দল অল্টারনেটিভ ফর ডয়চল্যান্ড (এএফডি) এআই-জেনারেটেড ভিডিও ও ছবি ইউটিউবে আপলোড করে অভিবাসন-বিরোধী প্রচার চালাচ্ছে। তারা এমন ছবি তৈরি করেছে যেখানে 'আদর্শ জার্মান' সমাজের এক বিশেষ চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে। এর মাধ্যমে অভিবাসীদের খারাপভাবে দেখানো হয়, যা সমাজে জাতিগত বিভেদ বাড়াচ্ছে।
• ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকরা এআই-জেনারেটেড ছবি দিয়ে রাজনৈতিক মিম এবং ভাইরাল ভিডিও তৈরি করছে। তারা কমলা হ্যারিসের সোভিয়েত পোশাক পরা ছবি বা কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানরা ট্রাম্পকে সমর্থন করছে এমন মিথ্যা ছবি তৈরি করে ইউটিউবে ছড়িয়ে দিয়েছে।
• ফ্রান্সে, মারিন লে পেনের ন্যাশনাল র্যালি-র মতো ডানপন্থী দলগুলি এআই দিয়ে এমন ছবি তৈরি করছে যেখানে দেখানো হচ্ছে অভিবাসীরা ফ্রান্সের উপকূলে এসে জড়ো হয়েছে। এই ছবিগুলো ইউটিউবের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে অভিবাসন-বিরোধী মনোভাব উস্কে দেওয়া হচ্ছে, যা ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচনের প্রচারেও ব্যবহৃত হচ্ছে।
• পোল্যান্ডে, ডানপন্থী দলগুলি (যেমন, ল অ্যান্ড জাস্টিস বা পিআইএস) এআই ব্যবহার করে, বিরোধী রাজনীতিবিদদের বিকৃত ছবি/ভিডিও তৈরি করে দেখাচ্ছে বিরোধীরা আপত্তিকর কাজের সঙ্গে জড়িত। কণ্ঠস্বর নকল করে বিতর্কিত মন্তব্য ছড়াচ্ছে। এর ফলে অনলাইন হয়রানি ও ভুল তথ্যের বিস্তার বাড়চ্ছে।
• অন্যান্য দেশ যেমন ইন্দোনেশিয়াতে এআই ব্যবহার করে মৃত নেতাদের পুনরুজ্জীবিত করে ভিডিও তৈরি করা হচ্ছে। স্লোভাকিয়াতে উদারপন্থী দলের নেতার একটি মিথ্যা অডিও ক্লিপ তৈরি করা হয়েছিল।
ভারতের ডানপন্থী দলগুলিও এই কাজে পিছিয়ে নেই। বিজেপির আইটি সেল বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, বিশেষ করে ইউটিউবে, ভুল তথ্য ছড়াতে এবং বিরোধীদের হেয় করতে এআই-জেনারেটেড মিম ও ভিডিও ব্যবহার করেছে। তারা রাহুল গান্ধিকে অদক্ষ নেতা হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য এ আই-জেনারেটেড মিম ছড়িয়েছে। দিল্লিতে আম আদমি পার্টি একটি ভিডিও প্রকাশ করে, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির সমালোচনা করতে দেখা যাচ্ছে, যা ইউটিউব সহ বিভিন্ন মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং পরে তা ভুয়ো বলে প্রমাণিত হয়।
এই ধরনের ভুয়ো ভিডিও ও অডিও ছড়ানোর ক্ষেত্রে ইউটিউব একটি প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে, যা এর তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এই ধরনের বিভ্রান্তিকর কন্টেন্ট দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ইউটিউবের অ্যালগরিদম প্রায়শই এই ধরনের কন্টেন্টকে আরও বেশি দর্শকের কাছে পৌঁছে দেয়, যা তথ্যের ভুল ব্যবহারকে ত্বরান্বিত করে।
আরও পড়ুন-ধ্রুব রাঠী, রভীশ কুমাররা পারেন, বাংলার ইউটিউবাররা পারেন না কেন?
ইউটিউব: ভুয়ো সাংবাদিকতা
ইউটিউবের হাত ধরে কর্মসংস্থান বাড়ছে এবং অর্থনীতি সচল হচ্ছে, এটা যেমন ঠিক, তেমনই জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে এবং ভুল তথ্যের বিস্তার ঘটছে, সেটাও ঠিক। ইউটিউবের আরেকটি বিপদের দিক হলো, কিছু কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের সাংবাদিক সেজে সংবাদ পরিবেশন করা। তাঁরা নিজস্ব স্টুডিও থেকে 'ব্রেকিং নিউজ' প্রচার করেন কিন্তু প্রথাগত সাংবাদিকতার মৌলিক নীতিগুলো, যেমন-তথ্য নির্ভুল কিনা যাচাই করা, পক্ষপাতহীনতা, নৈতিকতা এবং উৎসের গোপনীয়তা — অনেকেই মানেন না। এর ফলে ভুল তথ্য বা ভুয়ো খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষ করে রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িকতার মতো সংবেদনশীল বিষয়গুলিতে।
২০২৩ সালের মণিপুর হিংসার সময় কিছু ইউটিউব চ্যানেল গুজব ছড়িয়েছিল যে, সেনাবাহিনী একটি নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে, যা মণিপুরের পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছিল। এছাড়াও, নির্বাচনের আগে কিছু ইউটিউবার রাজনৈতিক নেতাদের ব্যক্তিগত জীবন বা তাদের বক্তব্যের খণ্ডিত অংশ বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে মিথ্যা প্রচার চালান, যা ভোটারদের প্রভাবিত করে। এই ধরনের ঘটনা তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং সাংবাদিকতার বস্তুনিষ্ঠতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ করে।
যদিও ইউটিউবের কমিউনিটি গাইডলাইনস (যেমন - ক্ষতিকর কন্টেন্ট, বিদ্বেষমূলক বক্তব্য, শিশুদের নিরাপত্তা লঙ্ঘন নিষিদ্ধ) এবং কপিরাইট নীতি রয়েছে, তবুও প্ল্যাটফর্মের বিশালতার কারণে ভুল তথ্য নিয়ন্ত্রণ একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলা করতে না পারলে ইউটিউবের মতো এই রমরমা প্ল্যাটফর্মের দীর্ঘমেয়াদি বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে পড়বে।
সব মিলিয়ে, ইউটিউব এক অসাধারণ ডিজিটাল বিপ্লব এনেছে। এটি মানুষকে আয়ের সুযোগ করে দিয়েছে, নতুন পেশা তৈরি করেছে এবং তথ্যের আদান-প্রদানে গতি এনেছে। এটি বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে এবং হাজার হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। তবে, এর ব্যাপক বিস্তারের পাশাপাশি এর কিছু নেতিবাচক দিকও সামনে আসছে। যেমন তথ্যের অপব্যবহার (রাজনীতির ময়দানে নীতি-নৈতিকতা বাদ দিয়ে মিথ্যা কুৎসা রটানো হচ্ছে), জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন সাংবাদিকতা। এই ইউটিউবের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এর ব্যবহারকারী এবং প্ল্যাটফর্ম কর্তৃপক্ষের ইতিবাচক মনোভাবের উপর। এদের যৌথ প্রচেষ্টাই পারে ইউটিউবের নেতিবাচক প্রভাবগুলিকে দূরে সরিয়ে, ইতিবাচক দিকগুলিকে বিকশিত করতে।




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp