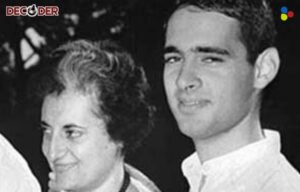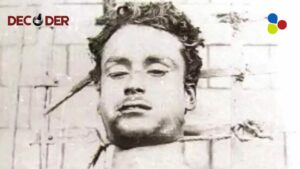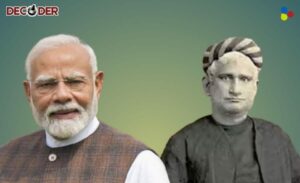অবন ঠাকুরের ছবির পেলবতায় মিশে আছে স্বতন্ত্র ইমপ্রেশনিস্ট স্পর্ধা
Montmartre and Bengal School of Art: ভ্যান গঘ জাহাজের নাবিকদের থেকে জাপান থেকে আসা উডকাট কিনে ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখতেন। ওঁর ছবিতে উডকাট স্টাইলের আনাগোনা এরপর থেকেই।
প্যারিস তখন এলিট বাসিন্দাদের ঘিরে আধুনিক শহরের রূপ নিচ্ছে। ফরাসি শিল্পীরা সে সময়ে শহরের বুলেভার্ডগুলির বিকল্প সন্ধান করছে। ছয়ের দশক থেকে প্যারিস ছাড়িয়ে ছোট্ট শহরতলি মঁমার্ত্র-কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে শিল্পীদের এক গ্রাম। এর কদর শুধুমাত্র ফ্রান্সেই নয়, সমগ্র পশ্চিমা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে এরপর। মঁমার্ত্র হয়ে উঠবে প্যারিসের সীমানার বাইরে, শহরের প্রাচীরের আড়ালে, একটি স্বাধীন গ্রাম।
যদিও পরবর্তীকালে মঁমার্ত্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্যারিসের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবু আজও বজায় রয়েছে এই গ্রামের স্বতন্ত্র চরিত্র। ছোট পাহাড়ের উপর গ্রাম, নগর পুনর্গঠনের জন্য উপযুক্ত ছিল না বলে অতীতের সংকীর্ণ গলি, ছোট-ছোট বাড়িঘর ও পুরনো উইন্ডমিলগুলি বর্তমানেও এই ল্যান্ডস্কেপের অংশ। ঐতিহাসিকভাবে, মঁমার্ত্র-র একটি ধর্মীয় পরিচয় ছিল— মঁমার্ত্র নামের অর্থ 'শহিদদের পাহাড়', যা সেন্ট ডেনিসের শহিদ হওয়ার ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে, পরিচয় বদলে মঁমার্ত্র দ্রুত হয়ে ওঠে নাইটলাইফের সমনামী। পাহাড়ের গা ঘেঁষে এখানে আঙুরের চাষ, প্রচুর পরিমাণ ওয়াইন তৈরি হয় এই অঞ্চলে। ঊনবিংশ শতকের প্যারিস শহরের তুলনায় কম করের আওতায় ছিল মঁমার্ত্র। অর্থাৎ, বাড়ি ভাড়া কম, সস্তায় মদ, সন্ধেবেলা নাচগানের ব্যবস্থা, উপরন্তু নদীর অপর পারেই একোল দ্য বোজ-আর্ত, আর এ পারের গ্রামীণ সৌন্দর্যের আহ্বান নিয়ে মঁমার্ত্র শিল্পীদের আকৃষ্ট করেছিল। এর মধ্যে ছিলেন ইমপ্রেশনিস্টরাও।

বিনোদনের এক আদর্শ গন্তব্য মঁমার্ত্র! এখানে শিল্পী ও সাধারণ মানুষের সহজ মেলামেশা। প্যারিস শহরকেন্দ্রিক উচ্চবিত্ত সমাজের তুলনায় এখানে অভিজ্ঞতার অন্য স্বাদ। শিল্পীরা এখানে স্থানীয় শ্রমজীবী তরুণীদের মডেল হিসেবে নিয়োগ করতেন, যারা প্রায়ই তাঁদের প্রেমিকাও হয়ে উঠতেন! এদুয়ার মানে, এডগার দেগা, অগুস্ত রেনোয়া, ক্যামিল পিসারো এবং পল সেজানরা মঁমার্ত্রে থাকতে শুরু করেন এবং নিজেদের স্টুডিও এখানেই গড়ে তোলেন। পাহাড়ের চূড়ার ক্যাফে ও ক্যাবারেগুলিতে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের আড্ডা বসত নিয়মিত। এখানেই সবচেয়ে সস্তায় থাকার ব্যবস্থা পাওয়া যেত।

আরও পড়ুন- “থিও ভ্যান গঘ: ১৮৫৭-১৮৯১” – অচেনা বই, অচিন এক জীবনের খোঁজ
ইমপ্রেশনিস্টদের অন্যতম জনপ্রিয় ক্যাফে ছিল র্যু দ্য বাতিনিওল-এর ক্যাফে গ্যেরবোয়া। এই ক্যাফেতেই ১৮৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মোনে প্রথমবার ইমপ্রেশনিস্টদের স্বাধীন প্রদর্শনীর পরিকল্পনা করেন। একোল দে বোজ-আর্ত যে প্রদর্শনীর প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিল। এলাকার আরেকটি জনপ্রিয় ক্যাফে ছিল নুভেল আতেন, যেখানে শিল্পী ও লেখকরা একত্রিত হতেন। দেগার ১৮৭৬ সালের বিখ্যাত চিত্রকর্ম ‘ল’আবসিন্থ’ এই ক্যাফের অভ্যন্তরের জীবন ধরে রেখেছে।

রেনোয়ার: মুলাঁ দ্য লা গালেত্তে
আজও মঁমার্ত্র-র রাস্তা ধরে হাঁটতে গেলে এইসব ক্যাফে-রেস্তোরাঁর দেখা মেলে। মুলাঁ দ্য লা গালেত্তের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চোখে ভাসে রেনোয়ারের একই নামের অন্যতম বিখ্যাত চিত্রকর্ম — এক উজ্জ্বল বিকেলে নৃত্য উৎসবে তরুণ প্যারিসিয়ানদের আনন্দ উপভোগের দৃশ্য। ১৮৮৬ সালে ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের এক চিত্রকর্মে এই জায়গাকেই ধরা হয়েছে, রাস্তা থেকে যেভাবে দেখা যায়।

ভ্যান গঘ: মুলাঁ দ্য লা গালেত্তে
ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ ছিল বিশ্বব্যাপী শিল্প জগতে এক পরিবর্তনশীল অধ্যায়। এই সময় ফ্রান্সে মঁমার্ত্র-ভিত্তিক ইমপ্রেশনিস্ট আন্দোলন নিয়ে কথা বলতে গেলে, এই লেখার প্রেক্ষিতে, কথা আসে ভারতে বেঙ্গল স্কুল অফ আর্ট নিয়ে। কিন্তু মঁমার্ত্র-র লম্বা সিঁড়ি দিয়ে পাহাড়ে ওঠার সময় বা আঙুরবাগানের পাশ কাটিয়ে হাঁটার সময়ে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে কোনও মিল পাওয়ার কথা নয়। ইমপ্রেশনিস্টদের জীবনযাপনের যে গল্প শোনা যায়, কলাভবনের শিল্পীদের জীবনের সঙ্গে তার মিল খোঁজার উদ্দেশ্যও এই লেখায় নেই। শান্তিনিকেতন এবং কলাভবনের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করে এই লেখার দৈর্ঘ্য বাড়ানো অবান্তর। শিল্পজগতের এই দুই আন্দোলনের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ভিন্ন। তবু সাধারণ চোখে দুই ধারার ছবি দেখতে দেখতে মনে হয়, এদের অন্তর্দৃষ্টিতে আত্মীয়তার আলো ছড়িয়ে। সেই আলো আর অনেকখানি স্পেসের সঠিক ব্যবহারের দিকে যাত্রাই হয়তো দুই ধারার শিরায় বয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথের ওয়াশ-এর কাজে ল্যান্ডস্কেপ জুড়ে বিস্তার আর নরম পেলব আলো। সম্পূর্ণ ভিন্ন মাধ্যমে আঁকা মোনের তেলরঙে সূর্যোদয়ের ছবিতে আমি একইরকম আলো দেখি। প্যাস্টেল শেডস, যা জীবনের কাছাকাছি, সহজ সাবলীল স্ট্রোক যেখানে কোনও দ্বিধা নেই, যেমন যা দেখি তাই ছবিতে রাখি—বসন্তের ঝিকিমিকি আলোয় উদ্ভাসিত লিলি-পন্ড হোক বা বরফের আলোয় জীর্ণ ভূমি, স্টিম-ইঞ্জিনের ধোঁয়ায় ঢাকা রেল স্টেশন থেকে কুয়াশাবৃত র্যুওঁ ক্যাথেড্রাল।

পড়েছি, ভ্যান গঘ জাহাজের নাবিকদের থেকে জাপান থেকে আসা উডকাট কিনে ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখতেন। ওঁর ছবিতে উডকাট স্টাইলের আনাগোনা এরপর থেকেই। ভারতে শিল্পের ইতিহাসে উডকাট বা লিনোকাটের প্রথম নিদর্শন হয়তো নন্দলাল বসুর কাজে। দেগার ছবিতে যে গতিময়তা, রেনোয়ার তাঁর ছবিতে যেভাবে দেখিয়েছেন চলমান চরিত্রদের, রামকিঙ্করের ছবিতেও দেখি একইরকম মুভমেন্টের আধিপত্য।
আরও পড়ুন- ভিনসেন্টের বিখ্যাত সব ছবির সেই গ্রাম, আজও যেন আস্ত ক্যানভাস
দুই ধারার মধ্যে সমান্তরাল চলন চোখে পড়া হয়তো আমার কাঁচা মনের ভ্রম। আশা করি এই বিষয়ের জ্ঞানীগুণীরা দোষ ধরবেন না। যদিও, ইমপ্রেশনিস্ট আন্দোলন আর বেঙ্গল স্কুল অফ আর্টের ইতিহাসের যে সাদৃশ্যটি একেবারেই মনগড়া নয়, তা হলো এদের স্পর্ধা! পৃথিবীর দুই প্রান্তে এই অনন্য স্পর্ধার উত্থান আমার চোখের ভুল নয়, তা বুঝি। আকাডেমিক চোখরাঙানি প্রত্যাখ্যান করে নতুন শিল্পভাবনার দিকে এগিয়ে যাওয়া এই দুই স্কুলের ভিত্তিস্থাপন। শিল্প এবং শিল্পীর স্বায়ত্তশাসন পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা। একটি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে, অন্যটি আকাডেমিক কাঠামোর বিরুদ্ধে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনায় গড়ে ওঠা বেঙ্গল স্কুল অব আর্ট ব্রিটিশ-শাসিত স্কুলগুলোর বিরোধিতার একটি অংশ। কলকাতার গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্টের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর ইউরোপিয় আর্ট শেখানোর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভারতীয় শিল্পধারার প্রতি ফিরে যাওয়ার আহ্বান। মুঘল মিনিয়েচার, অজন্তার গুহাচিত্র থেকে অনুপ্রাণিত হন বেঙ্গল স্কুলের শিল্পীরা। ভারতের বাইরে থেকে সেখানে মিশেছে জাপানি ওয়াশ পদ্ধতি। অর্থাৎ, শিল্পের অন্য ধারার সঙ্গে মিশ্রণ ঘটেছে, কিন্তু কোন শৈলীকে আপন করবেন সেই সিদ্ধান্ত ছিল শিল্পীদের। কোনও আরোপিত ধারার কাছে মাথা নত করেননি তাঁরা। ইতিহাসবিদ পার্থ মিত্রের মতে, “বেঙ্গল স্কুল শুধুমাত্র একটি শিল্প আন্দোলন ছিল না, এটি ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।”
অন্যদিকে, ফ্রান্সে ইম্প্রেশনিজম আন্দোলন প্যারিসের আকাদেমি দ্য বোজ-আর্ত-এর কঠোর নিয়ম-কানুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ক্লদ মোনে, এডগার দেগা, ও পিয়ের-অগুস্ত রেনোয়া-র মতো শিল্পীরা ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক বিষয়বস্তুর পরিবর্তে আধুনিক নগরজীবন ও ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তকে চিত্রায়িত করতে চেয়েছিলেন। টি. জে. ক্লার্ক লিখেছেন,
“ইমপ্রেশনিজম কেবলমাত্র একটি শৈলী ছিল না, এটি ছিল দৃষ্টিশক্তির পুনর্বিবেচনা।”
এক অর্থে, বেঙ্গল স্কুল অফ আর্টের বিপ্লবী সূচনার উল্টো পথে গমন ইমপ্রেশনিস্টদের। তাদের কৌশল ও উদ্দেশ্যের পার্থক্য সত্ত্বেও, পথচলার শুরু বিপরীতমুখী হলেও, বেঙ্গল স্কুল অফ আর্ট এবং ইমপ্রেশনিজমের মূলমন্ত্র ছিল প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও পুনর্নির্মাণ। শিল্পে আরোপিত কঠোর নিয়ম ভেঙে স্বাধীন চিত্রভাষা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। রঙের স্বাধীন ব্যবহার, তুলির সজীব স্পর্শ ও গভীর ভাববোধ— দু'টি আন্দোলনের এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে পাশাপাশি রাখায় কোনও দোষ আছে কি?




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp