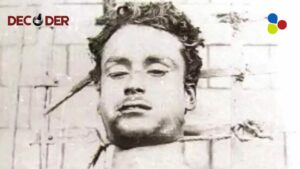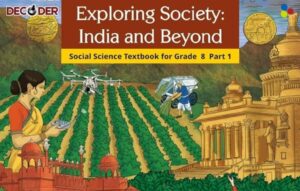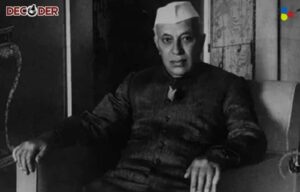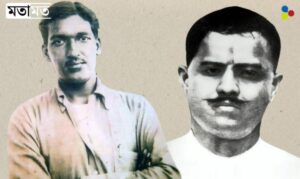পর্যটনের বহর প্রবল! তবু ভালো হাসপাতাল, রাস্তা নেই সাধের শান্তিনিকেতনে
Shantiniketan: আড়কাঠি বালিমাফিয়া ক্রমাগত বালি তুলে পাচার করছে। এখানেও ব্যবহৃত হচ্ছে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের নতুন প্রজন্ম।
যে কোনও শহর, জনপদ তৈরিতে চিকিৎসা ব্যবস্থার একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে। অর্থাৎ একটা পরিকাঠামো বা অবকাঠামোর প্রয়োজন হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে সে বিষয়ে কখনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বড় শহরগুলোর বাইরে পঞ্চাশ বছর আগে যেমন ছিল, এখনও তার বিরাট ব্যত্যয় কিছু ঘটেনি। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে এর ব্যতিক্রমও আছে। হাসপাতাল হয়েছে, তার গায়ে নীল-সাদা রঙের প্রলেপ পড়েছে কিন্তু ওষুধ, চিকিৎসার জন্য নির্ভরযোগ্য যন্ত্রপাতি বাড়ন্ত। প্রয়োজনের তুলনায় ডাক্তার অত্যন্ত কম। কথাগুলো লিখলাম বোলপুর মহকুমা শহরের কথা মাথায় রেখে। শুধু বোলপুর নয়, সারা বীরভূমেই চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। বোলপুর বা শান্তিনিকেতনে সেভাবে কেউ গুরুতর অসুস্থ হলে একদিকে বর্ধমান সদর হাসপাতাল বা কলকাতার হাসপাতাল আর অন্যদিকে দুর্গাপুরে বেসরকারি হাসপাতালই ভরসা। সেখানেই নিয়ে যেতে হয়। একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রের এই অবস্থা চলছে দশকের পর দশক। সরকারের কোনও উদ্যোগ নেই।
এখানে জানিয়ে রাখি, খোদ শান্তিনিকেতনের ইতিহাসটা ছিল একটু অন্যরকম। গত শতাব্দীর শুরুতে যখন শান্তিনিকেতন স্থাপিত হলো তখন রবীন্দ্রনাথ খেয়াল করলেন যে, এই ভূখণ্ডে মহামারির মতো ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, কলেরা লেগেই আছে। ফি বছর বহু মানুষ এতে মারা যায়। যেমন পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে, তেমনই ছাত্রছাত্রীরাও বাদ যায় না। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ করেন। কেননা এই সমস্যা তাঁকে বিচলিত করেছিল। তাঁর সৃষ্টিকর্মের মধ্যে তা নানাভাবে প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর উপন্যাস যেমন, 'গোরা'-য় কলেরার উল্লেখ পেয়েছি, তেমনই 'চতুরঙ্গ'-তে প্লেগের কথা লিখেছেন। তাছাড়া তাঁর কবিতাতেও এসেছে রোগের বিষয়। এক্ষুনি মনে পড়ছে 'পুরাতন ভৃত্য'-র কথা, 'অভিসার' বা 'নৈবেদ্য' কবিতাটি। ছোটগল্পেও আছে। এছাড়াও, এই সমস্ত রোগ নিয়ে চিঠি লিখেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, সরকারের সীমিত ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করা যাবে না। এর সমাধানের পথ তৈরি করলেন ভিন্ন এক প্রায়োগিক উপায়ে। জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে এক ধরনের নির্দিষ্ট পরিকল্পনানির্ভর সচেতনতা তৈরি করা শুরু হলো। প্রচলিত ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে, সমস্ত রকম সংস্কারের বাইরে তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক সচেতনতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন মানুষকে। তৈরি হলো নানা জায়গায় 'সেবাকেন্দ্র'। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রখ্যাত জীবাণু বিশেষজ্ঞ গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার জে এফ কেন্ড্রিক, ডাক্তার হ্যারি টিম্বার্স ও লেনার্ড এলমহার্স্ট। এই দীর্ঘ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে 'ম্যালেরিয়া' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,
"তার একটা প্রমাণ আছে আমাদের প্রতিবেশী গ্রামগুলোতে সম্মিলিত আত্মপ্রচেষ্টায় আরোগ্য বিধানের প্রতিষ্ঠায়।"
আরও পড়ুন-মদ, মাংস এবং … হোটেল-রিসর্টময় শান্তিনিকেতন এখন যেখানে দাঁড়িয়ে

সে সব এখন অতীত। যা থেকে আমরা শিক্ষা নিইনি বা নিতে চাইনি। ফলে এই আধুনিক চিকিৎসার যুগে এই গুরুত্বপূর্ণ মহকুমা শহরটি অনেকানেকই পিছনে পড়ে আছে। একটা অপরিকল্পিত শহরে কীভাবে বেহাল রাস্তাঘাটের জন্য রীতিমতো বিশৃঙ্খল অবস্থা তৈরি হয়, বিশেষ করে পর্যটকদের জন্য নানা উৎসবের সময়, তা বোলপুরে এলেই বোঝা যায়। চার দশক বা তারও আগে দেখেছি, বোলপুর স্টেশন থেকে শহরে ঢোকার রাস্তা যা ছিল তার চেয়েও রাস্তা সংকীর্ণ এখন। এই নিদারুণ অবস্থা মানুষ মেনে নিচ্ছে। মনে রাখতে হবে, এই শহরে সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি টোটো নিত্যদিন রাস্তায় থাকে। সঙ্গে আছে আরও সব নানা যানবাহন। ফলে আজ তার অবস্থা আরও মারাত্মক। কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে কোন পদক্ষেপ কখনও করেনি। সাধারণ্যে তা প্রকৃতই অতিষ্ঠ হওয়ার মতো। স্টেশন থেকে বেরিয়ে শহরের পথে গেলেই দেখা যাবে ট্রেকার বা ট্র্যাক্টরের উৎপাত। যারা অসম্ভব বেপরোয়া গাড়ি চালায়। অনেক গাড়িতে যথাযথ লাইটের ব্যবস্থা নেই। এদিকে শহরে ঢুকলে একটু বড় রাস্তা পেলেই মারাত্মক গতিতে চলছে অসংখ্য ডাম্পার। যার ফলে ঘন ঘন অ্যাক্সিডেন্ট। এই ডাম্পারগুলো বালি পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত। বালির কথায় পরে আসছি। আসলে লিখতে চাইছি, এই যে মানুষ মায় পর্যটকদের ভালো লাগার শহর, আকর্ষণের এই শহর (তা যে কোনও কারণেই হোক) তার এই হাল হবে কেন? প্রশ্ন আছে অযুত কিন্তু উত্তর নেই!
আরও পড়ুন-বাউল কম, শান্তিনিকেতন দাপাচ্ছে বাবুর বাড়ির ‘ফাউল’-রা
বোলপুর তথা শান্তিনিকেতন কিন্তু সাধারণ শহর নয়। বরং তার চেয়েও বড় কিছু। এর একটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে। আছে এক গড়ে ওঠার ইতিহাস। আছে স্রোতস্বিনী কোপাই নদী, আছে অনন্য প্রাকৃতিক বিস্তার। লাল খোয়াইয়ের দৃষ্টিসুন্দর মনোরম ভূদৃশ্য। আসলে এইসবই আছে, কিন্তু প্রশ্ন হলো কীভাবে আছে? আড়কাঠি বালিমাফিয়া ক্রমাগত বালি তুলে পাচার করছে। এখানেও ব্যবহৃত হচ্ছে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের নতুন প্রজন্ম। গ্রামে গ্রামে রাত বারোটায় জমায়েত হচ্ছে ছেলেরা। তারপর যাচ্ছে কোপাইয়ের নানা তীর সংলগ্ন এলাকায়। সারারাত কাজ করে সকালে গ্রামে ফিরছে। মাঝেমধ্যেই পুলিশের তাড়া খাচ্ছে। ধরা পড়লে জরিমানাও দিতে হচ্ছে। অথচ যারা কাজ করাচ্ছে তারা বহাল তবিয়তে আছে। এর সঙ্গে রাজনৈতিক যোগসাজশের কথা নতুন করে লেখার কারণ দেখছি না। এখন ভদ্দরলোকের সমাজ বলতেই পারে, চুরির কাজে মদত দেওয়াও অন্যায়। আলবাৎ অন্যায় কিন্তু এরা তো নাচার! এখানে কর্মসংস্থানের ছিটেফোঁটাও নেই। তাহলে এই গরিবগুর্বো সাঁওতালরা করবে কী? প্রকৃতপক্ষে এদেরই বিপথগামী হতে বাধ্য করা হচ্ছে।

একদিকে বালি তুলে পাচার করা আর অন্যদিকে কোপাইয়ের ধারে প্রোমোটারকুলের আনুকূল্যে এবং সবিশেষ অনুপ্রেরণায় গজিয়ে ওঠা বেআইনি অসংখ্য রিসর্ট আর ফ্ল্যাট কমপ্লেক্স। তা আবার সীমালঙ্ঘন করে ঢুকে পড়ছে খোদ কোপাইয়ের চরে, নদীর অংশ দখল করে। তা নিয়ে যে প্রতিবাদ হয়নি তা নয়। তবে তা খুবই সহজে দমিয়ে দেওয়া গেছে। প্রশাসন ঠুঁটো জগন্নাথ। তাহলে কী করে সেই নদীর নাব্যতা যথাযথ থাকবে? এরও কোন মীমাংসা নেই। বনভূমির কথা না লেখাই ভালো। ইচ্ছেমতো গাছ কাটা হচ্ছে। সোনাঝুরি হাটের দিকে তাকালে তা বিলক্ষণ ঠাহর করা যায়। ক্যানেলের ধারের রাস্তায় (আমার কুটির রোড) ছিল অত্যন্ত প্রাচীন ও দুর্মূল্য সব গাছ। সেইসব কোটি কোটি টাকার গাছ রাতারাতি কেটে ফেলা হলো। শোনা গেছে, বনদফতরকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েই তা কাটা হয়েছে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে বিশ্বভারতীর প্রকৃতিপ্রিয় ছাত্রছাত্রীরা গাছ জড়িয়ে বসে ছিল মধ্যরাত পর্যন্ত। তাঁদের মেরে ধরে তুলে দেওয়া হয়। সেখানে দেশি ও বিদেশি ছাত্রীরাও পার পায় না। মামলা হয় ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে। তাঁদের অভিভাবকদের শাসিয়ে বলপূর্বক মামলা তুলে নিতে বাধ্য করা হয়। এই পুরো ঘটনাটাই ঘটে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে একজন পঞ্চায়েত প্রধানের তত্ত্বাবধানে। ছাত্রছাত্রীদের তিনি নিজের হাতে মেরেছেন তাঁর দলবলসহ। এর উদ্দেশ্য-বিধেয় সম্পর্কে আর বিস্তারিত না লিখলেও চলবে। এই যদি অবস্থা হয় এমন পর্যটন কেন্দ্রের তবে কীভাবে চলবে এই সন্নিহিত অঞ্চলের দিন, প্রতিদিন? তাহাদের শান্তিনিকেতনের ভবিষ্যত নিয়ন্ত্রিত হবে কাদের দ্বারা? তা ভগাই জানে!




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp