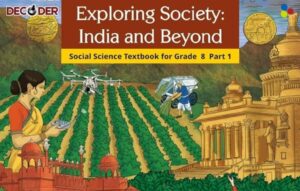তরুণ কবিদের মধ্যে আদৌ জেগে আছেন রবীন্দ্রনাথ?
Rabindranath Tagore: কেন আজও সেই ছায়াবৃক্ষের তলায় যান আজকের কবিতা লিখিয়েরা। আদৌ কি যান? শূন্য এবং প্রথম দশকের কবিদের কাছে কোথায় দাঁড়িয়ে আজকের রবীন্দ্রনাথ?
আধো আধো বুলি ফোটা সেই 'আমাদের ছোট নদী' কিংবা 'কুমোরপাড়ার গোরুর গাড়ি' মাখা 'সহজপাঠ' সকাল থেকে ক্রমে বেলা গড়ায়। মধ্যগগনের রবি ক্রমে ঢলে পাটে। বাংলা কবিতা সাবালক হয়ে বলে ওঠে 'তিন জোড়া লাথির ঘায়ে রবীন্দ্র-রচনাবলী লুটোয় পাপোশে।' কিন্তু আদৌ কি ফুরায় 'সঞ্চয়িতা'র পাতায় নয়নতারা রাখা ফুরফুরে সব দিন! তারপর? চক্রবৎ পরিবর্তন্তে কবিতার দিন-রাত্রি। পুরনো কবিরা যায়, নতুন কবিতা আসে। এ দেশ আসলে নিশীথ সূর্যের। যে দেশে রবি নেভে না কখনও, কোনওদিন।
রবীন্দ্রনাথ যখন কিশোর, সে সময়ে কবিতার ভুবনে মধ্যগগনে ছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী। কবির বউদিদি তথা কাদম্বরীর কাছে সেই বিহারীলাল ছিলেন কবিশ্রেষ্ঠ। তাঁর মতো কবিতা যে আর কেউ লিখতে পারেন না, সেই বাক্যবীজ রবির মনে পুঁতে দিয়েছিলেন কাদম্বরী। সেই বিহারীলালকেই একটা সময় টপকে গেলেন রবি সব দিক থেকে। ক্রমে সাহিত্যের জগতে কৃষিকাজ করতে করতে বুঝলেন, নদী সরলরৈখিক পথে চলে না। চলতে চলতে বাঁক বদলই তার ধর্ম। আর সেই বাঁক বদলের নামই আধুনিকতা। অপরিসীম প্রতিভা, নিরলস প্রচেষ্টায় পাথর ভাঙার কাজ যতটা সহজ ছিল রবির পক্ষে, রবীন্দ্র পরবর্তী কবিদের পক্ষে তা সহজ হল না স্বাভাবিক ভাবেই। কারণ রবির সামনে রবীন্দ্রনাথের আকৃতির বিপুল প্রতিভা দাঁড়িয়ে ছিল না। যা ছিল পরবর্তী প্রজন্মের কবিতা লিখিয়েদের সামনে। কিন্তু তাঁরা অতিক্রমণের পথে হাঁটলেনই না। বরং রবি-তেজে ঝলসে যাওয়াকেই শ্রেয় মনে করলেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচীরা ছিলেন যার পুরোভাগে। বুদ্ধদেব বসু লিখছেন,
“রবীন্দ্রনাথের বিরাট মহাজনি কারবারের পর খুচরো দোকানদার হওয়াতে লজ্জার কিছু নেই— সেটাকে তো অনিবার্য বলা যায়, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের মালপত্রও আপাতদৃষ্টিতে এক ব'লে বাংলা কাব্যে তাঁর আসন এমন সংশয়াচ্ছন্ন।”
রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক/ বুদ্ধদেব বসু
তবে সত্যেন্দ্রনাথেরা রবি-আঁচে ঝলসে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন কোন পথে আসলে ঘাপটি মেরে বিপদ। তার পরেও রবি-প্রভাব ছেড়ে বেরিয়ে আসা ততটাও সহজ ছিল না সেসময়। মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নজরুল ইসলামের হাত ধরে সেই অভিশাপ খানিকটা কাটল। এর মধ্যে সম্ভবত নজরুলই ছিলেন সবচেয়ে ক্ষমতাবান। কারণ সেই রবীন্দ্রতেজের সামনে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ আলাদা, স্বতন্ত্র এক কাব্যভাষা বোধহয় দাঁড় করাতে পেরেছিলেন একা তিনিই। আপাতদৃষ্টিতে যা ছিল তাঁর দুর্বলতা— যে ছিন্নমূল ভাব, দারিদ্র, পরবর্তীতে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া, এই সমস্ত অভিজ্ঞতাই তাঁকে সাহায্য করেছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতার সেই মায়াজাল ভাঙতে। তাঁর কবিতার যে প্রগলভতা, যে অসংযত ভাব, তা-ই তাঁকে জিতিয়ে দিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতার যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব, তা কাটিয়ে উঠতে পারেননি নজরুল। সেই সর্বব্যাপী চেষ্টাও তাঁর ছিল না। আর সেই জায়গাতেই এসে দাঁড়াল কল্লোল গোষ্ঠী।
রবীন্দ্র-বিরোধিতার মন্ত্র নিয়েই ময়দানে নামল তারা। ততদিনে বিদেশি সাহিত্যের সঙ্গে যাতায়াত আরও সহজ হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এই সময়ের কবিরা রবি-তেজ এড়াতে একের পর এক বিদেশি ভাষার কবির শরণাপন্ন হতে লাগলেন। বিষ্ণু দে-র কবিতায় দেখা গেল বেশ খানিকটা এলিয়টের প্রভাব, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের উপর ছিল ফরাসি কবি মালার্মের প্রভাব। বুদ্ধদেব বসু ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত ছিলেন আরেক ফরাসি কবি শার্ল বোদলেয়ারের থেকে। অমিয় চক্রবর্তীর অন্যতম পছন্দ ছিল জার্মান কবি রাইনার মারিয়া রিলকে। তবে এদের উপর কোনও একজন কবিরই প্রভাব ছিল বললে ভুল বলা হবে। এদের পড়াশোনার জগৎ এতটাই বিস্তৃত ছিল, যে সেই ছাপ মিলত তাঁদের কবিতার প্রতি স্তবকে স্তবকে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ যে স্বতস্ফূর্ত অনুভূতির প্রস্রবনের কথা বলেন, তার থেকে বেশ কিছুটা দূরে এই সব কবিরা। কারণ তাঁরা প্রতিটি শব্দ নির্বাচন করেন ভেবে, বেছে, রীতিমতো পড়াশোনা করে। এই সমস্ত তিরিশের দশকের কবিদের মধ্যে যিনি পরবর্তীকালে সুদূর প্রসারী প্রভাব রেখে যাবেন, তিনি জীবনানন্দ দাশ। ইংরেজি ভাষার অধ্যাপক জীবনানন্দের উপরেও ছিল বিদেশি সাহিত্যের প্রভাব। তবে রবিতেজ, বিদেশী সাহিত্যের ভাষাকে পেরিয়ে এক অন্যতর কবিতার ভুবন, কাব্যভাষা, বোধের জগৎ তিনি তৈরি করে ফেলেছিলেন নিজের অজান্তেই। যা কি আসলে পরবর্তী কালে আরও এক অনতিক্রম্য মহীরুহ হয়ে উঠবে বাংলা কবিতার দুনিয়ায়? যার ছায়া থেকে মুক্ত হতে পারবে না আধুনিকতম কবিতাও। তবে রবীন্দ্রনাথের মতো সর্বব্যাপী, বিরাট, বিপুল কোনওদিনই ছিলেন না তিনি। আয়ুতেও ছিলেন না, কাব্যসৃষ্টির বিশালতাতেও নয়। তবে সেই জীবনানন্দের হাত ধরেই রবীন্দ্র-বিরোধিতার সলতেকে মশাল করে তুলেছিলেন পরবর্তী প্রজন্মের কবিরা।
সময়টাও তখন ছিল বড়ই উত্তাল। ততদিনে একটা বিশ্বযুদ্ধ দেখে ফেলেছে পৃথিবী। তার প্রভাব এসে পড়েছে বাংলাতেও। অন্যদিকে ভারতে শুরু হয়ে গিয়েছে পুরোদমে আইন অমান্য আন্দোলন। দেশের বিভিন্ন জায়গায় জাগছে শ্রমিক আন্দোলন। মোটামুটি ৩৫ থেকেই ফ্যাসিবাদ বিরোধী ভাবনাচিন্তা ছড়িয়ে পড়েছে এ দেশে। যা অব্যবহিত পরেই একদল বামপন্থী কবির জন্ম দেবে এই বাংলায়। অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, দিনেশ দাসের মতো কবিরা এসে শোনাবেন 'লাল টুকটুকে দিন' আনার গল্প। কিন্তু সুভাষদের মতো চল্লিশের কবিরাও সেই ভাবে জীবনানন্দের মর্ম বুঝতে পারেননি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন,
“আমরা যখন জীবনানন্দকে নিয়ে হইচই শুরু করি, তখন প্রেমেন্দ্র মিত্র রীতিমতন বিস্ময়ের সঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, তোমরা ওঁর লেখায় কী পাও, ওঁর লেখায় তো নিজস্ব কোনো বক্তব্য নেই! সুভাষ মুখোপাধ্যায় সমেত বামপন্থী কবি ও সমালোচকরা এবং সজনীকান্ত দাশের মতন দক্ষিণপন্থীও প্রায় একই সুরে জীবনানন্দ দাশকে আক্রমণ করেছেন।”
রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার এবং পুনরাবিষ্কার /সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
সেই সুনীলরাই আবার পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার দুরন্ত মোহে লিখে ফেলেছিলেন রবীন্দ্র রচনাবলীকে পদাঘাত করার কথা। পরে অবশ্য স্বীকার করেছেন, সেসব যৌবনের প্রগলভতা মাত্র। তবে এ কথা ঠিক কৃত্তিবাসী গোষ্ঠী একরকম ভাবে জীবনানন্দকেই সিংহাসনে বসিয়েছিল। তবে ব্যাপকতার দিক দিয়ে জীবনানন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনও তুলনাই যে চলে না, সে কথাও না মানলেই নয়। তবে এ কথা ঠিক, কবিতার দুনিয়ায় নতুন একধরনের শব্দদেহ, সময়োপযোগী কণ্ঠস্বর তৈরি করতে পেরেছিলেন জীবনানন্দ। তবে তা-ও একসময় ভরে উঠেছিল পৌনপৌনিকতায়। রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় গুণটি বোধহয় নিজেকে বারবার ভাঙা। যে বয়সে এসে একধরনের একরোখা ভাব চেপে ধরে, পরিবর্তনকে মানতে অসুবিধা হয়, সেই বয়সে এসে নিজের সঙ্গে অফুরন্ত পরীক্ষানিরিক্ষা করে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। শেষের কবিতা উপন্যাসে তিনি নিজেই বলছেন,
“এ কথা বলব না যে, পরবর্তীদের কাছ থেকে আরো ভালো কিছু চাই, বলব অন্য কিছু চাই। ফজলি আম ফুরোলে বলব না, ‘আনো ফজলিতর আম।’ বলব, ‘নতুন বাজার থেকে বড়ো দেখে আতা নিয়ে এসো তো হে।’...”
শেষের কবিতা/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ফলে রবীন্দ্রনাথের অন্ধ অনুকরণ হোক, তা বোধহয় তেমন করে তিনিও চাননি। কল্লোল গোষ্ঠী হোক বা কৃত্তিবাস, তারা যত না রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি বিরোধিতার নিশানায় ছিলেন অন্ধ রবীন্দ্রানুসারীরা। সে কারণেই বোধহয় সারাদিন রবীন্দ্র-বিরোধিতা করার পর রাতে বাড়ি ফিরে 'পূরবী'র কবিতা মুখস্থ করে গিয়েছেন বুদ্ধদেব বসুরা। ফলে সুনীলরা যা বলেছেন, তা খুব ভুল বলে মালুম হয় না। তিনি লিখছেন,
“কোনো নবীন লেখক যদি সূচনাপর্বে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করে নিজস্ব ভাষা সন্ধানের চেষ্টা না করে, রবীন্দ্রনাথেই আপ্লুত হয়ে থাকে সে অতি মূর্খ। পরিণত বয়েসেও যদি কোনো লেখক রবীন্দ্রনাথের থেকে দূরে সরে থাকে, তাঁকে জীবনযাপনের সঙ্গী করে না নেয়, তা হলে সে আরও বড়ো মূর্খ।”
রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার এবং পুনরাবিষ্কার /সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ষাটের শুরুর দিকে কলকাতায় এলেন বিট কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ। ততদিনে বাংলায় শুরু হয়ে গিয়েছে হাংরি সাহিত্যের ধারা। সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে বুড়ো আঙুল দেখানোর এক উগ্র জোয়ারে ভাসতে লাগলেন একের পর এক কবি। তৈরি হল গোটা একটা সম্প্রদায়। তাদের বিরুদ্ধে শুরু হল অশ্লীলতার মামলা, ব্যাপক ধরপাকড়। শক্তির মতো অনেক কবিই গোড়া থেকে হাংরিদের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু পুলিশি ধরপাকড় শুরু হতে হাংরিদের হাত ছাড়েন তাঁরা। এরই মধ্যে সত্তরের উত্তাল সময়। একের পর এক মেধাবী মাথা রাষ্ট্রযন্ত্রের তলায় গুঁড়িয়ে গেল। সামগ্রিক ভাবে রবীন্দ্রবিরোধিতা বা রবীন্দ্র-আত্তিকরণের তেমন বড় কোনও প্রচেষ্টা ছিল না সত্তর-আশি জুড়ে। ততদিনে রবীন্দ্রনাথ নেই। কিন্তু বিশ্বভারতী ছিল। পান থেকে চুণ খসলেই বিশ্বভারতীর চোখরাঙানিও ছিল। নব্বইয়ের দশক সামগ্রিক ভাবে সমস্ত কিছু পাল্টে যাওয়ার সময়। নব্বইয়ে এসে মানুষের জীবন-যাপন বদলে গেল ভীষণ ভাবে । যন্ত্রসভ্যতা এসে গ্রাস করতে লাগল সব কিছুকে। ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল দুরদর্শন থেকে টেলিফোন। ইলেকট্রনিকস বিপ্লব, বিজ্ঞাপনের বাড়বাড়ন্ত মানুষের এতদিনের যে জীবনযাপনের ধরন, সেটাকে দিল আমূল বদলে। ফলে বদলে গেল কাব্যভাষা। মেট্রোপলিটন যে যাপন এতদিন তার অজানা-অচেনা ছিল, ক্রমে সেখানেই গিয়ে পড়ল মানুষ। প্রায় সকলেরই মনে পড়বে গিটার নিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ার জন্য বিশ্বভারতীর লাল চোখের সামনে পড়তে হয়েছিল সুমন চট্টোপাধ্যায়কে। তখনও অবশ্য তিনি কবীর সুমন হননি। তবে বিশ্বভারতীর এই কড়াকড়ি আজকের নয়। ষাটের দশকে বিশ্বভারতীর কাছ থেকে একটি চিঠি পান প্রখ্যাত গায়ক দেবব্রত বিশ্বাস। চিঠিতে তাঁকে জানানো হয়, তিনি স্ক্র্যাচ টেপে যে দু'টি গান জমা দিয়েছিলেন, সেই দু'টি গান তাঁকে রেকর্ড করার অনুমতি দেবে না বিশ্বভারতী। অত্যাধিক মেলোড্রামা ও অপ্রয়োজনীয় ইন্টারল্যুডের ব্যবহার নাকি সেই গান দু'টিকে আড়ম্বরপূর্ণ ও বিকৃত করে তুলেছিল। ২০০১ সালে বিশ্বভারতীর লাল চোখ থেকে মুক্ত হল রবীন্দ্রনাথের গান। বেঁধে রাখা ছেলের দল যেমন ছুটির ঘণ্টা শুনে ক্লাসরুম থেকে হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে, সে ভাবেই রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যবহারের ঘনঘটা শুরু হল সর্বোত্র। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলতেন, "বিধাতার রাজ্যে ভালো জিনিস অল্প হয় বলেই তা ভালো, নইলে সে নিজেরই ভিড়ের ঠেলায় হয়ে যেত মাঝারি।" রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গেও কি অনেকটা তেমনটাই হল না? সার্ধ শতবর্ষের গুঁতোয় রাস্তাঘাটে, সিগন্যালে, পাড়ার আড্ডায়, মোচ্ছবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাড়বাড়ন্তে প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার জোগার হল আম বাঙালির। আর সিনেমা-টিভির দৌলতে অবাঙালির কাছে রবীন্দ্রনাথ পৌঁছলেন ওই ভাঙা ভাঙা বুলিতে 'একলা চলো' পর্যন্তই।
সাম্প্রতিক কালে অনেকেই মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের লেখা ওই হাজার তিনেক গান আসলে রবীন্দ্রভুবনের অন্যতম সেরা সম্পদ। তার মূল শক্তি তার কথা, তার বোধ। যা এই এতগুলো বছর পরেও একই ভাবে মানুষকে নাড়া দেয়। মানুষের দুঃখে-সুখে, সমস্ত রকম অনুভূতিকে জারিত করে সেই সব শব্দের অনুরণন। শূন্য সময়ের কবিতাও দেখতে দেখতে কাটিয়ে ফেলল দু'টো দশক। এই দু'দশকে কম পালাবদল, কম পাল্টে যাওয়া দেখেনি তারা। প্রকৃতি পাল্টেছে। পাল্টেছে রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থা। করোনা অতিমারি মানুষকে এক নতুনতর সময়ের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে অতি দ্রুত। নব্বই যদি যন্ত্রসভ্যতার দশক হয়ে থাকে, তাহলে এটা ইন্টারনেটের যুগ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সময়। মানুষের বেঁচে থাকার ধরনটাই অনেকটা বদলে দিয়েছে এই ডিজিটাল আমল। রবীন্দ্রনাথ 'মুক্তধারা' নাটকে যন্ত্ররাজ বিভূতির আবিষ্কারের যে নগ্ন, ভয়ঙ্কর রূপটি দেখাতে পেরেছিলেন, শূন্য দশকে তা-ই যেন হয়ে উঠল অদৃশ্য, ইনভিজিবল। এ যেন ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ। সেই ছায়াবাজির যুগে কবিতার শরীর, ত্বক, মন, হৃদয় যে সবটাই বদলাবে, তা একরকম নিশ্চিত ছিল। কিন্তু সেই নতুন অবয়বেও কীভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে রইলেন রবীন্দ্রনাথ? কেন আজও সেই ছায়াবৃক্ষের তলায় যান আজকের কবিতা লিখিয়েরা। আদৌ কি যান? শূন্য় এবং প্রথম দশকের কবিদের কাছে কোথায় দাঁড়িয়ে আজকের রবীন্দ্রনাথ?

একটা বয়স পর্যন্ত কবিতার প্রতি তেমন আগ্রহ ছিল না কবি নীলাঞ্জন দরিপার। সেই জায়গাটাকে বদলে দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের গান। সুর পেরিয়ে সেই সব গানের কথা নীলাঞ্জনকে আকৃষ্ট করেছিল ভীষণ ভাবে। টেপ রেকর্ডারে শোনা সেই সব গান দ্রুত হাতে খাতায় লিখে রাখতেন তিনি। কিছু কিছু শব্দ, বাক্য শুনে মনে হত, এর আগে এমন কথা তো কেউ কখনও বলেনি। কিংবা হয়তো এই কথাগুলি আমারই বলার ছিল। সেই রবীন্দ্রগানের কথাই উদ্বুদ্ধ করেছিল খাতায় ইকিরমিকির লিখতে। সেখান থেকেই নীলাঞ্জনের কবিসত্তার পথচলা। গান দিয়ে শুরু হয়েছিল যে রাস্তা, তা ক্রমে পৌঁছয় 'দুই বিঘা জমি', 'পূজার সাজ', 'পূরাতন ভৃত্য' বা 'বীরপুরুষে'র মতো কবিতার ভুবনে। এই সব কবিতার ছন্দের যে কাঠামো, তা টেনেছিল নীলাঞ্জনকে। রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে নীলাঞ্জন জানালেন তার একান্ত কিছু ভাবনা। তিনি মনে করেন, আজ থেকে এক হাজার আগেই লেখা হোক বা পরে, জিনিসটা কবিতা। যার মূল উদ্দেশ্যই হল নিজের কথাটুকু বলা। যারা কবিতা লেখার চেষ্টা করেন, তাঁরা কীসের তাড়নায় তা লেখেন? আদতে কোন জিনিসটা তাঁকে দিয়ে কবিতা লিখিয়ে নেয়? আসলে যে কোনও অনুভূতি, তাকে নিজের করে নিয়ে তার দ্বারা তাড়িত হয়ে নিজের মধ্যে লেখার অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তোলা, যে কোনও কবির ক্ষেত্রে সেটা সাধারণ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াটাকে রপ্ত করতে হয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা এতটাই ব্যাপক, বাংলা সাহিত্যে তাঁর আগে বোধহয় আর কোনও নাম আসে না। কাঠামোগত ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে বাংলা কবিতা অনেকদিন আগে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু তার পরেও নিজের সঙ্গে যেভাবে পরীক্ষানিরিক্ষা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, যেভাবে নিজেকে বারবার ভেঙেছেন, তা অকল্পনীয়। একটা মানুষ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার দশ-পনেরো বছর পরে নিজেকে ভাঙছেন, অন্য রকম লেখার চেষ্টা করছেন। সত্তর-আশি-নব্বই বা আজকের দিনের ক'জন কবি সেই সাহস দেখাতে পারবেন, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। সাফল্যের চূড়ায় দাঁড়িয়ে নিজেরই নেওয়া পূর্বপথ নিজের হাতে ভেঙে নতুন পথ তৈরি করার সাহস, হাতে গোনা কবিদের ছিল বলেই মনে হয়। একজন কবি যেমন 'পুরাতন ভৃত্য' লিখছেন, তিনিই আবার 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' লিখছেন, সেই মানুষটাই আবার 'সোনার তরী' লিখছেন, কবিতার ক্ষেত্রেও এত রকম প্রকরণগত পরীক্ষানিরিক্ষা আর কেউ করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। বাংলা কবিতায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রবর্তনই হয় তাঁরই হাতে। রবীন্দ্রনাথ যে এখনও অবশ্যপাঠ্য, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। নীলাঞ্জন বলেন, ‘‘আসলে আমি আমার পূর্বজকে অনুকরণ করব না। কিন্তু পূর্বজকে বাদ দিয়ে আমার আসলে অস্তিত্বটাই নেই। ফলে পুরো পথটাকে না জেনে সাহিত্যচর্চা সম্ভব নয় একেবারেই।”
আজকের অন্যতম পরিচিত কবি তানিয়া চক্রবর্তী। তিনি মনে করেন, চারপাশের যা-ই বদলে যাক না কেন, আমাদের অনুভূতিস্তরগুলি তো বদলায়নি। তাই আজকাল রবীন্দ্রনাথের লেখার থেকেও তাঁর জীবন, তাঁর যাপনকে বোঝার চেষ্টা করেন কবি। তানিয়ার কথায়, ‘‘তাঁর সেই বিস্তারকে বোধহয় অস্বীকার করার জায়গা নেই। আজকের কাব্যভাষা বদলাতে পারে, প্রকরণের দিক দিয়ে কবিতা বদলে যেতে পারে। কিন্তু এই যে অনুভূতিমালা, তার তো কোনও বদল নেই। সবচেয়ে বড় কথা ররীন্দ্রনাথকে কোনও ধরাবাঁধা পরিকাঠামোয় আটকে রাখা কঠিন। এই সময়ে দাঁড়িয়ে যদি 'বৈশাখ' কবিতার কথা ধরা যায়, সেখানে একটি স্তবকে কবি বলছেন 'দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী', তার পরেই কবি বলছেন 'হে বৈরাগী, করো শান্তিপাঠ'। এই যে প্রকাশ ও সংবরণ, এই ব্যাপ্তিটাই আমাকে বারবার মুগ্ধ করে। বারবার মনে হয়, তাকে অস্বীকার করা যায় না, কারণ তিনি গোটা জীবনকে আচ্ছন্ন করে আছেন। অন্তরের গভীর থেকে গভীরতর জায়গায়, তার ছোটগল্প, তার গানগুলো আমায় সম্পৃক্ত করে ফেলে বারবার। তিনি তো সমস্ত কিছু প্রকাশ করেছেন। আবার সেই প্রকাশের যে বিপরীত পিঠ সংবরণ, তাকেও ধরছেন। কোথায় বাদ দেব তাঁকে! আসলে আমার মনে হয়, আমরা যাকে বাদ দিচ্ছি, সে-ও আমার ভিতরেই রয়েছে যাচ্ছে কোথাও। তাকে যদি অস্বীকার করতে হয় তাহলে তো কোথাও আমার জন্ম, আমার পূর্বপুরুষ- তাকেও অস্বীকার করতে হয়। আমার রক্ত, আমার দেহগঠনের ভিতরেই রয়েছে সেই অনুভূতিমালা। ওঁর যে ভাবদর্শন, তা এতটাই ব্যাপ্তিময়, যে কোনও অংশেই তাঁকে বাদ দেওয়া যায় না। শুধু তো কবিতা বা সাহিত্য নয়, তার সমস্ত জীবন, যাপন, বক্তৃতা, চিঠি, অভিনয়, সবেতেই তিনি চূড়ান্ত সংবেদী, চূড়ান্ত প্রকাশিত। ফলে তাঁকে শুধুমাত্র খুঁজতে হবে। আমার মনে হয়, তিনি সমস্ত ভাবকে ছুঁয়ে ফেলেছেন। যা অস্বীকার করার জায়গা নেই।”
আজকের দিনে যাঁরা কবিতা লিখছেন, চর্চা করছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম তন্ময় ভট্টাচার্য। তন্ময় জানান, ‘‘রবীন্দ্রনাথকে আসলে মানুষ দু'ভাবে দেখতে পারেন। প্রথম ভাগে পড়েন সাধারণ পাঠক। যিনি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি থেকে রসস্বাদন করবেন। অন্যদিকে যিনি কবিতাপ্রয়াসী, তিনি সবসময়ে রবীন্দ্রনাথকে অন্য চোখে অন্য ভাবে দেখার ও আবিষ্কার করার চেষ্টা করবেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায়, বাংলা ভাষার সবচেয়ে বড় স্রষ্টার নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তা আয়তনের দিক দিয়ে এবং অভিঘাতের দিক দিয়েও। রবীন্দ্রনাথ এমন একটা জায়গায় স্তম্ভ হিসেবে, একটা অক্ষ হিসেবে অবস্থান করছেন, যে তাঁর হিসেবে আমরা সাহিত্যের ইতিহাসে কবিতার যুগকে দুই ভাগে ভাগ করে নিই, একটা রবীন্দ্রপূর্ব, অন্যটা রবীন্দ্রোত্তর। এখন একজন কবিতাপ্রয়াসী রবীন্দ্রনাথকে পড়বেন কিনা, তা তাঁর নিজস্ব অভিরুচি। তবে আমি মনে করি অবশ্যই পড়া উচিত। রবীন্দ্রনাথকে পড়া মানে কিন্তু শুধু তাঁর কবিতা পড়া নয়। তাঁর গান, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, তাঁর চিঠিপত্র পড়া, তাঁর আঁকা এবং আঁকার পিছনে মনঃস্তত্বকে বোঝা। রবীন্দ্রনাথ একশো ষাট বছরে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছেন, তাঁকে পড়ার দরকার নেই, এ কথা সর্বৈব ভুল। তাঁর সময়ে দাঁড়িয়ে তাঁর ভাষা ছিল সমকালীন, আধুনিক। সেই ভাষার ভঙ্গিটা ফেলে এসেছি আমরা, কিন্তু দর্শন এবং ভাবনা তো পুরনো হয়নি। ফলে একজন তরুণ কবি অনায়াসে তাঁর দর্শন এবং ভাবনাটুকুকে শুষে নিতে পারেন। ভাষা বিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানের কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই রয়েছেন উত্তরাধিকার সূত্রে, বিবর্তনে। ঠিক যেমন ভাবে বিদ্যাপতি আছেন, চণ্ডীদাস আছেন, মুকুন্দরাম আছেন, তেমন ভাবেই রবীন্দ্রনাথও আছেন। আসলে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, ভারতচন্দ্র ছাড়া রবীন্দ্রনাথও তৈরি হতেন না। ঠিক তেমন ভাবেই পরবর্তীকালে যারা কবিতা লিখতে আসবেন, তাঁরা আরও বড় একটা কবিদের রেঞ্জ পাবেন। ফলে আজকের কবিদের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই আছেন। হয়তো সময়ের দূরত্বে তা স্পষ্ট না হয়ে ফিকে হয়েছে। কিন্তু আড়ালে তিনি ঠিকই আছেন। কারণ তিনি এমন একটা স্তম্ভ, যাঁকে ছাড়া বাংলা কবিতাকে ভাবা সম্ভব নয়।”
ছন্দের জাদু, অন্যতর বিষয় নির্বাচন এবং উজ্জ্বল বোধে পাঠকের চোখ টেনেছেন তরুণ কবি অভিরূপ মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে গিয়ে স্মৃতি হাতড়ে তিনি খুঁজে আনেন ছেলেবেলার দিন। কীভাবে তাঁর দাদামশাই তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিল রবীন্দ্রভুবনের এক আশ্চর্য গুপ্তধনরাশি। ইতিহাস ছাড়া যে বর্তমানকে রচনা করা যায় না, সেই বীজ প্রোথিত করে দিয়েছিলেন মাথায়। সেই থেকেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ অভিরূপের। সেই যাতায়াত আজও শেষ হয়নি তাঁর। রক্তকরবী থেকে বিশু পাগলের সংলাপের একটি অংশ তুলে আনেন অভিরূপ। যেখানে নন্দিনীকে বিশু বলে, "আমার সকাল কি তোর সকালের মতো যে, গান শুনতে পাব। এ-যে ক্লান্ত রাত্তিরটারই ঝেঁটিয়ে-ফেলা উচ্ছিষ্ট।" এই লাইনটার কাছে এসে থমকে দাঁড়ান কবি অভিরূপ। দীর্ঘ একাকিত্বের, বিষাদময় রাত্রির এই যে উপমা, তা লিখতে বোধহয় শুধু রবীন্দ্রনাথই পারেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে রবীন্দ্রনাথ 'নবজাতক' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ লিখছেন। সেখানে 'উদ্বোধন' নামক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন— 'বহু জনতার মাঝে অপূর্ব একা।' এই পঙক্তির কাছে এসে আশ্চর্য হন অভিরূপ। এই যে 'বহু জনতা'র ভারের পর 'মাঝে' শব্দটি লিখছেন তিনি,আর তার পরেই একাকিত্বটাকে বাড়িয়ে তুলছেন 'অপূর্ব' শব্দটি দিয়ে। এই সূক্ষ্ম, সাঙ্কেতিকতায় ভরা আশ্চর্য মায়ালোকই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ। অভিরূপের কথায়, এই যে বারবার রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাওয়া, এই যে আবিষ্কারের আনন্দ, এটাই বোধহয় সম্পদ। এই যে ভাণ্ডার সহজেই আমাদের জন্য খুলে রাখা আছে, যখনই বিপদে পড়ি, তখনই যেন সেই রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে নতুনত্বের হদিস পাই।”
আজকের দিনের আরেক কবি তৃষা চক্রবর্তী। তৃষা কিন্তু মনে করেন, আজকের কবিতা রবীন্দ্রনাথের কবিতার থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। ভাষার দিক থেকে, বোধের দিক থেকে। তবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর যে প্রতিপত্তি তাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তৃষার কথায়, ‘‘ধরা যাক, কোনও এক কবি রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাও পড়েননি। তা সত্ত্বেও তারা যদি অন্যান্য কবিদের লেখা পড়েন, তাঁরা আপনাআপনিই রবীন্দ্রনাথের ভাবনা, ভাষা, উপমা, সমস্ত কিছু ব্যবহারের যে একটা ফলাফল, তাকে ছুঁয়ে ফেলবেন। জীবনানন্দকে পড়লে মনে হয়, তিনি রবীন্দ্রনাথের থেকে অনেকখানি আলাদা। তবে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা এবং দর্শনের অনেকটাই হয়তো বিরোধীতায় বা সহাবস্থানে, নয়তো তর্ক করতে করতে তাদের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছে। যা চুঁইয়ে এসে ঢুকছে প্রতিনিয়ত আমাদের ভিতরেও। রবীন্দ্রনাথকে না ছুঁয়েও তার দর্শনের সঙ্গে সবসময় একটা কাউন্টার ঘটতেই থাকে আমাদের। কবিতা লেখার জন্য রবীন্দ্রনাথকে পড়ার দরকার বলে মনে হয়নি আমার কখনও। কিন্তু যেখানে রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে প্রয়োজনীয় যে কারণে, তা হল কবিতা লেখার ভিত। কখনও কখনও মনে হয় আমি যে কবিতা লিখছি, আমি কবিতার প্রতি কতটা সৎ, সমাজের প্রতি কতটা দায়বদ্ধ? এই যে চারপাশে এত অন্যায়, এত সামাজিক-রাজনৈতিক অবক্ষয়, সেখানে দাঁড়িয়ে কবিদের ভূমিকাটি ঠিক কী, এমন প্রশ্ন তো মাঝেমধ্যেই উঠে আসে। আজকাল অনেক সময়েই দেখা যায়, কোনও একজন কবি সমাজের কোনও একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলম ধরলে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, কেন অমুক সময়ে চুপ ছিলেন কবি? আসলে কবি তো যন্ত্র নয়। কোন বিষয় তাঁকে আলোড়িত করবে, কবিতাকে ঠেলে বের করে আনবে, তা বলে দেওয়া সম্ভব নয়। যে কোনও শিল্পচর্চা বা শিল্পী হয়ে ওঠা তো আসলে মানুষ হয়ে ওঠার একটা পথ। চারদিকে ঘটতে থাকা এই যে নিয়ত অন্যায়, অত্যাচার— তার প্রতিবাদ করতে না পারা, কাজের জায়গায় বঞ্চনা— সেখানে কথা বলতে না পারা। এই সমস্ত কিছুর পর যখন মনে হয়, আমি কি আর কবিতা লিখতে পারব, আদৌ কি লেখা উচিত? সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে বসি। প্রায় প্রতিবারই রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের গান শুশ্রূষার মতো কানের কাছে বলে যায়, 'দেখ্ রে চেয়ে আপন-পানে, পদ্মটি নাই'। এই যে নিজের কাছে সৎ থাকার জন্য অনুভূতির জারণ, নীতির পথে থাকার মধ্যেও যে একশো রকম প্রলোভন, সেখানে সাহস জোগান রবীন্দ্রনাথ, সাহস জোগান কবিতা লেখার।”

কবি সৌম্যজিৎ রজক জানিয়েছেন, বহু ব্যক্তিগত সঙ্কটেই তাঁকে স্বস্তি দেয় রবীন্দ্রনাথের লেখা, তাঁর গান, কবিতা। সৌম্যজিতের বক্তব্য, ‘‘আজকের দিনের ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে একটা তেত্রিশ-চৌত্রিশ বছরের যুবক হিসেবে রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত সঙ্কটে, সামাজিক বিভ্রান্তিতে রবীন্দ্রনাথের মতো করে কেউ সাহায্য করতে পারেন না আমাকে। বাংলা ভাষায়, বাঙালির বোধে, আমাদের রক্তে এমন ভাবে মিশে আছেন রবীন্দ্রনাথ, তাকে অস্বীকার করার জায়গা নেই। আসলে হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে যে মানুষ বাস করেছে, তাদের বোধ, তাদের জ্ঞান, তাদের সংস্কৃতি, তার প্রবাহমানতা এসেছে আমাদের জীবনে। সেই ধারাবাহিকতায় বিরাট মহিরুহ রবীন্দ্রনাথ। যার প্রভাব বিপুল, বিশাল, দু-কূলপ্লাবি, তিনি আছেন।”
আজকের কবি শাশ্বতী স্যান্যাল জানাচ্ছেন, রবীন্দ্রনাথকে আলাদা করে আত্মীকরণের প্রয়োজন নেই। কারণ রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভিতরে ঢুকে আছেন। গাছ যেভাবে মাটি থেকে জল শুষে নেয়, নাইট্রোজেনের ছোট ছোট দানা মাটি থেকে টেনে নেয়, ঠিক সেভাবেই। সাহিত্যের ভাষা থেকে কাঠামো, সব কিছুর জন্যই আমরা তাঁর কাছেই ঋণী। ফলে সরাসরি রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ বা অনুসরণের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। একই ভাবে আজকের সময়ে সেই প্রচেষ্টাটাও নেই বলেই মনে হয়। আজ আমরা যদি দু'পাতাও লিখে থাকি, সেই লেখার জন্যেও আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে ঋণী। তিনি স্বীকার-অস্বীকারের ঊর্ধ্বে।
তরুণ কবি পৃথ্বী বসু। তাঁর কথায়, ‘‘ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথকে এররকম ভাবে পড়েছি, বুঝেছি। এখন এই বয়সে এসে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ এমন একটা জানলা, যার কাছে দাঁড়ালে নানান দৃশ্য নতুন নতুন ভাবে দেখতে পাই। ছোটবেলায় যখন 'গোরা' পড়েছি, তখন প্রায় কিছুই বুঝিনি। এখন 'গোরা' পড়তে গিয়ে সম্পূর্ণ একটা নতুন বোধের কাছে গিয়ে দাঁড়াই। আমার মনে হয়, পাঁচ বছর পর যদি আবার 'গোরা' পড়তে বসি, তখন হয়তো আরও অন্য কিছু ধরা দেবে আমার কাছে। এখন এই যে রবীন্দ্রনাথের কাছে ফিরে ফিরে যাওয়ার দায়, সেই দায়টা আমার আছে কিনা সেটা প্রশ্ন। যদি সেই আগ্রহটা কেউ একবার পান, তাহলে আমার বিশ্বাস সে বারবার ফিরে যাবে রবীন্দ্রনাথের কাছে। এখন এই ইন্টারনেটের যুগে, হাতে হাতে ফোনের যুগে মনোযোগের অভাব একটা হচ্ছে, তা অস্বীকার করার জায়গা নেই। যা হয়তো এখনকার প্রজন্মের অনেককেই সেই ধৈর্যের জায়গাটাই তৈরি করতে দেয় না। কিন্তু কখনও না কখনও তো সেই ঘোলাজলটা থিতিয়ে যাবে। তখন যদি একবার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কাছে ফেরা যাক, তাহলে বোধহয় তাঁকে খুব একটা খালি হাতে ফিরতে হবে না। তবে এই ধৈর্যটা গড়ে তোলার জন্যও অভ্যাস প্রয়োজন। আসলে এখনকার সময়ে যে সাহিত্য, যে গান, যে সিনেমা মনোযোগ দাবি করে, তার থেকে ক্রমশ সরে আসছি আমরা। ভাষা তো বদলে যাওয়ারই। ফলে রবীন্দ্রনাথের ভাষার থেকে সরে এসেছে আজকের কবিতা, সাহিত্য। তবু যদি কষ্ট করে রবীন্দ্রনাথের ভাষাটাকেতে অতিক্রম করে তাঁর বোধের কাছে আমরা পৌঁছতে পারি, তাহলে রবীন্দ্রনাথের যে এই বিরাট বহুস্তরীয় সাহিত্যের জগৎ, তাকে ছোঁয়া অনেকটাই সহজ হবে।”
একশো ষাট বছর পেরিয়ে আসা বৃক্ষবৎ একটি মানুষ। যাঁকে ব্যক্তিগত শোক, যন্ত্রণা, বিচ্ছেদ এসে ছাড়খার করেছে বারংবার। অথচ কোন এক আশ্চর্য যাদুকাঠির ছোঁয়ায় সেই সমস্ত কিছুকে সোনা করে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ। সময়ের থেকে এগিয়ে ভেবেছেন, ভাবতে শিখিয়েছেন। কবিতার দেহ বদলেছে, তার অবয়ব, সৌষ্ঠব বদলেছে। কিন্তু তার আত্মা এখনও ছুঁয়ে রয়েছে সেই শাশ্বত কবিহৃদয়কে। এতগুলো বছর পেরিয়ে এসেও মানুষ আজও বিভ্রান্তির যুগে গিয়ে বসেন সেই বৃক্ষছায়ায়। কুড়িয়ে নেন জ্ঞানবৃক্ষের আপেল। এ দেশে আসলে সেই রবি কখনও অস্ত যায় না। কবি জয় গোস্বামী যথার্থই বলেন —
“সেই দেশ থেকে যেন দেখতে পাচ্ছি সমুদ্রের গর্ভ থেকে —সূর্যের দিকে জেগে উঠেছে—সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ। মৃত্যুর পর মৃত্যু পেরিয়ে যে বলতে পারে , আমি থাকবো। আমি বাঁচবো। রৌদ্রে বাদলে দিনে রাত্রে।
আমরা জানি , রবীন্দ্রনাথ চিরকালীন সেই গাছেরই মতো। যতদিন সভ্যতা থাকবে — থাকবেন রবীন্দ্রনাথ।”হৃদয়ে প্রেমের শীর্ষ/ জয় গোস্বামী




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp