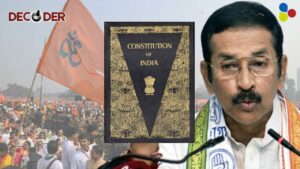বুদ্ধিজীবী কে?
সামাজিক বুদ্ধিজীবীকে বড় সংকটে নিস্পৃহ ভাবে, পূর্বপরম্পরা থেকে প্রমাণ তুলে এনে, নতুন ধারণাকে তার সঙ্গে জুড়ে, মানুষকে ভাবাতে হবে। কল্যাণের পক্ষে সওয়াল করতে হবে।
এই একটি প্রশ্ন আমাকে সবচেয়ে বেশি তাড়িয়ে মারে। প্রায় প্রতিদিন সামাজিক অন্যায়ের চাপে দিশেহারা মানুষ নাম তুলে তুলে বুদ্ধিজীবীদের খোঁজ করেন। সমাজমাধ্যমে বারবার, প্রায় রোজ একধরনের আস্থাহীনতার প্রকাশ, বুদ্ধিজীবীদের মেরুদণ্ডের দৃঢ়তা নিয়ে সাধারণ মানুষের প্রশ্ন আমাকে ভাবায়। আমি ভাবতে বসি, একদম গোড়ার কথা। বুদ্ধিজীবী কে? কাকে, কোন শর্তে আমি বুদ্ধিজীবী বলব? 'বুদ্ধিজীবী' ট্যাগটা বহনের জন্য একজন মানুষকে কোন কোন বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে? একজন বুদ্ধিজীবীর থেকে সাধারণ মানুষ কী প্রত্যাশা করেন? এই উত্তর অন্বেষণে আমি শুরুতেই কোনো নামকরা তাত্ত্বিকের উদ্ধৃতি ধার নেওয়ার সহজ রুটটায় পা ফেলতে চাই না। বরং নিজের সঙ্গেই সংলাপে জড়াতে চাই। তাতে দুটো সম্ভাবনা আছে। হয়তো পুরনো মদই নতুন বোতলে পরিবেশিত হবে। আবার, কে বলতে পারে, নতুন কোনো জানলার সন্ধান পেলেও পেতে পারি।
খুব সাধারণ ভাবে ভাবলে, বুদ্ধিকে যে জীবন বিশ্লেষণে কাজে লাগায় সেই বুদ্ধিজীবী। একজন অঙ্কবিদ বা একজন দাবাড়ু কাজের প্রতিটি ধাপে প্রবল বুদ্ধি খরচ করেন। ১৯৮৪-৮৫ সালে ক্যাসপারভ-কারপভ একটি ওয়ার্ল্ড চাম্পিয়নশিপ ম্যাচ খেলেছিলেন ১৫৯ দিন ধরে। মোট ৪৮টি গেম খেলতে হয়েছিল হারা জেতা নিশ্চিত করতে। পিয়েরি ফারমা-র অঙ্কের জটিল ধাঁধা সমাধান করতে ৩৫৮ বছর পাকদণ্ডী পথে ঘুরতে হয়েছে তাবড় অঙ্কবিদদের। কিন্তু দেখুন, এক্ষেত্রে জয় বা হার সবটাই ব্যক্তিগত। সামাজিক নয়। বরং যে বিজ্ঞানের আবিষ্কার জনজীবনে আলো আনছে, সেই উদ্ভাবনের পিছনে যারা ছিলেন বা আছেন, তারা একধরনের সামাজিক বুদ্ধিজীবিতা করছেন। ঠিক যেমন সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশে যারা নানা জ্ঞান চর্চা করছেন,মানুষকে রাজনৈতিক ঠিক ভুল সম্পর্কে সচেতন করছেন, নতুন চিন্তা সামনে আনছেন, প্রতিরোধের কৌশল শেখাচ্ছেন তারাও বুদ্ধিজীবিতায় শামিল।
অমোঘ প্রশ্নটা এখানেই আসে। যে চাষী মেঘের মন বোঝে, যে মিস্ত্রি দেওয়ালে গাঁথনি তোলে, যিনি সেলাই শেখান তিনি কি বুদ্ধি দিয়ে জীবন পরিচালনা করেন না? আলবাৎ করেন। কিন্তু মনে হয়, শ্রমিকের-কৃষকের মূল কাজ তার দায়িত্বে থাকা অংশে উৎপাদন সম্ভাবনা সুনিশ্চিত করা। একজন সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে দক্ষতা বিনিময় করা। সেইটুকু নিয়েই ভাববার সুযোগ পান তিনি। কায়িক শ্রমের বাড়বাড়ন্ত, দিনশেষের ক্লান্তি, একই জীবনচক্র তাকে এর বেশি ভাবতে দেয় না। তত্ত্বায়নের সুযোগ তার নেই। বুদ্ধিজীবীর তাহলে প্রাথমিক ভাবে রোজ শ্রমদানের বাধ্যতা খানিকটা হলেও কম। সেই কারণে তিনি সামাজিক বিষয়ে, শুধু একটি জীবন নয়, অনেক জীবন নিয়ে, নানা গোষ্ঠীর, পিছিয়ে পড়া মানুষের সমস্যা সংশয় নিয়ে নিরপেক্ষ ভাবে, দূরত্ব রেখে ভাবতে পারেন। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ-নীচুতলার বাসিন্দার তুলনায় অনেক বেশি করে সাংস্কৃতিক পরিসরে উপস্থিত থাকতে পারেন। নিজের চিন্তা প্রকাশ করতে পারেন মানুষের সামনে। মানুষ চায়, বুদ্ধিজীবী চিন্তার সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে সর্বদাই পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করবেন, যুক্তিবুদ্ধিকে সামনে রাখবেন, মিথ্যেকে পত্রপাঠ বিদায় করবেন, সত্যকে সমাজের সামনে তুলে ধরবেন তা সে যতই তেতো হোক। প্রকৃতপক্ষে, সমাজ-অর্থনীতির ধাঁচা, খেটেখাওয়া সাধারণ মানুষের পরিশ্রম-ঠাসা জীবন তাকে রোজের কাজ থেকে মুক্তি দিয়েছে। এই সুযোগ দিয়েছে। তাকে হাতে কোদাল নিতে হয়নি, খাবার ডেলিভারি করতে হয়নি, বদলে তিনি দু'দণ্ড চিন্তার অবকাশ পেয়েছেন। বলা যায়, তিনি জীবনের অর্থাৎ জনতার চিন্তাপ্রতিনিধি। আর সেই কারণেই তার উপর জনতার ভরসা। জনতা প্রত্যাশা করতে পারে, লোকটি নিঃশঙ্ক চিত্তে আমাদের জীবনভার লাঘব করবে। আরও একবার পরিষ্কার করে বলা দরকার, বিজ্ঞানে হোক বা শিল্পকলায়, একজন ব্যক্তি যখন নিজস্ব নৈপুণ্যে নিমজ্জমান, যখন তিনি সৃজনসমস্যার সঙ্গে ঘর করছেন, তার চিন্তা বা প্রকাশ যদি জনজীবন বিচ্ছিন্ন হয়, তবে তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী হলেও সামাজিক বুদ্ধিজীবী নন। সামাজিক বুদ্ধিজীবীকে বড় সংকটে নিস্পৃহ ভাবে, পূর্বপরম্পরা থেকে প্রমাণ তুলে এনে, নতুন ধারণাকে তার সঙ্গে জুড়ে, মানুষকে ভাবাতে হবে। জনকল্যাণের পক্ষে সওয়াল করতে হবে।
তাকে মানুষ নির্বাচন করে, বারবার পরীক্ষা করে। নানা সংকটে তার উপস্থিতি,বলা যাচাই করে। পরীক্ষায় বেশ কয়েকবার পাশ করতে হয়। যদি দেখা য়ায় বুদ্ধিজীবীর প্রতিক্রিয়া সমাজবদলের অনুঘটক হয়ে উঠছে, তখন একটা বড় অংশের মানুষ, যারা সেই বদলটা চাইছিল, তারা তাকে মনে আসন দেয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বুদ্ধিজীবী ভগবান নন। কারণ সকলে তার বিষয়ে নিঃসংশয় এমন ঘটনা ঘটে না। অন্ধ আনুগত্য তিনি চাইতেও পারেন না। গণতন্ত্রে মতপার্থক্য থাকবেই, ফলে বুদ্ধিজীবীর চিন্তাপদ্ধতিকে সবসময়েই চ্যালেঞ্জ করার কিছু লোক থাকবে। বুদ্ধিজীবীর কাজ, সেই বিরুদ্ধমত মেনেই নিরন্তর দায়বদ্ধতা বজায় রেখে সত্যের পক্ষে সওয়াল করা। তার নিজের মতটি তার মরণের পরেও প্রতিষ্ঠা পেতে পারে। এমনকী প্রতিষ্ঠা নাও পেতে পারে, কিন্তু তিনি তার চিন্তার প্রতি দায়বদ্ধ থাকবেন। খুব অল্প লোক তার মত বিশ্বাস করছে, এমন হতেই পারে। কিন্তু তিনি তার চিন্তাপদ্ধতির সঙ্গে নাছোড় সহবাস করবেন। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি এখানে কিছুতেই লক্ষ্য হতে পারে না। কাজেই, বুদ্ধিজীবীর পোশাক পরে, বুদ্ধিজীবীদের জন্য বরাদ্দ মঞ্চ ব্যবহার করে যিনি কোনো বক্তব্য রাখছেন, তাকেই বুদ্ধিজীবী ধরে নেওয়াটা একধরনের বোকামো, স্বার্থের বিষয়টি খতিয়ে দেখা উচিত। একজন বুদ্ধিজীবী তকমাধারী তখনই বুদ্ধিজীবী যখন তিনি স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশেই যা করছন তাতে সমাজকর্তৃক প্রযুক্ত উপাধির সঙ্গে সুবিচার হচ্ছে। দু'একটি চেনা উদাহরণ তুলে আনা যাক, ইতিহাস থেকে।
জালিয়ানওয়ালাবাহ হত্যাকাণ্ডের খবর রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন দেরি করে। কিন্তু খবর পেয়েই রবীন্দ্রনাথ গান্ধীকে সঙ্গে নিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগে পৌঁছতে চেয়েছিলেন। গান্ধী সেই প্রস্তাবে রাজি হননি। বলেছেন, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু এম্ব্যারাস দ্য গভর্নমেন্ট নাও। অর্থাৎ বুদ্ধিজীবী সমান মর্যাদায় আসীন কোনো ব্যক্তির সমর্থন পেল না। এবার সে কী করবে? রবীন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জন দাশের কাছে ছুটলেন। সেখানেও মতৈক্যে পৌঁছনো গেল না। অর্থাৎ ডাক শুনে কেউ এলো না। তা হলে এবার? রাতে তিনি পত্র লিখলেন ভাইসরয়কে। নাইটহুড ছাড়লেন। শুধু তাই নয়। পরের বছর ইংল্যান্ডে ভারত সচিব মন্টেগু-র সঙ্গে দেখা করে রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগের জন্য ক্ষমা চাওয়ার অনুরোধ করেন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে একজন বুদ্ধিজীবী কোনো অবস্থাতেই, কোনো প্রতিকূলতাতেই নিজের অবস্থান থেকে সরে আসছেন না। এবং সেই অবস্থানটা ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে জড়িত নয়, মানবিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। মনে রাখব রবীন্দ্রনাথের খেতাব ফেরানোর খবর জোড়াসাঁকো থেকেই নানা সংবাদমাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল। অর্থাৎ বুদ্ধিজীবী সংবাদমাধ্যমকে প্রত্যক্ষ ভাবে ব্যবহার করছেন। কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থে নয়, আমাকে দেখো নীতিতে নয়। সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলতে, সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষমতা সঞ্চার করতে। আনুকূল্যের আশা, রোষের ভয়- তাকে আটকাতে পারছে না।
১৯২৩ সালের ১৭ জানুয়ারি থেকে নজরুল ইসলামের জেলজীবন শুরু হয়। প্রথমে নজরুলকে প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারপর তাঁকে আলিপুর কারাগারে রাখা হয়। তাঁকে বিশেষ শ্রেণির বন্দির মর্যদা দেওয়া হয়েছিল। কয়েদিদের পোশাক পড়তে হতো না। খাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল সবিশেষ। এই সময় ওই জেলে ছিলেন মাওলানা আকরাম খাঁ , বাদশা মিঞা, চাঁদ মিঞা, শামসুদ্দিন-রা। নজরুল বিভিন্ন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে বেড়াতেন। বিকেলের দিকে অন্যান্য রাজবন্দীদের সাথে গানে গল্পে হইহুল্লোড়ে সময় কাটাতেন। কিন্তু প্রকৃত বন্দিজীবন যে এমন নয়, যুবক নজরুল বুঝলেন হুগলি জেলে এসে। চূড়ান্ত অব্যবস্থা, সহবন্দিদের নির্যাতনে তিতিবিরক্ত নজরুল ১৫ এপ্রিল অনশন ঘোষণা করলেন। জেল কর্তৃপক্ষ ৮ই মে (মঙ্গলবার, ২৫শে বৈশাখ ১৩৩০) নজরুলের নাকে নল ঢুকিয়ে খাওয়ানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। নজরুলের মৃত্যুর আশঙ্কায় ২১ মে কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আইনজীবীরা কলেজ স্কোয়ারে একটি জনসভা করে। এই সভায় নজরুলের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বেসরকারি জেল পরিদর্শক ডা. আব্দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দিকে নজরুলের অনশন ভঙ্গের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২২ মে সোহারাওয়ার্দি হুগলি জেলে যান। বন্দিদের উপর সদয় আচরণ করার শর্তে নজরুল অনশন ভঙ্গ করার জন্য অনুরোধ করেন। ২৩ মে, ৩৯ দিনের মাথায়, বিরজাসুন্দরী জেলে যান। নজরুল অনশন ভাঙেন। এরপর হুগলি জেল কর্তৃপক্ষ বন্দিদের প্রতি সদয় আচরণ করা শুরু করে। দেখা গেল, বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিস্বার্থে নয়, জনস্বার্থে লড়লেন। প্রতিপক্ষের শক্তি সহস্রগুণ বেশি হওয়া সত্ত্বেও টললেন না। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালালেন। বাজি রাখলেন নিজের সবচেয়ে বড় সম্পদ-স্বাস্থ্য। যার মাশুল তাকে পরে দিতে হবে।
জেলজীবনের শুরুতে নজরুলের লেখা ধূমকেতুর শেষ সম্পাদকীয় রাজবন্দির জবানবন্দি বুদ্ধিজীবিতার একটি ম্যানিফেস্টো হতে পারে। নজরুল লিখছেন,
আমি কবি, অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তি দানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সে বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায়বিচারে সে বাণী ন্যায়-দ্রোহী নয়, সত্য-দ্রোহী নয়। সে বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের দুয়ারে তাহা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান, অনির্বাণ, সত্য-স্বরূপ।
সত্য স্বয়ং প্রকাশ। তাহাকে কোনো রক্ত-আঁখি রাজদণ্ড নিরোধ করতে পারে না। আমি সেই চিরন্তন স্বয়ম্-প্রকাশের বীণা, যে বীণায় চির-সত্যের বাণী ধ্বনিত হয়েছিল।
অর্থাৎ, সত্যপ্রকাশের তাড়না থেকে একজন বুদ্ধিজীবীকে কখনও কোনো শক্তি সরিয়ে আনতে পারবে না। সত্যের আধার একজন বুদ্ধিজীবী। এখানেই প্রশ্ন। যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মুখোমুখি লড়ছেন বুদ্ধিজীবী, তার সঙ্গে কেমন সম্পর্ক হবে প্রতিষ্ঠানের? প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কি তিনি কখনও সুসম্পর্কে যাবেন? উত্তরে আরও একটি উদাহরণ সামনে আনা যাক।
১৯১৫-য় শান্তিনিকেতনে ছোটলাট লর্ড কারমাইকেলের আগমন ঘটে। শিল্পরসিক লাটসাহেবকে আম্রকুঞ্জে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে গিয়েছিলেন ছাতিমতলার বেদিতে। সেখানে কবির বক্তৃতা শুরু হওয়ার কিছু ক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল বিভিন্ন জেলে বাংলার রাজনৈতিক বন্দিদের ওপর ঘটে চলা অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ করছেন তিনি। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান-রাজশক্তি দেখলেই বুদ্ধিজীবী তেড়ে যাবেন এমন নয়, কিন্তু প্রতিষ্ঠান তাকে সত্যচুত করবে না, অবস্থানচ্যুত করবে না, তিনি প্রতিষ্ঠানের ভয়ে চুপ থাকবেন না। যে কথাগুলি বলার, তা বলবেনই। নেতামন্ত্রীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক হবে পারস্পরিক সম্মানের, প্রভু-ভৃত্যের নয়। একজন বুদ্ধিজীবী প্রতিষ্ঠানের থেকে সুবিধেও নিতে পারেন। তা বৃত্তি হোক, সংস্থার জন্য চাঁদা হোক বা সাম্মানিক-পুরস্কারপ্রদান। কিন্তু দেখতে হবে তা তার কণ্ঠস্বর রোধ করছে কিনা। যদি তাকে চুপ করে যেতে হয়, ভেবে কথা বলতে হয়, বুঝতে হবে প্রতিষ্ঠান তাকে পুরস্কৃত করেনি, সম্মানিত করেনি, কিনতে চেয়েছে। এবং তিনি চেয়ে বা না চেয়ে, ইচ্ছে করে বা অসহায়তায় সেটা মেনে নিয়েছেন। মেনে নেওয়ার অর্থ, বুদ্ধিজীবীর তকমা হারানো। অর্থাৎ এই সময়ে, কেন ওই ব্যক্তি নির্দিষ্ট বিষয়ে চুপ, এই প্রশ্ন না করে, যাচাই করা উচিত সেই ব্যক্তি কি গণবুদ্ধিজীবী হওয়ার জায়গায় রয়েছেন? সেই ব্যক্তি হয়তো তখনও তার নানা দক্ষতা ধরে রেখেছন, ভালো আঁকছেন, ভালো লিখছেন, কিন্তু গণবুদ্ধিজীবী হিসেবে খ্যাত হওয়ার অধিকার তিনি হারিয়েছেন।
আসলে বুদ্ধিজীবিতা একধরনের চলিষ্ণুতা। আর এই প্রতিষ্ঠানের ভয়ে চুপ করে যাওয়াটা একটা স্থিতাবস্থা। এই দুয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ বিরোধ রয়েছে। একজন বুদ্ধিজীবী সর্বদা ভাববেন, সত্য ছাড়া তার আর হারানোর কিছুই নেই। সত্যকে আগলে রাখতেই তার পথ চলা। তার কথায় কোনো পক্ষপাত থাকবে না, কোনো ভয় থাকবে না, কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। কিন্তু আরও একটি প্রশ্ন আছে। এই অবস্থায় কি সারাজীবন থাকা সম্ভব? যদি প্রত্যক্ষ আঘাতে, ভয়ে, অনেক হারিয়ে, একটু থিতু হওয়ার আশায় কেউ সরে দাঁড়ায় তা কি অপরাধ? ১৯২০ থেকে ১৯৩০ এই পর্বে নজরুলের পাঁচটি বই নিষিদ্ধ হয়েছে। যুগবাণী, বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, প্রলয়শিখা, চন্দ্রবিন্দু। তাছাড়াও সংস্করণ জব্দ হয়েছে ফণিমনসা, সর্বহারা, রুদ্রমঙ্গল, সঞ্চিতার। আর কোনো ভারতীয় কবিকে এই সময়তটে এই দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়েছে কি? ব্যক্তিগত দুর্ভোগও কম ছিল না নজরুলের। দুই পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। স্ত্রী পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছেন। জেলে যেতে হয়েছে। সব হারিয়ে তিনি যদি প্রত্যক্ষ বিপ্লব থেকে সরে জীবনে থিতু হতে চান তা কি অন্যায়? দেখা যাচ্ছে, পরের দশকে গানের মধ্যে দিয়ে তিনি তুলে আনছেন সমাজের অন্তঃপুরবাসিনীদের। সেও এক গণবুদ্ধিজীবিতায় পরোক্ষ অংশগ্রহণ। বিশেষ আর্থসামাজিক ভাবনার সফলতম প্রয়োগ। কিন্তু যদি তিনি সে পথেও না হাঁটতেন, কেবল বিনোদনের জন্যে গান লিখে অর্থ উপার্জন করতেন? আজ যদি উমর খলিদ এই অনন্ত দুর্ভোগের পর জেল থেকে বেরিয়ে আর প্রত্যক্ষ ভাবে শাসকের সঙ্গে সওয়ালজবাবে অংশ নিতে না চায়? তাহলে কি তিনি অপরাধী? যিনি সাম্প্রতিক অতীতে শাসকের সঙ্গে বিরোধিতায় জড়িয়েছেন, কিন্তু আজ আর জড়াতে চাইছেন না, ক্লান্ত বোধ করছেন, থিতু হতে চাইছেন, তিনি কি অপরাধ করছেন? তাহলে বুদ্ধিজীবীর জন্যে মাত্র দুটো পথ খোলা, হয় করো নয় মরো। এটাও কি সামাজিক স্বার্থপরতা নয়? আমার ঘানি পরকে দিয়ে টানানোর অভিপ্রায় নয়?
আমার মনে হয়, সরে দাঁড়ানোর অধিকার সব মানুষের আছে। বুদ্ধিজীবিতায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ একটি চয়েজ। কোনো চাপিয়ে দেওয়া শর্ত নয়। অসহায়তার জায়গা থেকে কেউ সরে দাঁড়াতে পারেন। সেই সরে দাঁড়ানো দেখতে হবে মানবিক ভাবেই। আর দশজন ব্যক্তি সরে দাঁড়ালে বৌদ্ধিকচর্চার মূলগত কোনো ক্ষতি হয় না কারণ তা অপরিমেয়, অফুরান, চলিষ্ণু একটি মশাল। এক হাত থেকে অন্য হাতে গিয়ে সে অনেকটা জায়গা জুড়ে আলো সঞ্চার করে। যিনি সরে দাঁড়াচ্ছেন, তার জন্যে মশাল নিভবে কেন? তবে হ্যাঁ, সরে দাঁড়িয়েছি, বুদ্ধিজীবির তকমা বহনে আমি রাজি নই, বরং আমি একজন সমাজমানুষ যার একটি অতীত রয়েছে, জ্ঞানচর্চার সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে, কিছু স্বতন্ত্র ভাবনা রয়েছে, এই বোধে পৌঁছনো, অন্তত এই সত্যটুকু জানান দেওয়ার সৎসাহসও একজন প্রাক্তন বুদ্ধিজীবীর থাকা উচিত। এই বিষয়ে কোনো আত্মশ্লাঘা তার থাকবে না, এমনটাই বাঞ্ছনীয়।
শেষ করব একটি প্রশ্ন দিয়ে। শুরু করেছিলাম কারা সক্রিয় গণবুদ্ধিজীবিতায় অংশ্রগ্রহণ করতে পারেন না সে কথা দিয়ে। কিন্তু সমাজমাধ্যমে যারা নিয়মিত বুদ্ধিজীবীরা কোথায় বলে চেঁচান, তাদের বেশির ভাগেরই অবস্থা ততটা প্রতিকূল নয়। তাদের সময় আছে। পকেটে অর্থ আছে। নিশ্চিন্তের চাকরি আছে। এমন অবস্থা থেকে সমাজমাধ্যমে বুদ্ধিজীবীরা কোথায় বলে চেঁচানোটা বিশুদ্ধ ধান্দাবাজি নয় কি? তিনি নিজে পথে নামছেন না কেন? কে আটকাচ্ছে তাকে? চাকরি হারানোর ভয়? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তা়ড়ানোর ব্যাপারে অনীহা? আরাম? আমার পতাকা আমি কেন বহন করব না? তাহলে যে প্রাক্তন বুদ্ধিজীবীকে তিনি কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে গালাগাল করছেন, তার সঙ্গে নিজের মূলগত প্রভেদটা কোথায়? দু'জনেই তো দিনশেষ নিরাপত্তাবিলাসী। প্রাক্তন বুদ্ধিজীবীর তো তাও একটা অতীত আছে, সুবিধেবাদী ফেসবুক টিপ্পনীবাজের কি তা-ও আছে? অন্যেকে দাগিয়ে দেওয়ার আগে হেঁটে দেখি না কিছুটা পথ, পায়ে কিছু কাঁটা ফুটুক না? অন্যের দিকে একটি আঙুল তুললে অন্তত তিনটি আঙুল থাকে নিজের দিকে ফেরানো। সে দিকে না তাকানোটাই আমাদের চরিত্র।




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp