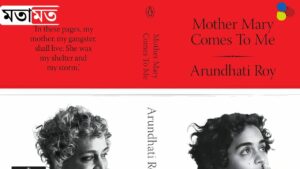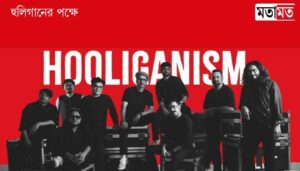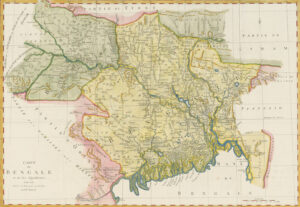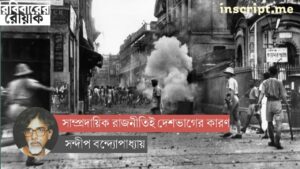অস্বস্তিকর, শ্বাসরোধী! কেন এই সময়ের সবচেয়ে জরুরি সিরিজ হয়ে উঠল অ্যাডোলেসেন্স?
Adolescence Review: ফিলিপ বারান্তিনি-নির্দেশিত এই সিরিজের চারটি পর্বই ওয়ান টেকে নেওয়া। অর্থাৎ, একটিই মাত্র শটে শুরু থেকে শেষ অবধি দেখানো হয়েছে, মাঝে কোনও কাট নেই।
বয়ঃসন্ধিকাল, যাকে ইংরেজিতে বলে অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ড— সে যে কী টালমাটাল আর দুর্বার এক পর্যায়, সে আমরা প্রায় সকলেই জানি, যারা বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে এসেছি কিছু বা বহুকাল আগে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার চৌকাঠে পা রেখে দুনিয়ার তাবৎ নিয়মকানুনকে নস্যাৎ করার আগুন জ্বলে বুকে, তাতে মরণঝাঁপ দেওয়ার চাড় সংবরণ করা মুশকিল।
আমি মনস্তত্ত্বের ছাত্র নই। বস্তুত, মনস্তত্ত্ব নিয়ে যে আমার বিপুল পড়াশোনা-জানা-বোঝা রয়েছে, তাও নয়। আমি যে বিষয় নিয়ে লেখাপড়া করেছি, সেই সোশিওলজিতে ঘটনাচক্রে জুভেনাইল ডেলিঙ্কুয়েন্সি বলে একটা বিষয় পড়তে হয়। সহজ ভাষায়, অ-প্রাপ্তবয়স্ক-কৃত এমন কোনও আচরণ, যা লিখিত আইনের পরিপন্থী। তাতে দেখা যাচ্ছে, সামাজিক-অর্থনৈতিক বিভিন্ন ঘটনা বয়ঃসন্ধিতে পা দেওয়া একজন একককে সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত করে। তার চারপাশের দুনিয়ায় যা ঘটছে, যাদের বৃত্তে সে রয়েছে— সেসব তার চেতন, অবচেতনকে গড়েপিটে নেয়— এ এক অনিবার্য সারসত্যি।
এত ভণিতার কারণ সহজ। সম্প্রতি নেটফ্লিক্স-এ মুক্তি পেয়েছে চার-পর্বের মিনি-সিরিজ ‘অ্যাডোলেসেন্স’। তেরো বছর বয়সি জেমি মিলার তার সহপাঠিনী কেটিকে নৃশংসভাবে খুন করার দায়ে অভিযুক্ত হয়; সেই অভিযোগ, তার গতিপ্রকৃতি নিয়েই এই চার-পর্বের সিরিজ। ব্রিটেনের স্কুলগুলির পাঠ্যক্রমে সেই সিরিজটি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে— এতই জোরালো এই সিরিজের অভিঘাত। জেমি মিলারকে দোষী ঠাউরে দেওয়া সহজ। কিন্তু, কোন ধরনের মানসিকতা থেকে সে তেরো বছর বয়সেই হাতে ছুরি নিয়ে সহপাঠিনীকে আক্রমণ করে খুন করার সিদ্ধান্তটি নিল? কোন হিমশীতল স্নায়ুর বশে সে ভিডিও টেপ দেখার আগে অবধি ক্রমাগত নাকচ করতে লাগল তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ? একে তো কেবলমাত্র ব্যক্তিগত পরিসরে আবদ্ধ রাখলে চলবে না। খতিয়ে, ভেবে দেখতে হবে তার বেড়ে ওঠার সময়টুকু, বুঝতে হবে তার চারপাশের অবস্থা, শিখতে হবে জেমির প্রজন্মের লব্জ, চিনতে হবে এই শ্রেণিটির মন। সিরিজটি তাই-ই করে।

জেমি মিলার এক আশ্চর্য উগ্র পৌরুষের বীজ বুকে নিয়ে বেঁচে আছে, অথচ, সেই বিষবৃক্ষ সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। নারীশরীরকে সে এক পণ্য ব্যতীত আর কিছু ভাবে না। এই বিষাক্ত ডিজিটাল দুনিয়ায়; যখন সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সাররা সযত্নে কানে বিষ ঢেলে দিচ্ছে, সে বোঝে না আদপে কী বারুদের স্তুপ সে মস্তিষ্কে লালন করছে। যখন ডি আই ব্যাসকোম্বকে তার পুত্র অ্যাডাম ধরে ধরে বোঝায়, প্রতিটি ইমোজির আছে নিজস্ব অর্থ; হৃদয়ের ইমোজির রঙ পাল্টে গেলে পাল্টে যায় প্রেরকের অভিসন্ধি— তখন ধাক্কা লাগে। যে মঞ্চ তৈরি হয়েছিল মানুষের সঙ্গে মানুষকে জুড়ে দেওয়ার জন্য, সেই মঞ্চেই মানুষ মানুষের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে অমোচনীয় ঘৃণা, অবিশ্বাস্য বিদ্বেষ! এই সিরিজকে যে সমসময়ের অন্যতম জরুরি সিরিজ বলে অভিহিত করা হচ্ছে, তার মধ্যে আশ্চর্যের কিচ্ছু নেই। তৃতীয় পর্বে যখন জেমি মিলাররূপী ওয়েন কুপার আর তার কাউন্সেলিং করতে আসা ব্রায়নির চরিত্রে অভিনয় করা এরিন ডোহার্টির একটি কথোপকথন হচ্ছে, তা বিস্ফোরক তর্কের রূপ নিচ্ছে ক্রমেই; ওই পর্বটির রেশ থেকে যায় বহুক্ষণ। মিলারের মস্তিষ্কে বইতে থাকা উগ্রতার চোরাস্রোতটি বেরিয়ে আসে সামনে। ব্রায়নির স্তব্ধতাই আসলে দর্শকের প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন। স্তব্ধতা! সেইটিই আসল শব্দ। স্তব্ধ হওয়া ছাড়া ওই দৃশ্যে আর কিছু করার থাকে না।

আরও পড়ুন- সিনেমায় বেনীআসহকলা-য় স্নান সেরে ওঠে যেসব শ্রেষ্ঠ দৃশ্যগুলি
ফিলিপ বারান্তিনি-নির্দেশিত এই সিরিজের চারটি পর্বই ওয়ান টেকে নেওয়া। অর্থাৎ, একটিই মাত্র শটে শুরু থেকে শেষ অবধি দেখানো হয়েছে, মাঝে কোনও কাট নেই। নিঃসন্দেহে তুখোড় প্রস্তুতি, নিবিড় পরিশ্রম আর অতুলনীয় যত্ন না থাকলে এই ট্রিটমেন্টে কাজ করা অসম্ভব। সিনেমাটোগ্রাফার ম্যাথিউ লিউইস অসম্ভব যত্ন নিয়ে প্রতিটি ফ্রেম তৈরি করেছেন। কাটের মাধ্যমে তো গল্প বলার গতি বেড়ে যায়। বা, গল্পের নির্মেদ অংশগুলিকে বাদ দেওয়া হয়ে থাকে। কখনও কখনও দু’টি বা ততোধিক শট জোড়ার কায়দাতেই বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক স্তর তৈরি করা যায়। সেই পরিসর এই সিরিজে ছিল না। একটানা, নিরবচ্ছিন্নভাবে চরিত্রের সঙ্গে থাকতে হয়েছে দর্শককে। কখনও কখনও দমবন্ধ হয়ে এসেছে। কাটের তৃষ্ণা এসেছে। মনে হয়, পুরো ঘটনাটা ঘটছে দর্শকের চোখের সামনে; দর্শক আসলে চেয়ার টেনে বসে আছে জেমির জেরার ঘরে; গাড়ির মধ্যে; পায়রার খোপের মতো জেমিদের রান্নাঘরে। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। এই দমবন্ধ করা পরিবেশ থেকে তাকে মুক্তি দিতে পারত ‘কাট’। দৃশ্যান্তর। তা নির্মাতারা দেন না। বোঝান, এই সিরিজ 'পজ' করে হয়তো কেউ থামিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু যে বাস্তব এই সিরিজে উঠে এসেছে, তার গতি রুদ্ধ করা আমাদের একার পক্ষে সম্ভব নয়। সিরিজের ক্ষেত্রে সেই এজেন্সি দর্শকের হাতে থাকলেও, সমাজের স্রোত থামাবার উপকরণ নাগরিকের হাতে নেই। এই করাল বাস্তবের সম্মুখীন হতেই হবে। আর সেই উপলব্ধি, সেই রেভেলেশন আমাদের চুপ করিয়ে রাখবে ব্রায়নির মতো, ডি আই ব্যাসকোম্বের মতো।

এই সিরিজের আবিষ্কার নিঃসন্দেহে ওয়েন কুপার। বয়স মাত্র তেরো বছর বটে, কিন্তু সে যে অভিনয়টা করেছে এই সিরিজে— তা অতুলনীয়। সময়ে সময়ে তাকে অসম্ভব ভয়াল, মারমুখী মনে হয়; বয়ঃসন্ধির ছেলের মধ্যে সমস্ত কিছু ভেঙে ফেলার যে চরমপন্থী প্রবৃত্তি থাকে, সেই ভাঙনের সম্ভাবনা সারাক্ষণ লেগে থাকে তার চোখেমুখে। এরিন ডোহার্টি, জেমির বাবার চরিত্রে স্টিফেন গ্রাহাম— প্রত্যেকেই এই সিরিজে অনবদ্য।
জেমি মিলার নিজেকে ‘আগলি’ মনে করে। চায়, সে সেই কথা উচ্চারণ করলে উল্টোদিকের মানুষটা তাকে সঙ্গে সঙ্গে 'ভ্যালিডেশন' দিক। বলুক, ‘না তো, তুমি তোমার মতো সুন্দর’ জাতীয় মন-ভজানো কথা। সে অম্লানবদনে ঘোষণা করে, সে চাইলেই একটা নারীশরীরকে স্পর্শ করতে পারত, কিন্তু করেনি— এ-ই কি তার যথেষ্ট উদারতার পরিচয় নয়? বুলিড হতে হতে, উগ্র পৌরুষের, ভ্রান্ত বিশ্ববীক্ষার বীজ বুকে নিয়ে সে যে কখন একটি অপরাধীতে পরিণত হয়েছে, টের পায়নি নিজে, টের পাননি তার অভিভাবকরাও। সে কারণেই সবটুকু খোলসা হওয়ার পর জেমির বাবা-মা ভেঙে পড়েন কান্নায়; অস্ফূটে উচ্চারণ করেন: আমরা চাইলে কি আরেকটু দায়িত্ব নিতে পারতাম, চাইলে কি জেমিকে আরেকটু যত্ন নিয়ে মানুষ করতে পারতাম?

আরও পড়ুন- বর্ষশেষের সেরা ২০২৪: কোন কোন সিনেমা-সিরিজ ভাবাল গোটা বছরে?
উত্তর আসে না। সিরিজ শেষ হয়। কানে লেগে থাকে দ্বিতীয় পর্ব সমাপনের সময়ে বাজতে থাকা গান ‘ফ্র্যাজাইল’। শোনা যায়, হিংসা কখনই শেষ কথা হতে পারে না। আমরা ফোন স্ক্রোল করতে থাকি সেই গানটুকু ব্লুটুথ ইয়ারফোনে নিয়েই। দেখি, একের পর এক ভিনধর্ম, ভিন জাত, অন্য লিঙ্গ, অন্য দেশকে নিয়ে লাগাতার আক্রমণাত্মক পোস্ট, ছবি, মীম। দেখি, বোমার আঘাতে ভেঙে গেল হাসপাতাল। দেখি, কমেন্টে কমেন্টে গালিগালাজের বন্যা, আক্রমণের ঢল। দেখি, শস্যের ফলনে উত্থান-পতন এলেও ঘৃণার চাষে বিন্দুমাত্র লাগাম পড়ছে না। প্রতিটি দেশই একে অপরের সঙ্গে তুমুল টেক্কা দিচ্ছে। আর, এর আঁচ এসে পড়ছে পরের প্রজন্মের গায়ে। তাদের হাতে মোবাইল। তাদের কানে বিষ ঢালছে কত যে ‘সোশাল ইনফ্লুয়েন্সার’! তারা জানছে, মতে না মিললে অন্য মানুষকে কুপিয়ে দেওয়া যায়। তারা শিখছে, না পাওয়া গেলে কেড়ে আদায় করতে হয়। তারা মানছে, প্রত্যাখ্যাত হলে অস্ত্র অথবা অ্যাসিড তুলে নিতে হয়।
আমরা এসব দেখে ফোন বন্ধ করে দিচ্ছি। ইস্কুলে যা হচ্ছে, ওসব ইস্কুল বুঝবে— এই ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছি। ক্রমশ দূরত্ব বাড়ছে মানুষের থেকে মানুষের। আর, ঝড়টা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে ক্রমশ। ধীর পায়ে। কিন্তু, নিশ্চিত পদক্ষেপে। একটা সময়ে আছড়ে পড়বে আমাদের ওপরই, তখন আর আমাদের কাছে বাস্তবেও পালানোর উপায় থাকবে না। ঠিক যেভাবে সিরিজে দমবন্ধ হয়ে আসতে আমরা ‘কাট’ খুঁজেছিলাম, ওয়ান শট ক্রমশ ফাঁসি হয়ে বসেছিল আমাদের গলায়; তেমন বিষের বজ্রমুষ্টি আমাদের গলা অবধি পৌঁছে গেল বলে।
‘অ্যাডোলেসেন্স’ সেই অস্বস্তিকর, শ্বাসরোধী, অসংবেদনশীল যুগটির একটা ছোট্ট রিমাইন্ডার।




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp