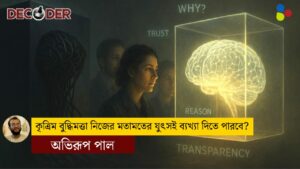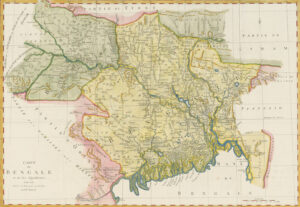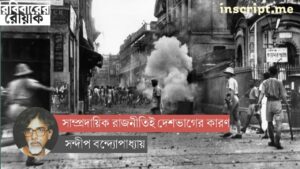উপচে পড়ছে জিবলি ছবি! শিল্পীর আসল শৈলী নকল করে শাস্তি পাবে AI?
Studio Ghibli AI Art:মিয়াজাকি বা স্টুডিও জিবলি কখনও AI-কে তাঁদের শৈলী ব্যবহারের অনুমতি দেননি। তবুও ব্যবহারকারীরা অনায়াসে জিবলির মতো ছবি তৈরি করতে পারছেন।
সম্প্রতি একটি বিতর্ক সোশ্যাল মিডিয়াকে শশব্যস্ত করে রেখেছে। OpenAI তাদের ব্যবহারকারীদের Studio Ghibli-র স্টাইলে ঢালাও ছবি তৈরি করার সুবিধা দিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই অজস্র 'অ্যানিমেশন'! অভিযোগ, Ghibli-র অনন্য শৈলীকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) মাধ্যমে অনুকরণ করা আসলে হায়াও মিয়াজাকি (Hayao Miyazaki) ও তাঁর টিমের উত্তরাধিকারকে অসম্মান করা। অ্যানিমেশনের এই শৈলী নিয়ে উদ্বেগ অমূলক নয়। জিবলি স্টাইল মানে শুধু বড় চোখ, নরম আলো আর ফ্যান্টাসি দৃশ্য নয়— এটি একজন মানুষের জীবনদর্শন ও অভিজ্ঞতা, তাঁর সারা জীবনের পরিশ্রমের ফসল। মিয়াজাকির প্রতিটি সিনেমায় রয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ভয়-যন্ত্রণা, শান্তিবাদী আদর্শ, প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা এবং মানবিক সংবেদনশীলতা। ফলে, AI শুধুমাত্র বাহ্যিক শৈলী অনুকরণ করে সেই শিল্পের প্রাসঙ্গিকতা বা গভীরতা ধারণ করতে পারে না।
Ghibli-র শিল্পীরা প্রতিটি ফ্রেম হাতে আঁকেন। সোশ্যাল মিডিয়া সূত্রেই জানা যাচ্ছে, দ্য উইন্ড রাইজেস (২০১৩) সিনেমার একটি চার সেকেন্ডের ভিড়ের দৃশ্য তৈরি করতে এক বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল। এই নিরলস পরিশ্রম, নিখুঁত দৃশ্যায়ন— AI যদি কয়েক সেকেন্ডে অনুরূপ ছবি তৈরি করে ফেলে, অনেকের কাছে সেটি একটি অবমাননা। তাঁদের মতে, এই অনুকরণশীলতা আসল শিল্পের রক্ত-ঘাম-উদ্যমের প্রতি অবহেলা।
কিছু নৈতিক প্রশ্নও উঠছে। মিয়াজাকি বা স্টুডিও জিবলি কখনও AI-কে তাঁদের শৈলী ব্যবহারের অনুমতি দেননি। তবুও ব্যবহারকারীরা অনায়াসে জিবলি-র মতো ছবি তৈরি করতে পারছেন। প্রশ্ন ওঠে, একটি সংস্থা (বা ব্যবহারকারী) কি কোনও শিল্পীর কাজ থেকে বিনামূল্যে উপকৃত হতে পারে? প্রকৃত শিল্পী কোনও স্বীকৃতি বা লাভ পাচ্ছেন না। অনেকেই বলছেন, OpenAI-এর উচিত ছিল স্টুডিও জিবলি-র অনুমতি নেওয়া। নতুন প্রযুক্তির জন্য নতুন নৈতিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তাও প্রকট হয়ে উঠছে।

হায়াও মিয়াজাকি
AI আমাদের জীবনে নানা ধরনের সুবিধা এনে দিচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের কর্মক্ষেত্র ও দৈনন্দিন জীবনে এর ব্যবহার একপ্রকার স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু স্টুডিও জিবলি ঘিরে শিল্প আর AI-এর সাম্প্রতিক এই দ্বন্দ্বে থমকে দাঁড়াতেই হয়। শিল্প নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আমার নেই, আছে কৌতূহল এবং বোঝার-শেখার-জানার ভালো লাগা থেকেই তার জন্ম। জীবনের বিভিন্ন বিপন্নতায় আশ্রয় পাওয়া গেছে শিল্পে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে শিখিয়েছে, অনেক সংকীর্ণতা, মানসিক দ্বন্দ্বে স্থিরতা দিয়েছে শিল্প। সেই প্রেক্ষিতেই মনে হয়, এই বিতর্ক শুধু প্রযুক্তির ব্যাপার নয়। ছায়ার মতো উঠে আসছে কিছু মৌলিক প্রশ্নও।
AI-এর মাধ্যমে তৈরি শিল্প কতটা গ্রহণযোগ্য?
শিল্পে AI-এর ব্যবহার কি ন্যায্য?
এর নৈতিক ভিত্তি কোথায়?
আরও পড়ুন-AI ২০২৪: কতদূর এগোল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা?
এই প্রসঙ্গে সবার আগে বোঝা দরকার, AI যখন কিছু নির্মাণ করে, সেই প্রক্রিয়াটা আসলে কেমন। এইসব ডিপ লার্নিং সিস্টেমে বিলিয়ন বিলিয়ন ইন্টারকানেক্টেড নোড থাকে স্তরে স্তরে সাজানো, গাণিতিক 'নিউরন' দিয়ে তৈরি। অনেকটা প্রাণীর মস্তিষ্কের বহুস্তরীয় সার্কিটের মতো। আমাদের মস্তিষ্ক এক বিস্ময়কর জৈব যন্ত্র। আমাদের চিন্তাভাবনা, কল্পনা, সৃষ্টিশীলতা— সবই তো নিউরনের বৈদ্যুতিক সংকেত আর রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফল। যখন একটি ডিপ নিউরাল নেটওয়ার্ক ছবি চিনতে শেখে, তখন এটি বিমূর্ত স্তর গঠন করে—একটি স্তর হয়তো ধারের রেখা শনাক্ত করে, অন্যটি আকার বা টেক্সচার, আর আরও উপরের স্তর বস্তু বা শৈলী চিনে নিতে শেখে। এই স্তরবিন্যাস অনেকটা মানুষের ভিজ্যুয়াল কর্টেক্সের মতো— সরল রেখা থেকে জটিল দৃশ্য পর্যন্ত। এই নেটওয়ার্ক সচেতন (conscious) নয়, এটা ঠিক কিন্তু এর শেখার প্রক্রিয়ার সঙ্গে আমাদের জৈবিক প্রক্রিয়ার এক আশ্চর্য মিল আছে।
মানুষের মস্তিষ্কে আছে প্রায় ৮৬ বিলিয়ন নিউরন, যা তৈরি করে প্রায় ১০০ ট্রিলিয়ন সংযোগ— যে সংখ্যাগুলো আমরা কল্পনাও করতে পারি না। এই নিউরনগুলো এমনভাবে যুক্ত যে, কেউ যদি মস্তিষ্কটিকে শুধুই একগুচ্ছ নিউরনের জাল হিসেবে দেখে, তবে সেটিও AI-এর কম্পিউটার চিপের মতোই 'যন্ত্রসদৃশ' মনে হতে পারে। তবু সেই জাল থেকেই তো জন্ম নিয়েছে শেক্সপিয়রের সনেট, ভ্যান গঘের তারা-ভরা রাত, মিয়াজাকির জাদুময় জগৎ। অন্যদিকে GPT-3-এর মতো মডেলে রয়েছে ১৭৫ বিলিয়ন প্যারামিটার, যেগুলো একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জটিল সমীকরণে সিদ্ধান্ত নেয়। এই প্যারামিটারগুলো অনেকটা ব্রেনের সিন্যাপ্সের মতো— মানুষ যেমন অভিজ্ঞতা থেকে শেখে ও নিউরনের সংযোগ জোরদার করে, AI-ও তেমনভাবে ডেটা থেকে শেখে।
'অ্যালগরিদম' শব্দটি শুনলে অনেকেই ভাবে এটি ধাপে ধাপে লেখা একধরনের রুটিন কোড। কিন্তু AI-কে কেউ হাতে ধরে শেখায় না বা সরাসরি প্রোগ্রাম করে দেয় না। এটি হাজার হাজার ছবি দেখে, নিজে নিজে শিখে নেয় এবং শেখা প্যাটার্নগুলো থেকে নতুন কিছু তৈরি করতে শেখে।
এই কারণেই গবেষণা কমিউনিটিতে বারবার বলা হচ্ছে— AI একধরনের কগনিশন বা চেতনার জন্ম দিচ্ছে। AI প্রতিদিন নিজেকে আরও বেশি ডেটা দিয়ে প্রশিক্ষিত করছে, আরও উন্নত মডেল তৈরি করছে, যাতে তা আরও মানবীয় 'আউটপুট' দিতে পারে। যেমন একটি শিশু তার চারপাশের মানুষ ও পরিবেশ থেকে শেখে, তেমনই AI-ও গড়ে উঠছে মানুষের চিন্তা, যুক্তি, শিল্পবোধ, অনুভব, ও পছন্দের সম্মিলিত ছাপ নিয়ে। AI এখনও পর্যন্ত মানুষের জটিল আবেগ, অভিজ্ঞতা বা সৃজনশীলতাকে পুরোপুরি অনুকরণ করতে পারে না। তবে ভাষা, ছবি, অডিও ডাটার মাধ্যমে এটি সেই অনুকরণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে— আর সেই প্রচেষ্টাও দিন দিন আরও নিখুঁত হচ্ছে। আর এখানেই প্রযুক্তির সম্ভাবনার সঙ্গে ঘুরপাক খাচ্ছে দার্শনিক ভাবনাও।
AI-কে আরও মানবীয় করে তুলতে যে ডেটা প্রয়োজন, তা তো মানুষেরই তৈরি। তাহলে সেই ডেটা ব্যবহার করা নৈতিকভাবে কতটা সঠিক?
যদি ডাটা আর অফুরান্ত এনার্জির জোগান দেওয়া যায়, তাহলে AI কি সত্যিই একদিন মানুষের জটিল মনন ও চিন্তাশক্তিকে অনুকরণ করতে পারবে?
মানবসমাজের কল্যাণ কীসে ? শুধু যন্ত্রের দক্ষতা বাড়ানোয়, না কি অনুভব, চিন্তা, ও সৃজনক্ষমতার বিকল্পও তৈরি করা প্রয়োজন?
বিজ্ঞানীদের সম্প্রদায় কোথায় দাঁড়িয়ে আছে AI ব্যবহারে? গত প্রায় দু'বছর ধরে কর্মক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগতভাবে AI ছাড়া চলে না। ব্যবহার করি রোজকার পেপার লেখা, কোডিং, এমনকী পড়াশোনার ক্ষেত্রেও। বন্ধু, অফিসের সহকর্মী— সবার জীবনেই AI ঢুকে পড়েছে। শিল্পে AI-এর ব্যবহারের সমালোচনায় লেখা হয়েছে,
“Art is not a mathematical equation to solve but a deeply human expression of emotion , struggle and imagination.”
আর গাণিতিক সমাধান বা বিজ্ঞান চর্চা? গভীর চিন্তা, বিশ্লেষণ, বছরের পর বছর অনুশীলনও কম পড়ে যায়, আসমুদ্র জ্ঞানের বালিকণাটুকুও শেখা হয় না। ইদানীং অনেক তত্ত্ব, প্রতিষ্ঠিত সমীকরণ/মডেল নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে বিভিন্ন টুল ব্যবহার করি আমরা। যেমন, এখন আর কেউই হাতে করে ক্যালকুলাস সমাধান করে না। তবু সেই সব গণিতবিদ বা বিজ্ঞানী, যাঁরা এই তত্ত্বগুলি তৈরি করেছেন বা এখনও করে চলেছেন— তাঁদের প্রাসঙ্গিকতা বা কৃতিত্ব কমে যায়নি। বরং শ্রদ্ধা, মুগ্ধতা বাড়ছে।
বিজ্ঞানের সৃজনশীল কাজ আজও মূলত মানুষের উদ্ভাবনী চিন্তা থেকেই হচ্ছে। AI এখানে টুল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেই সব কাজ দ্রুত সম্পাদনের জন্য। ছাত্র জীবনে গবেষণাপত্র, প্রজেক্ট প্রস্তাব লিখতে শিখেছি অনেক সময় ব্যয় করে, রাত জেগে কোডের বাগ (ভুল) ঠিক করেছি। এই কাজগুলো এখন হলে হয়তো আরও সহজেই করা যেত! তবে আমাদের শিক্ষকরা বলতেন, তাঁদের সময় গুগলও ছিল না, কোনও বই পেতে লাইব্রেরিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে হতো। আর এখন মুহূর্তেই অসংখ্য গবেষণাপত্র, লেকচার, কোড স্নিপেট পেয়ে যাই আমরা। প্রযুক্তি আমাদের জীবনের ধরন পালটে দেয়, এটাই স্বভাবিক। কিছুদিন আগেই OpenAI চালু করেছে ওয়েবসাইট ও অ্যাপ তৈরির ফিচার। আগে যারা এগুলি তৈরি করে উপার্জন করতেন, এখন তাঁরা এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি। কোন ধরনের কাজ ভবিষ্যতে টিকে থাকবে, নতুন কোন ধরনের কাজের সুযোগ তৈরি হবে, আগামী পৃথিবী কেমন হতে চলেছে— তা নিয়ে আলোচনা, তর্কও বাড়ছে কিন্তু বিজ্ঞানে AI-এর ব্যবহারের অনিবার্যতা অস্বীকার করার জায়গা নেই।
প্রশ্ন উঠছে, বিজ্ঞান সহজেই AI-কে গ্রহণ করেছে, তাহলে শিল্পে কেন এত সংশয়? শিল্পের সৃজনশীলতা বিজ্ঞানের চেয়ে কোথায় আলাদা, যে কারণে AI ব্যবহারে এত সমালোচনা হচ্ছে? কেন ভাবা হচ্ছে না যে, AI-ও সেই রকমই একটি শক্তিশালী টুল হতে পারে, যা শিল্পীদের পরিশ্রম কমিয়ে কল্পনা ও ভাবনার দিকে বেশি মনোযোগ দিতে সাহায্য করতে পারে?
আরও পড়ুন- মানুষের মস্তিষ্ক খেয়েই বাঁচছে AI! পারমাণবিক বোমার নিয়ন্ত্রণ নিতে চাইছে রোবটরা?
একথা সত্য যে, বিজ্ঞানের মতোই শিল্প সংক্রান্ত বহু কর্মক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে। AI অনেক কিছুতেই মানুষের চেয়েও দক্ষ হয়ে উঠেছে। মানুষ কি তবে ভয় পাচ্ছে যে এই পৃথিবীতে মানুষই আর মানুষের একমাত্র প্রতিযোগী নয়? মানুষেরই কি লাগাম পরানো উচিত AI-এর উন্নয়নে?

এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানে এর সঙ্গে শিল্পের আরও এক গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য চোখে পড়ে। বিজ্ঞানের জগতে তথ্য বিনিময় এবং ওপেন অ্যাক্সেস নীতির ব্যাপক চর্চা। আজকের দিনে IEEE, ACM বা Springer-এর মতো অনেক গবেষণা প্রকাশনা শুরুতে সাবস্ক্রিপশনভিত্তিক হলেও, কিছু সময় পর সেগুলো Sci-Hub বা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে উন্মুক্ত হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই গবেষকরা নিজেরাই তাঁদের কাজ ‘open archive’ করেন, arXiv, ResearchGate-এর মাধ্যমে। এর মূল উদ্দেশ্য একটাই— বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য জ্ঞানকে উন্মুক্ত রাখা। গবেষকরা চান তাঁদের কাজ যেন সবাই পড়তে ও ব্যবহার করতে পারে। এর ফলে তাঁদের প্রভাব বাড়ে, সাইটেশন পাওয়া যায়, যদিও সরাসরি আর্থিক লাভ হয় না। তাছাড়া, বিজ্ঞানে ব্যবহৃত অনেক ডেটা— যেমন ক্লাইমেট ডাটা, জেনেটিক সিকোয়েন্সেস বা মেশিন লার্নিং ডেটাসেট মানবতার জন্য 'public good' হিসেবে বিবেচিত হয়। এদের পুনঃব্যবহারকেও ততক্ষণ সমর্থন জোগানো হয় বা উৎসাহিত করা হয়, যতক্ষণ না তা কোনও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বা মানবাধিকারের লঙ্ঘন ঘটাচ্ছে।
অন্যদিকে, শিল্পের জগতে পরিস্থিতি ভিন্ন। একটি শিল্পকর্মের পূর্ণ মেধাস্বত্ব শিল্পীর নিজের। অধিকাংশ দেশের আইনে শিল্পীর ‘moral right’ বা নৈতিক অধিকার স্বীকৃত— তাঁর সৃষ্টি যেন বিকৃত না হয়, অনুমতি ছাড়া পুনরুৎপাদন, বিতরণ বা অনুকরণ করা আইনত দণ্ডনীয়। এখানেই শিল্প আর AI-এর দ্বন্দ্ব শুরু হয়। সাম্প্রতিক সময়ে AI মডেলগুলি লক্ষ লক্ষ বিদ্যমান চিত্রকর্ম ও আলোকচিত্র দিয়ে প্রশিক্ষিত হয়, যাতে তারা নতুন চিত্র সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু এই প্রশিক্ষণের ডেটাসেট সংগ্রহের সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের কোনও সম্মতি নেওয়া হয়নি এবং তাঁদের কোনও পারিশ্রমিকও দেওয়া হয়নি। ঠিক যেমনটা হয়েছে স্টুডিও জিবলি-র ক্ষেত্রেও। ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে একটি ঘটনা সামনে আসে। তিনজন চিত্রশিল্পী— সারা অ্যান্ডারসন, কেলি ম্যাককারনান, ও কারলা অর্টিজ যুক্তরাষ্ট্রে Stability AI, Midjourney এবং DeviantArt-এর বিরুদ্ধে মামলা করেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল, তাঁদের অনুমতি ছাড়াই AI মডেলগুলি তাঁদের শিল্পকর্ম দিয়ে প্রশিক্ষিত হয়েছে। তাঁদের মতে, এটি কপিরাইট লঙ্ঘন এবং সৃজনশীল অধিকারের পরিপন্থী। AI-এর পক্ষ থেকে পাল্টা যুক্তি উঠে আসে, যদি AI-এর তৈরি করা কাজটি যথেষ্ট নতুন এবং রূপান্তরিত হয় তাহলে তা 'fair use'-এর আওতায় পড়ে। এই আইনি ও নৈতিক বিতর্ক ভবিষ্যতে আরও দীর্ঘায়িত হবে। AI যদি অন্যের সৃষ্টিকর্ম থেকে শেখে এবং নতুন কিছু তৈরি করে, তবে সেই সৃষ্টিকে কতটা ন্যায্য বলা যাবে? AI কি কেবল একটি শক্তিশালী অনুকরণ মাধ্যম না কি সত্যিই সৃজনশীল?
এই প্রশ্নগুলির উত্তর পেতে আরও সময় লাগবে। তবে এই প্রশ্নগুলিই ভবিষ্যতের AI-চালিত শিল্পচর্চার নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমাদের ভুলে গেলে চলবে না—
মানুষের সৃষ্টিশীলতা গড়ে ওঠে তাঁর জীবনভিত্তিক প্রেক্ষাপট, অভিজ্ঞতা, দুঃখ-কষ্ট, দ্বন্দ্ব এবং মূল্যবোধ থেকে। যদি ভবিষ্যতে AI নিজস্ব একধরনের কগনিশন (চেতনা) অর্জন করে, তবে কি তা একই রকম অর্থবহ হয়ে উঠবে?
সেই কগনিশনকে কি আমরা মানবিক বলে মেনে নেব?
সেই দিন কত দূরে?
আর, যদি সত্যিই সেই দিন আসে, তবে কি মানবসভ্যতা বিপন্ন হয়ে পড়বে?
প্রশ্নগুলো জটিল। আর উত্তর মোটেও সহজ নয়।




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp