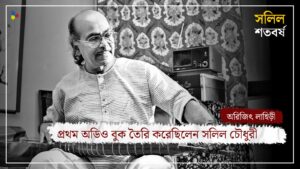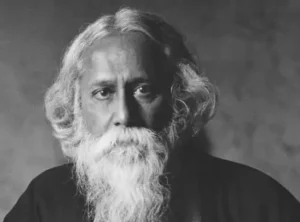রাশিয়ান চার্চের সঙ্গে মিল, তান্ত্রিক মতে তৈরি হংসেশ্বরীর তুলনা ভূ-ভারতে নেই
বাজি ধরে বলা যায় এর তুলনা রাজ্যে তো বটেই, গোটা দেশেই নেই। অবিশ্বাস্য দক্ষতায় অজানা একদল শিল্পী যে মিরাক্যল ঘটিয়েছিলেন আজ থেকে আড়াই শতক আগে, তা আজওস, এই ইন্টারনেট যুগেও বিস্মিত করার ক্ষমতা লাগে
ফেলুদার ভাষায় বললে, ‘ভ্রমণের বাতিকটা বাঙালিদের মধ্যে যেমন আছে, তেমন ভারতবর্ষের আর অন্য কোনও জাতের মধ্যে নেই। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যাতায়াতের খরচ যত বাড়ছে, ভ্রমণের নেশাও নাকি বাড়ছে পাল্লা দিয়ে’। এই কথাটি একশো শতাংশ সত্যি। তবে অতিমারীর পরে বেড়ানোর ধরন অনেকটা বদলে গিয়েছে। শহরের ভিড়ে নয়, প্রকৃতির মাঝে বেড়াতে যেতে চায় মানুষ। চাইছেন এমন কোথাও যেতে, যেখানে কিছুটা ফাঁকায় ফাঁকায় ঘুরে আসার সুযোগ আছে। তেমনই এক শান্ত, নিরিবিলি জায়গা হল কল্যাণীর হংসেশ্বরী মন্দির। কোনও এক রবিবারে সপরিবারে বেরিয়েই পড়তে পারেন কল্যাণীর উদ্দেশ্যে। মানবদেহের গঠনশৈলীকে মাথায় রেখে তৈরি এই মন্দির আপনাকে অবাক করতে বাধ্য। বাজি ধরে বলা যায় এর তুলনা রাজ্যে তো বটেই, গোটা দেশেই নেই। অবিশ্বাস্য দক্ষতায় অজানা একদল শিল্পী যে মিরাক্যল ঘটিয়েছিলেন আজ থেকে আড়াই শতক আগে, তা আজও, এই ইন্টারনেট যুগেও বিস্মিত করার ক্ষমতা রাখে।
এই মন্দিরে যাওয়ার রাস্তাও খুব সহজ। হাওড়া থেকে কাটোয়া লোকালে চেপে বাঁশবেড়িয়া স্টেশনে নেমে সেখান থেকে টোটো করে মন্দির যাওয়া যায়। এছাড়াও হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল পৌঁছে ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে মিনিবাস বা অটো করেও যাওয়া যায়।অটো বা টোটো থেকে নেমে রাস্তার মোড় থেকে গলিঘুঁজির মধ্যে পাক খেয়ে এক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাবেন অর্ধচন্দ্রাকৃতি এক সেকেলে রাজবাড়ির তোরণ দ্বারের সামনে। দেওয়ালের গা থেকে খসে পড়ছে মলিন পলেস্তারা, ওপরের নহবতখানায় শেষ কবে সানাই বেজেছে কেউ জানে না। সেখানে এখন ঝুল আর ধুলোর পরত। ফটকের ওপারে নিঃসঙ্গ বৃদ্ধের মতো দাঁড়িয়ে আছে বাঁশবেড়িয়া রাজবাড়ি। তার বাইরে ঠিক ডানদিকের ফ্রেম জুড়ে যেন কোনও ভিনদেশী কেল্লার মতো স্থির হয়ে আছে হংসেশ্বরি মন্দির। অসংখ্য চূড়া-বিশিষ্ট এই মন্দিরের দিকে তাকিয়ে আপনার যদি হঠাৎ ডিজনিল্যান্ড বা ক্রেমলিন দুর্গের কথা মনে পড়ে যায় তাহলে অবাক হবেন না। এই মন্দিরের নকশার চেয়েও অদ্ভুত অবশ্য মন্দির নির্মাণের গল্প।
ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায়, বাঁশবেড়িয়ার রাজা নৃসিংহদেব ছিলেন ধর্মপ্রাণ মানুষ, তিনি ১৭৯০ সাল নাগাদ কাশী গিয়ে বহু সাধক ও পণ্ডিতের সঙ্গলাভ করে তন্ত্রশাস্ত্র ও তান্ত্রিক সাধনার বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। কয়েক বছর পর নিজের জমিদারিতে ফিরে তিনি সিদ্ধান্ত নেন তার নিজের বাসভবনের সামনে একটি মন্দির নির্মাণ করবেন কিন্তু তা আর পাঁচটা সাধারণ মন্দিরের মতো হবে না। এর গঠনশৈলীতে থাকবে রাজা নৃসিংহদেবের গূঢ় তান্ত্রিক অভিজ্ঞান। তন্ত্রভিত্তিক যৌগিক সাধনায় মানুষের শরীরে পাঁচটি প্রধান নাড়ি (ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, বজ্রাক্ষ ও চিত্রিণী) এবং তেরোটা চক্র (মূলাধার, মণিপুর, সহস্রার) কল্পনা করা হয়ে থাকে। রাজা নৃসিংহদেব তান্ত্রিক কুলকুণ্ডলিনীর ধারণাকে মন্দিরের গঠনে শিল্পের আকারে ভাস্বর করে তোলার দুঃসাহসিক সংকল্প নিলেন। সেই মতো রাজস্থানের জয়পুর থেকে মন্দির নির্মাণ শিল্পীদের নিয়ে আসা হল, নিয়ে আসা হল ২১ মিটার মিনারের রূপো। উত্তরপ্রদেশের চুনার থেকে আনা হল বেলেপাথর। পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করে এমন এক স্থাপত্য তৈরি হল যার তুলনা ভূ-ভারতে বিরল। রাজা নৃসিংহদেব তার জীবদ্দশায় মন্দির সম্পূর্ণ করতে না পারলেও তার মৃত্যুর পর তার রানী শঙ্করী দেবী স্বামীর অসম্পূর্ণ কাজ পূরণ করেন এবং ১৮১৪ সালে এই মন্দির সকলের জন্য উন্মুক্ত হয়।
অনেকের মতে, নৃসিংহদেবের দ্বিতীয় রানি দেবী শঙ্করী ছিলেন উদার দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ, যিনি মন্দির সমাপ্তির পর্যায়ে মন্দিরের স্থাপত্যে রাশিয়ান সংমিশ্রণ এনেছিলেন। মস্কোর পোকরোভস্কি ক্যাথিড্রাল বা রাশিয়ার সেন্ট ব্যাসিল চার্চের সাথে এই মন্দিরের মিল আছে। মন্দিরটির স্থাপত্য কারুকার্যে উত্তর রাজস্থানের শেখাওয়াতি হাভেলির কিছু নির্মাণশৈলীও লক্ষ্য করা যায়।
মন্দিরের দিকে তাকালে দেখা যায়, সত্তর ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এই মন্দিরে তেরোটা মোচাকৃতি শিখর বা রত্ন আছে। প্রতিটি চূড়ার শীর্ষভাগ পদ্মকোরকের আদলে তৈরি, যা সাধারণত সুইস আল্পসে দেখা যায়। কিন্তু সাধারণ মন্দিরের রত্নের মতো করে এটা সাজানো নয়। এই মন্দিরের আট কোণে আটটা, মাঝখানে চারটে আর এবং কেন্দ্রস্থলে একটা শিখর আছে যা কুলকুণ্ডলিনীর একটি চক্রকে চিহ্নিত করে। আর প্রতিটি তল থেকে খাড়া সিঁড়ি উঠে গেছে এবং গর্ভগৃহ থেকে চুড়ো পর্যন্ত গোটা মন্দির অসংখ্য গোপন সিঁড়ি ও সংযোগপথ দিয়ে যুক্ত। অর্থাৎ মন্দিরের ভেতরটা একটা গোলকধাঁধার মতো যেখানে একবার ঢুকলে সঠিক পথ সন্ধান করে বেরনো মুশকিল।

মন্দিরের একতলার প্রধান গর্ভগৃহে অধিষ্ঠাত্রী দেবী হংসেশ্বরি। হংসেশ্বরি মন্দিরের গর্ভগৃহে দেখা যায় দেবী সহস্রদল নীল পদ্মের ওপর শায়িত মহাকালের হৃদয় থেকে উত্থিত দ্বাদশদল পদ্মের উপর এক মা মুড়ে অবস্থান করছেন। দেবীর গায়ের রঙ নীল, বাঁ হাতে খড়গ ও নরমুণ্ড, এবং ডান হাতে অভরমুদ্রা ও শঙ্খ। বছরে ৩৬৪ দিন দেবীর শান্ত মূর্তি, কেবল বাৎসরিক পূজার দিন রাতে এলোকেশী উগ্র মূর্তি। ওই দিন রাতে দেবীকে পরিয়ে দেওয়া হয় রূপোর মুখোশ ও সোনার জিভ।
হংসেশ্বরি মন্দিরের পাশেই রয়েছে অনন্ত-বাসুদেব মন্দির, রাজা নৃসিংহদেব এর পিতা রামেশ্বর রায় ১৬৭৯ সালে তৈরি করান। চারচালা কাঠামোর ওপর একরত্ন বিশিষ্ট এই মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির কারুকাজ মানুষকে অবাক করে। শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথ নাকি এই মন্দির দর্শনে এসে টেরাকোটার কাজ দেখে এতই বিমোহিত হলেন যে শান্তিনিকেতনে ফিরে তিনি তার প্রিয় ছাত্র নন্দলাল বসুকে এখানে পাঠান। নন্দলাল বসু প্রায় ৬ মাস এখানে থেকে টেরাকোটার কাজের সমস্ত ছবি নিজে এঁকে নিয়ে যান। এই টেরাকোটার কাজের মধ্যে বিভিন্ন দেবদেবী ও পৌরাণিক কাহিনি অঙ্কিত রয়েছে, অনেকটা যেন পটের মতো ধাপে ধাপে কাহিনি-বর্ণনা করা হয়েছে।
এছাড়া, বাঁশবেড়িয়ায় বেশ কিছু পুরোনো বনেদি বাড়ি আছে। তাই শুধু মন্দির দর্শন করে যেতে না চাইলে আশেপাশের জায়গাগুলো একটু ঘুরে দেখতে পারেন। আশা করি মন্দ লাগবে না। বেশি টাকা পয়সা খরচের ভয় নেই, সাধ ও সাধ্যের মধ্যে, তাই আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়ুন সেই দিকশূন্যপুরে যেখানে টেরাকোটা, পোড়ামাটি থেকে শুরু করে রাজস্থানী শৈলীরও নিদর্শন পাবেন।
হংসেশ্বরী মন্দিরের শিল্প অত্যন্ত নিপুণ, নিখুঁত ও মজবুত হওয়ায় তার স্থাপত্যে এখনও সেভাবে ফাটল ধরেনি। কিন্তু সংস্কার আর বয়সের ভারে রাজবাড়ির নহবতখানায় জীর্ণতার ছাপ। ১৮২০ সালে হংসেশ্বরি মন্দিরে মায়ের কিছু অলঙ্কার চুরি হয়ে যায় সেই সাথে অনন্ত বাসুদেব মন্দির থেকে প্রাচীন কষ্টিপাথরের একটি মূর্তিও চুরি হয়। পুরো এলাকাটাই এখন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধীনে। মন্দিরের সহকারী পুরোহিতের কথায়, “আইনি জটিলতায় সব থমকে আছে। সব জীর্ণ হয়ে পড়ছে। মন্দিরকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য একটা তোরণের প্রয়োজন। অনেকদিন মন্দিরে রঙের ছিটেফোঁটাও পড়েনি। দরকার সংস্কার, চাই ২৪ ঘণ্টার একটি রক্ষী। নেই পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা। সন্ধ্যের পর মন্দিরের বাইরে আড্ডা জমায় বহিরাগতরা”। মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের বক্তব্য, “কেন্দ্রীয় সংস্থা যদি এগিয়ে আসে তাহলে মন্দিরের আমূল সংস্কার সম্ভব। একটু সেজে উঠলে মন্দিরে ভিড় উপচে পড়বে”।
বাংলার বহু মন্দিরের হালই খুব খারাপ, তার মধ্যেই যদি কয়েকটা মন্দিরকে স্বমহিমায় দাঁড় করানো যায় তাহলে আখেরে লাভ বাঙালির, ভ্রমণপিপাসু বাঙালির, যাদের পায়ের তলায় সর্ষে।




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp