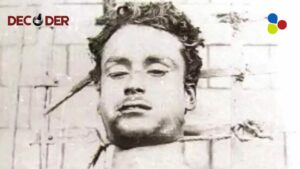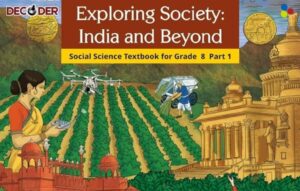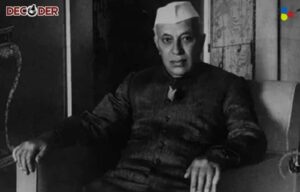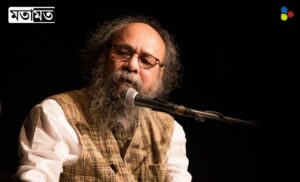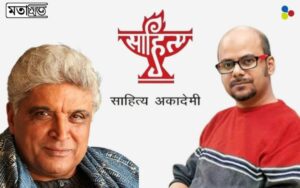হাতড়াই বইমেলা! ম্যাপ দেখে খুঁজে নিই প্রিয় বইয়ের বাড়ি
Kolkata Bookfair 2025: মনে পড়ে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের প্রাণপুরুষ সন্দীপ দত্তের কথা। মনে আছে ভাস্কর চক্রবর্তীর দীর্ঘদেহ আর অমলিন পদচারণা। মিস করছি হঠাৎ নেই হয়ে যাওয়া ‘জয় বৃক্ষনাথ’ বলা কমল চক্রবর্তীকেও।
১
যখন এই লেখা এবারের ‘আশমানদারি’-র কিস্তি হয়ে বেরোচ্ছে, তখন বইমেলার মাঠে 'খেলা ভাঙার খেলা'। এ বছরের মতো সাঙ্গ হয়ে এল বই পার্বণ। থিম দেশ ছিল জর্মানি। এবারেই প্রথম আসেনি বাংলাদেশের বইপত্র। মেলার মাঠে শিল্পীদের বসতে দেওয়া হয়নি বলে জানানো হয়েছে প্রতিবাদ। এবছর আলাদা চার দেওয়াল নির্দিষ্ট কোনও ‘হল’ ছিল না। এবছর ৯১ বছর বয়স্ক কথাসাহিত্যিক শংকর পাঠকদের সই দিয়েছেন বইমেলায় বসে। এ সমস্ত ঘটতে ঘটতে কখন যেন ফুরিয়ে এল এবারের বেলা। আবার অপেক্ষা আগামী বছরের। অনেক বই কেনা হলো, লিটল ম্যাগাজিনের আখড়ায় দেখা হল নতুন-পুরনো নানা মুখের সঙ্গে। আবার সেই ঘণ্টাধ্বনি, আবার সেই পরের বছর দেখা হবার প্রতিশ্রুতি, আবার সেই রঙ-বেরঙ অথবা শাদা-কালো ছবিতে স্মৃতির মুখ।
আমার মনে হয় একটা শহরের কথা। কথা নয়, ছবি। প্রতি বছর বইমেলা প্রাঙ্গণে গড়ে ওঠে নানা ঠিকানা লেখা একটা শহর। শেষদিন তাকে ভেঙে দেওয়া হয়। পরের বছর একই নামের বাড়ির অন্য একটা ঠিকানা। তাকে ম্যাপ দেখে খুঁজে নিই আমরা। প্রিয়জনের বাড়ি, প্রিয়মুখের আস্তানা। এই ধরা যাক, ‘ভাষাবন্ধন’ কিংবা ‘প্যাপিরাস’। এইসব স্টলের সঙ্গে মিশে থাকে বহু বহু স্মৃতি। ওই যে বললাম, বাড়ি। বাড়ির বাসিন্দা। কত বাসিন্দা বদলে যায়। নবারুণদার সঙ্গে আর দেখা হয় না। প্যপিরাসের অরিজিৎ কুমার এখন মেলায় কমই আসেন। লিটল ম্যাগাজিন চত্বরে প্রতি বছর দু-তিনবার হাজিরা দিতাম ‘রক্তমাংস’ পত্রিকার স্টলে। বসে থাকতেন গৌতম ঘোষ দস্তিদার আর ঊর্মিলাদি। আরও আগে, আমাদের সদ্য যৌবনে বইমেলায় দেখতাম ‘প্রমা’ পত্রিকার সুরজিৎ ঘোষ কিংবা ‘বিশ্ববাণী প্রকাশনী’-র ব্রজকিশোর মণ্ডলকে। নতুন নতুন নামের বাড়ি কিংবা টেবিল আসে, পুরনো বাসিন্দার জায়গা নেয় নতুন মুখ। বইমেলা থেকে বইমেলায় নিঃশব্দে ব্যাটন চলে যায় এক হাত থেকে অন্য হাতে। এই যে চারদিকে নতুন-নতুন নামের বাড়ি, নতুন-নতুন বন্ধু, পরিচিত, আত্মীয়। এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। আমার কলেজ জীবনের বন্ধু রাহুল বইমেলার মাসখানেক আগে থেকে ‘দেশ’ এবং অন্যান্য পত্রিকার সাহায্যে নতুন বইয়ের দীর্ঘ তালিকা তৈরি করত, তারপর বইমেলা থেকে ‘প্রায়োরিটি’ অনুযায়ী টাকা মেপে সেসব কিনে ফেলত। শেষে একটা বিজয়ীর হাসি দিত। আমরা চিরকাল বেহিসেবি, কতকটা ন্যালাখ্যাপা গোছের, প্রথমদিকে অপরিকল্পিত ব্যয় এবং কেনাকাটা শেষে হা-হুতাশে জর্জর, তারা রাহুলের ওই হাসিটাকে সহ্য করতে পারতাম না। প্রত্যেক মেলার শেষদিনে আমিও মনে করতে চেষ্টা করি কী কী বই কেনা বাকি রয়ে গেল, কোন কোন পত্রিকা পরে জোগাড় করতে হবে।
বইমেলার এক একটা দিন, এক একরকম রঙ্গরস নিয়ে হাজির হয়। বেশ কিছু স্টলে থাকে পুরনো বইপত্র। ‘দুষ্প্রাপ্য’ গ্রন্থরাজি। সে প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল ‘সুবর্ণরেখা’ বিপণির কর্ণধার ইন্দ্রনাথ মজুমদারের কথা। যাই হোক, সেইসব হাতফেরতা বইয়ের এলোমেলো পাহাড়ের মধ্য থেকে হঠাৎ হঠাৎ হাতে উঠে আসে এক একখানা অপূর্ব মণিরত্ন। একেবারে দৈবাৎ। না কি বলা ভালো, দৈব নির্ধারিত! সেইসব বইয়ের সঙ্গে কিছু উপরি প্রাপ্তিও থাকে। যেমন, আমার কাছে আছে রিলকের উপন্যাস, যার একদা মালিক ছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কিংবা শিবনারায়ণ রায়ের সই করা আঁদ্রে জিদের ডায়েরি। সেসবের উত্তেজনা প্রশমিত হলে লক্ষ্য করা যায়, আরও অনেক মনোগ্রাহী সব বিষয়ের ডিপো এই বইগুলি। যেমন কোনও বইয়ে লেখা আছে ‘রুপাই-কে শ্যামলদা’ অথবা ‘মনোজমামার জন্মদিনে মিঠু এবং সুমন’। কোনও সাল-তারিখ লেখা নেই। আমি সেইসব লেখার দিকে তাকিয়ে সারাদিন কাটিয়ে দিই। এঁরা কি এখনও বেঁচে-বত্তে আছেন? পরস্পরের সম্পর্ক কি অটুট আছে? কলকাতা নাকি অন্য কোনও শহরতলি বা সদর-মফসসলে থাকেন বা থাকতেন? বই, পুরনো বই, তাঁর নানা লেখা-উপহার-শুভেচ্ছা আর নাম এসবের রহস্যে মজে থাকি। বইমেলায় নতুন বই যেমন আকর্ষণীয়, পুরনো বইয়ের অনর্গল হাতছানিও কম রংদার নয়!
আরও পড়ুন- জামার তলায় চুরি করা রুশদি! বইমেলায় ক্রমেই ফিকে হচ্ছে বইপাগলরা
শেষদিনে এইসব আত্মীয় বন্ধু, নানা সাইন বোর্ড আর নম্বরের বাড়ি, নানা পুরনো-নতুন বই, মাঠকর্মী, দোকান-কর্মী, গিল্ড আপিসের পাহারাদার, বিদেশি অভ্যাগত, বইয়ের ভারী ব্যাগ হাতে জ্বলজ্বলে চোখের কিশোর-কিশোরী, এদের সবাইকে বলে আসা, ‘আসছে বছর আবার দেখা হবে। নতুন ঠিকানায়, নতুন শহরে!’ প্রসঙ্গত, বলে রাখি, সুবিধে যতই হোক, অনুষ্টুপ-দে’জ-আজকাল-আনন্দ এইসব প্রকাশনার নির্দিষ্ট বইঘর বোধহয় খোঁজার রোমাঞ্চ কমিয়ে দেয়। অবশ্য বাণিজ্যিক অভিমুখের প্রশ্নে ‘রোমাঞ্চ’ নিয়ে ভাবা একটু হাস্যকর চিন্তা। বুঝি, কিন্তু মানি না! এখানে একটা নিরুপায় হাসির ইমোজি বসাতে পারলে ভালো হতো। বাংলা গদ্যে মোবাইল এবং ইন্টারনেটের প্রভাব? এই রে!
২
বইমেলা শুরু হয়েছিল ‘পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড’-এর প্রযোজনায় ১৯৭৬ সালে। ১৯৮৪ সালে পেয়েছিল ‘আন্তর্জাতিক’ খেতাব। প্রথমে সেন্ট পলস ক্যথেড্রালের উল্টোদিকের মাঠে, তারপর রবীন্দ্রসদনের বিপরীতে, পরবর্তীকালে পার্ক স্ট্রিট, ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের বাইরের অংশ, মিলনমেলা এবং ২০২০ সাল থেকে সল্টলেক বা বিধাননগরের সেন্ট্রাল পার্কে বইমেলার আয়োজন। আমাদের কলেজকালে ‘পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা’ নামে আর একটি সরকারি বইমেলা হতো ওই আকাডেমির উল্টোদিকের মাঠে। এখন যার নাম ‘মোহর কুঞ্জ’। ১৯৮৪-১৯৯৪ সাল ছিল সেই সমান্তরাল মেলার ক্ষণজীবী মেয়াদ। এসব সাল-তারিখ আর অনুপুঙ্খ এক বোতাম টিপেই জানা যাবে মোবাইলে বা ল্যাপটপে গুগলের মাধ্যমে। ফলে, সেসব নিয়ে বেশি ফেনিয়ে লাভ নেই। বরং একটু ‘অধরা মাধুরী’ নিয়েই কথা বলা সমীচীন।
সে হলো আমার ব্যক্তিগত স্মৃতি। দপ্ করে যেন এক-একটা বছরের বইমেলা স্মৃতিতে জ্বলে ওঠে। কত-কত দিন, দুপুর-বিকেল-সন্ধ্যা, কত কুশীলব, কত বইপত্র, বন্ধু-বান্ধবী, স্বজন-পরিজন আর আড্ডা। আমার অল্প বয়সের ‘হিরো’-দের অধিকাংশই আজ প্রয়াত। কেউ কেউ শারীরিক কারণে বইমেলায় আর আসেন না। যেমন, প্রথমেই মনে পড়ে ‘তালপাতা’ প্রকাশনার প্রধান গল্পকার গৌতম সেনগুপ্তর কথা। মনে পড়ে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের প্রাণপুরুষ সন্দীপ দত্তের কথা। মনে আছে ভাস্কর চক্রবর্তীর দীর্ঘদেহ আর অমলিন পদচারণা। মিস করছি হঠাৎ নেই হয়ে যাওয়া ‘জয় বৃক্ষনাথ’ বলা কমল চক্রবর্তীকেও।
সেযুগে ছবি এবং যোগাযোগ এত বিপুল বিস্ফারে ঘরে-ঘরে পৌঁছে যায়নি। লেখক-লেখিকাদের চোখে দেখতে পাওয়া খুব সহজ ছিল না। বহু পাঠককেই অপেক্ষা করে থাকতে হতো প্রিয় লেখক/লেখিকার সঙ্গে মোলাকাতের। বইমেলায় ছিল তার সুবর্ণ সুযোগ। আমি নিজে দেখেছি, আটের দশকের গোড়ায়, রবীন্দ্রসদনের উল্টোদিকের মাঠে, বইমেলার সময়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আর নবনীতা দেবসেনকে অবলীলায় ঘাসে বসে গল্প করতে। বইমেলার মাঠে তখন প্রায় রোজই দেখা যেত সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রমাপদ চৌধুরীকে। প্রথম দেখার উত্তেজনা ছিল সমরেশ বসুকে দেখার দিন। রেলগাড়ির কামরার মতো দিনগুলো পিছনের থেকে সামনের দিকে চলে আসতে থাকে। ধূসর বিবর্ণতা থেকে আলোকোজ্জ্বল মায়াদর্পণে।
আরও পড়ুন- পুজোয় তো শাড়িও বেস্ট সেলিং হয়…
বইমেলাকে একেবারে প্রথম থেকে শেষ জড়িয়ে-জাপ্টে চাখতে শিখেছিলাম ১৯৮১ সালে। আমার বাবা, প্রয়াত আশীষ মজুমদার এবং তাঁর বন্ধুদের সূত্রে। তখন আমি সম্ভবত বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র। সেবছর ছিল ‘পরিচয়’ পত্রিকার পঞ্চাশ বছর! সে এক হইহই কাণ্ড! স্টলের মাথায় ‘পরিচয়’ লেখার পাশেই ছিল শাদা কাপড়ে নীল-সবুজ হরফে আমার বাবার হস্তাক্ষরে – ‘চাই সংস্কৃতি সচেতন রাজনীতি, চাই রাজনীতি সচেতন সংস্কৃতি’। বিকেল গড়াতে না গড়াতেই, সন্ধের ছোঁয়ায় এসে পড়তেন রথী-মহারথীরা। স্টলের মধ্যে বসে ছোটছোট কার্ডে নিমেষে অবাক-করা রঙ বেরঙের ছবি এঁকে দিতেন পূর্ণেন্দু পত্রী। সেই আঁকা দেখতে ভিড় জমে যেত। তারপর সেই ছবিগুলি হেঁকে বিক্রি করা হতো। তখন পূর্ণেন্দু পত্রী ‘কথোপকথন’ লিখে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। সন্ধেবেলা আসতেন শঙ্খ ঘোষ, সিদ্ধেশ্বর সেন, অমিতাভ দাশগুপ্ত। আমি তখন শঙ্খ ঘোষকে বেজায় ভয় পেতাম। কবিতায় বয়ঃসন্ধি পরিপোষক উপাদানের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি দেখে তখন আমি দূরে-দূরে থাকতাম। আসতেন দেবেশ রায় এবং অমলেন্দু চক্রবর্তী। সে বছর ‘পরিচয়’ পত্রিকার তরফে বেশ কিছু এক ফর্মার পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। তার মধ্যে ছিল আমার বাবার ‘ব্রেশ্টের কিছু’ – বের্টোল্ট ব্রেশ্টের গল্প এবং কবিতার তর্জমা। আর একটির কথা স্পষ্ট মনে আছে। সেটি সিদ্ধেশ্বর সেনের কৃশ কাব্যগ্রন্থ ‘ঘন ছন্দ মুক্তির নিবিড়’। সেটিই ছিল পঞ্চাশোর্ধ প্রৌঢ় কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ! কোনও কোনওদিন ঈষৎ টলায়মান শক্তি চট্টোপাধ্যায় নানা হইহল্লা করে যেতেন। বইগুলি হেঁকে হেঁকে বিক্রি করতাম আমরা। কখনও-কখনও এইসব মহারথীরাও সেই হাটুরে বৃত্তিতে যোগ দিতেন। একটি সমবয়সি উজ্জ্বল ছেলেকে পাশে দেখতাম হাঁকাহাঁকি করছে। তার নাম শুভকুমার বসু। তার দাদা শুনলাম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নামজাদা ছাত্র - নাটকেও কীর্তিমান - সৌমিত্র বসু। শুভ একটি পত্রিকা করে। তার নাম ‘চেনামুখ’। শুভর সঙ্গে আমার জমে গেল খুব। শুভর সঙ্গে লিটল ম্যাগাজিনের আখড়ায় গিয়ে আলাপ হলো গদ্যকার সুবিমল মিশ্রর সঙ্গে। ‘বিজ্ঞাপনপর্ব’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠান বিরোধী গর্জনে সেই যে মুগ্ধ হয়েছিলাম, তার রেশ আজও কাটল না। সুবিমলদার ‘হারান মাঝির বিধবা বৌ-এর মড়া অথবা সোনার গান্ধীমূর্তি ‘ পড়ার উত্তেজনা এখনও মনে আছে। রবীন ঘোষ, স্বাধীন বিশ্বাসদের সেই টেবিলকে আজও মনে মনে খুঁজি। আর আজকের পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়, বিষ্ণু দাশ, অনিতা রায়চৌধুরী প্রমুখ শিল্পীরা। আসতেন অজিত পাণ্ডে, প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী, মায়া সেন, একদিন এসেছিলেন, বোধহয় সবিতাব্রত দত্ত। সাহিত্য এবং সংস্কৃতি, বিশেষত অন্যান্য শিল্পের সংযোগ যে কতটা নিবিড়, সেটাই ছিল শিক্ষা।
৩
বছর কাটতে থাকে। পরবর্তী লেখক-কবিদের ধীরে ধীরে প্রতিপত্তি এবং যশ-দাপট বাড়তে থাকে। খুবই শীর্ণকায় মৃদুল দাশগুপ্ত তখন সবুজ মলাটের ‘জলপাই কাঠের এসরাজ’ সহ দেদীপ্যমান। স্টলে স্টলে ঘুরছেন অনতিতরুণ অনন্য রায়। তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম ‘আমিষ কবিতা’। এছাড়া, আটের দশকের শেষদিকে দেখেছি শামসের আনোয়ার, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নির্মল হালদারকে। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়রা জটলা বাঁধতেন সম্ভবত ‘কৃত্তিবাস’-এর স্টলের সামনে। একটা বড় ঘণ্টা ঝোলানো থাকত। বই কিনে সেই ঘণ্টা বাজালে পাওয়া যেত ‘ঘাটশিলার নুড়ি’। সেখানেই প্রথম দেখি প্রকাশ কর্মকার আর যোগেন চৌধুরীকে। জয় গোস্বামীকে প্রথম দেখেছি ১৯৮৭ সালে বইমেলার মাঠে। চোখে আলো। দেহে শীর্ণতা। দপ দপ করে একের পর এক বছর দেখা করে যেতে থাকে। এক বছর, সদ্য প্রকাশিত ‘উৎসব’ নামক শৈলেশ্বর ঘোষের কাব্যগ্রন্থটি (১৯৮৮) ঘিরে অনাবৃত ঊর্ধাঙ্গে কালিঝুলি মেখে নাচ-গান করছিলেন ‘কাগজের বাঘের’ ল্যাডলীদা, জীবনদা। এক বছর কবি জয় গোস্বামীর সই সহ বইয়ের জন্য গেট পর্যন্ত লাইন পড়েছিল। গম্ভীর মুখে হেঁটে যেতেন রণজিৎ দাশ আর হো-হো হাসিমস্করা করতে করতে দেখা যেত জয়দেব বসু এবং বিশ্বজিৎ পাণ্ডাকে। কোনও এক বছর অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত আর প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত সস্ত্রীক চারজন একসঙ্গে হাঁটছিলেন। সেই দৃশ্য দেখে আমাদের বন্ধু অকালপ্রয়াত প্রবীর দাশগুপ্ত বলেছিল, ‘ওই দ্যাখো, প্রাচী-প্রতিচীর মিলন পুঁথি’। টীকা এক্ষেত্রে, এ যুগে প্রয়োজন। প্রণবেন্দু বাবুর স্ত্রী ছিলেন মারিঅ্যান দাশগুপ্ত আর অলোকরঞ্জনের ট্রুডবার্টা দাশগুপ্ত।
আরও পড়ুন- বইমেলা নিয়ে কোনও আগ্রহই নেই ফরাসিদের
স্মৃতির সরণী বেয়ে বইমেলার সুখস্মৃতি কোনওদিন শেষ হবার নয়। কোনও এক বছর, বোধহয় ২০০১ সালে, আমাদের বন্ধু অভিজিৎ বসুর প্রকাশনায় ছোট্ট বই হয়ে বেরোয় ‘নর্মদার পুঁথি : বধ্যভূমিতে যুদ্ধ’। অরুন্ধতী রায়ের একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ আমি অনুবাদ করেছিলাম, সঙ্গে ছিল আরও অনুবাদ - মেধা পাটকর, সুন্দরলাল বহুগুণা, বাবা আমতে। সংকলন সম্পাদনায় ছিলেন শিবাদিত্য দাশগুপ্ত, সন্দীপন ভট্টাচার্য, আমার বোন অদিতি মজুমদার এবং দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়, সবার প্রিয় কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য। আমরা সবাই মিলে হইহই করে প্রচুর বিক্রি করেছিলাম মেলার মাঠে। সমস্ত টাকা তারপর পাঠানো হয়েছিল ‘নর্মদা বাঁচাও’ আন্দোলনের তহবিলে।
দুঃস্বপ্নের একটা স্মৃতি দিয়ে এই কিস্তি শেষ করি। ১৯৯৭ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি, বইমেলায় ভয়াবহ আগুন লেগে যায়। তখন সবে দুপুর মিশছে বিকেলের সঙ্গে। আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিচ্ছি। হঠাৎ একটা গোলমাল শুনে বাইরে এসে দেখি সবাই চার নম্বর গেটে জমায়েত হয়েছে। দূরে দিগন্তরেখায় কালো ধোঁয়ার বৈনাশিক রেখা উঠে গেছে আকাশ পর্যন্ত। পরের দিন গিয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনার অনুপুঙ্খ হয়েছিলাম। ধোঁয়া দেখতে দেখতে শিবাজীদাকে (বন্দ্যোপাধ্যায়) সামনে পেয়ে বলেছিলাম, "দেখলেন তো, জাক দেরিদাকে উদ্বোধনে আনার ফলাফল? পুরো মেলাটাকে ডিকনস্ট্রাক্ট করে চলে গেল।"



 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp