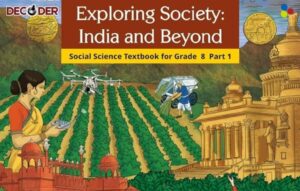বাবুদের শান্তিনিকেতন আসলে বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপ
Shantiniketan: শান্তিনিকেতনের বাবুবিবিদের বাড়িতে কাজের লোক হওয়া ছাড়া তো আর কোনও সম্পৃক্ততা নেই প্রাচীর সংলগ্ন গ্রাম সমূহের আদিবাসী ও সেখানকার কৌমসমাজের মানুষজনের।
জানা গেছে, ১৮৬৩ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন, তার কিছু আগে বর্ধমানের মহারাজা বর্ধমানেই মহর্ষিকে জমি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্ত মহর্ষি ভুবনডাঙায় এসে মন পরিবর্তন করেন। বীরভূম জেলার বোলপুরের এই ভুবনডাঙাতেই স্থাপিত হয় শান্তির আবাস।
এই গ্রামের ভুবন মোহন সিংহ আর রায়পুরের জমিদার এই জমি দেন। এই ভুবন সিংহের ছিল ডাকাতের দল। তিনি মহর্ষির ভক্ত হয়ে যান ও অঞ্চলের উন্নয়নে এগিয়ে আসেন। এই সংস্রব ত্যাগ করার ও হৃদয় পরিবর্তনের গল্প এখনও ইতিহাসের পাতায় পাতায় রয়ে গেছে।
প্রকৃতপক্ষে, এখানকার নির্মল ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ মহর্ষিকে আকৃষ্ট করেছিল। জানি না, হয়তো বীরভূমের জল-মাটি-হাওয়া তথা জলবায়ুর ভিন্ন প্রকৃতিও তাঁকে আকর্ষণ করে থাকতে পারে। তবে আজ সেই প্রাকৃতিক অবস্থার বিরাট রূপান্তর ঘটেছে। দীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বছরের বেশি সময় ধরে সাক্ষী থেকে দেখছি এই ক্রমপরিবর্তনের পালা। এক দিকে উষ্ণায়নের ছায়া যেমন পড়েছে, তেমনই স্থানীয় কুনীতি ও ব্যবসায়িক হানাদারিত্বের মনোভাবও কম ক্ষতি করেনি! সেসব কথায় পরে আসা যাবে। আসলে এখানকার পারিপার্শ্ব সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হবে, এই ঐতিহ্য-আশ্রিত শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী নিয়ে।
প্রাথমিকভাবে দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে একটি ধ্যান কেন্দ্র নির্মাণ করেন। ক্রমে সেখানে তৈরি করান তিরিশ ফুট বাই ষাট ফুট একটি কাঁচের কাঠামো যা লন্ডনের ক্রিস্টাল প্যালেসের অনুকরণে তৈরি। তার এক পাশে একটা ছাতিম গাছের ছায়ায় বসে মহর্ষি ধ্যান করতেন। আর তার আগে উপাসনা গৃহ। কেউ কেউ মন্দির বলে। মন্দির শব্দটি যেভাবে সাধারণের কাছে একটি একমাত্রিক অর্থ প্রতিপন্ন করে, মহর্ষির শান্তিনিকেতন বা রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী কোনও গতানুগতিক অর্থে তা উপস্থাপিত করে না। এই মন্দিরে কোনও দেবদেবী নেই। তাই উপাসনা গৃহ হলো প্রকৃতই অনুষ্ঠানের নিগড়ে বাঁধা এক প্রসন্ন জীবনচর্যায় নিবেদিত উচ্চতর বোধের আন্তরিক সাধনক্ষেত্র। কথাগুলো লিখে রাখছি তার কারণ, এই উপাসনালয় নিয়ে অনেক কথা হয়তো লিখব। এর নিয়মকানুন ও তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রাজনীতির কথা আসবে এই লেখায়। সে কারণেই উল্লেখ থাকল।

আরও পড়ুন- কিংবদন্তি ননী খেপির হারিয়ে যাওয়া, ফিরে আসা…
যেমন উল্লেখ থাক, পরবর্তীতে ১৯০১ সালে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে জনা পাঁচেক ছাত্র (তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সহ) এবং সমান সংখ্যক শিক্ষক নিয়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রাচীন ভারতের অরণ্য আশ্রমের ঐতিহ্য অনুসারে এবং গুরুকুলের ধারণায় প্রাণিত হয়ে পরীক্ষামূলক এই বিদ্যালয়ই ক্রমে বিশ্বভারতী হয়ে উঠবে তাঁর নিজস্ব একান্ত বিশ্বভাবনা ও তত্ত্বাবধানে। এখানে যেমন বিশ্বভ্রাতৃত্বের বোধকে তিনি প্রোথিত করতে চেয়েছিলেন তেমনই শিশুশিক্ষা, প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা এবং ব্যক্তি মনের সংবেদনশীলতাকে গাঢ় করার জন্য শিল্পকলা ও সঙ্গীতকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। বদ্ধ ক্লাসরুম নয়। মুক্ত আকাশের নীচে গাছের তলায় পঠনপাঠনের আয়োজন। তার সঙ্গে আশেপাশের গ্রামগুলোকে যুক্ত করে গ্রামীণ উন্নয়নের ধারাকে নির্দিষ্ট গতিমুখ দেওয়া। অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে বাঁচা ও পল্লীসমাজের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের এক সুনিবিড় বন্ধন তৈরি করা। কার্যত এটাই ছিল শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতীর অন্যতম গতিমুখ।
মানসিক ও বস্তুগত দারিদ্র্য দূর করে ধর্মীয় ও আঞ্চলিক বাধা অতিক্রম করে দর্শন ও ভাষা গবেষণার শ্রীক্ষেত্র হিসেবেও একে গড়তে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন বছরভর অসংখ্য মেলা ও উৎসব। পৌষ মেলা, বসন্ত উৎসব, মাঘোৎসব, হলকর্ষণ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাকার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এক সুনির্দিষ্ট মিলন উৎসবের বার্তা দেওয়া ছিল এর অন্যতম অভিপ্রায়। আসলে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যোগাযোগ সম্ভাবনাকে প্রবল গুরুত্ব দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শেষ পর্যন্ত তার কী গতি হলো, দেখে আজ তাজ্জব হতে হয়!

এখানে একটু ব্যক্তিগত ক'টা কথা লিখে যাই। রবীন্দ্রনাথের ওপর প্রায় বারোটা ছবির সঙ্গে শুধুমাত্র শান্তিনিকেতন নিয়ে একঘণ্টা কুড়ি মিনিট সময়সীমার একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছিলাম প্রায় দেড় দশক আগে। ছবিটি কেন্দ্রীয় সরকার ও বিশ্বভারতীর যৌথ উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল। ফলে বরাত পাওয়া সে ছবিতে অনেক কথা বলা যায়নি। তা ছিল পুরোটাই কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।
আরও পড়ুন- নেশা আর খিস্তির আড়ালে ঢাকা পড়ে গেলেন যে বাউল
এরপর ছবি করতে গিয়ে প্রথমেই যেটা লক্ষ্য করি তা হলো, চারিদিকে উঁচু প্রাচীর দিয়ে শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতীর এলাকা ঘিরে ফেলা হচ্ছে। এই অঞ্চল সন্নিহিত গ্রামীণ মানুষকে বিচ্ছিন্ন করার এ এক ভয়াবহ পরিকল্পনা। এর আরও পরে বিরাট বিরাট লৌহকপাট আর বিস্তর তালাচাবির ঝনঝনানি আমরা শুনতে থাকব। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসাধারণ চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত হব। পথচলতি মানুষকে বাধা দেওয়া ও নিরাপত্তারক্ষী আশ্রিত শাসনতন্ত্রে সেই মুক্ত মনোভাবের শান্তিনিকেতন আশান্তির আবহ তৈরি করছে। গবেষক, পর্যটকেরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ক্রমাগত। তাতে কোনও হেলদোল নেই কর্তৃপক্ষের।
গ্রামীণ জনজীবনের থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ বলে কি এর পরিচয় দেওয়া? কী জানি! শান্তিনিকেতনের বাবুবিবিদের বাড়িতে কাজের লোক হওয়া ছাড়া তো আর কোনও সম্পৃক্ততা নেই প্রাচীর সংলগ্ন গ্রাম সমূহের আদিবাসী ও সেখানকার কৌমসমাজের মানুষজনের। অথচ এর বিপ্রতীপেই আছে সেই শান্তিনিকেতনের ভাবধারা যা গ্রামীণ সমাজকে অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে কাছে টেনে নেওয়ার মূলগত আদর্শে স্থিত। যে আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছিল রামকিঙ্করের দৈনন্দিনতা ও শিল্পে। আরও অনেক ব্যক্তিত্বের কথাও লেখা যাবে পরবর্তীতে। যার শেষ নেই। ভালোমন্দ মিশিয়ে তাহাদের শান্তিনিকেতন। যা আমাদের ফেলে চলে গেছে।




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp