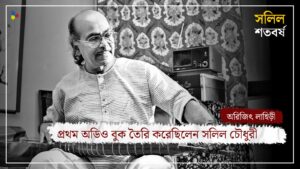ভাষার জন্য আমরা বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারি না?
১৯৩৮ সালের ২৬ জুলাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেলেন দৃষ্টিহীনতার ইতিহাস-লিখিয়ে সুবোধচন্দ্র রায়। তখন তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্র। তাঁর প্রবল আগ্রহ ‘অন্ধ’দের মনস্তত্ত্ব নিয়ে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে ‘অন্ধ’দের যেভাবে চরিত্রায়ণ করা হয় তা হতাশাব্যঞ্জক। সমস্ত ক্ষোভ উগরে দিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথের সামনে। বাংলার কোনো লেখকই ‘স্বাভাবিক’ (normal) ও ‘সফল’ (successful) দৃষ্টিহীনদের ছবি অঙ্কন করেননি এই ছিল তার অভিযোগ। এমনকী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ‘দৃষ্টিদান’ গল্পেরও সমালোচনা করে বসলেন রায়মশাই। ১৮৯৯ সালে ‘ভারতী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ‘দৃষ্টিদান’। সুবোধবাবুর মতে, ‘দৃষ্টিদান’ গল্পটি ‘অন্ধ’দের মনস্তত্ত্বের সঠিক বিচার করতে পারেনি। বিশেষত, কুমু যখন হেমাঙ্গিনীকে বলে: “অন্ধ কিছু ভোলে না বোন; আমার তো জগৎ নাই, আমি কেবল মন লইয়াই আছি।” এই বক্তব্যে সুবোধচন্দ্রের ঘোরতর আপত্তি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, প্রকৃতপক্ষে এই বক্তব্যের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ কী বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁর অভিযোগ ‘অন্ধ ব্যক্তিদের কোনো জগৎ নেই’—এই জাতীয় বাক্যবন্ধ সঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথ খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন সবটুকু। কবি বললেন, কোনো ‘সফল’ ও ‘স্বাভাবিক’ ‘অন্ধ’ ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই তাঁর। কুমুকে তিনি গড়ে তুলেছেন সম্পূর্ণ নিজস্ব অনুভূতি দিয়ে, ‘অন্ধত্বের মনস্তত্ত্ব’ সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা দিয়ে। তখন সুবোধবাবু কয়েকটা ইংরেজি গল্পের কথা বলেন, যেখানে ‘অন্ধ’ চরিত্রগুলো হতাশ নয় এবং আত্মহত্যার কথাও ভাবছে না তাঁরা। পরিবারের সঙ্গে সুস্থ ‘স্বাভাবিক’ একটি জীবন যাপন করছে তাঁরা।
তিনি আরো বলেন, এমন এক ধরনের সাহিত্য লিখতে হবে যেখানে ‘অন্ধত্ব’কে অভিশাপ হিসেবে দেখা হবে না এবং যা পাঠ করে পাঠক জানতে পারবে সমস্ত ‘অন্ধ’ ব্যক্তি ভিক্ষুক নয়, অন্যের ওপর নির্ভরশীল নয়, অসহায় নয়। এই প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথ রাজি হলেন। কবি ‘সফল’ ও ‘স্বাভাবিক’ একজন ‘অন্ধ’ নায়ক বা নায়িকাকে নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক বা উপন্যাস লিখবেন বলে কথা দিলেন। সেদিন সুবোধচন্দ্রের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য যাই থাকুক না কেন, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ‘দৃষ্টিদান’ পড়লে আমরা বুঝতে পারি, ‘কুমু’ চরিত্রটি ভীষণভাবে ‘মানবিক’ এবং ‘বিশেষ সক্ষমতা’র অধিকারী। হেমাঙ্গিনী যখন বাড়িতে এল, কুমু তাকে শয়নকক্ষে নিয়ে গেল। এরপর কুমু ডানহাত দিয়ে হেমাঙ্গিনীর কণ্ঠ বেষ্টন করে বলল, “আমি তোমাকে দেখিতেছি, ভাই।” এই বলে সে হেমাঙ্গিনীর কোমল মুখখানি হাত বুলিয়ে দেখল। অবশেষে কুমুর অনুমান, “মুখটি সুন্দর হইবে, বয়সও চোদ্দপনেরোর কম হইবে না।” অর্থাৎ ‘দেখা’ ক্রিয়াটি কুমু সম্পন্ন করছে স্পর্শের মাধ্যমেই। এইভাবে কুমু তাঁর নিজস্ব জগৎ নির্মাণ করেছে। চক্ষুষ্মানদের কাছে জগতের সংজ্ঞা যা, তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন সে জগৎ। এভাবেই রবীন্দ্রনাথ ‘দৃষ্টিহীন’ কুমুকে ‘দৃষ্টিদান’ করেছেন।
আজকে ভাষা দিবসে একটা প্রশ্ন তোলা দরকার হয়ে পড়েছে, যে প্রশ্নটি শিশুর মতো সরল হয়েও তীক্ষ্ণ এবং সৎ। ‘বিশেষ ভাবে সক্ষম মানুষে’রা যে ভাষা ও সংস্কৃতির ইতিহাস নির্মাণ করেছে তাঁকে কতটুকু মর্যাদা দিয়েছি আমরা, মনে রাখা তো অনেক দূরের কথা। আসলে ‘প্রতিবন্ধী’-কে শুধুমাত্র ‘বিশেষ ভাবে সক্ষম’ অভিধা দিলেই সামাজিক অবজ্ঞার সুরাহা ঘটে যায় না, দরকার রয়েছে তার ভাষা ও সংস্কৃতির জগতটিকে বোঝা। অনুভব করা দৃষ্টিহীনদের কাছে ভাষা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যের পাতায় তুলে এনেছেন এই সংস্কৃতির এক চিত্র। ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত ‘রজনী’ উপন্যাসের ‘নায়িকা’ রজনী।
সমস্ত উপন্যাসটি রজনীরই ভাষ্যে লেখা। সেই যুগে দাঁড়িয়ে একজন ‘জন্মান্ধ’কে নিয়ে একটা আস্ত উপন্যাস লেখা চাট্টিখানি ব্যাপার নয় মোটেই। ‘রজনী’তে আমরা দেখি, আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ বিকশিত হলেও রজনীর সুখ হয় না, সে সুখী হয় জুঁই ফুলের গন্ধে। এমন সৌন্দর্যবোধই তো তাঁর ‘বিশেষ সক্ষমতা’র পরিচায়ক। অথচ ‘বিশেষভাবে সক্ষম’ বাঙালিরা আমাদের তথাকথিত সাংস্কৃতিক ধারণায় সুস্থ, শক্তিশালী, স্বাধীন ও সুন্দর আদর্শ ‘বাঙালি-পরিচিতি’র সঙ্গে খাপ খায় না। সমাজ নির্মিত ‘সুন্দর’-এর প্রতর্কে যেন বাতিল তাঁরা। ফলে এই মানদণ্ড সামাজিকভাবে ‘বিশেষভাবে সক্ষম’দের ওপর আরোপ করেছে ‘মন্দ দেহ’-এর ধারণাটি। ১৮৭৭ সালেই এই তথাকথিত ‘সুন্দর’ ধারণাটিকে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করেছেন বঙ্কিম। তাই উপন্যাসে রজনী বলে ওঠে: “ফুলের স্পর্শ বড় সুন্দর—পরিতে বুঝি বড় সুন্দর হইবে—ঘ্রাণে পরম সুন্দর বটে।”
দৃষ্টিহীনদের ভাষা-সংস্কৃতির প্রতর্কে বলা দরকার বাংলা-ব্রেইল লিপির ইতিহাস, যা শতবর্ষাধিক পুরনো। ‘প্রবাসী’, ‘মডার্ণ রিভিউ’ এবং ‘বিশাল ভারত’ পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৮৯২ সালে প্রথম বাংলা বর্ণমালার ব্রেইল লিপি উদ্ভাবন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যাতে অন্ধ ছেলেমেয়েরা অক্ষর পড়তে পারে সেই উদ্দেশে, ১৮২৪ সালে লুই ব্রেইল ইংরেজি ভাষার বর্ণমালাকে পাঠ করার এক পদ্ধতি নির্মাণ করেন, যেটি ব্রেইল পদ্ধতি নামে পরিচিত। ব্রেইল হল ছয়টি বিন্দুর (⠿) সাহায্যে গঠিত একপ্রকার লিপি। ‘অন্ধেরা’ আঙুল দিয়ে অনুভব করে এগুলো পড়ে থাকে। উনিশ শতকের শেষ দশকে, এদেশে দুটি মাত্র ‘অন্ধ বিদ্যালয়’ ছিল—একটি অমৃতসরে এবং অপরটি মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত পালামকোট্টায়। দুটি বিদ্যালয়ই ব্রিটিশ মিশনারী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত; এবং তাঁরা ঐ সব অঞ্চলের ভাষায় উপযোগী করে ইংরেজি-ব্রেইল পরিবর্তিত করেন। কলকাতায় সেসময় ‘দাসাশ্রম’ নামে একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। এই আশ্রমের পত্রিকা ‘দাসী’। রামানন্দবাবু তার সম্পাদক। ‘দাসী’ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় তিনি অন্ধদের উপযুক্ত শিক্ষাদান বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ইংরেজি ব্রেইল কেমন করে বাংলায় পরিবর্তিত করা যেতে পারে তার সম্পূর্ণ বিবরণ দেন। বাঙালি ‘অন্ধ’দের ভাষা শিক্ষার ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। সেসময় বাংলায় কোনো ‘অন্ধ বিদ্যালয়’ ছিল না। ফলে রামানন্দবাবুর বাংলা-ব্রেইল উদ্ভাবন করা সত্ত্বেও এটা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।
অতঃপর ১৮৯৪ সালে অন্ধদের জন্য ‘কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়’ প্রতিষ্ঠা করেন লালবিহারী শাহ। তিনি রামানন্দবাবুর বাংলা-ব্রেইল সামান্য পরিবর্তন করে নতুন বাংলা-ব্রেইল লিপি প্রস্তুত করেন। ফলে লালবিহারী শাহের কৃতিত্বও কম কিছু নয়। প্রবাসী-সম্পাদক হিসেবে রামানন্দবাবুকে মনে রাখলেও বাংলা-ব্রেইল উদ্ভাবক রামানন্দকে ভুলে গিয়েছিল বাঙালি। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পর বিশ শতকের চারের দশকে এই ইতিহাস পুনরাবিষ্কার হয়। ১৯৪৩ সালে ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পরে আলোড়ন পড়ে যায়। রামানন্দবাবু তখন শয্যাশায়ী। ঐবছর নিখিল ভারত অন্ধ-আলোক-নিকেতনের ছাত্রছাত্রী ও কর্তৃপক্ষ তাঁর সঙ্গে দেখা করে এবং তাঁর এই মহৎ কাজের জন্য সকৃতজ্ঞ ও সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানায়। সেদিন রামানন্দবাবু যেটা চেয়েছিলেন, তা হল ‘বিশেষভাবে সক্ষম’ ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা শিখবে। তাঁরা পড়াশুনার মাধ্যমে অন্ধকার থেকে আলোর জগতে এসে পৌঁছবে। তাঁরা সমাজকে চিনতে শিখবে।
সমাজ নির্মিত ‘মন্দ দেহ’-র প্রতর্কটিকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস অর্জন করবে তাঁরা। সেই চ্যালেঞ্জ জানানোর সাহস ছিল ‘জন্মান্ধ’ কালীচরণ মিলের। সে আশ্বিন তন্তুবায় সম্প্রদায়ভুক্ত। ১৯৩১ সালে ‘তন্তুবায় সমাচার’ পত্রিকা কালীচরণ মিলের কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছে। ১৮৯৬ সালে কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ হাতিবাগান পল্লীতে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম শ্রীযুক্ত হীরালাল মিল। জন্ম থেকেই তিনি অন্ধ ছিলেন। কিন্তু পড়াশুনায় কালীচরণের প্রবল উৎসাহ। তাঁর গীতা মুখস্থ, সামবেদ পড়েছেন, ব্যাকরণ পড়েছেন। এমনকি তাঁর কবিত্ব প্রতিভা দেখে ভাটপাড়ার পণ্ডিতসমাজ তাঁকে ‘কালীচরণ শাস্ত্রী’— এই উপাধিতে ভূষিত করেন। পরবর্তীকালে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পুরাণদাস সপ্ততীর্থের সঙ্গে তাঁর দেখা হলে, তিনি তাঁকে সংস্কৃত পরীক্ষা দিতে উপযোগী করান। গবর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপাল সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুরের অনুমতি পেয়ে কালীচরণের পরীক্ষা নেন। পরীক্ষকের তরফ থেকে একজন লেখক দেওয়া হয়েছিল। তখন অর্থাৎ ১৯১৯ সালে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষায় জন্মান্ধ কালীচরণ প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং বৃত্তিলাভ করেন। এই ইতিহাস অভাবনীয়। প্রথমত এক তন্তুবায় সম্প্রদায়ের ছেলে, অর্থাৎ এক ‘দলিত’ ছেলে ‘শাস্ত্রী’ উপাধী পাচ্ছে, দ্বিতীয়ত এক ‘জন্মান্ধ’ ব্যক্তি সকল ‘চক্ষুষ্মান’দের পরাজিত করে সংস্কৃত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করছে এবং বৃত্তিলাভ করছে।
পরবর্তীকালে সমাজনির্মিত তথাকথিত ‘মন্দ দেহ’-কেই ভাষাপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম বানিয়ে তুলেছে আধুনিক ‘বিশেষভাবে সক্ষম’ পড়ুয়ারা। ‘মূক ও বধির’রা সৃষ্টি করেছে ‘সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ’। সেখানে ‘দেহ’ই একটি ভাবপ্রকাশক ‘শব্দসমষ্টি’। কলকাতায় ‘সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ’ নিয়ে আলোচনা চলছে বিশ শতকের কুড়ির দশক থেকেই। ১৯২৮ সালে ‘ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ সাইকোলজি’ পত্রিকায় এইচ. সি. ব্যানার্জি নামে এক স্কুল-শিক্ষিকা একটি নিবন্ধ লিখলেন—‘দ্য সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ডীফ-মিউটস’। তিনি ঢাকা, বরিশাল এবং কলকাতার আবাসিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখলেন, প্রত্যেক বিদ্যালয়েই শিক্ষকেরা ‘সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ’-এর প্রতি অনুৎসাহিত। আসলে শিক্ষকদের সঠিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না সেসময়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ‘সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ’-এর প্রতি আগ্রহ ক্রমেই বেড়ে চলেছে।
উল্লেখ্য ১৮৯২ সালে বাবু গিরিন্দ্রনাথ বোস উইলিয়াম ভন প্রাগের কাছে আবেদন জানান যে, তিনি ‘মূক ও বধির’দের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করতে চান। উইলিয়াম ভন প্রাগ ছিলেন লণ্ডনের ‘স্কুল অ্যান্ড ট্রেনিং কলেজ ফর টিচারস অফ দ্য অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য ওরাল ইনস্ট্রাকশন অফ দ্য ডীফ অ্যান্ড ডাম্ব’-এর পরিচালক। দুজন বাঙালিকে লণ্ডনে পাঠানো হয়। কিভাবে মূক ও বধিরদের শিক্ষা দান করা যেতে পারে সেই প্রশিক্ষণ নিয়ে তাঁরা ফিরলেন। অতঃপর ১৮৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘কলিকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয়’। সেসময় বিভিন্ন অভিজাত পরিবার এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে পূর্ণ সমর্থন করেছিল। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই আজীবন সদস্য ছিলেন মহীশূরের মহারাজা বাহাদুর, পাটনা শহরের নবাব সয়ীদ বাদশা, কোচবিহারের মহারাজা, ত্রিপুরার মহারাজা ইত্যাদি গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। এখানে ঠাকুরবাড়ির একটা বড় ভূমিকা ছিল। মহারাজা বাহাদুর স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে ব্যাপক সহযোগিতা করেছিলেন।
‘বিশেষভাবে সক্ষম’দের প্রকৃত সমজদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো বটেই। তাই তিনি ‘সুভা’র মতো গল্প লিখতে পেরেছেন। ‘সাধনা’ পত্রিকায় ১৮৯০ সালে গল্পটি প্রকাশিত হয়। গল্পের নায়িকা সুভা কথা বলতে পারে না। কিন্তু তাতে কোনো সমস্যা হয় না তাঁর। রবীন্দ্রনাথ বলেন: “যে কথা কয় না সে যে অনুভব করে ইহা সকলের মনে হয় না, এইজন্য তাহার সাক্ষাতেই সকলে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা করিত। সে যে বিধাতার অভিশাপস্বরূপে তাহার পিতৃগৃহে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে এ কথা সে শিশুকাল হইতে বুঝিয়া লইয়াছিল।” সুভার কথা ছিল না, কিন্তু তার সুদীর্ঘ পল্লব বিশিষ্ট বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ ছিল এবং তার ‘ওষ্ঠাধর’ ভাবের আভাসমাত্রে কচি কিশলয়ের মতো কাঁপিয়া উঠিত। সে ছিল নির্জন দ্বিপ্রহরের মতো শব্দহীন ও সঙ্গীহীন। তবে সুভার যে গুটিকতক অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল ছিল। তাঁদের নাম—সর্বশী ও পাঙ্গুলী। না, এরা মানুষ নয়। এরা গোয়ালের দুটি গাভী। গাভীদুটি সুভার পদশব্দ চিনত—তাঁর কথাহীন একটা করুণ সুর ছিল, তার মর্ম তারা ভাষার অপেক্ষা সহজে বুঝত। সুভা কখন তাদের আদর করছে, কখন ভর্ৎসনা করছে, কখন মিনতি করছে, তা তারা মানুষের অপেক্ষা ভালো বুঝতে পারত। কবি তাই বলছেন: “কথায় আমরা যে ভাব প্রকাশ করি সেটা আমাদিগকে অনেকটা নিজের চেষ্টায় গড়িয়া লইতে হয়, কতকটা তর্জমা করার মতো; সকল সময়ে ঠিক হয় না, ক্ষমতা অভাবে অনেক সময়ে ভুলও হয়। কিন্তু, কালো চোখকে কিছু তর্জমা করিতে হয় না।”
গল্পের শেষে গিয়ে দেখা যায় ‘সুভা’কে তাঁর মা বাবা কলকাতায় গিয়ে এক পাত্র দেখে বিয়ে দিয়ে দিলেন জাতি কূল মান বাঁচাতে। কিন্তু পাত্র যখন জানল সুভা বধির, সুভা বেচারা বেকায়দায় পড়ে গেল। “সে চারিদিকে চায়—ভাষা পায় না—যাহারা বোবার ভাষা বুঝিত সেই আজন্ম পরিচিত মুখগুলি দেখিতে পায় না।” অবশেষে আমাদের নিজের কাছে একটি প্রশ্ন থাকবে, যে ভাষা দুটি গাভী বুঝে নিতে পারে, তা মানুষের বোধগম্য হয় না! ‘সুভা’রা অসহায়, নাকি সত্যিকারের অসহায় সেইসব মানুষগুলো যারা সুভার ভাষা বুঝতে পারেনি কখনো? আজ ভাষাদিবসের সকালে আসুন না আমরাও ভালোবেসে ‘বিশেষভাবে সক্ষম’ মানুষের ভাষা শিখে নেওয়ার শপথ নিই। যার বলে বলীয়ান হয়ে আমরাও হয়ে উঠব, সত্যিকারের ‘বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন’।




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp