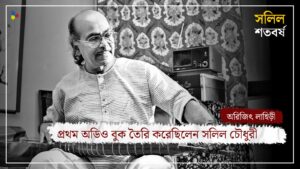স্বাধীনতার পর বাঙালির চরিত্র কীভাবে পাল্টে গেল, লিখে রেখেছিলেন মতি নন্দী
Moti Nandi: স্বাধীনতা-পরবর্তী বিভিন্ন দশকে বাঙালি সমাজ ও শহর কলকাতা কীভাবে তার চরিত্র বদলেছে, মতি নন্দীর গল্পের ধারা অনুসরণ করলে তার রূপরেখা বুঝে নেওয়া সম্ভব।
''চেনা পরিবেশ নিয়ে লিখতে আমি নিজেকে বিশ্বস্ত অনুভব করি। এমনিতে উত্তর কলকাতার ভাঁড়ারে প্রচুর গল্পের উপাদান। বিচিত্র মানুষজন, জীবনযাপন। গলি, রাস্তাও যেন এক একটা ক্যারেক্টার।''
একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর অদম্য কলকাতা-অবসেশন নিয়ে এমনটাই জানিয়েছিলেন মতি নন্দী৷ স্বাভাবিকভাবেই পালটা প্রশ্ন ধেয়ে এসেছিল— আচ্ছা, লিখতে বসে একই পটভূমিকে বারবার স্থাপনের সময় পাঠকের আনুকূল্য কিংবা মনোযোগ হারানোর ভয় কাজ করে না? একটু থেমে মতির জবাবও ছিল অব্যর্থ— ''...পরিবেশ এক হলেও আমার সব গল্প কিন্তু আলাদা। মানুষগুলোর ক্রাইসিস ভিন্ন। আপনি গল্প পড়তে চান, পরিবেশে অত নজর না দিয়ে গল্পটাই পড়ুন।''
পটভূমিকে অগ্রাহ্য করার নিদান দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু প্রশ্ন তো উঠবেই— মতি নন্দীর গল্পে কলকাতার প্রচণ্ড উপস্থিতিকে উপেক্ষা করা কি আদতে রসভঙ্গের সামিল নয়? ডিকেন্সের আখ্যানে যেমন লন্ডন, গিনসবার্গের কবিতায় যেমন নিউইয়র্ক বিশেষ মাত্রা নিয়ে উপস্থিত, মতির গল্প-উপন্যাসে কলকাতার তাৎপর্যও ঠিক ততটাই! শহরের স্থানিক বৈশিষ্ট্য, রাস্তাঘাটের ব্যস্ততা, গলির বিবর্ণতা তুলে ধরে কখনও সমবেত জনতার ঔদাসীন্যের ওপর আলো ফেলতে চেয়েছেন তিনি, কখনও ভিড়ে মিশে থাকা ব্যক্তিমানুষের জীবনদর্শনকে গল্পের বিষয় করে তুলেছেন। হয়তো এ কারণেই পূর্ণেন্দু পত্রীর মনে হয়েছিল, মতি নন্দীর গল্পে নায়ক-নায়িকাদের পাশাপাশি উত্তর কলকাতার কানাগলিগুলি 'সহ-নায়কের মতো তাৎপর্যময় এক ভূমিকা'-র দাবি রাখে। অতিরঞ্জন নয়। বাস্তব বর্ণনার গুণে ইঁট-কাঠ-পাথরের শহরকে প্রবলভাবে জীবন্ত তুলে ধরছিলেন মতি, তাকে নিছক প্রতীকায়িত করেননি। মতি নন্দীর কলকাতা সাহিত্যিক দেবেশ রায়ের ভাষায়— 'প্রতীকহীন, রূপকহীন, শুধুই বাস্তব'।
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দ্বিতীয় ইনিংসের পর, সহদেবের তাজমহল, নারান-এর মতো উপন্যাসে লেখক ভারতের অন্যান্য অঞ্চল কিংবা কলকাতার নিকটবর্তী গ্রামকে পটভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছেন। কিন্তু ছোটোগল্প লিখতে বসে কলকাতার পরিসর ছেড়ে এক পা বেরোননি। একটি সাক্ষাৎকারে মতি নন্দী বলেছিলেন,
''শুধু শ্রেণি নিয়েই গল্প-উপন্যাস হয় না। মধ্যবিত্তরা একটা শ্রেণি হতে পারে, কিন্তু তা অজস্র রকমের মানুষে আকীর্ণ। মানুষটাই আসল।''
অর্থাৎ, মতি নন্দীর আখ্যানের বিন্যাস শ্রেণি থেকে ব্যক্তিতে নয়, ব্যক্তি থেকে শ্রেণিতে। আর এই সূত্রেই কলকাতার একটি বিশেষ ভৌগোলিক ও সামাজিক চেহারা মতি নন্দীর ছোটোগল্পে মূর্ত হয়েছে।
উত্তর কলকাতার গলিজীবনের সার্থক রূপকার তিনি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় গল্পের পুঁজি সংগ্রহ করেছিলেন। তাই জীবনের প্রায় পঞ্চাশ বছর কাটিয়েছেন যে তারক চ্যাটার্জি লেনে, উত্তর কলকাতার সেই গলি ও সেখানকার জীবন তাঁকে অসংখ্য আখ্যানের রসদ জুগিয়েছে। গলিকেন্দ্রিক লেখাগুলি কোন রসায়নে তৈরি হয়েছে তা লেখক নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন—
''... ওই গলির চরিত্রগুলোকে আমি কাছ থেকে দেখেছি। ওদের নিয়ে লিখতে বসলেই দেখেছি, বেরিয়ে আসে এমন একটা গল্প, যাতে আছে আমার অনুভূতি আর স্পন্দন।… কী ঘটবে, সে সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা তো থাকেই। হয়তো সেটা একটা সাধারণ ঘটনা। নিজে দেখেছি, অথবা কারও কাছ থেকে শোনা। সেটাই মনের মধ্যে ঘুরতে থাকে। ভাবি, এই ঘটনাটাই যদি তারক চ্যাটার্জি লেনে ঘটত, তাহলে আমার দেখা চরিত্রগুলো কীভাবে রিঅ্যাক্ট করত? এটা ভাবলেই লেখা তরতর করে এগিয়ে যায়।"
উত্তর কলকাতার অপ্রশস্ত গলি, বাজারহাট, রাস্তাঘাট বর্ণনার ক্ষেত্রে মতি নন্দী মাঝেমধ্যেই উপমা, চিত্রকল্পের আশ্রয় নিয়েছেন। লেখকজীবনের গোড়ার দিকের জনপ্রিয় গল্প 'বেহুলার ভেলা'। সেখানে শোভাবাজার অঞ্চলের বাজারের প্রবেশপথ প্রমথর চোখে ধরা দেয় এভাবে—
''ডাব বোঝাই একটা ঠেলাগাড়ি পথ জুড়ে মাল খালাস করছে, চারধারে যেন কাটামুণ্ডুর ছড়াছড়ি। তার ওপর আস্তাকুঁড়টাও জিনিসপত্রের দামের মতো বেড়ে এসেছে গেট পর্যন্ত।"
অবিন্যস্ত, ঘিঞ্জি পরিবেশের সঙ্গে এভাবেই বাজার অর্থনীতি ও মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গ জুড়ে যায়। কিংবা ''হাড়গোড়সার ছেলের হাত-পায়ের মতোই ন্যাতানো গলিটা। হল্কা বাতাস পর্যন্ত স্যাঁতসেঁতিয়ে যায়। এ গলিতে ঢুকলে গায়ে চিটচিটে ঘাম হয়।''— গলির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের পাশাপাশি জীবন্ত হয়ে ওঠে বসবাসকারী মানুষদের শারীরিক, মানসিক অপুষ্টি ও দৈন্যের দৃশ্য।
আরও পড়ুন- রোগে অনটনে জেরবার! চাকরি চেয়ে যে অবাক করা চিঠি লিখেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়…
মধ্যবিত্ত শ্রেণির নানান স্তর এই গলিতে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে বেঁচে থাকে। বিত্ত, রুচি তৈরি করে অনিবার্য বিভাজনরেখা। নিম্নমধ্যবিত্ত প্রমথ মাংস কিনে ফেরার পথে মনেপ্রাণে চায় বিত্তবান মিহিরবাবু কিংবা উকিলবাবুর পরিবার যেন তার মাংসের ঠোঙার দিকে তাকায়, তাকিয়ে ঈর্ষা অনুভব করে। আবার সেই প্রমথই তাঁর স্ত্রী অমিয়ার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে ''উকিলবাবুর ছেলেদের নামগুলো বেশ''— চিন্তা করে ঈর্ষান্বিত হয়। দু'টি আলাদা আর্থিক স্তরের মানুষের দ্বন্দ্বের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় ধর্মঘট, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে মিহিরবাবুর সঙ্গে প্রমথর তর্ক-বিতর্কে।

বদ্ধ গলিতে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তার পরিবারকে নিয়ে বেঁচে থাকে প্রমথ। সে বাকি পাঁচজনের যন্ত্রণাটা বোঝে। মেয়ে পুতুলকে দেখে তার দুঃখ হয়— ''...এইটুকু তো বয়েস, খাঁচার মতো ঘরে কতক্ষণ আর আটকা থাকতে মন চায়।'' ছেলে খোকনকে রাস্তায় খেলে বেড়াতে দেখে সে চিন্তা করে— ''...থাক, এখন বাড়ি গিয়েই বা করবে কি। তাছাড়া, ঘুপচি ঘরের মধ্যে আটকা থাকতেই বা চাইবে কেন।'' ধীরে ধীরে প্রমথর পারিবারিক দুরবস্থার সঙ্গে এক হয়ে গেছে শহর কলকাতার সমূহ দুর্দশা— ''প্রমথ কাঁদুনে গ্যাসের শেল ফাটতে দেখেছে এই সেদিন, অনেকের সঙ্গে সেও রুদ্ধশ্বাসে ছুটেছে, ঘোড়সোয়ার পুলিসের নাগাল ছাড়িয়েও ছুটেছে। তাই সে বোঝে অমিয়ার অবস্থাটা, যখন উনুনে আগুন পড়ে। কোথায় পালাবে সে ওইটুকু বাড়ির চৌহদ্দি ছাড়িয়ে? যেখানেই যাক না, ধোঁয়া তাকে খেতে হবেই, ওই সময়টায় সকলেই উনুন ধরায়।'' প্রমথ জানে, গোটা কলকাতার পরিস্থিতি হুবহু এই গলির মতো। সর্বত্র আগুন জ্বলছে, সর্বত্র অস্তিত্বের সংকট। 'বেহুলার ভেলা' একটি বিশেষ গলির দমচাপা জীবনের গল্প হয়েও ছয়ের দশকের কলকাতার জীবনযন্ত্রণাকে স্পর্শ করেছে।
বদ্ধ ডোবা বা পানাপুকুর। তাতে ভেসে বেড়ানো পাতিহাঁস, শ্যাওলা, কাদা, পাঁক ইত্যাদি চিত্রকল্পে গলির অবরুদ্ধ জীবনের চেনা ছবি প্রকাশিত হয়েছে 'চোরা ঢেউ' গল্পে। গল্পের শুরুই হচ্ছে— ''মেজ-জেঠিমারা উঠে যাচ্ছে বস্তিতে।" পাড়ার জনপ্রিয় চরিত্র মেজ-জেঠিমা। অর্থাভাবে তাঁকে তথাকথিত নিচুস্তরের জীবনে 'নেমে যেতে' হয়েছিল। 'উঠে যাচ্ছে' শব্দবন্ধে সেই তথ্যগোপনের প্রচেষ্টায় মেজ-জেঠিমার অবনমনের রূঢ়তা প্রকট।
''দুটো ঠেলাগাড়িতে রংচটা তোবড়ানো ট্রাঙ্ক, ছেঁড়া তোশক, তক্তাপোশ, পুরানো জুতো আর ঘুঁটে সামনে রেখে মেজ-জেঠিমার রিকশাটা কর্পোরেশনের জলমিস্ত্রিদের গর্ত-বোজানো গলিটায় টালমাটাল হতে হতে হুশ করে বেরিয়ে গেল বড়ো রাস্তার স্রোতে।''
একদিকে 'রংচটা', 'তোবড়ানো', 'ছেঁড়া' এবং 'টালমাটাল' শব্দস্রোত যেমন মহিলার বিবর্ণ এবং দুর্দশাগ্রস্ত ভবিতব্যের প্রতীক, তেমনই 'গর্ত-বোজানো গলি'-র উল্লেখে গলিনিবাসী জনগণের দুর্দশা চেপে রাখার কৌশলটিও আর গোপন থাকে না। এই কর্কশ বিবরণের পরেই লেখক মোক্ষম চিত্রকল্পের আশ্রয় নেন— ''তারপরই যেন বদ্ধ ডোবার থসথসে পাঁকে নদর গদর করতে করতে কতকগুলো পাতিহাঁস নেমে পড়ল। তাদের ঠোঁটের খোঁচায় অনেক কালের জমা বাতাস উঠে এল কাদার তল থেকে।"
এমন 'ইমেজ' গল্পে একাধিকবার এসেছে। পাড়ায় নতুন আসা তরুণ দম্পতি যখন একসঙ্গে গলা ছেড়ে গান গাইতে থাকে, তখন অনিবার্যভাবে সেদিনের 'সন্ধ্যাটা পুরুষছোঁয়া কিশোরীর মতো শিউরে' ওঠে আর 'ডোবার জলে দু-জোড়া রাজহাঁস পাখার ঝাপটে চারপাশের নোনাধরা দেয়ালে অবাকের পলেস্তরা' ধরায়। নবদম্পতির আগমনে সেই নিস্তরঙ্গ পানাপুকুরের মতো বদ্ধ গলিতে হঠাৎ চাঞ্চল্য দেখা দেয়। সকলে চোখ ফেরায় নিজেদের অতীত অথবা মনের গোপন ইচ্ছেটুকুর দিকে— বন্ধ্যা জীবনের গতানুগতিকতায় যা এতকাল চাপা পড়ে ছিল। নবাগত পরিবারের হারমোনিয়াম, আয়না, রজনীগন্ধার মালা কিংবা তাদের সাজসজ্জার ধরন গলির আর পাঁচটা মেয়েদের প্রভাবিত করে। ধীরে ধীরে তারা রোজকার জীবনে বদল আনতে চায়। তাদের দেখাদেখি স্বাস্থ্যচেতনা, গৃহসজ্জা বিষয়ে সকলে সচেতন হয়ে ওঠে। বুল্টা জেদ ধরে তাকে শাড়ি কিনে দিতে হবে। নতুন বউ ধুলোধূসরিত হারমোনিয়াম নিয়ে গান গাইতে বসার পরিকল্পনা শুরু করে। কিছুদিন বাদে যখন সেই 'এক জোড়া রাজহাঁস ডোবার জল ঘুলিয়ে, পানা কেটে, সাঁতরে ফিরে যায়' এবং তাদের বাসায় 'তেল-চিটচিটে বালিশ, কলাইচটা থালা আর কয়লার থলি জড়াজড়ি করে' এসে পৌঁছোয় তখন পাড়ার ভানুদি বলে ওঠেন— ''কী নোংরা বাপু। আগের ওরা কী সাজানো পরিপাটিই না ছিল!'' অর্থাৎ, বুঝতে অসুবিধে থাকে না, বদ্ধ গলির বাসিন্দাদের আত্মদর্শনের প্রক্রিয়া আপাতত সম্পূর্ণ হয়েছে। সময় সেখানে ছিল স্তব্ধ হয়ে। রুচির বিকাশের কোনও চল ছিল না। কাদা বা পাঁক রূপে প্রতীকায়িত কেচ্ছাকাহিনিতেই সকলে মজে থাকতে চাইত। নবদম্পতির আসা-যাওয়ার ঘাত-প্রতিঘাতে এই মালিন্য, স্থবিরতা ঘুচে যায়।
'নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থানে' এই সমস্যা আরও গভীর। গল্পের শুরুতে একটি ধূসর অ্যাম্বাসাডার 'সাত হাত চওড়া' ঘোষপাড়া লেনে প্রবেশ করতে না পারলে পাড়ার বাসিন্দা ফ্যালার ইচ্ছে করে 'হারকিউলিস হয়ে দু-হাতের চাড়ে বাড়িগুলোকে ঠেলে, জায়গাটাকে সতেরো করে দিতে।' এরপর এই সংকুচিত পরিসরে গজিয়ে ওঠা জীর্ণ বাড়িঘরের বর্ণনায় উপমা প্রয়োগে লেখক গলির জ্যামিতি ছাপিয়ে জৈব স্বরূপ তুলে ধরেন—
''বাড়িগুলো কলিচটা; বালি বেরিয়ে পাণ্ডুর বর্ণ। ওর মধ্যেই কালীবাবুর বাড়িটা সদ্য কলি ফেরানো, ফলে মনে হয় গলিটার শ্বেতী হয়েছে।… জানালাগুলো লটপটে বুকপকেটের থেকেও অর্থহীন, ঝড়বৃষ্টিতে কাজে আসে না। গলিতে দাঁড়িয়ে আকাশে তাকালে প্রথমেই মনে হবে, চিরকুট শাড়ি ফেঁসে গিয়ে বিব্রত কোনো গৌরাঙ্গীর দেহ।"
এই শীর্ণ গলিতেই বিভিন্ন পরিবারের সমস্যা, ব্যক্তিমানুষের জীবনযন্ত্রণাকে টুকরো টুকরো পর্বের আকারে লেখক তুলে ধরেন। অনন্ত সিংগী আর বাসুদেব নাগের মধ্যে টিউবওয়েল বসানো, মোটরগাড়ি রাখাকে কেন্দ্র করে ঝগড়া বেঁধে যায়। কালীবাবু একদিকে তাঁর জামাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন— ''শুধু শিক্ষা, কালচার দিয়ে একটা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। এজন্য দরকার ডিক্টেটার। চাবুক হাতে দেশকে শাসন করতে হয়।'' অন্যদিকে তিনিই বাড়ির ঝি আঙুরকে 'কমপক্ষে চার মাস স্পর্শ করা হয়নি' ভেবে বিছানায় গা এলিয়ে দেন। চাকুরিজীবী রবীন যেমন তার স্ত্রীর কাছে খোঁজ নেয় ''যে-লোকটা বরাবর বাসে ওদের পিছনে দাঁড়িয়েছিল তার স্বভাবটা কেমন?'', সে-ই কিনা একদিন পরস্ত্রী পারুলের সঙ্গে অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত হয় আর 'ঠিক সেই সময়েই, ঘোষপাড়া লেনে দপ করে অন্ধকার' নামে। হঠাৎ অন্ধকার নামার ঘটনা গল্পে প্রায় ধ্রুবপদের মতো পুনরাবৃত্ত হয়। অন্ধকারের আড়ালেই গলিনিবাসীদের আদিম প্রবৃত্তির নখ-দাঁত বের করা চেহারা প্রকট হয়ে ওঠে। এই পরিবেশ কোনও কোনও বাসিন্দাদের মনে ক্রোধের জন্ম দেয়। তাই সত্যচরণ তেইশ নম্বরের ভাঙা ট্যাঙ্কের পাশে অশ্বত্থ গাছটা 'বাড়তে' চাইলেই 'লাঠি পিটিয়ে' তার ডালগুলো ভেঙে দেয়, ফ্যালা আপনমনে বিড়বিড় করে— ''শালার বাড়িগুলো ভেঙে না পড়লে আর গলি চওড়া হবে না।''
গলি বা পাড়ায় বিচিত্র মানসিকতার একত্র সহবাসের পাশাপাশি অন্য আরেকটি নাগরিক জীবনরূপ মতি নন্দীর গল্পে প্রায়শই ঘুরেফিরে আসে। সেটা হচ্ছ— বাড়িওয়ালা-ভাড়াটিয়ার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। আর এই সংঘাতের সূত্রে কলকাতার কিছু পরিচিত সংকট একাধিক আখ্যানে জায়গা করে নেয়, যার একটি জল সরবরাহের সমস্যা। 'উৎসবের ছায়ায়' গল্পে ভাড়াটিয়া মন্মথ রাত্রিবেলা কাজ থেকে ফিরে শৌচকর্মের জন্য ন্যূনতম জল পায় না কারণ 'কলঘর বাড়িওয়ালার এক্তিয়ারে'। শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় মতি নন্দীর গল্প সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন—
''চিরাচরিত নিয়মে মতি সমস্যার মাঝখানে ঢুকে গল্প শুরু করে। একটা দৃশ্য বা একটা সংলাপ। একটা ফাটল তৈরি করে। তারপর সেই ফাটলের ফাঁক দিয়ে দিয়ে গভীরে ঢোকে।''
'জলের ঘূর্ণি ও বকবক শব্দ' এর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এ গল্পেরও আলম্বন জলসংকট। সেখানে 'তিনটি পরিবারের জন্য উঠোনে এজমালি একটি জলের কল।' জলের দখল নিয়ে বাকিদের স্বার্থপরতা পূর্ণিমাকে রাগিয়ে তুললে স্বামী বিশ্বনাথ তাকে শান্ত করে এই বলে—''কলকাতার জলের অবস্থাটা আগে বোঝ। কল দিয়ে বেরোবার জন্য জলটা কোথায়? জল দেবে কর্পোরেশন, বাড়িওয়ালা তো নয়।'' কিন্তু স্রেফ এই সমস্যার কথা বলা তো লেখকের অন্বিষ্ট নয়। তাই তিনি দেখান কীভাবে এক সময় এই জলের সংকটই ঘটনাচক্রে পূর্ণিমাকে ভয়াবহ ও জটিল আত্মসংকটের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়। ক্ষমতার নোংরা অপব্যবহার ও আত্মসমর্পণের রূপও এই প্রসঙ্গে নজরে আসে। 'নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান' গল্পে পারুল তার মতোই আরেক ভাড়াটিয়া রবীনের কথার প্রতিবাদ করতে পারে না। কারণ গোটা বাড়ির ছাদ ব্যবহারের একমাত্র অধিকারী রবীনের পরিবার, যেহেতু তারা ভাড়া বেশি দেয়। ইচ্ছে করলেই তারা ''যে-কোনো মুহূর্তে একতলার লোকদের ছাদে যাওয়া বন্ধ করে দিতে পারে।'' 'শবাগার' গল্পে ভাড়াটিয়া শিপ্রা বাড়িওয়ালা মুকুন্দর লালসার শিকার হয়। বাড়িওয়ালা-ভাড়াটিয়ার নেপথ্যে শোষক ও শোষিতের এই স্বরূপ উপস্থাপনের মধ্যমে লেখক কলকাতার সামাজিক শোষণের একটি বিশেষ চরিত্র নির্মাণ করেছেন।
মহানগরের বাস্তব চেহারা আর জীবনের বাস্তবতা কোথাও গিয়ে যেন এক হয়ে গিয়েছে 'শহরে আসা' গল্পে। যেখানে শহর কলকাতাকে এক নিম্নমধ্যবিত্ত খেটেখাওয়া মানুষ দুলালের চোখ দিয়ে দেখানো হয়েছে। শহর ছাড়িয়ে গ্রামে তার বাস। বৃদ্ধ বয়সে বছর সতেরোর গিরিবালার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। পেশায় দর্জি দুলাল একদিন পাঁচ টাকা উপরি পেয়ে স্ত্রীকে 'শহর দেখাতে' আনে। হাওড়া স্টেশনে নেমেই দুলাল প্রাণপণ চেষ্টা করে তার গ্রাম্য সত্তাটিকে চাপা দিয়ে কলকাতার সঙ্গে তার নিবিড় সখ্যের সম্পর্ককে বিস্মিত স্ত্রীর সামনে তুলে ধরতে। এর জন্য কখনো-কখনো মিথ্যের আশ্রয়ও নিতে হয়। তার গর্বিত স্বরূপ ছলনার আশ্রয়ে প্রকাশিত হয় এভাবে—''বিদেশিকে নিজের সাম্রাজ্য দেখাবার ভঙ্গিতে দুলাল আঙুল দিয়ে গঙ্গার ওপারে উঁচু একটা বাড়ি দেখিয়ে বলল, ওটা বিশতলা। আমি একবার উপরতলায় উঠেছিলুম।''
আরও পড়ুন- যৌন জটিলতাও হয়ে উঠেছিল স্নিগ্ধ! নজরুলের যে গল্পের হদিশ আজও জানেন না পাঠক
গিরিবালার বিস্ময় এবং দুলালের ভ্রান্ত অহংবোধ আরোপিত হয়েছে কলকাতার বর্ণনায়। গল্পে 'উচ্চতা'-র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উচ্চতা সম্ভ্রম জাগায়। হাওড়া ব্রিজ, বিশতলা বিল্ডিং, দোতলা বাস (লক্ষ্যণীয়, দুলাল তার স্ত্রীকে নিয়ে বাসের ওপরতলায় বসে), পোল এবং পোলের আলো দেখিয়ে দুলাল তার স্ত্রীর চোখে আসলে সেই সম্ভ্রমের ছাপ খুঁজতে চায়। গিরিবালার মননে এই উঁচু স্মারকগুলি কলকাতার প্রাথমিক পরিচয় গড়ে তোলে। তার বিস্ময় জাগে। যা দেখে কলকাতাকে এতক্ষণ ধরে নিজের চিরপরিচিত শহর হিসেবে দাবি করা দুলালের অস্মিতা তৃপ্ত হয়। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে স্বামী-স্ত্রী হাওড়া পেরিয়ে যত ব্যস্ত কলকাতার মধ্যে প্রবেশ করে, বিস্ময়ের পাশাপাশি তাদের গ্রাস করতে থাকে ভয়। অফিসপাড়া ডালহৌসি ও ধর্মতলার জনাকীর্ণ রাজপথের ভিড়ে গিরিকে হঠাৎ হারিয়ে ফেলে দুলালের ঠকঠক করে কাঁপতে থাকা কিংবা লোকভরতি বাসে গিরির সম্ভ্রমরক্ষার চিন্তায় তার চিন্তিত হয়ে পড়া আসলে এক নির্মোক-খসে-পড়া গ্রামীণ সাদাসিধে মানুষের সত্তায় নাগরিক আগ্রাসনের দ্যোতক। উঁচু ইমারতের শহর, ব্যস্ততার শহর হিসেবে লেখক কলকাতার একটি প্রচলিত মূর্তিকে এখানে দাঁড় করিয়েছেন।
যদিও পাশাপাশি এই নির্মম, যান্ত্রিক শহরের বিপরীত ছবি ফুটে উঠেছে রাইদার সঙ্গে দুলালের সাক্ষাতের দৃশ্যে। যুদ্ধের আগে তারা একসঙ্গে শিয়ালদার একটি মেসে কাজ করত। দুলাল রাইদার কাছে পেয়েছিল ভাইয়ের স্নেহ। কিন্তু অনেককাল আগে রাইমোহনের কাছ থেকে দু-টাকা ধার নিয়েও সে ফেরত দেয়নি। এতদিন পর দেখা করতে এসে দুলালের মনে এই চিন্তার কাঁটা খচখচ করতে থাকে। গল্পের শেষে রাইমোহন নববধূ গিরিবালাকে যখন প্লাস্টিকের সিঁদুর কৌটো দিয়ে আশীর্বাদ করেন, তখন ''আপনা থেকেই দুলালের হাত পকেটে চলে গেল। নোট দুটো এগিয়ে দিয়ে বলল, রাইদা এই নাও।'' অন্যদিকে গিরি আশীর্বাদের বস্তুটি গ্রহণ করার সময় রাইমোহনের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকে 'যেন হাওড়া ব্রিজ বা সেই বিশতলা বাড়িটা দেখছে।' তাৎপর্যপূর্ণভাবে ফের একবার লেখক 'উচ্চতা'র অনুষঙ্গকে হাজির করেন। এতক্ষণ শহরের যে-স্থাপত্যসূচক নিশানগুলি দেখে গ্রাম্য নববধূটি হতভম্ব ও হতচকিত হয়ে উঠছিল, সে এবার বিস্মিত হয় স্নেহের একটি সুউচ্চ মানবিক প্রকাশ লক্ষ্য করে। সারাদিন রাজপথ ঘুরে যে-শহর গিরিবালার চোখে ধরা দিয়েছিল, তা ছিল মুখর। কিন্তু হাঁফধরা জনস্রোতে সে প্রাণের আরাম পায়নি। অথচ শেষপর্যন্ত 'ট্রামরাস্তার ধারের চায়ের দোকানে' শহরের একটি ক্ষমাসুন্দর মুখ তার সামনে ভেসে ওঠে, যার দিকে তাকিয়ে শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে নত হওয়া যায়।
গল্পের শেষে আত্মাভিমানী দুলাল বখশিশ বাবদ বাকি তিপ্পান্ন পয়সা দোকানের কর্মচারীর হাতে দেয়। সে সেলাম জানায়। নিঃস্ব দুলাল গিরিকে নিয়ে বাড়ির পথ ধরে। গল্পের এই অংশের বর্ণনাটি তাৎপর্যপূর্ণ—
''কী লাভ হল, এই কথা দুলাল ভাবল। গুম গুম শব্দ হচ্ছে ট্রাম চলার। পায়ের নিচে ব্রিজটা থরথরিয়ে কাঁপছে। দুলালের মনে হল এত বড়ো লোহার জিনিসটা যদি ভেঙে পড়ে তাহলে সে মরে যাবে।''
গল্পের শুরুতে যে-শহর তার পরিচিত বলে দুলাল শ্লাঘাবোধ করেছিল, দিনান্তে সেখানে দাঁড়িয়ে সে পায়ের তলার মাটি খুঁজে পায় না। ভেঙে পড়া দুলালকে ভরসা জুগিয়ে 'যেন হাওড়া ব্রিজ বা বিশতলা বাড়ি দেখার বিস্ময় নিয়ে দুলালের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে' গিরিবালা জানায়, কর্মচারীটি যখন সেলাম করছিল তখন তাকে দেখতে দারগাবাবুর মতো লাগছিল। এভাবেই দিনের শেষে গ্রাম্য দম্পতির কাছে কলকাতা হয়ে ওঠে ভালোবাসার শহর। জীবনের বাস্তবতা ও মানবমনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির সমান্তরালে কলকাতার একাধিক পরিচিতি নির্মাণ করেছেন মতি নন্দী।

শহরে আসার আরেক আখ্যান 'ছ'টা পঁয়তাল্লিশের ট্রেন'। বিনোদ তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে কলকাতা বেড়াতে আসে। গড়ের মাঠ, ভিক্টোরিয়া, মনুমেন্ট কিংবা চিড়িয়াখানা দেখতে যাওয়াটা বাকিদের চাহিদা হলেও বিনোদ চেয়েছিল কলকাতায় তাদের পুরনো বাড়ি ঘুরে আসতে। শিকড়ের টানেই তার শহরে আসা। চিরাচরিত মুল্যবোধ ও নীতি-আদর্শে বিশ্বাসী বিনোদের কাছে কলকাতার তাৎপর্য এই ফিরে পাওয়ায়। পরিবারে, সমাজে যে বদলে যাওয়া সংস্কার, বিচার তার চোখে পড়ে, তার সঙ্গে একাত্ম হওয়া বিনোদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এই বদল ধরা পড়ে মন্তব্য ও প্রতি-মন্তব্যে। মেট্রো হলে সিনেমা দেখা বিনোদের কাছে অপছন্দের, কারণ সেখানে 'ইংরেজি বই দেখায়'। আবার সীতার কাছে ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক, কারণ, বিডিওর বড় মেয়ে কিছুদিন আগেই সেখানে এসে সিনেমা দেখে গেছে। 'শহরতলি'-তে বাস করা বিনোদ এভাবেই 'মহানগরে'-র সামাজিক রুচির পরিবর্তনকে চিনতে ব্যর্থ হয়। জাঁকজমক দ্রষ্টব্যস্থান ঘুরে আমোদ পাওয়ার বদলে নিজের পুরাতন, ক্ষয়ে যাওয়া বাড়িতে পা রেখে সে স্বস্তি অনুভব করে। চরিত্রগুলির অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে দু'টি আলাদা প্রজন্ম, আলাদা মানসিকতার বহিঃপ্রকাশকে তুলে ধরে মতি নন্দী আটের দশকের কলকাতার সামাজিক চেহারা ও তার রূপবদলকে আলোচ্য গল্পে প্রকাশ করতে চেয়েছেন।
এই পরিবর্তনের ছাপ সাতের দশকের শেষ থেকে নয়ের দশকের শুরু পর্যন্ত লেখা চতুর্থ সীমানা, কপিল নাচছে এবং ষোলোকে পনেরো করা— এই তিনটি গল্পগ্রন্থে স্পষ্ট দেখা যায়। ছয়ের দশকের গোড়া থেকেই বাঙালি জীবনে সমাজপ্রগতির লক্ষণ দেখা যেতে থাকে। সমাজোন্নয়নের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নানান পেশার উদ্ভব ঘটে। বাড়ে চাকুরিজীবীর সংখ্যা। আর এই সংখ্যাবৃদ্ধি বাঙালির চিরাচরিত যৌথ পরিবারব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলে। এই প্রসঙ্গে অমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য—
''এই ভাঙনের পথ ধরে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজ শেষ পর্যন্ত এমন একটি স্তরে এসে পৌঁছোয় যেখানে স্বামী, স্ত্রী ও তাঁদের সন্তানাদি নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্র একক পরিবারই হয়ে ওঠে বাঙালি সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই ক্ষুদ্র পরিবারের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছেলেমেয়েরা সংসারের আরও পাঁচজনকে ভালোবাসার ও তাঁদের সঙ্গে মানিয়ে চলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তারা অনিবার্যভাবেই আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর হয়ে ওঠে এবং এভাবেই বাঙালি জীবনে ধীরে ধীরে প্রকট হয়ে ওঠে স্বার্থসর্বস্বতা।''
অপেক্ষাকৃত বিত্তবানেরা নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি নিয়ে বাস করতে মহানগরের নানান প্রান্তে গজিয়ে ওঠা আবাসন, ফ্ল্যাট-বাহারি স্কাইলাইনে বাসা বাঁধে। আর যাদের আয় কম, তারা ব্যায়সংকোচের উদ্দেশে সরে যায় শহরতলি ঘেঁষে।
সাতের দশকের মাঝামঝি সময়ে লেখা গল্প 'চতুর্থ সীমানা'। চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত নিখিল কলকাতার বাইরে নতুন কলোনিতে দোতলা বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা করে। প্লট কিনে এভাবে বাড়ি তৈরির হুজুগ তখন সদ্য দেখা দিয়েছে। এই নির্মাণের ছবি গল্পে ফুটে উঠেছে এভাবে— ''কাঁচা ড্রেনের উপর সিমেন্টের সেতু। পার হয়ে কলোনির সদর। সোজা রাজপথ, কলোনিকে দুভাগ করে 'এ' এবং 'বি' ব্লক তৈরি করেছে। বাস চলাচলের রাস্তার ধার থেকেই বাড়িগুলো তৈরি হতে হতে পিছু হটেছে। প্রায় আধাআধি বাড়িতে ভরে গেছে। পিছন দিকে এখনও মাঠ। মাটি পড়ছে জমি ভরাট হচ্ছে। দু-চার বর্ষা না গেলে আর বাড়ি উঠবে না।'' বর্ণনায় 'পিছু হটছে' পুরনো কলকাতার সঙ্গে উদীয়মান শহরতলি ও সেখানে বসবাকারীদের স্থানিক ও মানসিক দূরত্বকে চিহ্নিত করে।
'জালি' গল্পের বিবরণও প্রায় অনুরূপ। সেখানে বিমানের বাড়ির পশ্চিমের বারান্দায় দাঁড়ালে দূরে ''বাস, মোটর, অটোরিক্সার চলাচল দেখা যায়। আরও দূরে দেখা যায় ট্রেন। বাড়িটার পিছনে এলিট আর স্কাইলাইন নামে দুটো হাউজিংইয়ের সীমানা— পাঁচিলের সংযোগ যেখানে হয়েছে তার পাশেই প্রায় বিঘা পাঁচেক সরকারি জমি।'' সুতরাং, শহর ছাড়িয়ে নির্জন, নিরিবিলি পরিবেশে বাস করা এই সময় মধ্যবিত্ত বাঙালির পরম প্রাপ্তি হয়ে উঠেছিল। পাশাপাশি শহরের জনবাহুল্য সম্পর্কেও তাদের মনে জন্ম নিচ্ছিল বীতরাগ। 'চতুর্থ সীমানা' গল্পে এই নির্জনতা প্রসঙ্গে নিখিলের মন্তব্য— ''নতুন জায়গা, একি কলকাতার মতো পুরনো?'' এই ব্যবধান, কলকাতা ছেড়ে চলে আসা কোথাও যেন মানবিক সম্পর্কেও বিচ্ছেদ ঘনিয়ে তোলে। রুবির নতুন পরিবার-পরিকল্পনায় তার শাশুড়ির ঠাঁই হয় না। বদলে জজ, অধ্যাপক, সাব-এডিটরদের মতো বিত্তবানদের সঙ্গে একই পরিসরে থাকতে পারার রোমাঞ্চে সে মশগুল হয়ে ওঠে। গল্পের শেষে যদিও পারিবারিক বন্ধনের ছবি আমাদের নজর কাড়ে। ছোটোকাকির অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা দিতে বিনোদকে গৃহ পরিকল্পনায় খরচ কমাতে হত। মানসিক টানাপড়েনের মধ্যে থাকতে থাকতে সে একসময় কল্পনায় দেখতে পায় তার পরিকল্পিত বাড়ির চতুর্থ পিলার হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ছোটোকাকিমা। নিজের ভালোবাসার মানুষটিকে বাঁচাতে অপরাধবোধে ক্লিন্ন নিখিল চিৎকার করে ওঠে— ''না, না, ছোটোকাকি যেও না, আমার জমির সীমানা তাহলে হারিয়ে যাবে।"
ছয়ের দশকের শুরুতে লেখা গল্প 'দুর্ঘটনা'-য় আমরা দেখি অশোক মনে মনে ভেবেছে— ''সুকুমার বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেল। আমিও পারি বিয়ে করে আলাদা হতে।'' কিন্তু বৃদ্ধা মা আর অবিবাহিতা বোনের কথা চিন্তা করে আলাদা হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সাতের দশকে এসে 'চতুর্থ সীমানা'-র নিখিল পুরোপুরি না হলেও এই পারিবারিক বন্ধন ছিঁড়ে প্রায় বেরিয়ে এসেছে। আর আটের দশকের শেষের দিকে লেখা গল্প 'কপিল নাচছে' কিংবা 'জালি'-তে আমরা আর কোনও যৌথ পরিবারের চিহ্নই খুঁজে পাই না— পাই না কোনও জনাকীর্ণ গলি বা পাড়ার বর্ণনা। কলকাতার বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ তখন শহরের এক কোণে কিংবা শহরতলির ফাঁকা পরিসরে গড়ে তুলেছে পছন্দের আবাসন। স্বাধীনতা-পরবর্তী বিভিন্ন দশকে বাঙালি সমাজ ও শহর কলকাতা কীভাবে তার চরিত্র বদলেছে, মতি নন্দীর গল্পের ধারা অনুসরণ করলে তার রূপরেখা বুঝে নেওয়া সম্ভব।
তথ্যসূত্র:
১. পাঠসারণীতে মতি নন্দী: রবিন পাল
২. নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান (সাক্ষাৎকার সংকলন)— মতি নন্দী
৩. মতি নন্দী: মানস চক্রবর্তী সম্পাদিত
৪. বাঙালি রাজনীতির পঞ্চাশ বছর: অমলকুমার মুখোপাধ্যায়




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp