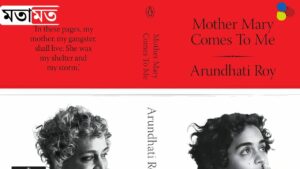বাঙালি দর্শকের অস্পৃশ্য উদাসীনতা ছিল ঋতুপর্ণর চিত্রঙ্গদার প্রতি
Rituparno Ghosh: "আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম যে, এই অগ্রজরা, যাঁদের আমরা নানাভাবে সমাজ বদলানোর কথা বলতে শুনেছি- বিকল্প যৌনতার সামনে এসে তাঁরা আসলে যে কী করুণভাবে চূড়ান্ত দক্ষিণপন্থী এবং রক্ষণশীল।"
একুশটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি, দু'টি তথ্যচিত্র, চারটি শর্ট ফিল্ম এবং চারটি টেলি ফিল্ম তৈরি করেছিলেন ঋতুপর্ণ ঘোষ। তবে, তাঁর ছবিগুলি যদি কেউ ধারাবাহিক পথে দেখতে-দেখতে আসেন তাঁর কাছে ‘চিত্রাঙ্গদা’ এক বিশেষ ও অন্য ধারার চলচ্চিত্ররূপে দেখা দিতে বাধ্য। আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়, তাঁর তৈরি ছবিগুলির মধ্যে ‘চিত্রাঙ্গদা’ অন্যতম। কেন? এখানেই এসে পড়ে একটি শব্দ- ‘সম্পর্ক’।
যখন মন নামক পাহাড়ের গভীর খাদে ঝুঁকে দেখা যায় না আর কিছুই, তখন সম্পর্কের মধ্যেকার রহস্য ফুরিয়ে যায়। এমন অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই রয়েছে। ‘চিত্রাঙ্গদা’-র ক্ষেত্রেও অনেক বছর আগে থেকে এমন এক সম্পর্ক তৈরি হয়ে আছে আমার মনে। বহু বার, বিশেষভাবে এই ছবিটি দেখেছি আমি। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, সিনেমার একটি দৃশ্যই বারংবার দেখেছি। আর, আমার সামনে খুলে গেছে সংকেত রহস্যময় শিল্পের সহস্র জানালা।
আফসোস হয়েছে এই ভেবে যে, সিনেমায় এত দূর গভীরে ভাবতে পেরেছিলেন যে-মানুষটা, এর পরবর্তী ছবিতে তিনি কী করতেন! জীবনের অজস্র সাক্ষাৎকারে ঋতুপর্ণ বলেছিলেন, ‘মহাভারত’ নিয়ে একটি ছবি বানানো ওঁর ইচ্ছে। কেমন হতো সেই ‘মহাভারত’, তাও জানতে ইচ্ছে করে।
এইসব ইচ্ছের কোনও শুশ্রূষা নেই, জানি কিন্তু যে ছবি থেকে এত-এত সংকেত-স্তর খুঁজে পাই, সেই ‘চিত্রাঙ্গদা’ রিলিজের পরের ঘটনাচিত্র কেমন ছিল? সে কথা তো জানতেই পারি আমরা। খুঁজতে খুঁজতে কয়েকটি তথ্য পেলাম। ‘নির্জন সিনে-মন’-এ ভাগ করে নিচ্ছি।

আরও পড়ুন- ঋতুপর্ণর চিত্রাঙ্গদা: ফেলে আসা প্রথম প্রেমের অবিচল চরণধ্বনি
৩১ মার্চ, ২০১৩। ‘সংবাদ প্রতিদিন’-এর ‘রোববার’-এ ‘চিত্রাঙ্গদা’ সম্পর্কে ঋতুপর্ণ ঘোষ লিখছেন:
৬০তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের ফলাফল ঘোষিত হয়ে গেল। আমার কপালে জুটল ‘চিত্রাঙ্গদা’-র জন্য বিশেষ জুরি পুরস্কার।
সংবাদমাধ্যম থেকে জানলাম যে, ‘চিত্রাঙ্গদা’-র এই বিশেষ পুরস্কার প্রাপক আমি। পরিচালক এবং প্রধান অভিনেতার কাজের স্বীকৃতি। চমৎকার!আমার প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘উনিশে এপ্রিল’। সেটা ছিল ১৯৯৩। তারপর ‘দহন’। এরপর গোটা এক দশক জুড়ে আমি ছিলাম বাঙালি দর্শকের ‘নয়নের মণি’, বাংলা সিনেমার ‘পোস্টার বয়’।
বাংলার এবং ভারতের নানা অগ্রণী, চলচ্চিত্র গোষ্ঠীর আন্তর্জাতিক বিশিষ্টরা আমার কাজ দেখে ‘ভালো’ বলেছেন, ‘বাহবা’ দিয়েছেন, ‘পিঠ’ চাপড়েছেন এবং এই করে দশটা বছর শান্তিতে কেটে গিয়েছে।
২০০৩-এ ‘চোখের বালি’। আমার সঙ্গে দর্শকের সর্বত্তুঙ্গ সেতু। কেবল নিখাদ প্রশংসার নয়, অনেক সমালোচনারও বটে। ‘কেন, বিনোদিনী কি কলকাতায় পাওয়া যেত না?’ ইত্যাদি। তা সত্ত্বেও, সব থেকে ইনটেন্স কোনও সম্পর্ক যদি আমার দর্শকের সঙ্গে স্থাপিত হয়ে থাকে- তাহলে সেটা ‘চোখের বালি’ দিয়ে।
একথা সত্য যে ‘চোখের বালি’ অনেক অর্থেই ঋতুপর্ণ ঘোষের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দর্শকের সঙ্গে পরিচালকের সংযোগ-মুহূর্তের সর্বোচ্চ অবস্থান যেমন এই ছবি, তেমনই ঋতুপর্ণ ঘোষের ফিল্ম কেরিয়ারকে যদি দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়, তার মধ্যবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চাইবে ‘চোখের বালি’।

ছবির একটি দৃশ্যে ঋতুপর্ণ ঘোষ ও কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়
আরও পড়ুন- মা আর সন্তানের নাড়ির স্বরে দেহের সংজ্ঞা লেখে ঋতুপর্ণর চিত্রাঙ্গদা
তাঁর চলচ্চিত্রজীবনের দু'টি পর্যায়ের কথা যখন এসেই পড়ল, তখন স্বীকার করতেই হয়, ‘চোখের বালি’-র পরবর্তী ছবিগুলি অনেক বেশি সংকেতবহুল, ফলে বাংলায় জনপ্রিয় না হওয়ার মতো অনেক ঐশ্বর্য সেসব ছবির ছিল। নিজের জীবনের এই সময়টা সম্পর্কে ঋতুপর্ণ বলছেন:
তারপর ধীরে ধীরে ঋতুপর্ণ ঘোষ বদলাতে লাগল। বাংলা সিনেমার নিটোল আবেগঘন পারিবারিক উপভোগের আয়োজনে কোথায় যেন প্রবেশ করল অস্বস্তি। ‘যৌনতা নিয়ে আবার এত বাড়াবাড়ি কেন?’ ঋতুপর্ণ-র ছবি মানেই নিত্যনতুন বলিউড আমদানি। তবু আমার দর্শকেরা নির্জলা বাঙালি-ভজনায় বাদ সাধলেও তখনও আমার নতুন ছবি বাঙালি দেখছেন।
এইবার সেই কঠিনতম অধ্যায়। ঋতুপর্ণ পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে পরপর তিনটে ছবিতে পৃথিবীর মূলধারার অন্যতম গোপন সিন্দুকটা খুললেন- যার নাম ‘সমকাম’। আমার দর্শকরা কিছুটা হলেও হতচকিত হলেন।
সব থেকে নিরাশ হলেন বাংলার মার্ক্সবাদী বিদগ্ধ বিশিষ্টরা। এবং আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম যে, এই অগ্রজরা, যাঁদের আমরা নানাভাবে সমাজ বদলানোর কথা বলতে শুনেছি- বিকল্প যৌনতার সামনে এসে তাঁরা আসলে যে কী করুণভাবে চূড়ান্ত দক্ষিণপন্থী এবং রক্ষণশীল। তাঁদের সমস্ত প্রতিবাদগুলোই কেবল অর্থনৈতিক অসাম্যের, গণতন্ত্রের এবং ধর্মনিরপেক্ষতার। তাঁদের বিপ্লবের মধ্যে যৌনতার স্থান নেই কোথাও।
ঠিক এইখানে আজ আমরা আসতে চাইব। এরপরই লেখাটিতে ঋতুপর্ণ সোজাসুজি কথা বলেছেন ‘চিত্রাঙ্গদা’ সম্পর্কে। বলেছেন, অন্তরের আনন্দ ও স্বীকৃতির কথা, যা তাঁর মন এবং ছবিটি সম্বন্ধে ঋতুপর্ণর ভাবনার ব-দ্বীপের কাছে পৌঁছিয়ে দেয় আমাদের। ঋতুপর্ণ লিখছেন:
গত বছর অগাস্ট মাসের শেষ দিনে ‘চিত্রাঙ্গদা’ মুক্তি পেল কলকাতা প্রেক্ষাগৃহে। অল্প কিছু মানুষের খুব ভালো লেগেছিল, তাঁরা আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, একদল আবার ছবি দেখে গুম হয়ে গিয়েছেন। আর বেশিরভাগ মানুষই বিষয়-বিতৃষ্ণা থেকে ছবিটা দেখতেই যাননি। আজ জাতীয় পুরস্কারের স্বীকৃতির কারণে যত ‘এসএমএস’ বা অভিনন্দন পাচ্ছি, তার ক্ষুদ্র একটি সংখ্যাকেও যদি দর্শক-সংখ্যার প্রতিনিধি বলে ভাবতে পারতাম, তা হলে ‘চিত্রাঙ্গদা’-কে কয়েক সপ্তাহ মাছি তাড়িয়ে উঠে যেতে হতো না।
একটাই অনুরোধ। যাঁরা তখন ছবিটিকে খারাপ ভেবেছিলেন, দয়া করে আজ সরকার-প্রদত্ত রজত কমলের দ্যুতিতে নিজের মতামত জোর করে সংশোধন করবেন না।
মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি ‘চিত্রাঙ্গদা’-র জন্য পুরস্কার লাভ আমার কাছে আমার বাকি সব ক’টি জাতীয় পুরস্কারের থেকে অনেক মূল্যবান।
আমাদের মনে হতে পারে, এক অভিমানস্বর এখানে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে ঋতুপর্ণকে। সেই অভিমানের সঙ্গে যেন-বা কিছু আক্রমণের ভঙ্গিমাও মিলেমিশে আছে। কিন্তু ছবিটির কাছে বারংবার দাঁড়ালে, এই ধারণা পালটে যায়। তখন মনে হয়, এ কেবল একজন বড় আর্টিস্টের অসহায়তার আর্তি।
আরও পড়ুন- সমপ্রেমের আলোয় রবীন্দ্রনাথের ‘চিত্রাঙ্গদা’-কে নতুন করে দেখেছিলেন ঋতুপর্ণ

কেন হয় এমন? কারণ, একইসঙ্গে ঋতুপর্ণ বলছেন তাঁর কাছে ‘চিত্রাঙ্গদা’-র জন্য প্রাপ্ত রাষ্ট্রীয় সম্মান অন্য জাতীয় পুরস্কারগুলির থেকে বেশি মূল্যবান, আবার এই ঋতুপর্ণই ছবিটি রিলিজের পরপর একটি সাক্ষাৎকারে নিজেই স্বীকার করে নিচ্ছেন, ছবিটিতে তাঁর কী কী ভুল রয়ে গেল! অর্থাৎ, নিরপেক্ষতার অবস্থান থেকে তিনি বিচ্যুত হননি কখনও। সাক্ষাৎকারটিতে ঋতুপর্ণ বলছেন:
There are a few technical flaws. For instance, in sexual reassignment surgery, so much of hormones are injected in you that your voice changes. I knew about it but didn’t go for it… Second, all the stage scenes have been shown from the audience’s perspective. A choreographer doesn’t view the stage like the audience does. He moves around, sees it from various angles. I should have kept that in mind. I also feel the scene featuring Kaushiki (Chakrabarty) on stage should have been designed more intelligently. It’s too much of a crowd at the center… Actually, I couldn’t oversee the scenes that had me in them.
Besides, some people have told me that they felt the dancer part of Rudra (a choreographer, played by Rituparno) has not been established well. I was aware of it. Juggling acting, costumes and direction wasn’t easy. Then I would have had to learn dance three months earlier than when I started.
পাঠকমাত্রই, বুঝতে পারছেন ঋতুপর্ণ কতখানি নিরপেক্ষ এবং পক্ষপাতহীন ছিলেন নিজের শিল্পকর্ম সম্পর্কে। এই সাক্ষাৎকারে বলা কথাগুলিকে আমরা যেমন মনে রাখতে চাইব, ত্রুটি হিসেবে ভাবতে চাইব যে, ‘চিত্রাঙ্গদা’-য় যা দেখছি তার বিপরীতে কী কী করা সম্ভব হতো, তেমনই বাংলায় আজ থেকে এক দশক আগে রিলিজ করা এমন আশ্চর্য এক সিনেমা সম্পর্কে বাঙালি দর্শকের অস্পৃশ্য উদাসীনতাকেও আমরা যেন মনে রাখি! কারণ, ঋতুপর্ণ ঘোষের চলচ্চিত্রচর্চায় এই ঘটনা আরও অজস্র তাচ্ছিল্যের মতোই গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস-তথ্য!




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp