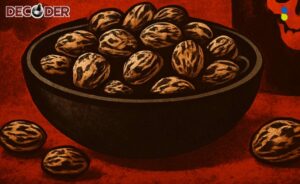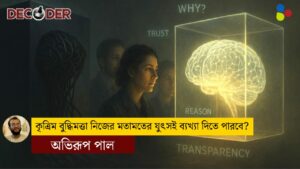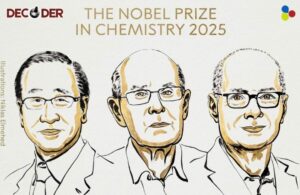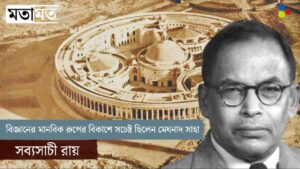QR Code: যা স্ক্যান করছেন তা আদৌ নিরাপদ তো?
QR Code Scan: যখন কোনও ব্যক্তি কিউআর কোড স্ক্যান করেন, তখন তাঁর ফোনের ক্যামেরার কিউআর রিডার কোডটি পড়ে, ফলে ওই কোডে থাকা তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাঁর ফোনে একটি অ্যালগরিদম চালু করে।
না শুধু টাকা পয়সা লেনদেনের জন্য নয়, বইমেলার বুকলিস্ট থেকে আরম্ভ করে রেস্তোরাঁর খাবারের মেনুকার্ড, সবই এখন কিউআর কোডে উপলব্ধ। একটা ছোট বর্গাকার জায়গায় আঁকা হিজিবিজি কোড দেখতে দেখতে আমরা এমনই অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, চোখে আলাদা করে আর কিছু মনেও হয় না। কী আছে ওই হিজিবিজি ডটগুলোর মধ্যে? কী নেই! নাড়ি- নক্ষত্র সব ভরা আছে ওর ভিতরে। ‘কুইক রেসপন্স কোড’ বা সংক্ষেপে ‘কিউআর কোড’, ‘বার কোডের’-ই অনেক উন্নত সংস্করণ বলা যেতে পারে। ‘বার কোডে’ সর্বোচ্চ ২০টি তথ্য সংরক্ষিত রাখা যায়। যেকোনও নামী-দামী ব্র্যান্ডের পণ্যের গায়ে লেবেলের সঙ্গে বারকোড লাগানো থাকে। এতে পণ্যটির দাম, প্যাকেটবন্দি হওয়ার তারিখ— এসব লেখা থাকে। এটিকে সাধারণত যেকোনও এক দিক থেকে স্ক্যান করতে হয়, কারণ এতে অনুভূমিক দিক বরাবর তথ্য রক্ষিত থাকে। অপরদিকে কিউআর কোডে অনেকগুলো গ্রিডে তথ্য সুরক্ষিত থাকে, সেজন্য বার কোডের তুলনায় এক্ষেত্রে অনেক বেশি তথ্য ধরে রাখা সম্ভব সবচেয়ে ছোট গ্রিডে ২১টি সারি এবং ২১টি স্তম্ভ এবং সবচেয়ে বড় গ্রিডে ১৭৭টি স্তম্ভ এবং ১৭৭টি সারি থাকে, গাণিতিকভাবে বললে ম্যাট্রিক্স আকারে সজ্জিত থাকে সমস্ত তথ্য।
জাপানি গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থা, ডেনসো ওয়েভের এক প্রকৌশলী, মাসাহিরো হারা ‘গো’ (Go) নামের এক খেলা খেলছিলেন। এর উপকরণ খুবই সাদামাটা। একটা পাথর বা বোর্ডের ওপর খোপ খোপ বর্গাকার দাগ কাটা থাকে, যেখানে সাদা ও কালো দু'ধরনের পাথর দিয়ে খেলা হয়। হারা এই খেলা খেলতে গিয়ে আবিষ্কার করে ফেলেন কিউআর কোড।
আরও পড়ুন- যত্রতত্র কিউআর কোড স্ক্যান করছেন, কী ভয়াবহ বিপদ লুকিয়ে রয়েছে জানেন?
এখন তো অনলাইনে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে খুব সহজেই কিউআর কোড তৈরি করা যায়। এর মূলত দু'টি অংশ রয়েছে— এনকোডার ও ডিকোডার। এনকোডার প্রদত্ত তথ্যগুলিকে কিউআর কোডে রূপান্তরিত করে। আবার, কোনও স্ক্যানিং ডিভাইস দিয়ে কোডটি স্ক্যান করা হলে, এনকোড করা তথ্যগুলিকে ডিকোড করতে কাজে লাগে ডিকোডার। সাধারণত গ্রিডে সাজানো বর্গাকার খোপ খোপ বিন্দুগুলিতে চার রকম কায়দায় তথ্য জমা থাকে— অক্ষর, সংখ্যা বা অক্ষর-সংখ্যা মিশিয়ে মানে আলফানিউমেরিক বিন্যাসে, বাইনারি (কেবল ০ ও ১ ব্যবহার করে) এবং 'কাঞ্জি' (চিনা অক্ষর ব্যবহার করে জাপানি লেখার রীতি) পদ্ধতিতে। যত বেশি তথ্য লুকনো থাকবে, কোডগুলি তত জটিল হতে থাকবে ক্রমশ।

বর্গাকার এই কোডের তিন কোণায় আরও তিনটি বর্গাকার খোপ থাকে, যেগুলি কিউআর কোড শনাক্তকরণে কাজে লাগে। প্রকৌশলীরা এদের বলেন ‘ফাইন্ডার প্যাটার্ন'। কোডের চারপাশে যে সাদা ফাঁকা মার্জিন অঞ্চল থাকে, তার নাম ‘কোয়াইট জোন’ , যেটি স্ক্যানারকে কোডটি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আলাদা করতে সাহায্য করে। ‘ফাইন্ডার প্যাটার্ন'-গুলির চারপাশে একটি সাদা ফাঁকা জায়গা থাকে, যেটি এনকোডিং অঞ্চলকে নিখুঁতভাবে শনাক্ত করতে স্ক্যানারকে সাহায্য করে, এর নাম ‘সেপারেটর’।
এই সেপারটরের মধ্যে থাকা অনুভূমিক ও উলম্বভাবে সাজানো যে ‘টাইমিং প্যাটার্ন’ থাকে, সেটি কোডের আকার, ঘনত্ব, স্থানাঙ্ক এবং সংস্করণ (version) বুঝতে সাহায্য করে। আর বর্গাকার কিউআর কোডের ডানদিকের চতুর্থ কোণে ছোট বর্গাকার প্যাটার্ন লক্ষ্য করা যায়, যেটি কোডের পঠনযোগ্যতা ও অ্যালাইনমেন্ট, এসব ব্যাপার পুখানুপুঙ্খভাবে খেয়াল রাখে। সেগুলির নাম ‘অ্যালাইমেন্ট জোন’।
কীভাবে কাজ করে এই কোড?
কিউআর কোডের বর্গাকার গ্রিডগুলি গুচ্ছ গুচ্ছ বিন্দুর সমাহার। প্রতিটি কালো বিন্দুগুলিতে ১ ও খালি ঘরগুলিতে ০ আছে বলে ধরা হয়। সমস্ত তথ্য বাইনারি পদ্ধতিতে সঞ্চিত থাকে, কারণ কম্পিউটার আবার ০ ও ১ ছাড়া কিছুই বোঝে না। এই গ্রিডগুলিতে কোনও ওয়েব অ্যাড্রেসের ইউআরএল, ছবি, ভিডিও, গুগল লিঙ্কসহ আরও অনেক তথ্য সংরক্ষিত থাকে। যখন কোনও ব্যক্তি কিউআর কোড স্ক্যান করেন, তখন তাঁর ফোনের ক্যামেরার কিউআর রিডার কোডটি পড়ে, ফলে ওই কোডে থাকা তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাঁর ফোনে একটি অ্যালগরিদম চালু করে। যদি কিউআর কোডে একটি ইউআরএল সংযুক্ত থাকে, তাহলে তাতে ক্লিক করা মাত্রই পৌঁছে যাওয়া যাবে কাঙ্খিত সাইটে।
আরও পড়ুন- নিরুদ্দেশ মানুষকে খুঁজবে কিউআর লকেট! ২৪-এর তরুণের আবিষ্কার ঘিরে শোরগোল দেশে
কিউআর-এর ফাঁদ
যেখানে হাত ছোঁয়ালেই রয়েছে মুশকিল আসান, তার আড়ালে থাকা বিপদ অনেকসময়ই আমরা টের পাই না। আসলে যে জিনিস যত ভালো, তার নকল বেরোয় তত তাড়াতাড়ি। বর্তমান সাইবার অপরাধের দুনিয়ায় এই বিষয়টি যেন আরও বেশি করে সত্যি। হ্যাকাররা অনেক সময় এর সঙ্গে সন্দেহজনক ইউআরএল যুক্ত করে রাখে, তখন ব্যবহারকারী স্ক্যান করার পর সেই লিঙ্কে আঙুল ছোঁয়ানো মাত্রই ঢুকে পড়বেন কোনও অজানা ওয়েহসাইটে, যেখান থেকে তাঁর স্মার্টফোন, বা ডিভাইসে ঢুকে পড়তে পারে ম্যালওয়্যার বা ভাইরাস। অনেক সময় যে অ্যাপ দিয়ে আমরা কিউআর স্ক্যান করি, তার নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো না হওয়ায় সেখান থেকে আমাদের মোবাইল বা ল্যাপটপে ঢুকে পড়তে পারে ম্যালওয়্যার। এর থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য স্ক্যান করার পর দেখে নিতে হবে সুরক্ষিত ওয়েবসাইটে ঢুকছি কিনা। আর যেসব ইন্টারফেস ব্যবহার করে আমরা স্ক্যান করছি সবসময় সতর্ক থাকতে হবে, সেগুলি প্লে-স্টোর থেকে ডাউনলোড করা কিনা! কোনও এপিকে ফাইল বা সামাজিক মাধ্যমে পাঠানো কোনও লিঙ্ক ব্যবহার করে ডাউনলোড করা নয়তো?
সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের একটি ঘটনা বলে লেখার ইতি টানা যাক। এক বিরিয়ানির দোকানে গ্রাহকরা টাকা মেটাচ্ছেন কিউআর কোড স্ক্যান করে। কিন্তু পরে বিক্রেতা দেখেন যে, তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কোনও টাকাই আসেনি! ব্যাঙ্কে খোঁজ নিয়ে দেখেন, তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কোনও সমস্যা নেই। উপায়ান্তর না দেখে থানায় অভিযোগ করেন বিক্রেতা। পুলিশ তদন্তে নেমে রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজে দেখতে পায়, মুখ ঢেকে এক ব্যক্তি গভীর রাতে কিউ আর কোডগুলো বদলে নতুন কোড সেঁটে যাচ্ছে দোকানে। পরদিন গ্রাহক টাকা পাঠালে তা জমা পড়ছে দুষ্কৃতীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে! সেই জন্য টাকা পাঠানোর পর দু'পক্ষরই দেখে নেওয়া উচিত টাকা ঠিকঠাক জায়গায় জমা পড়ছে তো? সেই সঙ্গে খেয়াল রাখা উচিত স্ক্যান করার সময় কোনও অবাঞ্ছিত তথ্য চাওয়া হচ্ছে কিনা। নাহলে ১০ টাকা পেমেন্ট করতে গিয়ে বা লোভনীয় খাবারের রিভিউ দিতে গিয়ে গ্রাহক সর্বস্বান্ত হতেই পারেন কারণ, হ্যাকারের ফাঁদ আন্তর্জালের সবখানেতেই পাতা।




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter LinkedIn
LinkedIn
 Whatsapp
Whatsapp